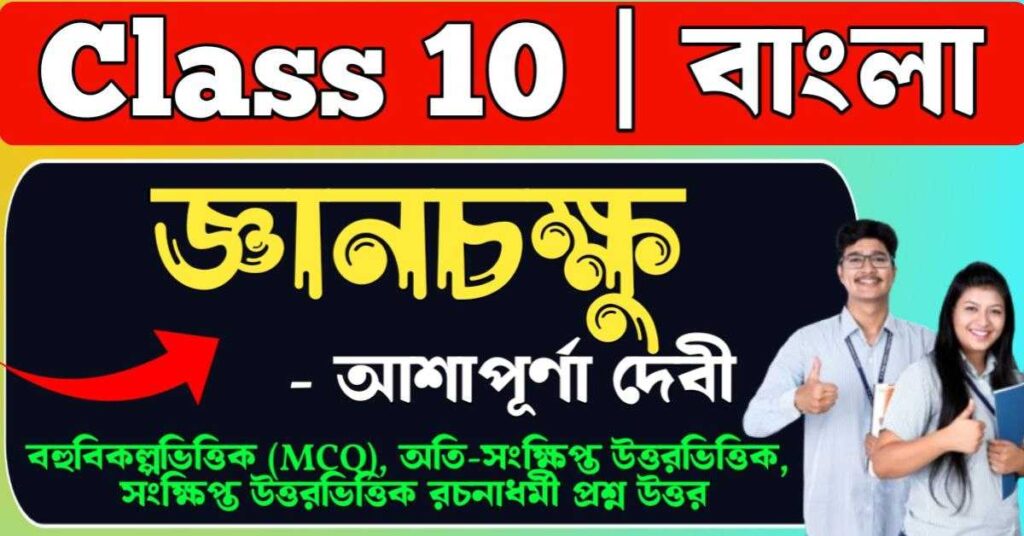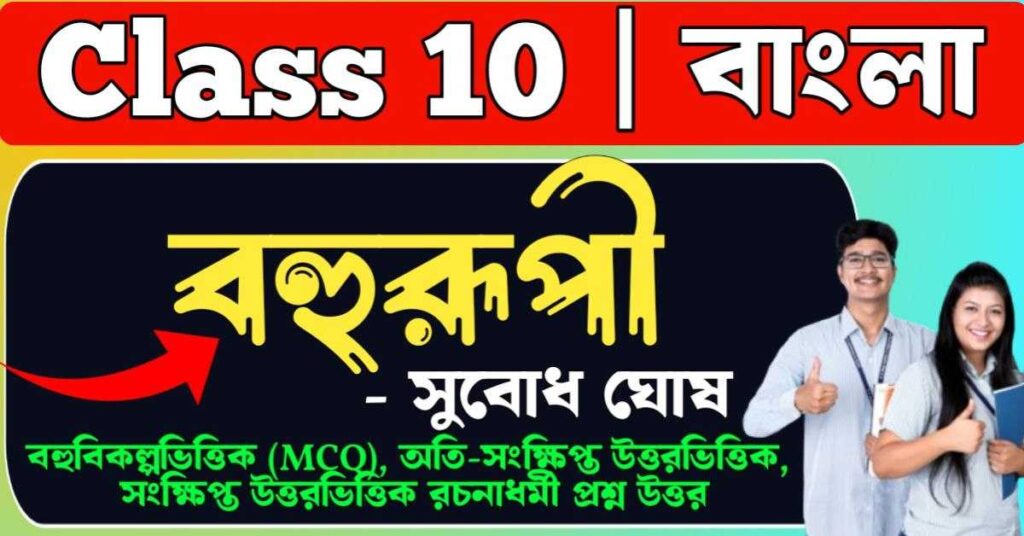আফ্রিকা কবিতার প্রশ্ন উত্তর
আফ্রিকা ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর )
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৫০টি)
১. ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি কার লেখা?
২. ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
৩. স্রষ্টা আফ্রিকাকে কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?
৪. “এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে” – ‘ওরা’ কারা?
৫. “সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী” – ‘পুণ্যবাণী’টি কী?
৬. ‘বনস্পতির নিবিড় পাহারায়’ কে ছিল?
৭. স্রষ্টা কীসে অধৈর্য হয়েছিলেন?
৮. “নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার…” – কার চেয়ে?
৯. ‘মানহারা মানবী’ বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
১০. ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ কীসের রূপ ধরে এসেছিল?
১১. “বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে” – কীভাবে?
১২. “চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।” – কারা?
১৩. আফ্রিকার অপমানিত ইতিহাসের চিহ্ন কেমন?
১৪. ‘যুগান্তরের কবি’ কখন আসবেন?
১৫. ‘নিভৃত অবকাশে’ আফ্রিকা কী সংগ্রহ করছিল?
১৬. আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের রক্ত ও অশ্রুতে কী মিশেছিল?
১৭. ‘পত্রপুট’ কাব্যগ্রন্থটি প্রথম কবে প্রকাশিত হয়?
১৮. “শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে” – কীভাবে?
১৯. ‘পঙ্কিল’ শব্দটির অর্থ কী?
২০. আফ্রিকার ‘ছায়াবৃতা’ রূপ কোথায় ছিল?
২১. স্রষ্টা আফ্রিকাকে কী দিয়ে বেঁধেছিলেন?
২২. ‘অন্তঃপুর’ বলতে কী বোঝায়?
২৩. “সেই মুহূর্তে তাদের…” – কাদের কথা বলা হয়েছে?
২৪. সাম্রাজ্যবাদীদের মন্দিরে কী বাজছিল?
২৫. ‘কালো ঘোমটা’ কিসের প্রতীক?
২৬. “শিশুরা খেলছিল…” – কোথায়?
২৭. ‘ছিন্নভিন্ন’ হল কে?
২৮. ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ – এই অলঙ্কারটি হল–
২৯. আফ্রিকার বাষ্পাকুল অরণ্যপথে কী ছিল?
৩০. ‘যুগান্তরের কবি’কে কবি কী করতে বলেছেন?
৩১. “পরিচয়हीनতার কালো ঘোমটার নীচে” – কার কথা বলা হয়েছে?
৩২. ‘দুর্বোধ সংকেত’ কোথায় ছিল?
৩৩. ‘লোহার হাতকড়ি’ কীসের প্রতীক?
৩৪. “অভিশাপ দিচ্ছিল…” – কাকে?
৩৫. ‘মানুষ-ধরার দল’ কাদের বলা হয়েছে?
৩৬. ‘তান্ডব’ কীসের?
৩৭. আফ্রিকাকে কারা পাহারা দিচ্ছিল?
৩৮. ‘দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে’ – এই আহ্বান কার প্রতি?
৩৯. ‘কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে’ – এই চিত্রকল্পটি কী বোঝায়?
৪০. “গর্বে অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে” – কাদের কথা বলা হয়েছে?
৪১. আফ্রিকার ইতিহাসে কিসের চিহ্ন রয়েছে?
৪২. ‘আফ্রিকা’ কবিতায় কোন সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে?
৪৩. ‘দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতো’ – কাদের?
৪৪. সাম্রাজ্যবাদীদের দেবতা কেমন ছিল?
৪৫. কবি কাকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন?
৪৬. ‘তান্ডবের দুন্দুভিনিনাদ’ – এখানে ‘দুন্দুভি’ কী?
৪৭. আফ্রিকার প্রকৃতি কেমন ছিল?
৪৮. “অপরিচিত ছিল তোমার…” – কী?
৪৯. ‘আফ্রিকা’ কবিতায় কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠেছে?
৫০. “আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে” – এই সময়টি কীসের ইঙ্গিত দেয়?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৪০টি)
১. ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর: ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি ‘পত্রপুট’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
২. স্রষ্টা আফ্রিকাকে কোথা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন?
উত্তর: স্রষ্টা আফ্রিকাকে প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।
৩. আফ্রিকাকে কে পাহারা দিচ্ছিল?
উত্তর: বনস্পতিরা নিবিড় পাহারা দিয়ে আফ্রিকাকে আড়াল করে রেখেছিল।
৪. নিভৃত অবকাশে আফ্রিকা কী সংগ্রহ করছিল?
উত্তর: নিভৃত অবকাশে আফ্রিকা দুর্গমের রহস্য সংগ্রহ করছিল।
৫. “বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে” – কীভাবে?
উত্তর: বিরূপের ছদ্মবেশে ভীষণকে বিদ্রূপ করছিল।
৬. কারা লোহার হাতকড়ি নিয়ে এসেছিল?
উত্তর: ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে এসেছিল।
৭. ‘মানুষ-ধরার দল’ কাদের বলা হয়েছে?
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদী দাস ব্যবসায়ীদের ‘মানুষ-ধরার দল’ বলা হয়েছে।
৮. আফ্রিকার অপমানিত ইতিহাসে কারা চিরচিহ্ন দিয়ে গেল?
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা তাদের কাঁটা-মারা জুতোর তলায় আফ্রিকার অপমানিত ইতিহাসে চিরচিহ্ন দিয়ে গেল।
৯. ‘মানহারা মানবী’ কে?
উত্তর: ‘মানহারা মানবী’ হল অপমানিত, লাঞ্ছিত আফ্রিকা।
১০. ‘যুগান্তরের কবি’কে কবি কী করতে বলেছেন?
উত্তর: ‘যুগান্তরের কবি’কে কবি মানহারা আফ্রিকার দ্বারে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে বলেছেন।
১১. আফ্রিকার বাষ্পাকুল অরণ্যপথে কী ছিল?
উত্তর: আফ্রিকার বাষ্পাকুল অরণ্যপথে তার অপমানিত ইতিহাসের পঙ্কিল চিহ্ন ছিল।
১২. সাম্রাজ্যবাদীদের মন্দিরে কী বাজছিল?
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদীদের মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যায় পূজার ঘণ্টা বাজছিল।
১৩. আফ্রিকার শিশুরা কোথায় খেলছিল?
উত্তর: আফ্রিকার শিশুরা মায়েদের কোলে খেলছিল।
১৪. ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ কেমন রূপ ধারণ করেছিল?
উত্তর: ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ নগ্ন রূপ ধারণ করেছিল।
১৫. ‘কালো ঘোমটা’র নীচে কী অপরিচিত ছিল?
উত্তর: ‘কালো ঘোমটা’র নীচে আফ্রিকার মানবিক রূপ অপরিচিত ছিল।
১৬. ‘পঙ্কিল’ শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ লেখো।
উত্তর: ‘পঙ্কিল’ শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ হলো কর্দমাক্ত।
১৭. ‘দুন্দুভি’ কী?
উত্তর: ‘দুন্দুভি’ হলো দামামা জাতীয় এক ধরনের বড় রণবাদ্য।
১৮. আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা কীসের মন্ত্র জাগাচ্ছিল?
উত্তর: আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা প্রকৃতির চেতনাতীত মনে মন্ত্র জাগাচ্ছিল।
১৯. ‘নগ্ন রূপ’ কীসের?
উত্তর: সভ্য মানুষের বর্বর লোভের নগ্ন রূপের কথা বলা হয়েছে।
২০. “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে” – কখন দাঁড়াতে বলা হয়েছে?
উত্তর: আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে দাঁড়াতে বলা হয়েছে।
২১. স্রষ্টা কেন অধৈর্য হয়েছিলেন?
উত্তর: নতুন সৃষ্টিকে বারবার বিধ্বস্ত করার কারণে স্রষ্টা অধৈর্য হয়েছিলেন।
২২. ‘বনস্পতি’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘বনস্পতি’ শব্দের অর্থ হলো বিশাল আকৃতির গাছ বা মহীরুহ।
২৩. “শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে” – কীভাবে?
উত্তর: নিজেকে উগ্র ও ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ করে শঙ্কাকে হার মানাতে চাইছিল।
২৪. সাম্রাজ্যবাদীদের নখ কার চেয়ে তীক্ষ্ণ ছিল?
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদীদের নখ আফ্রিকার নেকড়ের চেয়েও তীক্ষ্ণ ছিল।
২৫. আফ্রিকার ইতিহাসে কাদের পায়ের চিহ্ন রয়েছে?
উত্তর: আফ্রিকার ইতিহাসে দস্যু বা সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ের চিহ্ন রয়েছে।
২৬. আফ্রিকার আলো কেমন ছিল?
উত্তর: আফ্রিকার আলো ছিল কৃপণ বা স্বল্প।
২৭. রুদ্র সমুদ্রের বাহু কী করেছিল?
উত্তর: রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।
২৮. ‘অন্তঃপুর’ শব্দটি কবিতায় কোন অর্থে ব্যবহৃত?
উত্তর: ‘অন্তঃপুর’ শব্দটি কবিতায় আফ্রিকার গভীর, রহস্যময় ও সুরক্ষিত অরণ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
২৯. কবি যুগান্তরের কবিকে কী ঘোষণা করতে বলেছেন?
উত্তর: কবি যুগান্তরের কবিকে ‘ক্ষমা করো’—এই পুণ্যবাণী ঘোষণা করতে বলেছেন।
৩০. ‘ছায়াবৃতা’ কে?
উত্তর: ‘ছায়াবৃতা’ হলো আফ্রিকা।
৩১. “অভিশাপ দিচ্ছিল…” – কাকে?
উত্তর: অদৃষ্টকে অভিশাপ দিচ্ছিল।
৩২. সাম্রাজ্যবাদীদের দেবতা কী করছিল?
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদীদের দেবতা কোনো প্রতিবাদ না করে চুপচাপ পূজার ঘণ্টার শব্দ শুনছিল।
৩৩. ‘প্রাচী ধরিত্রী’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: ‘প্রাচী ধরিত্রী’ বলতে এশিয়া ও ইউরোপ সহ মূল ভূখণ্ডকে বোঝানো হয়েছে।
৩৪. আফ্রিকার অরণ্যকে ‘সূর্যহারা’ বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: কারণ আফ্রিকার অরণ্য এতটাই ঘন ছিল যে, সেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না।
৩৫. ‘অপরিচিত’ কী ছিল?
উত্তর: আফ্রিকার মানবিক রূপ অপরিচিত ছিল।
৩৬. ‘মানুষ-ধরার দল’ গর্বে কেমন ছিল?
উত্তর: ‘মানুষ-ধরার দল’ গর্বে অন্ধ ছিল।
৩৭. ‘বাষ্পাকুল অরণ্যপথ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: ‘বাষ্পাকুল অরণ্যপথ’ বলতে আফ্রিকার স্যাঁতস্যাঁতে, ঘন জঙ্গলের পথকে বোঝানো হয়েছে, যা কান্না বা অশ্রুতে ভেজা।
৩৮. ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা?
উত্তর: ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি গদ্যছন্দে লেখা।
৩৯. “বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে” – ‘ভীষণ’ কে?
উত্তর: ‘ভীষণ’ হলো প্রতিকূল, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি।
৪০. ‘শেষ পুণ্যবাণী’ কী হবে?
উত্তর: ‘শেষ পুণ্যবাণী’ হবে ‘ক্ষমা করো’।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ৩ (২৫টি)
১. “ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা” – কে, কোথা থেকে, কীভাবে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?
উত্তর: কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, স্রষ্টা তাঁর নতুন সৃষ্টিতে অধৈর্য হয়ে প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রুদ্র সমুদ্রের বাহু দিয়ে তিনি আফ্রিকাকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে বনস্পতির নিবিড় পাহারার মধ্যে নির্বাসিত করেছিলেন।
২. “বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে/বিরূপের ছদ্মবেশে” – পঙক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: এই পঙক্তিটির মাধ্যমে কবি আফ্রিকার আদিম, প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে তার অধিবাসীদের সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন। ‘ভীষণ’ বলতে ভয়ঙ্কর প্রকৃতি এবং ‘বিরূপের ছদ্মবেশ’ বলতে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য নিজেদের ভয়ঙ্কর ও উগ্র রূপে সাজিয়ে তোলাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আফ্রিকা ভয়কে জয় করার জন্য নিজেই ভয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল।
৩. “এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে” – ‘ওরা’ কারা? তাদের আগমনের কারণ ও পরিণতি কী হয়েছিল?
উত্তর: এখানে ‘ওরা’ বলতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দাস ব্যবসায়ীদের বোঝানো হয়েছে। তাদের আগমনের কারণ ছিল আফ্রিকার সম্পদ লুণ্ঠন এবং সেখানকার মানুষদের দাসে পরিণত করা। এর পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ। তারা আফ্রিকার শান্তি ও স্বাধীনতা হরণ করে, সেখানকার মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং আফ্রিকার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে।
৪. “সভ্যের বর্বর লোভ/নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।” – ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ একটি विरोधाभाস অলঙ্কার। এখানে ‘সভ্য’ বলতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের সভ্য বলে দাবি করত। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ ছিল বর্বর বা অসভ্যদের মতো। তারা আফ্রিকার সম্পদ লুণ্ঠন ও মানুষ কেনাবেচার মতো যে নির্লজ্জ ও অমানবিক কাজ করেছিল, তাকেই কবি ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ বলেছেন।
৫. “চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।” – কারা, কীভাবে চিরচিহ্ন দিয়ে গেল?
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা আফ্রিকার অপমানিত ইতিহাসে চিরচিহ্ন দিয়ে গেল। তারা আফ্রিকাকে শোষণ ও শাসন করতে এসে সেখানকার মানুষদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, তাদের রক্ত ও অশ্রুতে নিজেদের পথকে কর্দমাক্ত করেছিল, সেই কলঙ্কের দাগই আফ্রিকার ইতিহাসে চিরস্থায়ী চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। তাদের কাঁটা-মারা জুতোর তলার কাদার পিণ্ড সেই কলঙ্কেরই প্রতীক।
৬. ‘মানহারা মানবী’ বলে আফ্রিকাকে সম্বোধন করার কারণ কী?
উত্তর: কবি আফ্রিকাকে একজন নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যেভাবে আফ্রিকার সম্পদ, স্বাধীনতা এবং সম্মান হরণ করেছে, তা যেন এক নারীর সম্মান হরণের সমান। আফ্রিকার এই লাঞ্ছিত, অপমানিত অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্যই কবি তাকে ‘মানহারা মানবী’ বলে সম্বোধন করেছেন।
৭. “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;/বলো ‘ক্ষমা করো’ ” – কবি কাকে, কেন ক্ষমা চাইতে বলেছেন?
উত্তর: কবি ‘যুগান্তরের কবি’ অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিবেকবান কবি বা মানবসমাজকে এই আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ক্ষমা চাইতে বলেছেন কারণ, সভ্য ইউরোপীয়রা আফ্রিকার উপর যে অকথ্য অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছে, তা সমগ্র মানবজাতির জন্য এক লজ্জার বিষয়। সেই সম্মিলিত পাপের স্খালনের জন্য এবং আফ্রিকার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য কবি ক্ষমা চাইতে বলেছেন।
৮. “সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী” – কোন বিষয়টিকে ‘পুণ্যবাণী’ বলা হয়েছে এবং কেন?
উত্তর: ‘ক্ষমা করো’—এই কথাটিকেই ‘পুণ্যবাণী’ বলা হয়েছে। ক্ষমা চাওয়া হলো নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়ার লক্ষণ। সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা আফ্রিকার উপর যে পাপ করেছে, সেই পাপ স্খালনের একমাত্র পথ হলো অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা। এই কাজটি একটি পুণ্যের কাজ, তাই কবি একে ‘পুণ্যবাণী’ বলেছেন এবং চেয়েছেন এটিই যেন সভ্যতার শেষ কথা হয়।
৯. আফ্রিকার আদিম রূপের বর্ণনা দাও।
উত্তর: কবিতার শুরুতে আফ্রিকার আদিম রূপের এক রহস্যময় বর্ণনা পাওয়া যায়। স্রষ্টা তাকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় রেখেছিলেন। তার অরণ্য ছিল ঘন, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছত না (‘কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে’)। তার প্রকৃতি ছিল রহস্যময় এবং তার অধিবাসীরা প্রকৃতির ভয়ঙ্করতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে উগ্র রূপে নিজেদের প্রকাশ করত।
১০. ‘পত্রপুট’ কাব্যগ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা কী?
উত্তর: ‘পত্রপুট’ কথার অর্থ হলো পাতার ঠোঙা। কবি যেন চিঠির আকারে তাঁর নানা ভাবনা, অনুভূতি ও বক্তব্যকে এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত করেছেন। ‘আফ্রিকা’ কবিতাটিও যেন আফ্রিকার প্রতি লেখা একটি চিঠি, যেখানে তার জন্ম, লাঞ্ছনা এবং ভবিষ্যতের প্রতি এক মানবিক আবেদন রয়েছে। এই আঙ্গিকের দিক থেকে কাব্যগ্রন্থের নামকরণটি সার্থক।
১১. “শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে” – কে, কীভাবে শঙ্কাকে হার মানাতে চাইছিল?
উত্তর: আফ্রিকার আদিম প্রকৃতি এবং তার অধিবাসীরা শঙ্কাকে হার মানাতে চাইছিল। ‘শঙ্কা’ বলতে এখানে প্রতিকূল প্রকৃতি এবং অজানা বিপদকে বোঝানো হয়েছে। তারা নিজেদের উগ্র, ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ করে এবং তান্ডবের দ্বারা প্রকৃতির চেতনাতীত মনে মন্ত্র জাগিয়ে এই ভয়কে জয় করতে চাইছিল।
১২. “কালো ঘোমটার নীচে/অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ” – ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: ‘কালো ঘোমটা’ হলো আফ্রিকার রহস্যময়, দুর্গম প্রকৃতি এবং তার বাহ্যিক উগ্রতার প্রতীক। বাইরের জগৎ আফ্রিকার এই বাহ্যিক রূপটিকেই চিনত। কিন্তু এই আবরণের নীচে যে একটি মানবিক সত্তা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা রয়েছে, তা ছিল সকলের কাছে অপরিচিত। সাম্রাজ্যবাদীরা এই মানবিক রূপকে চেনার চেষ্টাও করেনি।
১৩. সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বিচারিতার পরিচয় দাও।
উত্তর: সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে নিজেদের ‘সভ্য’ বলে দাবি করত এবং তাদের নিজেদের দেশে ঈশ্বরের উপাসনা করত (“সকাল-সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে… পূজার ঘণ্টা বাজছিল”)। অন্যদিকে, সেই তারাই আফ্রিকায় গিয়ে বর্বরদের মতো আচরণ করত, সেখানকার মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত এবং তাদের দাসে পরিণত করত। এই दोहरा আচরণই তাদের দ্বিচারিতার পরিচয়।
১৪. “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে” – ‘দ্বার’ শব্দটি এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত?
উত্তর: ‘দ্বার’ শব্দটি এখানে শুধুমাত্র দরজা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি এক প্রতীকী অর্থ বহন করে। ‘মানহারা মানবীর দ্বারে’ দাঁড়ানো বলতে বোঝানো হয়েছে, আফ্রিকার সামনে নত হওয়া, তার ইতিহাস ও যন্ত্রণাকে স্বীকার করা এবং তার প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। এটি এক নৈতিক অবস্থান গ্রহণের প্রতীক।
১৫. ‘যুগান্তরের কবি’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: ‘যুগান্তরের কবি’ বলতে কবি ভবিষ্যতের সেই কবি বা মানবসমাজকে বুঝিয়েছেন, যারা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা বর্ণবিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতার কথা বলবে। এই কবি হবেন নতুন যুগের বার্তাবহ, যিনি অতীতের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবেন এবং সমস্ত মানবজাতির পক্ষ থেকে আফ্রিকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।
১৬. “তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে” – এই পঙক্তিটির তাৎপর্য কী?
উত্তর: এই পঙক্তিটির মাধ্যমে কবি আফ্রিকার অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ও নীরব কান্নাকে প্রকাশ করেছেন। আফ্রিকার অধিবাসীদের কান্নার কোনো ভাষা ছিল না, যা সভ্য জগৎ শুনতে পায়। তাদের সেই নীরব কান্না যেন আফ্রিকার ঘন, স্যাঁতস্যাঁতে অরণ্যের বাষ্পের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ‘বাষ্পাকুল’ শব্দটি একই সঙ্গে অরণ্যের আর্দ্রতা এবং আফ্রিকার অশ্রুসিক্ত অবস্থাকে বোঝায়।
১৭. “যখন পশ্চিম দিগন্তে…” – এই সময়কালে সাম্রাজ্যবাদীরা কী করছিল?
উত্তর: যখন পশ্চিম দিগন্তে অর্থাৎ ইউরোপে দিন শেষ হয়ে আসছিল, তখন সেখানকার গির্জাগুলিতে দয়াময় ঈশ্বরের নামে পূজার ঘণ্টা বাজছিল। শিশুরা মায়েদের কোলে খেলছিল এবং কবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে মেতেছিল। ঠিক সেই সময়েই তাদের লোভী প্রতিনিধিরা আফ্রিকায় ধ্বংসলীলা চালাচ্ছিল।
১৮. আফ্রিকার ইতিহাসকে ‘অপমানিত’ ও ‘পঙ্কিল’ বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: আফ্রিকার ইতিহাসকে ‘অপমানিত’ বলা হয়েছে কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা তার সম্মান ও স্বাধীনতা হরণ করেছে। তাকে ‘পঙ্কিল’ বা কর্দমাক্ত বলা হয়েছে কারণ, শোষকদের অত্যাচারের ফলে সৃষ্ট আফ্রিকার মানুষের রক্ত ও অশ্রু সেই ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। দস্যুদের জুতোর তলার কাদার মতো সেই কলঙ্ক আফ্রিকার ইতিহাসে লেগে আছে।
১৯. ‘আফ্রিকা’ কবিতায় স্রষ্টার ভূমিকা কী?
উত্তর: ‘আফ্রিকা’ কবিতায় স্রষ্টা এক দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছেন। একদিকে তিনি আফ্রিকাকে সৃষ্টি করে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, তিনি যেন তাঁর সৃষ্টির এই লাঞ্ছনা দেখে ব্যথিত। কবি স্রষ্টার এই কর্মকাণ্ডের বর্ণনার মাধ্যমে আফ্রিকার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং তার অনন্য পরিচয়ের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন।
২০. আফ্রিকার জন্মবৃত্তান্ত কবি কীভাবে বর্ণনা করেছেন?
উত্তর: কবি এক পৌরাণিক ভঙ্গিতে আফ্রিকার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, স্রষ্টা যখন তাঁর নতুন সৃষ্টি নিয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। রুদ্র সমুদ্রের বাহু দিয়ে তাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় এক নির্জন মহাদেশে নির্বাসিত করেন, যা তাকে এক রহস্যময় পরিচয় দান করে।
২১. “নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে” – এই তুলনাটির সার্থকতা কী?
উত্তর: নেকড়ে একটি হিংস্র পশু, কিন্তু সে তার প্রয়োজনে শিকার করে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল তার চেয়েও বেশি হিংস্র। তাদের হিংস্রতা ছিল লোভের তাড়নায়। তারা শুধুমাত্র আফ্রিকার সম্পদ লুণ্ঠন করেনি, সেখানকার মানুষদের জীবন ও সম্মানও হরণ করেছে। এই তুলনাটির মাধ্যমে কবি সাম্রাজ্যবাদীদের পাশবিকতাকে প্রকৃতির হিংস্রতার চেয়েও ভয়ংকর বলে দেখিয়েছেন।
২২. কবিতাটির মূল ভাব কোন ছত্রে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে?
উত্তর: কবিতাটির মূল ভাব সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;/বলো ‘ক্ষমা করো’ ” – এই ছত্র দুটিতে। এই লাইন দুটি শুধুমাত্র আফ্রিকার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে না, এটি সাম্রাজ্যবাদের পাপের জন্য সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে এক নৈতিক দায় স্বীকার এবং অনুশোচনার আহ্বান জানায়, যা কবিতার মূল বক্তব্য।
২৩. “প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু” – বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: ‘প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু’ বলতে কবি আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সেই সব গুপ্ত জ্ঞান ও মন্ত্রকে বুঝিয়েছেন, যা সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে থাকে। আফ্রিকা তার নিভৃত অবকাশে যে রহস্যময় জ্ঞান সংগ্রহ করেছিল, তা দিয়ে সে প্রকৃতির চেতনাতীত মনে জাদু বা প্রভাব বিস্তার করতে পারত। এটি আফ্রিকার এক আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিত দেয়।
২৪. “তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে” – ক্রন্দন ‘ভাষাহীন’ কেন?
উত্তর: আফ্রিকার ক্রন্দন ‘ভাষাহীন’ কারণ, সভ্য জগৎ সেই কান্নার ভাষা বোঝেনি বা বোঝার চেষ্টাও করেনি। তাদের যন্ত্রণা এতটাই গভীর এবং তাদের উপর অত্যাচার এতটাই নির্মম ছিল যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এই নীরব, অব্যক্ত যন্ত্রণাকেই কবি ‘ভাষাহীন ক্রন্দন’ বলেছেন, যা প্রকৃতির বাষ্পের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।
২৫. ‘আফ্রিকা’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের কোন বিশ্বমানবতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর: এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির কবি নন, তিনি বিশ্বমানবতার কবি। তিনি আফ্রিকার লাঞ্ছনাকে সমগ্র মানবজাতির অপমান বলে মনে করেছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ভণ্ডামির সমালোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতের মানবসমাজের কাছে অন্যায়ের প্রতিকার হিসেবে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর গভীর বিশ্বমানবতাবাদের পরিচয় দেয়।
ঘ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৫ (১০টি)
১. ‘আফ্রিকা’ কবিতার মূল বক্তব্য বা বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি কেবল একটি মহাদেশের বর্ণনা নয়, এটি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, মানবিকতার অবমাননা এবং তার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ শৈল্পিক প্রতিবাদ।
কবিতার বিষয়বস্তু:
১. আফ্রিকার সৃষ্টি ও বিচ্ছিন্নতা: কবিতার শুরুতে কবি এক পৌরাণিক আবহে আফ্রিকার জন্ম ও তার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন। স্রষ্টা তাকে প্রাচী ধরিত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক রহস্যময়, দুর্গম পরিবেশে নির্বাসিত করেন।
২. সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন: এরপর কবিতায় চিত্রিত হয়েছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আগমন। তারা ‘লোহার হাতকড়ি’ নিয়ে এসে আফ্রিকার শান্তি ও স্বাধীনতা হরণ করে। কবি তাদের ‘মানুষ-ধরার দল’ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাদের লোভকে ‘সভ্যের বর্বর লোভ’ বলে ধিক্কার জানিয়েছেন।
৩. শোষণ ও লাঞ্ছনা: সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাদের শোষণ আফ্রিকার ইতিহাসকে ‘পঙ্কিল’ ও ‘অপমানিত’ করে তোলে। আফ্রিকার ভাষাহীন কান্নায় অরণ্যপথ বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।
৪. মানবিক আবেদন ও ক্ষমা প্রার্থনা: কবিতার শেষে কবি এক মানবিক আবেদন জানিয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতের কবির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই ‘মানহারা মানবী’ আফ্রিকার দ্বারে দাঁড়িয়ে সমগ্র সভ্য জগতের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইতে। এই ক্ষমা প্রার্থনাই হবে সভ্যতার ‘শেষ পুণ্যবাণী’।
উপসংহার: সুতরাং, কবিতাটি আফ্রিকার লাঞ্ছনার ইতিহাস তুলে ধরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং বিশ্বমানবতার জাগরণের আহ্বান জানায়।
২. “চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।” – কারা, কীভাবে আফ্রিকার অপমানিত ইতিহাসে চিরচিহ্ন দিয়ে গেল? এই ‘চিরচিহ্ন’-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতায় এই পঙক্তিটি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্থায়ী ক্ষতের এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেয়।
চিহ্ন স্থাপনকারী: এখানে যারা চিরচিহ্ন দিয়ে গেল, তারা হলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দস্যু ও দাস ব্যবসায়ীরা। কবি তাদের ‘মানুষ-ধরার দল’ বলে অভিহিত করেছেন, যাদের নখ নেকড়ের চেয়েও তীক্ষ্ণ।
চিহ্ন স্থাপনের পদ্ধতি: তারা আফ্রিকায় এসে সেখানকার মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের দাসে পরিণত করেছে এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। তাদের এই শোষণ ও অত্যাচারের ফলে আফ্রিকার মানুষের রক্ত ও অশ্রু ঝরেছে। সেই রক্ত ও অশ্রুতে ভেজা মাটিতে সাম্রাজ্যবাদীরা হেঁটে বেড়িয়েছে। তাদের এই হিংস্র কার্যকলাপই আফ্রিকার ইতিহাসে কলঙ্কের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।
‘চিরচিহ্ন’-এর স্বরূপ: এই ‘চিরচিহ্ন’ শুধুমাত্র একটি বাহ্যিক দাগ নয়, এর স্বরূপ অত্যন্ত গভীর ও multifaceted।
১. भौतिक চিহ্ন: কবি এই চিহ্নকে “দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলার কাদার পিণ্ড” বলে বর্ণনা করেছেন। এটি শোষণের এক স্থূল, কদর্য भौतिक রূপ।
২. মানসিক ও ঐতিহাসিক চিহ্ন: এই চিহ্ন আফ্রিকার মনে ও ইতিহাসে এক স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এটি পরাধীনতা, লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আফ্রিকাকে বহন করতে হয়েছে।
৩. নৈতিক চিহ্ন: এই চিহ্ন শোষক সভ্যতার কপালেও এক কলঙ্কতিলক এঁকে দিয়েছে। এটি তাদের ‘সভ্য’ মুখোশের আড়ালে থাকা বর্বরতার এক চিরস্থায়ী প্রমাণ।
৩. “দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;/বলো ‘ক্ষমা করো’ ” – ‘মানহারা মানবী’ কে? কবি কাকে, কেন এই আহ্বান জানিয়েছেন? এই আহ্বানের তাৎপর্য কী?
উত্তর:
‘মানহারা মানবী’র পরিচয়: ‘মানহারা মানবী’ বলতে কবি রূপকার্থে আফ্রিকা মহাদেশকে বুঝিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা আফ্রিকার সম্পদ, স্বাধীনতা ও মানুষের সম্মান হরণ করে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। একজন নারীর সম্মান হরণের মতোই এই ঘটনা আফ্রিকার পক্ষে গ্লানিকর। তাই কবি আফ্রিকাকে ‘মানহারা মানবী’ বলে সম্বোধন করেছেন।
আহ্বানের লক্ষ্য ও কারণ: কবি এই আহ্বান জানিয়েছেন ‘যুগান্তরের কবি’র প্রতি। যুগান্তরের কবি হলেন ভবিষ্যতের সেই বিবেকবান শিল্পী বা মানবসমাজ, যিনি সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতার কথা বলবেন। কবি তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন কারণ, সভ্য ইউরোপ আফ্রিকার উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, তা সমগ্র মানবজাতির জন্য এক পাপ ও লজ্জা। সেই সম্মিলিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই এই ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন।
আহ্বানের তাৎপর্য: এই আহ্বানের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।
১. নৈতিক দায় স্বীকার: এর মাধ্যমে কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নৈতিক অবস্থান নিয়েছেন এবং শোষক সভ্যতার পক্ষ থেকে দায় স্বীকারের কথা বলেছেন।
২. মানবিকতার পুনর্গঠন: কবি মনে করেন, ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমেই মানব সমাজে হারানো বিশ্বাস ও সম্প্রীতি ফিরে আসতে পারে। এটিই হবে প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ।
৩. ভবিষ্যতের প্রতি বার্তা: এই আহ্বান ভবিষ্যতের প্রজন্মের প্রতি এক বার্তা—অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয়।
৪. ‘আফ্রিকা’ কবিতার প্রথম স্তবকে আফ্রিকার যে রহস্যময় ও আদিম রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘আফ্রিকা’ কবিতার প্রথম স্তবকে রবীন্দ্রনাথ এক পৌরাণিক ও রহস্যময় আবহে আফ্রিকার জন্ম ও তার আদিম রূপের ছবি এঁকেছেন, যা তাকে অন্যান্য মহাদেশ থেকে এক স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে।
সৃষ্টি ও বিচ্ছিন্নতা: কবি কল্পনা করেছেন, স্রষ্টা যখন তাঁর নতুন সৃষ্টি নিয়ে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি প্রাচী ধরিত্রী বা মূল ভূখণ্ড থেকে আফ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। রুদ্র সমুদ্রের শক্তিশালী বাহু দিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে নির্বাসিত করেন।
রহস্যময় প্রকৃতি: এই বিচ্ছিন্ন আফ্রিকা ছিল এক রহস্যময় জগৎ। তাকে পাহারা দিত ‘বনস্পতি’ বা বিশাল বিশাল গাছপালা। তার অরণ্য ছিল এতটাই ঘন যে, সেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না, তাই কবি তাকে ‘কৃপণ আলোর অন্তঃপুর’ বলেছেন। এই আলো-আঁধারির পরিবেশ তার রহস্যময়তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।
আদিম জীবন: এই দুর্গম পরিবেশে আফ্রিকা তার আদিম সত্তাকে নিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। সে প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে (‘ভীষণকে’) জয় করার জন্য নিজেই এক উগ্র রূপ (‘বিরূপের ছদ্মবেশ’) ধারণ করেছিল। সে প্রকৃতির গোপন রহস্য (‘দুর্গমের রহস্য’) সংগ্রহ করছিল এবং তার নিজস্ব জাদু ও মন্ত্রের দ্বারা প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করছিল।
উপসংহার: এভাবেই, প্রথম স্তবকে কবি আফ্রিকাকে এক স্বতন্ত্র, আদিম, রহস্যময় এবং শক্তিশালী সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে।
৫. ‘আফ্রিকা’ কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের যে চিত্র কবি এঁকেছেন, তা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আফ্রিকা’ কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এক নির্মম ও ধিক্কারপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি ইউরোপীয় শোষকদের ভণ্ডামি ও বর্বরতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন।
আগ্রাসনের চিত্র:
১. দস্যুর আগমন: সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকায় এসেছিল ‘লোহার হাতকড়ি’ নিয়ে, যা তাদের দাসত্বের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে। কবি তাদের ‘মানুষ-ধরার দল’ বলে অভিহিত করেছেন, যারা পশুর চেয়েও হিংস্র (“নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে”)।
২. সভ্যতার মুখোশে বর্বরতা: এই আগ্রাসনকারীরা নিজেদের ‘সভ্য’ বলে দাবি করত, কিন্তু তাদের লোভ ছিল ‘বর্বর’। কবি এই विरोधाभाস ব্যবহার করে তাদের ভণ্ডামিকে তুলে ধরেছেন। তাদের ‘নির্লজ্জ অমানুষতা’ আফ্রিকার মানবিক রূপকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।
৩. শোষণ ও লাঞ্ছনা: তারা আফ্রিকার সম্পদ লুণ্ঠন করেছে এবং সেখানকার মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। আফ্রিকার ‘ভাষাহীন ক্রন্দন’ এবং ‘অপমানিত ইতিহাস’-এর বর্ণনার মাধ্যমে কবি এই শোষণের গভীরতা প্রকাশ করেছেন।
৪. দ্বিচারিতা: কবি দেখিয়েছেন, যখন এই সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকায় ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, ঠিক তখনই তাদের নিজেদের দেশে গির্জায় ‘পূজার ঘণ্টা’ বাজছিল। এই চিত্র তাদের দ্বিচারিতা ও নৈতিক অধঃপতনকে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করে।
উপসংহার: এভাবেই, রবীন্দ্রনাথ প্রতীক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এক শক্তিশালী ও মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন।
৬. ‘আফ্রিকা’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনা ও ঐতিহাসিক চেতনার মেলবন্ধন কীভাবে ঘটেছে, তা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কাব্যিক রূপায়ণ নয়, এটি কবির সুগভীর কল্পনা এবং প্রখর ঐতিহাসিক চেতনার এক অনবদ্য মেলবন্ধন।
কবি-কল্পনার প্রকাশ:
কবিতার শুরুতেই কবির কল্পনা পৌরাণিক আবহে আফ্রিকার জন্মবৃত্তান্ত রচনা করেছে। স্রষ্টার অধৈর্য, রুদ্র সমুদ্রের বাহু দিয়ে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নেওয়া, বনস্পতির পাহারা—এই সমস্ত বর্ণনা কবির অপূর্ব কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। আফ্রিকাকে ‘মানহারা মানবী’ হিসেবে কল্পনা করা এবং ‘যুগান্তরের কবি’র প্রতি তাঁর আহ্বানও তাঁর কল্পনারই ফসল।
ঐতিহাসিক চেতনার প্রকাশ:
এই কল্পনার আবরণের নীচে রয়েছে প্রখর ঐতিহাসিক চেতনা। কবি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আফ্রিকার শোষণ ও দাস ব্যবসার ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। “এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে”, “মানুষ-ধরার দল”, “সভ্যের বর্বর লোভ” – এই সমস্ত পঙক্তি উনিশ শতকের ঔপনিবেশিকতার ঐতিহাসিক সত্যকে নির্দেশ করে। আফ্রিকার অপমানিত ইতিহাস, তার রক্ত ও অশ্রুর বর্ণনা কোনো কল্পনা নয়, তা এক নির্মম ঐতিহাসিক বাস্তবতা।
মেলবন্ধন: কবি এই ঐতিহাসিক সত্যকে সরাসরি প্রবন্ধের মতো বর্ণনা না করে, তাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে এক শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। তিনি ইতিহাসকে রূপকের মাধ্যমে, চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এভাবেই, আফ্রিকার ভৌগোলিক সৃষ্টি থেকে শুরু করে তার ঐতিহাসিক লাঞ্ছনা পর্যন্ত সমগ্র বিষয়টি কবির কল্পনা ও ঐতিহাসিক চেতনার মেলবন্ধনে এক সার্থক কবিতায় পরিণত হয়েছে।
৭. “তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী/হয়ে উঠুক ‘ক্ষমা করো’।” – এই পঙক্তিটির তাৎপর্য ও কবির মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘আফ্রিকা’ কবিতার এই শেষ পঙক্তি দুটি শুধুমাত্র কবিতার উপসংহার নয়, এটি কবির গভীর মানবতাবাদী দর্শন এবং ভবিষ্যতের প্রতি এক শক্তিশালী বার্তা।
পঙক্তিটির তাৎপর্য:
১. পাপের স্বীকারোক্তি: ‘ক্ষমা করো’ কথাটি বলার অর্থ হলো নিজের ভুল বা পাপকে স্বীকার করা। কবি চেয়েছেন, তথাকথিত সভ্য জগৎ আফ্রিকার প্রতি তার করা অন্যায়ের কথা স্বীকার করুক।
২. নৈতিক উত্তরণ: ক্ষমা চাওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং নৈতিক শক্তির পরিচায়ক। কবি মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা যদি তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায়, তবেই তার নৈতিক উত্তরণ ঘটবে।
৩. ‘পুণ্যবাণী’: এই ক্ষমা প্রার্থনার কাজটি একটি পুণ্যের কাজ। কারণ এটি হিংসা ও ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পথ খুলে দেয়। তাই কবি একে ‘পুণ্যবাণী’ বলেছেন।
কবির মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি:
রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা কালের নন, তিনি সমগ্র মানবজাতির কবি। তিনি আফ্রিকার যন্ত্রণা অনুভব করেছেন এবং শোষক সভ্যতার পক্ষ থেকে এক নৈতিক দায় অনুভব করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিশোধ বা হিংসার মাধ্যমে নয়, বরং অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমেই মানব সমাজে প্রকৃত শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তিনি কোনো ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ না থেকে, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল কামনা করেছেন। এই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর গভীর মানবতাবাদের পরিচয় দেয়।
৮. ‘আফ্রিকা’ কবিতায় প্রকৃতির যে দুটি ভিন্ন রূপের ছবি আঁকা হয়েছে, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আফ্রিকা’ কবিতায় প্রকৃতির দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের ছবি এঁকেছেন—একটি আফ্রিকার আদিম, রহস্যময় প্রকৃতি এবং অন্যটি ইউরোপের শান্ত, সৌন্দর্যময় প্রকৃতি।
আফ্রিকার প্রকৃতি: আফ্রিকার প্রকৃতি ছিল আদিম, দুর্গম এবং রহস্যময়। কবি তাকে ‘ছায়াবৃতা’ বলেছেন। বিশাল বনস্পতি তাকে পাহারা দিত। তার অরণ্য ছিল ‘সূর্যহারা’ এবং ‘বাষ্পাকুল’, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছত না। এই প্রকৃতি ছিল ভীষণ, যার সঙ্গে সংগ্রাম করে সেখানকার অধিবাসীদের বাঁচতে হতো। আফ্রিকার প্রকৃতি ছিল বন্য, অকৃত্রিম এবং স্বাধীন।
ইউরোপের প্রকৃতি (কবিতায় উল্লিখিত): কবিতার শেষাংশে কবি ইউরোপের প্রকৃতির একটি স্নিগ্ধ চিত্র এঁকেছেন, যা আফ্রিকার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে “কবিরা সঙ্গীতে বেড়িয়েছিল/সুন্দরকে আরাধনায়”। এই চিত্রটি ইউরোপের একটি শান্ত, সুসংস্কৃত এবং শিল্পময় পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়। সেখানে শিশুরা মায়েদের কোলে খেলছিল, যা এক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজকে বোঝায়।
বৈপরীত্য ও তাৎপর্য: কবি এই দুটি ভিন্ন প্রকৃতির চিত্র তুলে ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বিচারিতাকেই স্পষ্ট করেছেন। যে সভ্যতার মানুষ নিজের দেশে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শান্তি উপভোগ করে, সেই সভ্যতার লোকেরাই অন্য দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে ধ্বংস করে। এই বৈপরীত্য কবিতার মূল বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।
৯. “যেখানেChesapeake Bay থেকে আসা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নগ্ন অমানুষিকতা প্রকাশ করেছিল, সেই সময়ে তাদের নিজেদের দেশে কী ঘটছিল? কবি এই বৈপরীত্য কেন দেখিয়েছেন?
উত্তর:
সাম্রাজ্যবাদীদের দেশের চিত্র: ‘আফ্রিকা’ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, যখন সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকায় তাদের ‘বর্বর লোভ’ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে তাদের নিজেদের দেশে, অর্থাৎ ইউরোপে, এক শান্ত ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলছিল। সেখানে—
১. সকাল-সন্ধ্যায় গির্জাগুলিতে ঈশ্বরের নামে ‘পূজার ঘণ্টা’ বাজছিল।
২. শিশুরা মায়েদের কোলে নিশ্চিন্তে খেলছিল।
৩. কবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে গান রচনা করছিলেন।
বৈপরীত্য দেখানোর কারণ: কবি এই বৈপরীত্য দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতাকে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করার জন্য।
১. নৈতিক অধঃপতন: এর মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, যে সভ্যতা বাইরে দয়া, ধর্ম ও সৌন্দর্যের কথা বলে, তার অন্তরে রয়েছে লোভ, হিংসা ও বর্বরতা।
২. ভণ্ডামি উন্মোচন: তারা একদিকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, আবার অন্যদিকে ঈশ্বরেরই সৃষ্টি মানুষকে দাসে পরিণত করে। এই ভণ্ডামিকে উন্মোচন করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য।
৩. অপরাধের তীব্রতা বৃদ্ধি: এই বৈপরীত্য আফ্রিকার উপর করা অপরাধের তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কারণ, এই অপরাধীরা অজ্ঞ বা অসভ্য ছিল না, তারা ছিল তথাকথিত ‘সভ্য’ জগতের মানুষ, যারা জেনেশুনে এই অমানবিক কাজ করেছিল।
১০. ‘আফ্রিকা’ কবিতার মূল কাব্যিক সৌন্দর্য ও শিল্পগুণ বিচার করো।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর গভীরতার জন্যই নয়, এর অনবদ্য কাব্যিক সৌন্দর্য ও শিল্পগুণের জন্যও বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।
শিল্পগুণ:
১. গদ্যছন্দের ব্যবহার: কবিতাটি গদ্যছন্দে লেখা, যা কবির বক্তব্যকে একাধারে আবেগপূর্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলেছে। এই ছন্দ কবিতার বর্ণনায় এক মহাকাব্যিক বিস্তার এনেছে।
২. চিত্রকল্পের ব্যবহার: কবি অসাধারণ সব চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। “রুদ্র সমুদ্রের বাহু”, “বনস্পতির নিবিড় পাহারা”, “সভ্যের বর্বর লোভ”, “দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলার কাদার পিণ্ড”—এই চিত্রকল্পগুলি কবিতার ভাবকে মূর্ত করে তুলেছে।
৩. রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার: আফ্রিকাকে ‘মানহারা মানবী’ হিসেবে কল্পনা করা, ‘লোহার হাতকড়ি’কে দাসত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা, এবং ‘যুগান্তরের কবি’কে ভবিষ্যতের বিবেকের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা—এই রূপক ও প্রতীকগুলি কবিতার ব্যঞ্জনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
৪. विरोधाभाস অলঙ্কার: “সভ্যের বর্বর লোভ”-এর মতো विरोधाभाস (Oxymoron) ব্যবহার করে কবি সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ভণ্ডামিকে শাণিতভাবে আক্রমণ করেছেন।
৫. শব্দের ব্যঞ্জনা: ‘পঙ্কিল’, ‘বাষ্পাকুল’, ‘বীভৎস’-এর মতো শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কবি একাধারে আফ্রিকার যন্ত্রণা এবং শোষণের কদর্যতাকে প্রকাশ করেছেন।
উপসংহার: বিষয়বস্তুর মহত্ত্বের সঙ্গে শিল্পগুণের এই অপূর্ব মেলবন্ধনের ফলেই ‘আফ্রিকা’ একটি কালজয়ী কবিতায় পরিণত হয়েছে।
Class 10 bengali আফ্রিকা question answer
আফ্রিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার প্রশ্ন উত্তর, MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 bengali আফ্রিকা কবিতার প্রশ্ন উত্তর