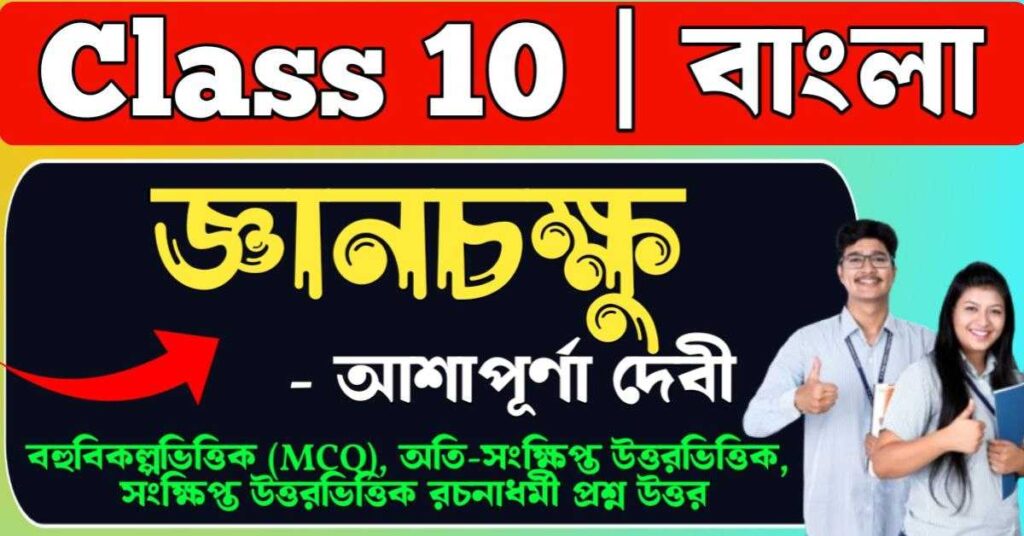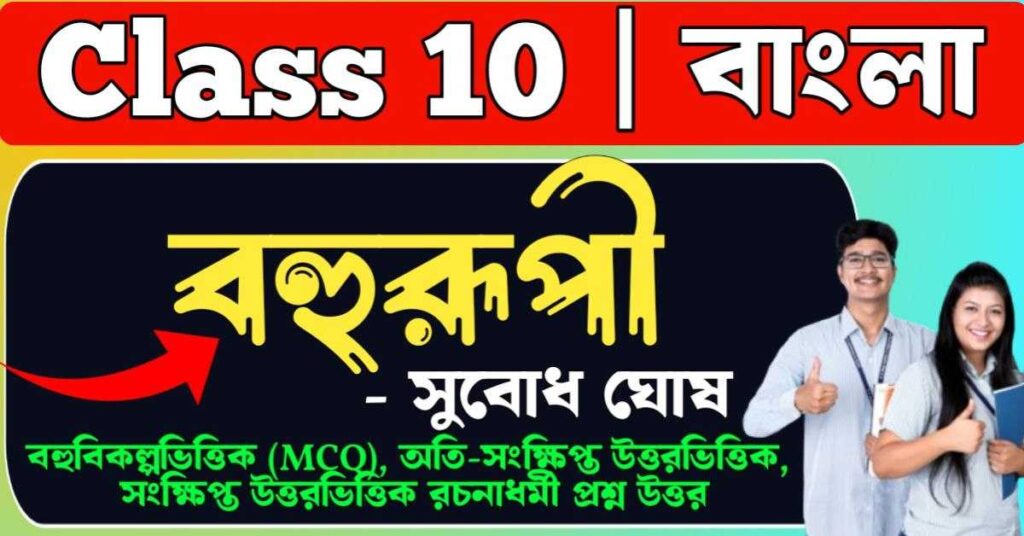প্রলয়োল্লাস কবিতার প্রশ্ন উত্তর
প্রলয়োল্লাস ( কাজী নজরুল ইসলাম )
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৫০টি)
১. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটির কবি কে?
২. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
৩. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর” – এই আহ্বানটি কবিতায় কতবার আছে?
৪. “নূতনের কেতন ওড়ে” – কীসের ঝড়ে?
৫. “আসছে এবার অনাগত” – ‘অনাগত’ কে?
৬. দিগম্বরের জটায় কে হাসে?
৭. ‘প্রলয়োল্লাস’ শব্দটির অর্থ কী?
৮. “ভেঙে আবার গড়তে জানে সে” – ‘সে’ কে?
৯. “সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে” কী আঘাত করার কথা বলা হয়েছে?
১০. কাদের জয়ধ্বনি করতে বলা হয়েছে?
১১. “ঝামর কেশের দোলায়” – ‘ঝামর’ শব্দের অর্থ কী?
১২. প্রলয় কীভাবে আসছে?
১৩. “দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা” কোথায় দেখা যায়?
১৪. ‘দিগম্বরের জটায়’ – ‘দিগম্বর’ কে?
১৫. “সর্বনাশী-জ্বালিয়া-দেওয়া-ধূমকেতু” – এটি কার বিশেষণ?
১৬. কবি কাকে ‘চিরসুন্দর’ বলেছেন?
১৭. “ওই আসে সুন্দর” – সুন্দর কীসের বেশে আসে?
১৮. জগৎ জুড়ে কী ঘনিয়ে আসছে?
১৯. ‘রক্ত-মাখা-তৃপাণ’ হাতে কে আসে?
২০. “বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে” – কে?
২১. “ওই ভাঙা-গড়া খেলা যে তার” – ‘তার’ বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
২২. ‘কেতন’ শব্দের অর্থ কী?
২৩. “বিশ্বমায়ের আসন” কোথায় পাতা?
২৪. কবি কাদের ভয় করতে বারণ করেছেন?
২৫. ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
২৬. ‘সিন্ধু-পার’ বলতে কোন স্থানকে বোঝানো হয়েছে?
২৭. ‘রণ-বেশে’ কে হাসছে?
২৮. “অট্টরোলের হট্টগোলে” স্তব্ধ হয় কী?
২৯. ‘তৃপাণ’ শব্দের অর্থ কী?
৩০. “আসছে নবীন” – নবীন কী করতে আসছে?
৩১. “বধূরা প্রদীপ তুলে ধর” – কেন?
৩২. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি কীসের মধ্যে নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছেন?
৩৩. “অগ্নিবীণা” কী ধরনের কাব্যগ্রন্থ?
৩৪. ‘মহাকাল-সারথি’ কে?
৩৫. “এবার মহানিশার শেষে” – কী আসবে?
৩৬. ‘মভৈঃ’ শব্দের অর্থ কী?
৩৭. প্রলয় কীভাবে দুলছে?
৩৮. ‘কালবোশেখী’ কিসের প্রতীক?
৩৯. “অ-সুন্দরে করতে ছেদন” – ‘অ-সুন্দর’ কী?
৪০. কবি কাদের জন্য দিগন্তের কাদন তুলেছেন?
৪১. “ওই নূতনের _____ ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়।” – শূন্যস্থান পূরণ কর।
৪২. ‘দ্বাদশ রবি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৪৩. ‘উল্কা’ কী?
৪৪. ” सिंधु-নদের বন্দনা” – এই কথাটি কোন কবিতার?
৪৫. কবি হাসির কারণ কী বলেছেন?
৪৬. “এবার ____ মহানিশার শেষে” – শূন্যস্থান পূরণ কর।
৪৭. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কোন দেবতার প্রসঙ্গ আছে?
৪৮. কবি কিসের হট্টগোলের কথা বলেছেন?
৪৯. ‘কেতন’ কোথায় ওড়ে?
৫০. কবিতাটির শেষে কবি কীসের ইঙ্গিত দিয়েছেন?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৪০টি)
১. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
উত্তর: ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
২. কবি কাদের জয়ধ্বনি করতে বলেছেন?
উত্তর: কবি পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী মানুষদের জয়ধ্বনি করতে বলেছেন।
৩. নূতনের কেতন কীসের মতো ওড়ে?
উত্তর: নূতনের কেতন কালবোশেখীর ঝড়ের মতো ওড়ে।
৪. ‘দিগম্বর’ কে?
উত্তর: ‘দিগম্বর’ হলেন মহাদেব বা শিব।
৫. দিগম্বরের জটায় কী হাসে?
উত্তর: দিগম্বরের জটায় শিশু-চাঁদের কর বা কিরণ হাসে।
৬. ‘প্রলয়োল্লাস’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘প্রলয়োল্লাস’ শব্দের অর্থ হলো প্রলয় বা ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ।
৭. সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে কে আঘাত করে?
উত্তর: প্রলয়ংকর শক্তি ধূমকেতুর মতো সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে আঘাত করে।
৮. ‘দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা’ কোথায় জ্বলে?
উত্তর: ‘দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা’ ভয়ঙ্করের নয়ন-তলে জ্বলে।
৯. ‘ঝামর’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘ঝামর’ শব্দের অর্থ হলো রুক্ষ বা বিবর্ণ।
১০. ‘চিরসুন্দর’ কে?
উত্তর: ভাঙনকারী মহাকাল বা শিবই হলেন ‘চিরসুন্দর’।
১১. কবি কী করতে বারণ করেছেন?
উত্তর: কবি প্রলয়কে দেখে ভয় করতে বারণ করেছেন।
১২. ‘রক্ত-মাখা-তৃপাণ’ হাতে কে আসে?
উত্তর: ‘রক্ত-মাখা-তৃপাণ’ হাতে আসে ভয়ঙ্কর।
১৩. বধূদের কী করতে বলা হয়েছে?
উত্তর: বধূদের প্রদীপ তুলে ধরে ভয়ঙ্করকে বরণ করতে বলা হয়েছে।
১৪. ‘মহানিশার শেষে’ কী আসবে?
উত্তর: ‘মহানিশার শেষে’ অরুণ হেসে ঊষা আসবে।
১৫. ‘কেতন’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘কেতন’ শব্দের অর্থ হলো পতাকা।
১৬. কাল-ভয়ঙ্করের বেশে কে আসে?
উত্তর: কাল-ভয়ঙ্করের বেশে সুন্দর আসে।
১৭. নবীন কী করতে আসে?
উত্তর: নবীন জীবনহারা, অসুন্দরকে ছেদন বা ধ্বংস করতে আসে।
১৮. ‘অট্টরোলের হট্টগোলে’ কী স্তব্ধ হয়?
উত্তর: ‘অট্টরোলের হট্টগোলে’ চরাচর স্তব্ধ হয়।
১৯. ‘তৃপাণ’ কী?
উত্তর: ‘তৃপাণ’ হলো খড়্গ বা তরবারি।
২০. ‘ঈশান-বিষাণে’ কী দুলছে?
উত্তর: ‘ঈশান-বিষাণে’ প্রলয় দুলছে।
২১. জগৎ জুড়ে কী ঘনিয়ে আসছে?
উত্তর: জগৎ জুড়ে প্রলয়-নিশা ঘনিয়ে আসছে।
২২. ‘বিপুল’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘বিপুল’ শব্দের অর্থ হলো বিশাল বা বৃহৎ।
২৩. বিশ্বমায়ের আসন কোথায়?
উত্তর: বিশ্বমায়ের আসন বিপুলের বুকে।
২৪. ‘মভৈঃ’ ধ্বনি কোথা থেকে শোনা যায়?
উত্তর: ‘মভৈঃ’ ধ্বনি প্রলয়ের রথের ঘর্ঘর বা চাকার শব্দ থেকে শোনা যায়।
২৫. ‘জরায়-মৃত’ কাদের বলা হয়েছে?
উত্তর: জরাগ্রস্ত, প্রাণহীন, মৃতপ্রায় মানুষদের ‘জরায়-মৃত’ বলা হয়েছে।
২৬. ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’—এই পঙক্তিটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: এই পঙক্তিটি দ্বারা কবি প্রলয়কে আবাহন ও স্বাগত জানাতে বুঝিয়েছেন।
২৭. কবি নজরুল কীসের কবি হিসেবে পরিচিত?
উত্তর: কবি নজরুল ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে পরিচিত।
২৮. কবিতায় ধ্বংসের দেবতার রূপ কী?
উত্তর: কবিতায় ধ্বংসের দেবতা ভয়ঙ্কর, কিন্তু তিনিই আবার চিরসুন্দর।
২৯. কালবোশেখীর ঝড় কিসের প্রতীক?
উত্তর: কালবোশেখীর ঝড় নতুনের আগমন এবং বিপ্লবী শক্তির প্রতীক।
৩০. ‘সিন্ধু-পার’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: ‘সিন্ধু-পার’ বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা ইংরেজদের দেশকে বোঝানো হয়েছে।
৩১. কবিতার শেষে কবি কীসের আশা প্রকাশ করেছেন?
উত্তর: কবিতার শেষে কবি এক নতুন সকাল বা ঊষার আগমনের আশা প্রকাশ করেছেন।
৩২. ‘অ-সুন্দর’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: ‘অ-সুন্দর’ বলতে পুরনো, জরাগ্রস্ত, অন্যায়-অত্যাচারে পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।
৩৩. ‘প্রলয়-নিশা’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘প্রলয়-নিশা’ শব্দের অর্থ হলো প্রলয়ের রাত বা ধ্বংসের অন্ধকারময় সময়।
৩৪. কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি কাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন?
উত্তর: কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।
৩৫. ‘রণ’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘রণ’ শব্দের অর্থ হলো যুদ্ধ।
৩৬. ‘উল্কা’ ছোটায় কে?
উত্তর: নীল খিলানের অর্গল বা আগল ভেঙে উল্কা ছোটে।
৩৭. প্রদীপ তুলে ধরতে বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: প্রলয়রূপী সুন্দরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রদীপ তুলে ধরতে বলা হয়েছে।
৩৮. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি কোন সময়ের রচনা?
উত্তর: ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল সময়ের রচনা।
৩৯. মহাকাল কীসের সারথি?
উত্তর: মহাকাল রক্ত-তড়িত-চাবুক হেনে রথের সারথি।
৪০. কবি কেন হাসতে বলেছেন?
উত্তর: কারণ ধ্বংসের এই রাত্রি শেষ হলেই নতুন ভোরের আগমন ঘটবে, তাই কবি হাসতে বলেছেন।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ৩ (২৫টি)
১. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর” – কবি কাদের, কেন জয়ধ্বনি করতে বলেছেন?
উত্তর: কবি পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী, হতাশ দেশবাসীকে জয়ধ্বনি করতে বলেছেন। কারণ, প্রলয় বা ধ্বংস আসছে শুধুমাত্র ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং পুরনো, জরাগ্রস্ত সমাজকে ভেঙে এক নতুন সুন্দর জগৎ তৈরি করার জন্য। এই নতুনের আগমনকে স্বাগত জানাতেই কবি জয়ধ্বনি করতে বলেছেন।
২. “ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর” – ‘সে’ কে? এই পঙক্তিটির তাৎপর্য কী?
উত্তর: এখানে ‘সে’ বলতে প্রলয়ংকর শিব বা মহাকালকে বোঝানো হয়েছে, যিনি ধ্বংসের দেবতা হলেও তিনিই আবার সৃষ্টির দেবতা। এই পঙক্তিটির তাৎপর্য হলো, ধ্বংসই শেষ কথা নয়, ধ্বংসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির বীজ। পুরনো, জীর্ণ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলেই এক নতুন ও সুন্দর ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।
৩. “ওই নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়” – ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: এই পঙক্তিতে ‘কালবোশেখীর ঝড়’ হলো প্রলয় বা বিপ্লবের প্রতীক। আর ‘নূতনের কেতন’ হলো নতুন যুগের বা স্বাধীনতার আগমনের প্রতীক। কবি বলতে চেয়েছেন যে, কালবোশেখীর ঝড়ের মতো ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার মধ্যেই নতুন যুগের পতাকা উড়ছে। অর্থাৎ, বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক রূপ দেখেই নতুন যুগের আগমনকে চেনা যায়।
৪. দিগম্বরের জটায় শিশু-চাঁদের কর হাসার তাৎপর্য কী?
উত্তর: দিগম্বর বা মহাদেব হলেন ধ্বংসের দেবতা, তাঁর জটা ধ্বংসের প্রতীক। কিন্তু সেই ধ্বংসের মধ্যেই ‘শিশু-চাঁদের কর’ বা নতুন চাঁদের স্নিগ্ধ আলো হাসছে। এর তাৎপর্য হলো, ধ্বংস যতই ভয়াবহ হোক না কেন, তার মধ্যেই নতুন সৃষ্টি, নতুন আশা ও সৌন্দর্যের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে।
৫. “আসছে নবীন-জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!” – ‘নবীন’ ও ‘অ-সুন্দর’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর: এখানে ‘নবীন’ বলতে নতুন যুগের বিপ্লবী শক্তিকে বোঝানো হয়েছে। আর ‘অ-সুন্দর’ বলতে পুরনো, জরাগ্রস্ত, প্রাণহীন, অন্যায়-অত্যাচারে পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। কবি বলতে চেয়েছেন যে, নতুন বিপ্লবী শক্তি আসছে এই পুরনো, অন্যায়ের সমাজকে ধ্বংস করে এক নতুন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য।
৬. “এবার মহানিশার শেষে/আসবে ঊষা অরুণ হেসে” – এই পঙক্তিটির মধ্যে দিয়ে কবি কীসের ইঙ্গিত দিয়েছেন?
উত্তর: এই পঙক্তিটির মধ্যে দিয়ে কবি এক গভীর আশার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ‘মহানিশা’ হলো পরাধীনতার অন্ধকার এবং ধ্বংসের রাত্রি। কবি বিশ্বাস করেন, এই অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়। এই প্রলয়ের রাত্রি শেষ হলেই ‘ঊষা’ বা নতুন সকাল আসবে। ‘অরুণ হেসে’ কথাটি সেই নতুন যুগের আনন্দময় ও উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে।
৭. সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধূমকেতুকে আঘাত হানতে বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: ‘সিন্ধু-পার’ বলতে এখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে এবং ‘সিংহ-দ্বার’ হলো তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র। ধূমকেতু হলো ধ্বংসের প্রতীক। কবি চেয়েছেন, বিপ্লবী শক্তি যেন ধূমকেতুর মতো ভয়ংকর রূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে।
৮. “বধূরা প্রদীপ তুলে ধর” – বধূদের প্রতি কবির এই আহ্বানের কারণ কী?
উত্তর: ভারতীয় সংস্কৃতিতে বধূরা প্রদীপ তুলে মঙ্গলময় শক্তিকে বরণ করে। কবি এখানে প্রলয় বা ধ্বংসকে অমঙ্গল হিসেবে না দেখে, মঙ্গলময় শক্তি হিসেবে দেখেছেন। কারণ এই প্রলয়ই নতুন যুগের সূচনা করবে। তাই কবি দেশের নারীদের আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যেন এই প্রলয়ংকর কিন্তু সুন্দর শক্তিকে প্রদীপ জ্বেলে বরণ করে নেন।
৯. “বিশ্বমায়ের আসন” এবং “বিপুলের বুকে” – এই শব্দগুচ্ছের তাৎপর্য কী?
উত্তর: ‘বিশ্বমাতা’ হলেন সমগ্র বিশ্বের জননী। তাঁর ‘আসন’ বলতে বোঝানো হয়েছে সমগ্র বিশ্ব বা ब्रह्मांड। ‘বিপুলের বুকে’ কথাটির অর্থ হলো এই বিশাল বিশ্বের হৃদয়ে। কবি বলতে চেয়েছেন যে, এই ধ্বংসের ফলে যে নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে, সেখানে কোনো সংকীর্ণতা থাকবে না, তা হবে এক বিশাল, উদার বিশ্বসমাজ, যেখানে বিশ্বমাতা অধিষ্ঠিত থাকবেন।
১০. ‘প্রলয়’ এবং ‘উল্লাস’ – এই দুটি বিপরীতধর্মী বিষয় কবিতায় কীভাবে একসঙ্গে এসেছে?
উত্তর: কবিতায় ‘প্রলয়’ বা ধ্বংস হলো পুরনো, জীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া। এই ধ্বংস সাধারণ মানুষের কাছে ভীতিকর। কিন্তু কবি এই ধ্বংসের মধ্যেই নতুন সৃষ্টির আনন্দ বা ‘উল্লাস’ খুঁজে পেয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, এই প্রলয়ের মাধ্যমেই পরাধীনতার অন্ধকার দূর হবে এবং নতুন যুগের আলো আসবে। তাই ধ্বংসের ভয় ও সৃষ্টির আনন্দ—এই দুই বিপরীত বিষয়ই কবিতায় একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।
১১. ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা কী?
উত্তর: ‘অগ্নিবীণা’ নামটি দুটি শব্দের সমন্বয়—’অগ্নি’ ও ‘বীণা’। ‘অগ্নি’ হলো বিদ্রোহ, বিপ্লব ও ধ্বংসের প্রতীক। ‘বীণা’ হলো সুর, সৃষ্টি ও ভালোবাসার প্রতীক। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি বিদ্রোহের আগুনের পাশাপাশি সৃষ্টির সুরও বাজিয়েছেন। তাই ধ্বংস ও সৃষ্টির এই সমন্বয়ের জন্য কাব্যগ্রন্থের নামকরণটি অত্যন্ত সার্থক।
১২. “রক্ত-মাখা-তৃপাণ” – এই চিত্রকল্পটি কীসের প্রতীক?
উত্তর: ‘তৃপাণ’ শব্দের অর্থ তরবারি। ‘রক্ত-মাখা-তৃপাণ’ চিত্রকল্পটি যুদ্ধের ভয়াবহতা, হিংসা এবং আত্মত্যাগের প্রতীক। এটি বোঝায় যে, নতুন যুগ বা স্বাধীনতা বিনা রক্তপাতে আসবে না। এর জন্য অনেক সংগ্রাম ও আত্মবলিদান প্রয়োজন। ভয়ঙ্কর এই রক্তমাখা তরবারি হাতে নিয়েই পুরনোকে ধ্বংস করতে আসছে।
১৩. “ওই আসে সুন্দর/কাল-ভয়ঙ্করের বেশে” – সুন্দর কীভাবে কাল-ভয়ঙ্করের বেশে আসে?
উত্তর: ‘সুন্দর’ বলতে এখানে নতুন যুগ বা মুক্তিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই সুন্দর সরাসরি আসে না। সে আসে ‘কাল-ভয়ঙ্করের বেশে’ অর্থাৎ ধ্বংসের রূপ ধরে। কারণ পুরনো অন্যায়ের সমাজকে ধ্বংস না করলে নতুন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই সুন্দরের আগমন হয় ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, যা আপাতদৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর মনে হয়।
১৪. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় দাও।
উত্তর: ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন (“সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে… আঘাত হান”)। তিনি পুরনো, জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার কথা বলেছেন। প্রলয় বা ধ্বংসকে তিনি ভয় না পেয়ে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই ধ্বংসাত্মক, আপসহীন মনোভাবই তাঁর বিদ্রোহী সত্তার পরিচায়ক।
১৫. “স্তব্ধ চরাচর” – চরাচর কেন স্তব্ধ হয়ে যায়?
উত্তর: ‘অট্টরোল’ মানে হলো বিকট বা উচ্চ হাসি। ‘হট্টগোল’ মানে গণ্ডগোল। প্রলয়ংকর শিব যখন তাঁর ধ্বংসের অট্টহাসি হাসেন, তখন সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সমগ্র জগৎ বা চরাচর ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি প্রলয়ের ভয়াবহতা ও তার 엄청 প্রভাবকে তুলে ধরেছেন।
১৬. “দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা” – এই উপমাটি ব্যবহারের কারণ কী?
উত্তর: পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, মহাপ্রলয়ের সময় বারোটি সূর্যের একসঙ্গে উদয় হয়, যার প্রচণ্ড তাপে জগৎ ধ্বংস হয়ে যায়। কবি ভয়ঙ্করের চোখের জ্বালাকে সেই ‘দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা’-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রলয়ের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যে কতটা তীব্র ও সর্বগ্রাসী, তা বোঝাতে চেয়েছেন।
১৭. “জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন” – ‘ছেদন’ শব্দটি কেন ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: ‘ছেদন’ শব্দের অর্থ কেটে ফেলা। কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, পুরনো জরাগ্রস্ত সমাজকে সংস্কার করা সম্ভব নয়, তাকে সমূলে উৎপাটিত বা কেটে ফেলতে হবে। এই শব্দটি বিপ্লবী শক্তির আপসহীন ও চরম পদক্ষেপকে নির্দেশ করে। নবীন শক্তি কোনো আপস করতে নয়, বরং পুরনোকে পুরোপুরি ধ্বংস করতেই আসছে।
১৮. কবি কেন দেশবাসীকে ভয় পেতে বারণ করেছেন?
উত্তর: কবি দেশবাসীকে ভয় পেতে বারণ করেছেন কারণ, যে প্রলয় আসছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর হলেও তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মুক্তির সম্ভাবনা। এই প্রলয় হলো পুরনোকে ধ্বংস করে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া। তাই এই ধ্বংসকে ভয় না পেয়ে তাকে স্বাগত জানানো উচিত, কারণ এর ফলেই পরাধীনতার অন্ধকার দূর হবে।
১৯. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর” – এই আহ্বান কাদের প্রতি এবং কেন?
উত্তর: এই আহ্বান পরাধীন, হতাশ ও ভয়ার্ত ভারতবাসীর প্রতি। কবি তাদের জয়ধ্বনি করতে বলেছেন কারণ, যে প্রলয়ংকর শক্তি আসছে, সে হলো মুক্তিদাতা। তার আগমনে পুরনো শাসন ও শোষণ ধ্বংস হবে এবং নতুন যুগের সূচনা হবে। এই মুক্তিদাতার আগমনকে উৎসবের আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেওয়ার জন্যই কবি এই আহ্বান জানিয়েছেন।
২০. কবিতায় ব্যবহৃত পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলির উল্লেখ করো।
উত্তর: কবিতায় ব্যবহৃত পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলি হলো—’দিগম্বর’ (শিব), ‘শিশু-চাঁদ’, ‘দ্বাদশ রবি’ এবং মহাকালের ধারণা। কবি এই পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলি ব্যবহার করে কবিতার ভাবকে এক মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও গভীরতা দান করেছেন। শিবের ধ্বংস ও সৃষ্টির রূপকল্পটিই কবিতার মূল ভিত্তি।
২১. “ওই আসছে ভয়ঙ্কর” – ‘ভয়ঙ্কর’-এর রূপের বর্ণনা দাও।
উত্তর: ‘ভয়ঙ্কর’ আসছে রুক্ষ, বিবর্ণ চুল দুলিয়ে, কালবোশেখীর ঝড়ের মতো। তার চোখে দ্বাদশ সূর্যের আগুন, তার হাতে রক্তমাখা তরবারি এবং সে বজ্রের মশাল জ্বেলে আসছে। তার রণ-বেশে থাকা সত্ত্বেও সে হাসছে, যা ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়।
২২. “ওই ভাঙা-গড়া খেলা যে তার” – এই খেলার स्वरूप কী?
উত্তর: এই খেলার ফর্ম হলো দ্বৈত। একদিকে এটি ভাঙার খেলা—পুরনো, জীর্ণ, অন্যায়ের সমাজকে ধ্বংস করা। অন্যদিকে এটি গড়ার খেলা—সেই ধ্বংসস্তূপের উপর এক নতুন, সুন্দর ও ন্যায়পূর্ণ জগৎ গড়ে তোলা। মহাকাল বা শিবের কাছে এই সৃষ্টি ও ধ্বংস এক লীলা বা খেলার মতো, যা নিরন্তর চলতে থাকে।
২৩. “নীল খিলানের অর্গল” – ‘খিলান’ ও ‘অর্গল’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘খিলান’ শব্দের অর্থ হলো গম্বুজ বা খিলানযুক্ত সিলিং, এখানে নীল আকাশকে বোঝানো হয়েছে। ‘অর্গল’ শব্দের অর্থ হলো হুড়কো বা খিল। কবি কল্পনা করেছেন, নীল আকাশের দরজা যেন বন্ধ ছিল, যা ভেঙে উল্কা বা ধূমকেতুর মতো বিপ্লবী শক্তি পৃথিবীতে নেমে আসছে।
২৪. “জরায়-মৃত”— কাদের বলা হয়েছে? তাদের জন্য কবি কী করছেন?
উত্তর: যারা জরাগ্রস্ত, প্রাণহীন, পরিবর্তনের ভয়ে নিশ্চল হয়ে আছে, সেই সব মৃতপ্রায় মানুষদের ‘জরায়-মৃত’ বলা হয়েছে। কবি তাদের জন্য ‘দিগন্তের কাঁদন’ বা সমবেদনা জানাচ্ছেন। কারণ, এই প্রলয়ে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের ধ্বংসের মাধ্যমেই নতুনের জন্ম হবে।
২৫. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি কীভাবে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন?
উত্তর: ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি ধ্বংসের বর্ণনার মধ্য দিয়েই তীব্র আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই প্রলয় বা ধ্বংসই নতুন সৃষ্টির পথ তৈরি করে। “ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর”, “এবার মহানিশার শেষে/আসবে ঊষা অরুণ হেসে”—এই পঙক্তিগুলির মাধ্যমে কবি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, পরাধীনতার অন্ধকার কেটে গিয়ে স্বাধীনতার নতুন সকাল আসবেই।
ঘ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৫ (১০টি)
১. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
উত্তর:
ভূমিকা: যেকোনো সাহিত্যের নামকরণ তার বিষয়বস্তু ও মূল ভাবের ধারক। কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটির নামকরণ দুটি বিপরীতধর্মী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—’প্রলয়’ ও ‘উল্লাস’, যা কবিতার মূল সুরকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে।
‘প্রলয়’-এর প্রকাশ: কবিতা জুড়ে কবি এক ভয়াবহ প্রলয় বা ধ্বংসের ছবি এঁকেছেন। “কাল-ভয়ঙ্করের বেশে” যে শক্তি আসছে, তা পুরনো, জীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে চায়। “রক্ত-মাখা-তৃপাণ”, “বজ্র-শিখার মশাল”, “অট্টরোলের হট্টগোল”—এই সমস্ত চিত্রকল্প ধ্বংসের ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে। এই প্রলয় হলো পরাধীনতা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত সংহার।
‘উল্লাস’-এর প্রকাশ: কবি এই প্রলয় বা ধ্বংসকে দেখে ভীত নন, বরং আনন্দিত। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন “তোরা সব জয়ধ্বনি কর”। এই উল্লাসের কারণ হলো, কবি জানেন যে, এই ধ্বংসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই প্রলয়ই “জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন” করে এক নতুন সুন্দর জগৎ গড়ে তুলবে। এই ধ্বংসের রাত্রি শেষ হলেই “আসবে ঊষা অরুণ হেসে”।
সমন্বয় ও সার্থকতা: কবি ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই ‘প্রলয়’ তাঁর কাছে ভয়ের কারণ নয়, ‘উল্লাস’-এর কারণ। যেহেতু কবিতার মূল ভাবই হলো ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুনের আবাহন, তাই ‘প্রলয়োল্লাস’ নামকরণটি কবিতার বিষয়বস্তু ও কবির আশাবাদী দর্শনকে সার্থকভাবে ধারণ করেছে।
২. “ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর।” – ‘সে’ কে? তার ভাঙা-গড়ার খেলার स्वरूपটি কবিতার বিষয়বস্তু অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও।
উত্তর:
‘সে’-এর পরিচয়: ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ‘সে’ বলতে কবি প্রলয়ংকর শিব বা মহাকালকে বুঝিয়েছেন। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, শিব একদিকে যেমন ধ্বংসের দেবতা, তেমনই তিনি সৃষ্টির দেবতা। এই দ্বৈত সত্তারূপেই তিনি ‘চিরসুন্দর’।
ভাঙা-গড়ার খেলার স্বরূপ:
১. ভাঙার খেলা: কবিতার প্রেক্ষাপটে, ‘ভাঙা’ বলতে পুরনো, জরাগ্রস্ত, পরাধীন সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করাকে বোঝানো হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন ও তার ফলে সৃষ্ট অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ—এই সমস্ত ‘অ-সুন্দর’-কে মহাকাল বা তাঁর প্রতীক বিপ্লবী শক্তি ভেঙে চুরমার করে দেবে। এই ভাঙার রূপ ভয়ংকর—”রক্ত-মাখা-তৃপাণ” হাতে, “বজ্র-শিখার মশাল” জ্বেলে তার আগমন।
২. গড়ার খেলা: কিন্তু এই ভাঙাই শেষ কথা নয়। মহাকালের খেলার দ্বিতীয় অংশ হলো ‘গড়া’। তিনি পুরনোকে ধ্বংস করেন এক নতুন, সুন্দর জগৎ গড়ার জন্য। এই ধ্বংসের মধ্য দিয়েই পরাধীনতার ‘মহানিশা’ শেষ হবে এবং স্বাধীনতার ‘ঊষা’ আসবে। এই নতুন জগৎ হবে অন্যায়মুক্ত, শোষণমুক্ত এবং সুন্দর।
উপসংহার: সুতরাং, মহাকালের এই ভাঙা-গড়ার খেলা আসলে এক চক্রাকার প্রক্রিয়া। ধ্বংসের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন। যা কিছু অসুন্দর ও জীর্ণ, তাকে ভেঙে ফেলেই তিনি এক চিরসুন্দর জগৎ গড়ে তোলেন। এই ধ্বংসাত্মক সৃষ্টিশীলতাই হলো তাঁর খেলার মূল স্বরূপ।
৩. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি প্রলয়ের যে ভয়ঙ্কর রূপ চিত্রিত করেছেন, তা নিজের ভাষায় লেখো। এই ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে কবি কীভাবে আশার আলো খুঁজে পেয়েছেন?
উত্তর:
ভূমিকা: কাজী নজরুল ইসলাম ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় প্রলয়ের এক দ্বৈত রূপ চিত্রিত করেছেন। একদিকে তা ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক, অন্যদিকে তা আশার বার্তাবহ।
প্রলয়ের ভয়ঙ্কর রূপ:
কবি প্রলয়কে এক জীবন্ত, শক্তিশালী সত্তা হিসেবে এঁকেছেন। সে আসছে “কাল-ভয়ঙ্করের বেশে”, যার রুক্ষ চুল দুলছে। তার চোখে বারোটি সূর্যের আগুন, হাতে রক্তমাখা তরবারি এবং সে বজ্রের মশাল জ্বেলে আসছে। তার ভয়ঙ্কর অট্টহাসিতে চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়। সে ধূমকেতুর মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রে আঘাত হানে। তার আগমনে জগৎ জুড়ে প্রলয়ের অন্ধকার রাত্রি ঘনিয়ে আসে। এই চিত্রগুলি প্রলয়ের এক ধ্বংসাত্মক ও ভয়ংকর রূপকে তুলে ধরে।
আশার আলোর সন্ধান: এই ভয়ংকর রূপের মধ্যেই কবি আশার আলো খুঁজে পেয়েছেন।
১. ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি: কবি দেখেছেন, ধ্বংসের দেবতা শিবের জটাতেই শিশু-চাঁদের আলো হাসে। এর অর্থ, ধ্বংসের অন্ধকারেই সৃষ্টির আলো লুকিয়ে আছে।
২. প্রলয়ই মুক্তিদাতা: এই প্রলয় আসছে পুরনো, অসুন্দরকে ধ্বংস করতে। তাই এই ধ্বংসাত্মক রূপই মুক্তির পথ তৈরি করবে।
৩. নতুন ভোরের ইঙ্গিত: কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রলয়ের রাত্রি শেষ হলেই নতুন সকাল আসবে। “এবার মহানিশার শেষে/আসবে ঊষা অরুণ হেসে” – এই পঙক্তিটিই তাঁর চূড়ান্ত আশাবাদ।
উপসংহার: এভাবেই, কবি প্রলয়ের ভয়ংকর রূপের বর্ণনা দিয়েও তার বিনাশী শক্তির আড়ালে থাকা সৃষ্টিশীল ও মঙ্গলময় রূপটিকে আবিষ্কার করেছেন এবং দেশবাসীকে আশার বাণী শুনিয়েছেন।
৪. “তোরা সব জয়ধ্বনি কর” – কবি কাদের এবং কেন বারবার জয়ধ্বনি করতে বলেছেন?
উত্তর:
ভূমিকা: ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় “তোরা সব জয়ধ্বনি কর” পঙক্তিটি ধ্রুবপদের মতো বারবার ফিরে এসেছে। এই আহ্বানের মাধ্যমে কবি পরাধীন দেশবাসীর মনে সাহস ও উদ্দীপনা সঞ্চার করতে চেয়েছেন।
আহ্বানের লক্ষ্য: এই আহ্বান পরাধীন, হতাশ, ভয়ার্ত ভারতবাসীর প্রতি। যারা ব্রিটিশ শাসনে অত্যাচারিত এবং মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না, কবি তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন।
জয়ধ্বনির কারণ:
১. প্রলয়কে স্বাগত জানানো: যে প্রলয়ংকর শক্তি আসছে, সে আপাতদৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর হলেও আসলে সে মুক্তিদাতা। সে পুরনো জীর্ণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন যুগের সূচনা করতে আসছে। এই মুক্তিদাতার আগমনকে ভয় না পেয়ে, উৎসবের আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নেওয়ার জন্যই জয়ধ্বনি করতে বলা হয়েছে।
২. ভয়কে জয় করা: জয়ধ্বনি হলো ভয়ের বিপরীত এক উল্লাসের প্রকাশ। কবি চেয়েছেন, দেশবাসী যেন ধ্বংসের ভয়কে জয় করে, সাহসের সঙ্গে বিপ্লবকে আলিঙ্গন করে।
৩. আত্মবিশ্বাস জাগানো: জয়ধ্বনি আত্মবিশ্বাস ও শক্তির প্রতীক। এই আহ্বানের মাধ্যমে কবি দেশবাসীর মনে শক্তি ও বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন যে, পরিবর্তন আসন্ন এবং তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।
৪. নতুনের আবাহন: এই জয়ধ্বনি শুধুমাত্র ধ্বংসের জন্য নয়, এটি নতুনের আগমনের জন্য। “নূতনের কেতন” উড়ছে, তাই সেই নতুনকে স্বাগত জানানোর জন্যই এই জয়ধ্বনি।
উপসংহার: সুতরাং, এই জয়ধ্বনি হলো ভয়কে জয় করে, সাহসের সঙ্গে বিপ্লবকে বরণ করে নেওয়ার এবং নতুন যুগের প্রতি আস্থা রাখার এক সম্মিলিত আহ্বান।
৫. “আসছে নবীন-জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!” – এই পঙক্তিটির আলোকে ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার এই পঙক্তিটি সমগ্র কবিতার মূল সুর ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করে আছে। এটি কবিতার আশাবাদী দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।
পঙক্তিটির বিশ্লেষণ:
‘নবীন’: ‘নবীন’ বলতে এখানে শুধুমাত্র তরুণ প্রজন্মকে বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে এক নতুন বিপ্লবী শক্তিকে, যে শক্তি প্রচলিত জীর্ণতাকে মানে না। এই নবীনই হলো প্রলয়ের চালিকাশক্তি।
‘জীবন-হারা অ-সুন্দর’: এই শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে কবি পরাধীন, শোষিত, জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন। যে সমাজে প্রাণ নেই, সৌন্দর্য নেই, আছে শুধু অন্যায় ও অত্যাচার, তাকেই তিনি ‘জীবন-হারা অ-সুন্দর’ বলেছেন।
‘করতে ছেদন’: ‘ছেদন’ অর্থাৎ কেটে ফেলা। কবি এখানে সংস্কার বা পরিবর্তনের কথা বলেননি, বলেছেন সমূলে উৎপাটিত করার কথা। এই নবীন শক্তি আসছে পুরনো ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলতে।
মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্ক:
এই পঙক্তিটিই কবিতার মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করে। কবিতাটির মূল বক্তব্য হলো, ধ্বংসাত্মক প্রলয়ের মধ্য দিয়েই নতুন ও সুন্দর জগতের সৃষ্টি হয়। এই লাইনটি স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রলয়ের উদ্দেশ্য ধ্বংস নয়, বরং ‘অ-সুন্দর’-কে ধ্বংস করে এক নতুন জীবন ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করা। কবি যে ‘উল্লাস’-এর কথা বলেছেন, তার কারণও এই লাইনে নিহিত। দেশবাসী আনন্দিত হবে কারণ, এই নবীনের আগমনে তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে। এভাবেই, এই পঙক্তিটি কবিতার ধ্বংসাত্মক ও সৃজনশীল—উভয় দিককে যুক্ত করে মূল বক্তব্যকে সার্থক করে তুলেছে।
৬. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি একদিকে ধ্বংসের ছবি এঁকেছেন, আবার অন্যদিকে নতুন আশার বাণী শুনিয়েছেন। এই দ্বৈত ভাবনার প্রকাশ কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি ধ্বংস ও সৃষ্টির দ্বৈত ভাবনার এক অপূর্ব শৈল্পিক সমন্বয়। কবি প্রলয়ের ভয়াবহ রূপের বর্ণনার পাশাপাশি তার মধ্যে থেকে নতুন আশার আলো দেখিয়েছেন।
ধ্বংসের ছবি:
কবি প্রলয়কে চিত্রিত করেছেন এক ভয়ংকর সত্তা হিসেবে। সে আসছে “কাল-ভয়ঙ্করের বেশে”, তার হাতে “রক্ত-মাখা-তৃপাণ”। তার আগমনে চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়, জগৎ জুড়ে প্রলয়ের অন্ধকার রাত্রি ঘনিয়ে আসে। সে “সর্বনাশী-জ্বালিয়া-দেওয়া-ধূমকেতু”র মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রে আঘাত হানে। এই চিত্রগুলি ধ্বংসের এক ভয়াবহ ও নির্মম ছবি তুলে ধরে।
নতুন আশার বাণী:
এই ধ্বংসের চিত্রের মধ্যেই কবি আশার বাণী শুনিয়েছেন।
১. ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি: কবি দেখিয়েছেন, ধ্বংসের দেবতা শিবের জটাতেই “শিশু-চাঁদের কর” হাসে, যা ধ্বংসের মধ্যে নতুন সৃষ্টির প্রতীক।
২. ধ্বংসের উদ্দেশ্য: এই ধ্বংসলীলার উদ্দেশ্য হলো “জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন”। অর্থাৎ, পুরনো জীর্ণতাকে ধ্বংস করে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য।
৩. নতুন ভোরের আগমন: কবি চূড়ান্ত আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, “এবার মহানিশার শেষে/আসবে ঊষা অরুণ হেসে”। তিনি দেশবাসীকে ভয় না পেয়ে হাসতে বলেছেন, কারণ এই ধ্বংসের রাত্রি কেটে গেলেই স্বাধীনতার নতুন সকাল আসবে।
উপসংহার: এভাবেই, কবি ধ্বংসের ভয়াবহতাকে স্বীকার করেও, তাকে নতুন সৃষ্টির সোপান হিসেবে দেখেছেন। এই দ্বৈত ভাবনার সার্থক প্রকাশের ফলেই ‘প্রলয়োল্লাস’ একটি সার্থক বিপ্লবী ও আশাবাদী কবিতায় পরিণত হয়েছে।
৭. “ওই ভাঙা-গড়া খেলা যে তার” – ‘তার’ বলতে কার কথা বলা হয়েছে? তার এই ভাঙা-গড়া খেলার स्वरूप ও উদ্দেশ্য কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
পরিচয়: ‘তার’ বলতে এখানে মহাকাল বা প্রলয়ংকর শিবকে বোঝানো হয়েছে। পৌরাণিক বিশ্বাসে, শিব হলেন ধ্বংস ও সৃষ্টির দেবতা। তাঁর এই দ্বৈত রূপকেই কবি এখানে ব্যবহার করেছেন।
খেলার স্বরূপ: এই ভাঙা-গড়া খেলা হলো এক নিরন্তর চক্রাকার প্রক্রিয়া।
ভাঙা: খেলার প্রথম অংশ হলো ‘ভাঙা’ বা ধ্বংস। যখন পৃথিবীতে অন্যায়, অত্যাচার, জরা ও স্থবিরতা বেড়ে যায়, তখন মহাকাল তাঁর প্রলয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন। তিনি পুরনো, পাপপূর্ণ বিশ্বকে ভেঙে চুরমার করে দেন। কবিতায় এই ভাঙার রূপ চিত্রিত হয়েছে কালবোশেখীর ঝড়, ধূমকেতু এবং রক্তমাখা তরবারির মাধ্যমে।
গড়া: খেলার দ্বিতীয় অংশ হলো ‘গড়া’ বা সৃষ্টি। ধ্বংসস্তূপের উপরই তিনি এক নতুন জগৎ গড়ে তোলেন। এই নতুন জগৎ হয় অন্যায়মুক্ত, শোষণমুক্ত এবং প্রাণবন্ত। কবিতায় এই গড়ার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে “নূতনের কেতন”, “আসবে ঊষা অরুণ হেসে” ইত্যাদি চিত্রকল্পের মাধ্যমে।
উদ্দেশ্য: এই খেলার মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের ভারসাম্য রক্ষা করা। যা কিছু পুরনো, জীর্ণ, অসুন্দর ও প্রাণহীন, তাকে ধ্বংস করে নতুন, সুন্দর ও প্রাণবন্ত কিছু সৃষ্টি করাই এই খেলার লক্ষ্য। এটি একটি চিরন্তন নিয়ম, যার মাধ্যমে জগৎ এগিয়ে চলে। কবি এই পৌরাণিক ধারণাটিকে পরাধীন ভারতের মুক্তির প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করে বুঝিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসের মাধ্যমেই ভারতের নতুন স্বাধীনতা আসবে।
৮. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি যে সমস্ত পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, তার পরিচয় ও সার্থকতা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: কাজী নজরুল ইসলাম ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ভাবকে তীব্র ও শক্তিশালী করার জন্য পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের সার্থক ব্যবহার করেছেন।
পৌরাণিক চিত্রকল্প:
১. দিগম্বর ও শিশু-চাঁদ: কবি প্রলয়ংকরকে শিব বা ‘দিগম্বর’-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিবের ধ্বংসাত্মক রূপের (জটা) মধ্যেই তিনি স্নিগ্ধ শিশু-চাঁদের আলোর মতো নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়েছেন।
২. দ্বাদশ রবি: ভয়ঙ্করের চোখের জ্বালাকে কবি মহাপ্রলয়ের সময়ের ‘দ্বাদশ রবি’র সঙ্গে তুলনা করে ধ্বংসের তীব্রতাকে প্রকাশ করেছেন।
প্রাকৃতিক চিত্রকল্প:
১. কালবোশেখী: কালবোশেখীর ঝড় যেমন পুরনো, শুকনো পাতাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন প্রাণের পথ করে দেয়, তেমনই বিপ্লবী শক্তি পুরনো সমাজকে ধ্বংস করে নতুন যুগের সূচনা করে।
২. ধূমকেতু ও উল্কা: ধূমকেতু বা উল্কা যেমন আকস্মিকভাবে আঘাত হেনে ধ্বংস সাধন করে, তেমনই বিপ্লবী শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানবে।
সার্থকতা: এই সমস্ত চিত্রকল্প কবিতার বক্তব্যকে এক মহাকাব্যিক বিস্তার ও গভীরতা দিয়েছে। পৌরাণিক চিত্রকল্পগুলি ধ্বংস ও সৃষ্টির চিরন্তন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, আর প্রাকৃতিক চিত্রকল্পগুলি বিপ্লবের ভয়াবহতা ও তার অবশ্যম্ভাবী আগমনকে মূর্ত করে তুলেছে। এই চিত্রকল্পের সার্থক প্রয়োগই কবিতাটিকে শক্তিশালী ও আবেদনময়ী করেছে।
৯. “এবার মহানিশার শেষে/আসবে ঊষা অরুণ হেসে” – ‘মহানিশা’ ও ‘ঊষা’ কিসের প্রতীক? এই পঙক্তিটির মধ্যে দিয়ে কবির যে চরম আশাবাদ ফুটে উঠেছে, তা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
প্রতীকী অর্থ:
‘মহানিশা’: ‘মহানিশা’ বা গভীর রাত্রি এখানে শুধুমাত্র সময়ের একটি অংশ নয়। এটি পরাধীনতার অন্ধকার, শোষণ, বঞ্চনা এবং হতাশার প্রতীক। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের দুঃখময় অবস্থাকেই কবি ‘মহানিশা’ বলেছেন। কবিতার বর্ণিত প্রলয় বা ধ্বংসের সময়টিও এই মহানিশারই অংশ।
‘ঊষা’: ‘ঊষা’ বা ভোর হলো নতুন দিনের সূচনার প্রতীক। এখানে ঊষা হলো স্বাধীনতা, মুক্তি এবং এক নতুন, সুন্দর যুগের প্রতীক। ‘অরুণ হেসে’ কথাটি সেই নতুন যুগের আনন্দময়, উজ্জ্বল এবং রক্তিম সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।
কবির চরম আশাবাদ:
কবিতার সামগ্রিক ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ আবহের পরেও, কবি এই পঙক্তিটির মাধ্যমে তাঁর চূড়ান্ত আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কোনো অন্ধকারই চিরস্থায়ী নয়। রাত্রির পরেই যেমন দিন আসে, তেমনই পরাধীনতার এই ‘মহানিশা’ একদিন শেষ হবেই। প্রলয় বা বিপ্লবের পথ ধরেই সেই স্বাধীনতার ‘ঊষা’ আসবে। এই গভীর বিশ্বাস ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই কবিকে এবং তাঁর মাধ্যমে দেশবাসীকে সমস্ত ভয় ও হতাশার ঊর্ধ্বে উঠে আশাবাদী হতে অনুপ্রাণিত করেছে। এটিই কবিতার মূল চালিকাশক্তি।
১০. ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাকে একটি জাগরণমূলক কবিতা বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: হ্যাঁ, ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাকে নিঃসন্দেহে একটি সার্থক জাগরণমূলক কবিতা বলা যায়। এই কবিতার মূল উদ্দেশ্যই হলো পরাধীন, হতাশ দেশবাসীর মনে সাহস, শক্তি ও চেতনার জাগরণ ঘটানো।
যুক্তিসমূহ:
১. ভয়কে জয় করার আহ্বান: কবি দেশবাসীকে প্রলয়ের ভয়ংকর রূপ দেখে ভয় পেতে বারণ করেছেন (“তোরা সব জয়ধ্বনি কর”, “এবার তোরা ভয় পেয়েছিস, তাই দেখি তোর হেসেই আকুল”)। তিনি ভয়কে জয় করে বিপ্লবকে স্বাগত জানানোর কথা বলেছেন, যা এক ধরনের মানসিক জাগরণ।
২. নতুনের আবাহন: কবি দেখিয়েছেন যে, প্রলয়ের মধ্য দিয়েই ‘নবীন’ বা নতুন যুগের আগমন ঘটছে। এই নতুনের প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে এবং তাদের নিষ্ক্রিয়তা থেকে জাগিয়ে তোলে।
৩. সক্রিয় অংশগ্রহণের ডাক: “বধূরা প্রদীপ তুলে ধর” – এই আহ্বানের মাধ্যমে কবি দেশের নারীদেরও এই মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে বলেছেন। এটি এক সামাজিক জাগরণের ডাক।
৪. উদ্দীপক শব্দ ও ছন্দ: কবিতার দ্রুত লয়ের ছন্দ, ওজস্বী শব্দ ব্যবহার (“অট্টরোলের হট্টগোলে”, “রক্ত-মাখা-তৃপাণ”) এবং ‘জয়ধ্বনি কর’ পঙক্তিটির বারবার ব্যবহার পাঠকের মনে এক ধরনের উদ্দীপনা ও জাগরণ সৃষ্টি করে।
উপসংহার: যেহেতু কবিতাটি মানুষকে ভয়, হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত করে সাহস, আশা ও সক্রিয়তার পথে চালিত করে, তাই একে একটি সার্থক জাগরণমূলক কবিতা বলাই যুক্তিযুক্ত।
Class 10 bengali প্রলয়োল্লাস question answer
প্রলয়োল্লাস কাজী নজরুল ইসলাম কবিতার প্রশ্ন উত্তর, MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 bengali প্রলয়োল্লাস কবিতার প্রশ্ন উত্তর