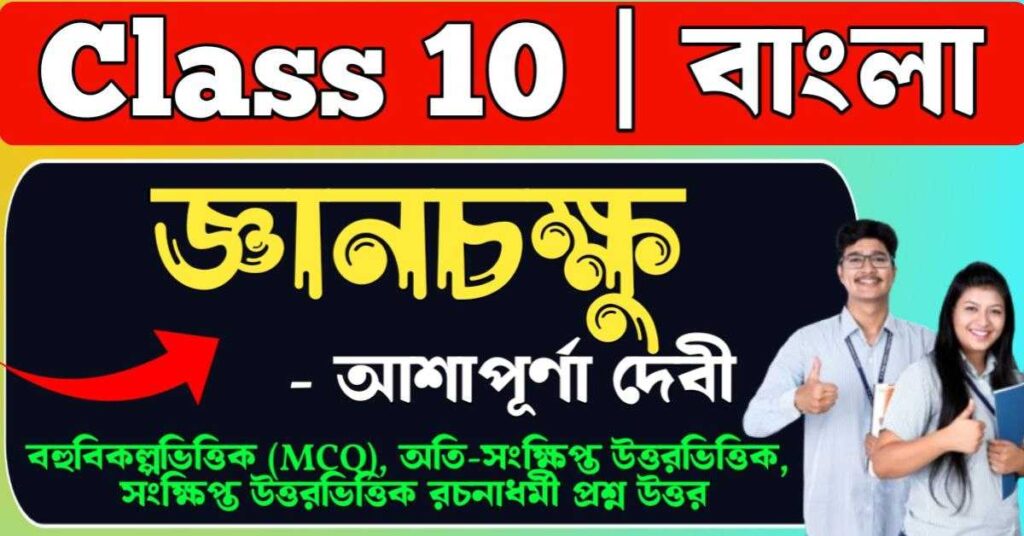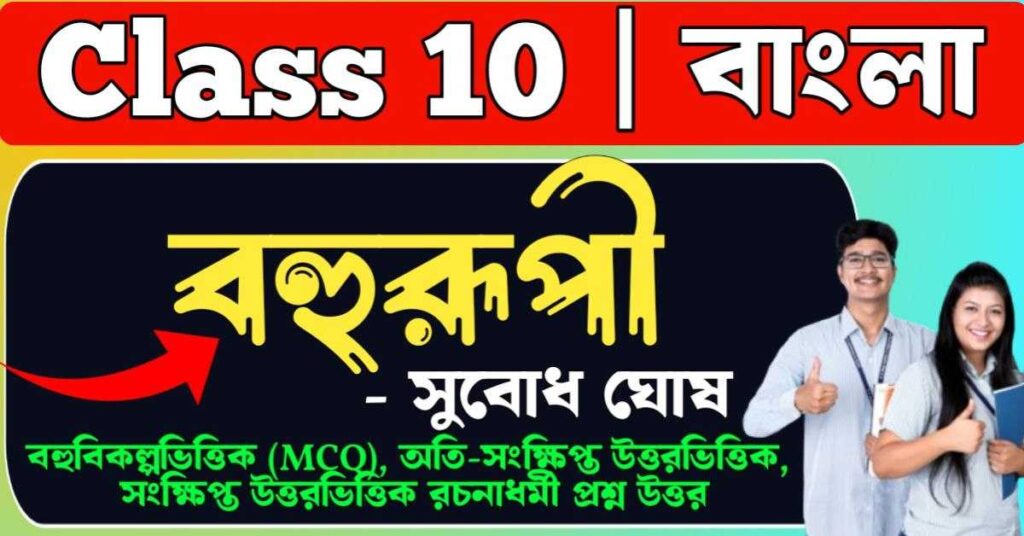বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধের প্রশ্ন উত্তর
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ( রাজশেখর বসু )
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৫০টি)
১. ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধটির লেখকের ছদ্মনাম কী?
২. লেখকের আসল নাম কী?
৩. লেখকের মতে, বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের পাঠক কয় প্রকার?
৪. প্রথম শ্রেণীর পাঠক কারা?
৫. “এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।” – কোন কথাটি?
৬. লেখকের মতে, কোন শব্দটি বাংলা ভাষায় চালানো যেতে পারে?
৭. পরিভাষা রচনার দায়িত্ব কার উপর দেওয়া উচিত বলে লেখক মনে করেন?
৮. “অনেক সময় দরকারি বিদেশি শব্দ…” – লেখকের মতে কী করা উচিত?
৯. “আমাদের অলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন।” – সেগুলি কী কী?
১০. বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে কোন গুণের প্রয়োজন নেই?
১১. “এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে…” – কোন দোষের কথা বলা হয়েছে?
১২. “যার পেটে খেলে পিঠে সয়” – এই প্রবাদটি কী প্রসঙ্গে ব্যবহৃত?
১৩. ‘Sensitized paper’-এর কী অনুবাদ করা হয়েছিল?
১৪. ‘অভিধা’ শব্দের অর্থ কী?
১৫. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিল?
১৬. বৈজ্ঞানিক রচনার ভাষা কেমন হওয়া উচিত?
১৭. ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’ – এই বাক্যটির বিশেষত্ব কী?
১৮. পরিভাষা রচনায় কাদের অংশগ্রহণ করা উচিত নয়?
১৯. “তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে” – কাদের চেষ্টা?
২০. লেখকের মতে, ‘অক্সিজেন’ ও ‘হাইড্রোজেন’-এর বাংলা কী হওয়া উচিত?
২১. “তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবার একটা কারণ” – কারণটি কী?
২২. ‘পরিভাষা’ শব্দের অর্থ কী?
২৩. কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার কম?
২৪. লেখকের মতে, বাংলায় বিজ্ঞান রচনার প্রধান বাধা কী?
২৫. ‘প্রয়াস’ শব্দের অর্থ কী?
২৬. বৈজ্ঞানিক লেখকের কী থাকা আবশ্যক?
২৭. “এই ধারণা একেবারে ভুল” – কোন ধারণা?
২৮. ‘সন্দর্ভ’ শব্দের অর্থ কী?
২৯. উপমা প্রয়োগে লেখকের মতে কাদের লেখা শ্রেষ্ঠ?
৩০. ‘অরণ্যে রোদন’ প্রবাদটির অর্থ কী?
৩১. রাজশেখর বসু পেশায় কী ছিলেন?
৩২. দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক কারা?
৩৩. ‘পরিপাট্য’ শব্দের অর্থ কী?
৩৪. কোন ধরনের রচনায় লেখকের স্বাধীনতা কম?
৩৫. “বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় এখনো নানা রকম বাধা আছে।” – প্রধান বাধাটি কী?
৩৬. ‘অলংকার’ প্রয়োগ করা যেতে পারে কোথায়?
৩৭. ‘হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড’ – এটি কার উক্তি?
৩৮. ‘অত্যুক্তি’ দোষ কখন ঘটে?
৩৯. পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টা বাংলায় কত বছর ধরে চলছে?
৪০. ‘The temper of the pot is in the baking’ – এই বাক্যের ভাবার্থ কী?
৪১. লেখকের মতে, ‘বৈজ্ঞানিক’ শব্দের অর্থ কী?
৪২. ‘আক্ষরিক’ অনুবাদ করলে কী দোষ ঘটে?
৪৩. ‘ন্যাসান্যাল’ শব্দের অর্থ কী?
৪৪. লেখকের মতে, অল্পবয়স্ক পাঠকদের জন্য কী প্রয়োজন?
৪৫. পরিভাষা সমিতির কাজ কী?
৪৬. “এই রকম বর্ণনা…” – কোন ধরনের বর্ণনা?
৪৭. ‘অবকাশ’ শব্দের অর্থ কী?
৪৮. লেখক কাকে ‘পন্ডিত’ বলেছেন?
৪৯. লেখকের মতে, বিজ্ঞান আলোচনার জন্য কী বর্জন করা উচিত?
৫০. প্রবন্ধের শেষে লেখক কীসের উপর জোর দিয়েছেন?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৪০টি)
১. ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধটির লেখকের ছদ্মনাম কী?
উত্তর: ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধটির লেখকের ছদ্মনাম পরশুরাম।
২. লেখকের মতে, বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের পাঠক কয় শ্রেণীর?
উত্তর: লেখকের মতে, বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভের পাঠক দুই শ্রেণীর।
৩. ‘অভিধা’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘অভিধা’ শব্দের অর্থ হলো বাচ্যার্থ বা শব্দের মূল ও সরল অর্থ।
৪. পরিভাষা রচনায় কাদের অংশগ্রহণ করা উচিত?
উত্তর: পরিভাষা রচনায় বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লেখকদের অংশগ্রহণ করা উচিত।
৫. কোন ইংরেজি শব্দগুলি বাংলায় চালানো যেতে পারে বলে লেখক মনে করেন?
উত্তর: অক্সিজেন, ভিটামিন-এর মতো সর্বজনগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য ইংরেজি শব্দগুলি বাংলায় চালানো যেতে পারে বলে লেখক মনে করেন।
৬. ‘The temper of the pot is in the baking’ – এই প্রবাদটির একটি উপযুক্ত বাংলা অনুবাদ কী হতে পারে?
উত্তর: এর উপযুক্ত বাংলা অনুবাদ হতে পারে—”আগুনে পোড়ানোর ফলেই পাত্রের মেজাজ বা গুণ বোঝা যায়”।
৭. বৈজ্ঞানিক রচনার ভাষা কেমন হওয়া উচিত?
উত্তর: বৈজ্ঞানিক রচনার ভাষা অত্যন্ত সরল, স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।
৮. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে পরিভাষা সমিতি নিয়োগ করে?
উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে পরিভাষা সমিতি নিয়োগ করে।
৯. ‘Sensitized paper’-এর কী বাংলা করা হয়েছিল?
উত্তর: ‘Sensitized paper’-এর বাংলা করা হয়েছিল ‘সুগ্রাহী কাগজ’।
১০. বৈজ্ঞানিক রচনায় কোন ধরনের শব্দের প্রয়োজন নেই?
উত্তর: বৈজ্ঞানিক রচনায় ব্যঞ্জনা বা লক্ষণা গুণের শব্দের প্রয়োজন নেই।
১১. ‘অরণ্যে রোদন’ প্রবাদটি কী প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: অল্পবয়স্ক পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করা ‘অরণ্যে রোদন’ বা নিষ্ফল খেদের সমান—এই প্রসঙ্গে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।
১২. ‘এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না’ – কোন দোষ?
উত্তর: ইংরেজি ভাষার আক্ষরিক অনুবাদের ফলে রচনা যে অবোধ্য ও বিকৃত হয়, সেই দোষের কথা বলা হয়েছে।
১৩. শব্দের ত্রিবিধ গুণ কী কী?
উত্তর: শব্দের ত্রিবিধ গুণ হলো—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা।
১৪. ‘ন্যাসান্যাল’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘ন্যাসান্যাল’ (National) শব্দের অর্থ হলো জাতীয়।
১৫. পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টা বাংলায় কত বছর ধরে চলছে?
উত্তর: লেখকের সময়কালে পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টা বাংলায় ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চলছিল।
১৬. উপমা প্রয়োগে কাদের লেখা শ্রেষ্ঠ?
উত্তর: উপমা প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লেখকদের লেখাই শ্রেষ্ঠ।
১৭. ‘পরশুরাম’ কার ছদ্মনাম?
উত্তর: ‘পরশুরাম’ রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম।
১৮. ‘অত্যুক্তি’ দোষ কখন ঘটে?
উত্তর: যখন উপমা বা অলংকারের প্রয়োগ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তখন ‘অত্যুক্তি’ দোষ ঘটে।
১৯. হিমালয়কে ‘পৃথিবীর মানদণ্ড’ কে বলেছেন?
উত্তর: মহাকবি কালিদাস হিমালয়কে ‘পৃথিবীর মানদণ্ড’ বলেছেন।
২০. ‘পরিভাষা’ রচনা করা একজনের কাজ নয় কেন?
উত্তর: কারণ বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করলে পাঠকদের অসুবিধা হয়, তাই একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।
২১. রাজশেখর বসু পেশায় কী ছিলেন?
উত্তর: রাজশেখর বসু পেশায় ছিলেন একজন রসায়নবিদ।
২২. ‘সন্দর্ভ’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘সন্দর্ভ’ শব্দের অর্থ হলো প্রবন্ধ বা রচনা।
২৩. কোন ধরনের পাঠক ইংরেজি জানে না বা অল্প জানে?
উত্তর: প্রথম শ্রেণীর পাঠক ইংরেজি জানে না বা অল্প জানে।
২৪. বিজ্ঞান লেখকের কী গুণ থাকা আবশ্যক?
উত্তর: বিজ্ঞান লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান এবং বাংলা ভাষায় রচনার দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
২৫. ‘পরিভাষা’ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
উত্তর: ‘পরিভাষা’ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Technical Term।
২৬. ‘বৈজ্ঞানিক’ শব্দটি প্রবন্ধে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর: ‘বৈজ্ঞানিক’ শব্দটি প্রবন্ধে ‘বিজ্ঞান সম্পর্কিত’ বা ‘Scientific’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
২৭. লেখক কাদের লেখা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন?
উত্তর: লেখক কালিদাস এবং ব্রহ্মমোহন মল্লিকের লেখা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন।
২৮. প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের জন্য লেখা কেমন হওয়া উচিত?
উত্তর: প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের জন্য লেখা সহজবোধ্য হওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করা যেতে পারে।
২৯. পরিভাষা রচনায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ছিল?
উত্তর: পরিভাষা রচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ছিল।
৩০. ‘যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয়’—তারা কয় শ্রেণীর?
উত্তর: তারা দুই শ্রেণীর।
৩১. ‘অনেক সময় অনর্থক hinaus’ হয় কেন?
উত্তর: যখন কোনো রচনায় অকারণ পান্ডিত্য দেখানো হয় বা দুর্বোধ্য পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, তখন তা অনর্থক hinaus হয়।
৩২. ‘লক্ষণা’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘লক্ষণা’ শব্দের অর্থ হলো লক্ষ্যার্থ বা শব্দের গভীরতর অর্থ।
৩৩. ‘ব্যঞ্জনা’ কী?
উত্তর: ‘ব্যঞ্জনা’ হলো শব্দের সেই গুণ, যা তার বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে ছাপিয়ে এক নতুন অর্থ বা ভাব প্রকাশ করে।
৩৪. লেখকের মতে, বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবের একটি কারণ কী?
উত্তর: লেখকের মতে, বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবের একটি কারণ হলো মাতৃভাষায় উপযুক্ত বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের অভাব।
৩৫. ‘পরিভাষা’ প্রচলিত না হলে কী অসুবিধা হয়?
উত্তর: ‘পরিভাষা’ প্রচলিত না হলে একই শব্দের নানা রকম প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়, যা পাঠকদের বিভ্রান্ত করে।
৩৬. ‘পরিপাট্য’ শব্দের একটি সমার্থক শব্দ লেখো।
উত্তর: ‘পরিপাট্য’ শব্দের একটি সমার্থক শব্দ হলো সুবিন্যস্ত বা শৃঙ্খলা।
৩৭. ‘এইরূপ বিধানের’ বিরুদ্ধে কারা আপত্তি করেন?
উত্তর: ‘এইরূপ বিধানের’ বিরুদ্ধে কিছু খুঁতখুঁতে লোক বা পণ্ডিত আপত্তি করেন।
৩৮. ‘সন্দিগ্ধ’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘সন্দিগ্ধ’ শব্দের অর্থ হলো সন্দেহযুক্ত।
৩৯. লেখকের মতে, কাদের লেখা রচনার পরিপাট্যের জন্য জনপ্রিয়?
উত্তর: লেখকের মতে, পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা রচনার পরিপাট্যের জন্য জনপ্রিয়।
৪০. ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য কী?
উত্তর: ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার বাধাগুলি দূর করে সহজ, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
গ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৫ (১০টি)
১. ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধার কথা বলেছেন, তা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: রাজশেখর বসু তাঁর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাধার কথা উল্লেখ করেছেন।
বাধাগুলি নিম্নরূপ:
১. পারিভাষিক শব্দের অভাব: লেখকের মতে, প্রধান বাধা হলো বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পারিভাষিক বা টেকনিক্যাল শব্দের অভাব। বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ ব্যবহার করায় পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।
২. লেখকের অভাব: বাংলায় এমন লেখকের অভাব রয়েছে, যাঁরা বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন এবং একই সঙ্গে সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারেন।
৩. ভাষারীতিগত সমস্যা: অনেক লেখক অকারণ পাণ্ডিত্য দেখানোর জন্য ভাষাকে কঠিন ও দুর্বোধ্য করে তোলেন। আবার, অনেকে ইংরেজি ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গিকে নষ্ট করে ফেলেন, যা রচনাকে বিকৃত করে।
৪. পাঠকের অনীহা: আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার কম হওয়ায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ার মতো পাঠকের সংখ্যাও কম। এই কারণে প্রকাশকরাও এই ধরনের বই ছাপাতে আগ্রহী হন না।
উপসংহার: এই সমস্ত বাধা দূর করতে পারলেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে লেখক মনে করেন।
২. “যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয়, তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।” – এই দুটি শ্রেণীর পাঠকের পরিচয় দাও। তাদের জন্য বিজ্ঞান রচনার ভাষা কেমন হওয়া উচিত বলে লেখক মনে করেন?
উত্তর:
ভূমিকা: রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার পাঠকদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষারীতি নির্ধারণের কথা বলেছেন।
পাঠকদের পরিচয়:
১. প্রথম শ্রেণী: এই শ্রেণীর পাঠকরা ইংরেজি জানেন না বা খুব অল্প জানেন। তাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করতে চান। সাধারণ মানুষ এবং অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।
২. দ্বিতীয় শ্রেণী: এই শ্রেণীর পাঠকরা ইংরেজি জানেন এবং বিজ্ঞান বিষয়েও তাঁদের জ্ঞান রয়েছে। তাঁরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পড়তে চান মূলত আনন্দ বা কৌতূহলের জন্য। অভিজ্ঞ ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষকরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।
ভাষারীতি কেমন হওয়া উচিত:
প্রথম শ্রেণীর জন্য: এদের জন্য বিজ্ঞান রচনার ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। কঠিন পারিভাষিক শব্দের পরিবর্তে প্রয়োজনে বহুল প্রচলিত ইংরেজি শব্দ (যেমন: অক্সিজেন, ভিটামিন) ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করার জন্য উদাহরণ ও উপমা ব্যবহার করা আবশ্যক।
দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য: এদের জন্য রচনায় নির্ভুল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। তবে এক্ষেত্রেও ভাষার সরলতা ও স্পষ্টতা বজায় রাখা প্রয়োজন। অকারণ পাণ্ডিত্য দেখানো বা ভাষাকে দুর্বোধ্য করা উচিত নয়।
৩. “এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না।” – কোন দোষের কথা বলা হয়েছে? এই দোষ থেকে মুক্তির জন্য লেখক কী কী পরামর্শ দিয়েছেন?
উত্তর:
দোষের পরিচয়: এখানে লেখক ইংরেজি ভাষার আক্ষরিক অনুবাদের দোষের কথা বলেছেন। অনেক লেখক ইংরেজি বাক্যরীতির হুবহু অনুকরণ করে বাংলা প্রবন্ধ লেখেন। এর ফলে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি নষ্ট হয় এবং রচনাটি অত্যন্ত কৃত্রিম, অবোধ্য ও শ্রুতিকটু হয়ে ওঠে। লেখক মনে করেন, এই দোষটি বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উন্নতির পথে এক বিরাট বাধা।
মুক্তির পরামর্শ: এই দোষ থেকে মুক্তির জন্য লেখক নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছেন—
১. মূল ভাব গ্রহণ: লেখকের মতে, ইংরেজি থেকে শুধু মূল ভাবটি গ্রহণ করতে হবে। তারপর তা বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী সহজ করে লিখতে হবে।
২. আক্ষরিক অনুবাদ বর্জন: Passive voice বা অন্যান্য ইংরেজি বাক্যরীতির আক্ষরিক অনুবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।
৩. ভাষার স্বাভাবিকতা রক্ষা: লেখককে খেয়াল রাখতে হবে যেন তাঁর লেখা সাবলীল ও স্বাভাবিক হয়, পড়ে যেন মনে না হয় এটি কোনো বিদেশি ভাষার অনুবাদ।
৪. अभ्यास: এই দক্ষতা অর্জনের জন্য লেখককে ক্রমাগত अभ्यास করে যেতে হবে।
লেখকের মতে, এই পরামর্শগুলি মেনে চললেই বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই দোষ থেকে মুক্ত হতে পারবে।
৪. পরিভাষা রচনা প্রসঙ্গে লেখকের মতামত আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে রাজশেখর বসু পরিভাষা বা টেকনিক্যাল টার্ম রচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত মতামত দিয়েছেন।
লেখকের মতামত:
১. সম্মিলিত প্রচেষ্টা: লেখকের মতে, পরিভাষা রচনা কোনো একজন লেখকের কাজ নয়। এটি একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল হওয়া উচিত। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর এই দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন, যেখানে বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লেখকরা মিলেমিশে পরিভাষা তৈরি করবেন।
২. শব্দের নির্বাচন: পরিভাষা তৈরির সময় শব্দের উৎস কী হবে, তা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। শব্দটি সংস্কৃত, ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষা থেকে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মূল লক্ষ্য হবে শব্দটি যেন সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য এবং বিষয়টির অর্থ প্রকাশে সক্ষম হয়।
৩. ইংরেজি শব্দের গ্রহণ: যে সমস্ত ইংরেজি শব্দ (যেমন: অক্সিজেন, ভিটামিন) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত, সেগুলির বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির কোনো প্রয়োজন নেই। সেগুলি সরাসরি ব্যবহার করাই শ্রেয়।
৪. স্থিতি ও প্রচার: একবার কোনো পরিভাষা গৃহীত হলে, সমস্ত লেখকের উচিত সেই শব্দটিই ব্যবহার করা, যাতে পাঠকদের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।
উপসংহার: এভাবেই, লেখক পরিভাষা রচনায় গোঁড়ামি ত্যাগ করে এক উদার, বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত পথের নির্দেশ দিয়েছেন।
৫. “আমাদের অলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন” – শব্দের ত্রিবিধ পরিচয় দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে কোন ধরনের শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক এবং কেন, তা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: রাজশেখর বসু তাঁর প্রবন্ধে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অনুসারে শব্দের তিনটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যা বৈজ্ঞানিক রচনার ভাষারীতি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শব্দের ত্রিবিধ পরিচয়:
১. অভিধা: এটি শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ (dictionary meaning)। যেমন: ‘মাথা’ বলতে শরীরের একটি অঙ্গকে বোঝায়।
২. লক্ষণা: এটি শব্দের লক্ষ্যার্থ বা গভীরতর অর্থ। যেমন: ‘দেশের মাথা’ বলতে দেশের প্রধান ব্যক্তিকে বোঝায়।
৩. ব্যঞ্জনা: এটি শব্দের ব্যঙ্গার্থ বা ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ, যা বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে ছাপিয়ে এক নতুন ভাব প্রকাশ করে। যেমন: “মাথা নেই তার মাথা ব্যথা”—এখানে প্রথম ‘মাথা’ হলো মস্তিষ্ক এবং দ্বিতীয় ‘মাথা’ হলো দুশ্চিন্তা।
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে শব্দের প্রয়োগ: লেখকের মতে, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে শুধুমাত্র ‘অভিধা’ গুণসম্পন্ন শব্দের প্রয়োগই আবশ্যক। কারণ—
১. স্পষ্টতা: বিজ্ঞানের মূল ধর্ম হলো স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা। অভিধা গুণসম্পন্ন শব্দ ব্যবহার করলে অর্থ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে না।
২. নির্দিষ্টতা: লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার প্রয়োগ বক্তব্যকে অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক করে তুলতে পারে, যা বিজ্ঞানের পরিপন্থী। বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রতিটি শব্দের একটিমাত্র নির্দিষ্ট অর্থ থাকা প্রয়োজন।
উপসংহার: তাই, লেখক মনে করেন, সাহিত্যিক রচনায় লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার স্থান থাকলেও, বৈজ্ঞানিক রচনাকে সহজ, সরল ও দ্ব্যর্থহীন করার জন্য শুধুমাত্র অভিধা গুণসম্পন্ন শব্দের ব্যবহারই অপরিহার্য।
৬. “তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবার একটা কারণ, রচনার পরিপাট্য।” – ‘তাঁদের’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? রচনার ‘পরিপাট্য’ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? জনপ্রিয়তার অন্য কারণগুলি কী?
উত্তর:
‘তাঁদের’ পরিচয়: এখানে ‘তাঁদের’ বলতে লেখক পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লেখকদের (যেমন—হাক্সলি, এডিংটন প্রমুখ) বুঝিয়েছেন।
রচনার ‘পরিপাট্য’: ‘পরিপাট্য’ বলতে লেখক বুঝিয়েছেন রচনার সুশৃঙ্খল বিন্যাস এবং পরিচ্ছন্ন প্রকাশভঙ্গি। এর অর্থ হলো—
১. বিষয়বস্তুকে যুক্তিপূর্ণভাবে সাজানো।
২. অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য বর্জন করা।
৩. ভাষাকে সহজ ও স্পষ্ট রাখা।
৪. বিষয়বস্তু অনুযায়ী অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ ভাগ করা।
এই সুশৃঙ্খল বিন্যাসের জন্যই তাঁদের লেখা পড়তে ভালো লাগে এবং বুঝতে সুবিধা হয়।
জনপ্রিয়তার অন্য কারণ:
রচনার পরিপাট্য ছাড়াও তাঁদের জনপ্রিয়তার অন্য কারণগুলি হলো—
১. ভাষার সরলতা: তাঁরা অত্যন্ত কঠিন বিষয়কেও সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন।
২. উপযুক্ত উপমা: তাঁরা জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বোঝানোর জন্য দৈনন্দিন জীবন থেকে উপযুক্ত উপমা ব্যবহার করতেন, যা পাঠকদের কাছে বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তুলত।
৩. লেখকের গভীর জ্ঞান: তাঁরা যে বিষয়ে লিখতেন, সেই বিষয়ে তাঁদের গভীর জ্ঞান ছিল, যা তাঁদের লেখাকে নির্ভরযোগ্য করে তুলত।
৭. উপমা প্রয়োগ প্রসঙ্গে লেখকের মতামত কী? একটি উপযুক্ত ও একটি অনুপযুক্ত উপমার উদাহরণ দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে লেখক বৈজ্ঞানিক রচনায় উপমা বা অলংকারের প্রয়োগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।
লেখকের মতামত:
লেখকের মতে, বৈজ্ঞানিক রচনায় অলংকার বা উপমা প্রয়োগের খুব বেশি সুযোগ নেই। তবে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য মাঝে মাঝে উপমা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সেই উপমা যেন—
১. বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
২. বাড়াবাড়ি বা অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট না হয়।
৩. বক্তব্যকে অস্পষ্ট না করে, বরং আরও স্পষ্ট করে তোলে।
সাহিত্যের মতো বিজ্ঞানে কল্পনার স্বাধীনতা নেই, তাই উপমা প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।
উপযুক্ত উপমার উদাহরণ: প্রবন্ধ অনুসারে একটি উপযুক্ত উপমা হলো মহাকবি কালিদাসের উক্তি—”হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড”। এখানে হিমালয়ের বিশালতাকে পৃথিবীর মাপকাঠির সঙ্গে তুলনা করে তার মহত্ত্বকে সহজ ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।
অনুপযুক্ত উপমার উদাহরণ: একটি অনুপযুক্ত উপমার উদাহরণ হলো—”অক্সিজেন বা হাইড্রোজেনের গন্ধ নেই, বর্ণ নেই, স্বাদ নেই…এরা জলের মতো”। এই তুলনাটি ভুল কারণ, জলও বর্ণহীন ও গন্ধহীন হলেও তার স্বাদ আছে। এই ধরনের ভুল উপমা পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে।
৮. “এই ধারণা একেবারে ভুল।” – কোন ধারণা এবং কেন তা ভুল? পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় মনে রাখা উচিত?
উত্তর:
ভুল ধারণা: এখানে যে ধারণাটিকে ভুল বলা হয়েছে, তা হলো—পরিভাষা রচনা করা কোনো একজন লেখকের কাজ।
ভুল হওয়ার কারণ: এই ধারণাটি ভুল কারণ—
১. বিভ্রান্তি সৃষ্টি: যদি প্রত্যেক লেখক নিজের ইচ্ছা মতো পরিভাষা তৈরি করেন, তাহলে একই ইংরেজি শব্দের বিভিন্ন বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি হবে। এর ফলে পাঠকদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে এবং জ্ঞানচর্চা ব্যাহত হবে।
২. অগ্রহণযোগ্যতা: একজন লেখকের তৈরি করা শব্দ অন্য লেখকের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট পরিভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠবে না।
পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়:
১. পরিভাষা রচনার দায়িত্ব কোনো একটি বিশেষজ্ঞ সমিতির (যেমন—বিশ্ববিদ্যালয়) উপর দেওয়া উচিত।
২. শব্দটি যেন সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হয়।
৩. শব্দটি যেন মূল অর্থটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।
৪. যে সমস্ত বিদেশি শব্দ বহুল প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য, সেগুলি অপরিবর্তিত রাখা উচিত।
৫. একবার কোনো পরিভাষা গৃহীত হলে, সকলের উচিত সেই শব্দটিই ব্যবহার করা।
৯. ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধটিকে একটি সার্থক প্রবন্ধ বলা যায় কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: হ্যাঁ, রাজশেখর বসুর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধটিকে নিঃসন্দেহে একটি সার্থক প্রবন্ধ বলা যায়। একটি সার্থক প্রবন্ধের সমস্ত গুণাবলী এর মধ্যে উপস্থিত।
যুক্তিসমূহ:
১. সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু: প্রবন্ধটির একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সমস্যা ও তার সমাধান। লেখক এই মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হননি।
২. যুক্তিপূর্ণ আলোচনা: লেখক তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অকাট্য যুক্তি ও উপযুক্ত উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। পরিভাষা, ভাষারীতি বা পাঠকের শ্রেণীবিভাগ—প্রতিটি বিষয়েই তাঁর আলোচনা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ।
৩. তথ্য ও গভীরতা: প্রবন্ধে লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি, বিভিন্ন লেখকের উদাহরণ এবং অলংকারশাস্ত্রের প্রসঙ্গ এনে তাঁর আলোচনার গভীরতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছেন।
৪. স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষা: প্রবন্ধের ভাষা অত্যন্ত সহজ, স্পষ্ট এবং সাবলীল। লেখক নিজে যে ভাষারীতির কথা বলেছেন, তাঁর নিজের রচনাতেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে।
৫. সুচিন্তিত সমাধান: প্রবন্ধটি শুধু সমস্যার কথা বলেই থেমে থাকেনি, তার সমাধানের বাস্তবসম্মত পথও দেখিয়েছে, যা লেখকের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।
উপসংহার: এই সমস্ত গুণাবলীর জন্যই ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ একটি কালোত্তীর্ণ ও সার্থক প্রবন্ধ।
১০. রাজশেখর বসুর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ভাষারীতি কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন? তিনি নিজে কি সেই রীতি অনুসরণ করেছেন?
উত্তর:
ভূমিকা: রাজশেখর বসু ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধে বিজ্ঞান রচনার ভাষারীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক আদর্শ ভাষারীতির প্রস্তাব দিয়েছেন।
প্রস্তাবিত ভাষারীতি:
লেখকের মতে, বিজ্ঞান রচনার ভাষা হওয়া উচিত—
১. সরল ও স্পষ্ট: ভাষা হবে সহজবোধ্য এবং বক্তব্য হবে দ্ব্যর্থহীন। অকারণ পাণ্ডিত্য বা কঠিন শব্দ পরিহার করতে হবে।
২. পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত: রচনা হবে সুশৃঙ্খল এবং বাহুল্যবর্জিত।
৩. আক্ষরিক অনুবাদ মুক্ত: ইংরেজি বাক্যরীতির হুবহু অনুকরণ না করে বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী লিখতে হবে।
৪. অভিধাশ্রয়ী: ভাষার মূল অর্থ বা বাচ্যার্থের উপর জোর দিতে হবে, লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার প্রয়োগ করা উচিত নয়।
লেখকের নিজের অনুসরণ:
হ্যাঁ, লেখক নিজে এই প্রবন্ধে তাঁর প্রস্তাবিত ভাষারীতি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন।
১. তাঁর প্রবন্ধের ভাষা অত্যন্ত সহজ, স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল।
২. তিনি যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সাজিয়েছেন, যা তাঁর রচনার পরিপাট্যের পরিচয় দেয়।
৩. তিনি অকারণ কোনো অলংকার বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেননি।
এভাবেই, লেখক তাঁর নিজের রচনাতেই এক আদর্শ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষারীতির উদাহরণ স্থাপন করেছেন।
Class 10 bengali বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান question answer
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রাজশেখর বসু প্রবন্ধের প্রশ্ন উত্তর, MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 bengali বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধের প্রশ্ন উত্তর