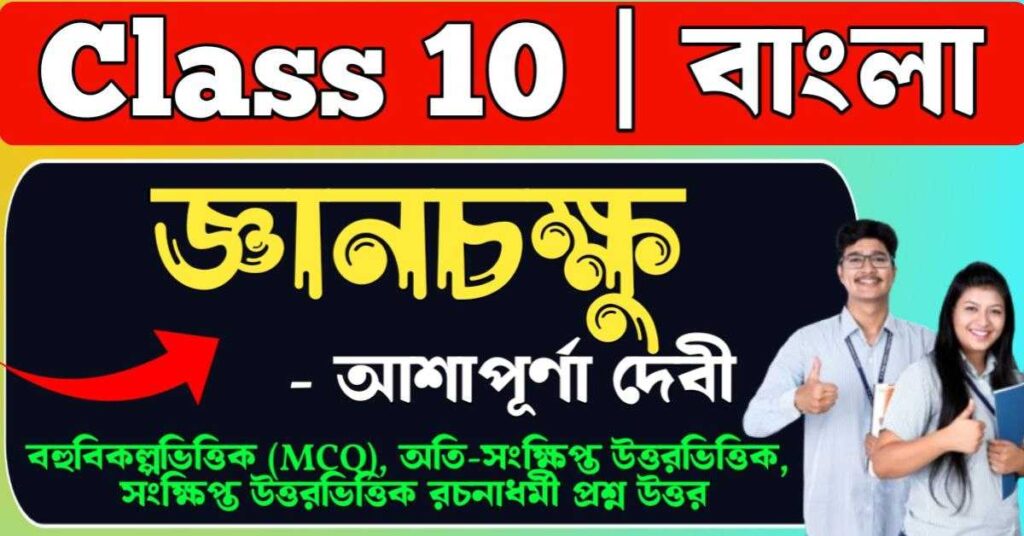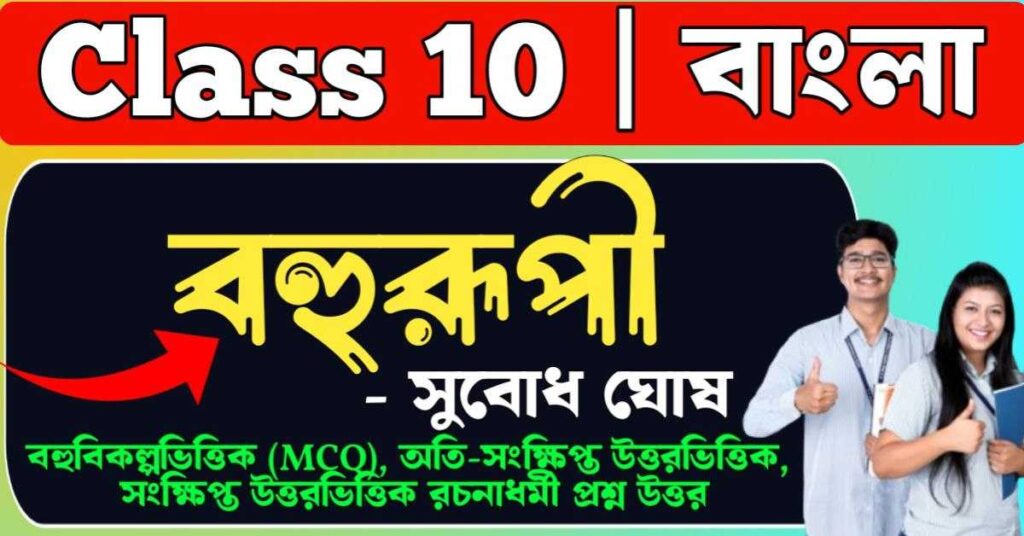সিরাজদ্দৌলা নাটকের প্রশ্ন উত্তর
সিরাজদ্দৌলা – শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (১০টি)
১. ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অবলম্বনে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা। তাঁর চরিত্রের মধ্যে দেশপ্রেম, অসহায়তা, আবেগ এবং ট্র্যাজেডির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য:
১. দেশপ্রেমিক ও অসাম্প্রদায়িক: সিরাজ ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, “বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়—মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা,” তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দেয়।
২. আবেগপ্রবণ ও তরুণ: সিরাজ ছিলেন তরুণ এবং অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। তিনি ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইংরেজদের ঔদ্ধত্যে সহজেই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়তেন। তাঁর এই আবেগপ্রবণতাই অনেক সময় তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে ছাপিয়ে গেছে।
৩. নিঃসঙ্গ ও অসহায়: সিরাজ তাঁর রাজদরবারে ছিলেন অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। তাঁর কাছের মানুষেরা—যেমন মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ—সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশে তিনি ছিলেন একজন অসহায় শাসক।
৪. ট্র্যাজিক নায়ক: সিরাজের চরিত্রে ট্র্যাজিক নায়কের সমস্ত গুণাবলী বর্তমান। তিনি দেশের জন্য ভালো কিছু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং কাছের মানুষদের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তোলে। তাঁর অসহায় আত্মসমর্পণ এবং পরিণতি পাঠকের মনে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার করে।
২. “বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়—মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।” – বক্তা কে? তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে কোন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?
উৎস ও বক্তা: উক্তিটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ থেকে গৃহীত। এর বক্তা হলেন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা।
প্রসঙ্গ: রাজদরবারে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল, তখন সিরাজ তাঁর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত সভাসদদের একত্রিত করে বাংলার সম্মান রক্ষার জন্য আবেদন জানান। সেই প্রসঙ্গেই তিনি এই উক্তিটি করেন।
মানসিকতার পরিচয়:
এই উক্তিটির মাধ্যমে সিরাজের কয়েকটি মহৎ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—
১. অসাম্প্রদায়িক চেতনা: সিরাজ বাংলাকে শুধুমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের দেশ হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে বাংলা ছিল হিন্দু ও মুসলমান—উভয়েরই মাতৃভূমি। এই ভাবনা তাঁর গভীর অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দেয়।
২. ঐক্যবদ্ধতার আহ্বান: তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে দেশের অভ্যন্তরীণ ঐক্য অপরিহার্য। তাই তিনি ধর্মের বিভেদ ভুলে সকলকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
৩. দেশপ্রেম: ‘মাতৃভূমি গুলবাগ’ অর্থাৎ ফুলের বাগান—এই উপমার মাধ্যমে তিনি বাংলার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও মমতা প্রকাশ করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, এই সুন্দর দেশ যেন সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় সুরক্ষিত থাকে।
সুতরাং, এই উক্তিটি সিরাজের একজন আদর্শ, অসাম্প্রদায়িক ও দেশপ্রেমিক শাসকের পরিচয় বহন করে।
৩. ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অবলম্বনে ঘসেটি বেগমের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশের অন্যতম প্রধান খল চরিত্র হলো ঘসেটি বেগম। তিনি সিরাজের মাসি এবং তাঁর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য:
১. প্রতিহিংসাপরায়ণা: ঘসেটি বেগম সিরাজের প্রতি ছিলেন তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাঁর পালিত পুত্রকে সরিয়ে সিরাজ নবাব হওয়ায় তিনি সিরাজকে কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। সিরাজের পতনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর উক্তিতে, “আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই, আছে শুধু প্রতিহিংসা” – এই মনোভাব স্পষ্ট।
২. ক্ষমতালোভী ও ষড়যন্ত্রকারী: তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতালোভী। নিজের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
৩. কুটবুদ্ধিসম্পন্না: ঘসেটি বেগম ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও কুটবুদ্ধিসম্পন্না। তিনি জানতেন কীভাবে অন্যদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে হয়। সিরাজ যখন তাঁকে বন্দি করেন, তখনও তিনি নিজের অসহায়ত্বের অভিনয় করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেন।
৪. নাটকের চালিকাশক্তি: তাঁর ষড়যন্ত্র ও কার্যকলাপ নাটকের ঘটনাকে গতি দিয়েছে এবং সিরাজের ট্র্যাজেডিকে ত্বরান্বিত করেছে। তিনি নাটকের প্রধান প্রতিপক্ষ শক্তির অন্যতম প্রতিনিধি।
৪. “আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।” – বক্তা কে? তাঁর এই উক্তির কারণ ও অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা আলোচনা করো।
উৎস ও বক্তা: উক্তিটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ থেকে গৃহীত। এর বক্তা হলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা।
উক্তির কারণ: ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় সিরাজ যখন বুঝতে পারেন যে, তাঁর সেনাপতি মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের মতো প্রধান স্তম্ভরাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি এদের শাস্তি দিতে পারছেন না, কারণ তাতে হয়তো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। দেশের এই দুর্দিনে প্রধান ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দিতে না পারার এই অক্ষমতার জন্যই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।
অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা:
এই উক্তির মধ্যে সিরাজের গভীর যন্ত্রণা ও হতাশা লুকিয়ে আছে।
১. নিঃসঙ্গতা: তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই বিশাল রাজদরবারে তিনি একা। যাদের উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন, তারাই তাঁর পতনের কারণ।
২. শাসকের অসহায়ত্ব: একজন শাসক হয়েও তিনি জেনে-শুনে বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিতে পারছেন না। এই পরিস্থিতি তাঁর কাছে চরম অপমানের ও যন্ত্রণার।
৩. দেশের জন্য চিন্তা: তিনি জানেন, এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম হবে বাংলার পরাধীনতা। দেশের এই ভবিষ্যৎ ভেবেই তাঁর যন্ত্রণা আরও তীব্র হয়েছে।
সুতরাং, এই উক্তিটি সিরাজের একজন ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে তাঁর অসহায়ত্ব ও গভীর যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ।
৫. “কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা” – কে, কাদের উদ্দেশে এই মন্তব্য করেছেন? তাঁর এই মন্তব্যের কারণ কী?
বক্তা ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি: উক্তিটি নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটসকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। তবে এর মাধ্যমে তিনি সমস্ত ইংরেজ কোম্পানিকেই সম্বোধন করেছেন।
মন্তব্যের কারণ:
সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে ভদ্র ও সম্মানজনক আচরণ করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে একটি和平পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তাঁর এই ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে বারবার তাঁকে অপমান ও অমান্য করেছে। তাদের কার্যকলাপ ছিল—
১. শর্ত লঙ্ঘন: তারা আলিনগরের সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে চন্দননগর আক্রমণ করেছে।
২. ষড়যন্ত্র: তারা নবাবের সভাসদদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।
৩. ঔদ্ধত্য: তারা নবাবের দূতকে অপমান করেছে এবং নবাবের নির্দেশ অমান্য করে চলেছে।
ইংরেজদের এই ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েই সিরাজ এই মন্তব্যটি করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, ইংরেজরা ভদ্রতার ভাষা বোঝে না, তারা শক্তির ভাষা বোঝে। তাই তিনি তাদের সঙ্গে আর ভদ্র আচরণ করতে রাজি নন।
৬. ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশ অবলম্বনে লুৎফউন্নিসার চরিত্রটির ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে লুৎফউন্নিসা বা লুৎফা হলেন নবাবের বেগম। তিনি নাটকের একটি পার্শ্বচরিত্র হলেও, তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী।
চরিত্রের ভূমিকা:
১. প্রেমময়ী স্ত্রী: লুৎফা ছিলেন সিরাজের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্তা ও প্রেমময়ী। তিনি সিরাজের সমস্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মানসিক যন্ত্রণার সময়ে তাঁর পাশে থেকেছেন।
২. প্রেরণার উৎস: যখন সিরাজ চতুর্দিকের বিশ্বাসঘাতকতায় হতাশ ও বিপর্যস্ত, তখন লুৎফা তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন। তিনি সিরাজকে তাঁর নবাবের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে দৃঢ় থাকতে অনুপ্রাণিত করেছেন।
৩. বিচক্ষণ উপদেষ্টা: লুৎফা শুধুমাত্র একজন প্রেমময়ী স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিচক্ষণ। তিনি সিরাজকে ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং তাকে কঠোর হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
৪. নাটকের করুণ রসের উৎস: সিরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে লুৎফার জীবনও ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়। সিরাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর অসহায় পরিণতি পাঠকের মনে গভীর করুণার সঞ্চার করে।
উপসংহার: এভাবেই, লুৎফা চরিত্রটি সিরাজের নিঃসঙ্গ জীবনে ভালোবাসা, প্রেরণা ও বিচক্ষণতার এক বিশ্বস্ত আশ্রয় হিসেবে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
৭. “জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী” – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।
উৎস ও প্রসঙ্গ: উক্তিটি ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে নবাব সিরাজদ্দৌলা করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের আগের রাতে, যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর সেনাপতি ও সভাসদরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হয়ে তিনি এই উক্তিটি করেন।
তাৎপর্য বিশ্লেষণ:
এই উক্তিটির মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক ও প্রতীকী তাৎপর্য লুকিয়ে আছে।
১. স্বাধীনতার অবসান: ‘সৌভাগ্য সূর্য’ এখানে বাংলার স্বাধীনতা ও গৌরবের প্রতীক। ‘অস্তাচলগামী’ অর্থাৎ অস্ত যাচ্ছে, যা বোঝায় যে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ডুবতে চলেছে। সিরাজ বুঝতে পেরেছিলেন, এই যুদ্ধের ফল যাই হোক না কেন, বাংলার স্বাধীনতা আর রক্ষা করা সম্ভব নয়।
২. অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত: সূর্য অস্ত গেলে যেমন অন্ধকার নেমে আসে, তেমনই বাংলার স্বাধীনতা অস্ত গেলে পরাধীনতার অন্ধকার নেমে আসবে। এই উক্তির মাধ্যমে সিরাজ বাংলার এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন।
৩. ট্র্যাজিক উপলব্ধি: এটি সিরাজের এক গভীর ট্র্যাজিক উপলব্ধি। তিনি শুধু নিজের পতন নয়, সমগ্র জাতির পতনকে চাক্ষুষ করছেন। একজন দেশপ্রেমিক শাসকের কাছে এর চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কিছু হতে পারে না।
সুতরাং, এই উক্তিটি শুধুমাত্র একটি সংলাপ নয়, এটি বাংলার ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণের মর্মস্পর্শী কাব্যিক প্রকাশ।
৮. ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তার পরিচয় দাও।
ভূমিকা: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের মূল উপজীব্য হলো বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে এক বহুমুখী ষড়যন্ত্র, যা তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল।
ষড়যন্ত্রের পরিচয়:
এই ষড়যন্ত্রের দুটি দিক ছিল—অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক।
১. অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র: সিরাজের বিরুদ্ধে প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল তাঁরই দরবারের সভাসদ ও আত্মীয়স্বজন।
- ঘসেটি বেগম: সিরাজের মাসি, যিনি প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন।
- মীরজাফর: নবাবের প্রধান সেনাপতি, যিনি সিংহাসনের লোভে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।
- রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ: এঁরা ছিলেন প্রভাবশালী অমাত্য ও বণিক, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।
উপসংহার: এই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ষড়যন্ত্রের মিলিত আঘাতেই সিরাজের পতন ঘটে এবং বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়।
৯. “তাঁর পরিচ্ছদ, অঙ্গে অঙ্গুরীয়, কানে হীরকখন্ড, সবই আছে, নেই শুধু…? কী নেই এবং কেন নেই?” – এই উক্তিটির আলোকে সিরাজের মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করো।
ভূমিকা: নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশে এই বর্ণনার মাধ্যমে নবাব সিরাজের গভীর মানসিক সংকটকে তুলে ধরেছেন।
কী নেই এবং কেন নেই:
সিরাজের বাহ্যিক আড়ম্বর—রাজকীয় পোশাক, আংটি, হীরার দুল—সবই ছিল। কিন্তু যা ছিল না, তা হলো তাঁর ‘মন’ বা মানসিক শান্তি ও আত্মবিশ্বাস। তাঁর মন ছিল না কারণ—
১. চরম বিশ্বাসঘাতকতা: তিনি জানতে পেরেছেন যে তাঁর প্রধান সেনাপতি মীরজাফর সহ অন্যান্য সভাসদরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর মনকে ভেঙে দিয়েছে।
২. নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ব: এই ষড়যন্ত্রের পরিবেশে তিনি নিজেকে একা ও অসহায় বোধ করছেন। তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর পাশে দাঁড়ানোর মতো বিশ্বস্ত লোক খুব কম।
৩. আসন্ন পতনের আশঙ্কা: তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন যে, এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁর এবং বাংলার পতন আসন্ন। এই আসন্ন সর্বনাশের চিন্তা তাঁর মনের সমস্ত শান্তি কেড়ে নিয়েছে।
মানসিক অবস্থা:
এই উক্তির মাধ্যমে সিরাজের এক বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি বাহ্যিকভাবে নবাব হলেও, মানসিকভাবে তিনি ছিলেন একজন পরাজিত, হতাশ ও নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁর বাহ্যিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে তাঁর ভেতরের শূন্যতার এই বৈপরীত্য তাঁর ট্র্যাজেডিকে আরও গভীর করে তুলেছে।
১০. ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের নামকরণ কতখানি সার্থক, তা আলোচনা করো।
ভূমিকা: যেকোনো সাহিত্যের নামকরণ তার বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের উপর ভিত্তি করে হয়। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকটির নামকরণ কেন্দ্রীয় চরিত্র-ভিত্তিক এবং তা সর্বাংশে সার্থক।
নামকরণের সার্থকতা:
১. কেন্দ্রীয় চরিত্র: নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সিরাজদ্দৌলাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর সিংহাসন আরোহণ, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব এবং তাঁর ট্র্যাজিক পতন—এই সবই নাটকের মূল উপজীব্য।
২. নাটকের দ্বন্দ্ব: নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হলো সিরাজের আদর্শ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে তাঁর সভাসদদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সংঘাত। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রয়েছেন সিরাজ নিজেই।
৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: নাটকটি পলাশীর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত, যার প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র হলেন সিরাজদ্দৌলা। তাঁর নামেই সেই যুগের ইতিহাস পরিচিত।
৪. ট্র্যাজেডির নায়ক: সিরাজ এই নাটকের ট্র্যাজিক নায়ক। তাঁর পতন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির পতন নয়, একটি জাতির পরাধীনতার সূচনা। তাঁর নামে নামকরণ হওয়ায় নাটকের এই ট্র্যাজিক আবেদনটি আরও তীব্র হয়েছে।
উপসংহার: যেহেতু নাটকের কাহিনী, দ্বন্দ্ব, চরিত্র এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট—সবকিছুই সিরাজদ্দৌলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তাই ‘সিরাজদ্দৌলা’ নামকরণটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সার্থক।
Class 10 bengali সিরাজদ্দৌলা question answer
সিরাজদ্দৌলা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাটকের প্রশ্ন উত্তর, MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 bengali সিরাজদ্দৌলা নাটকের প্রশ্ন উত্তর