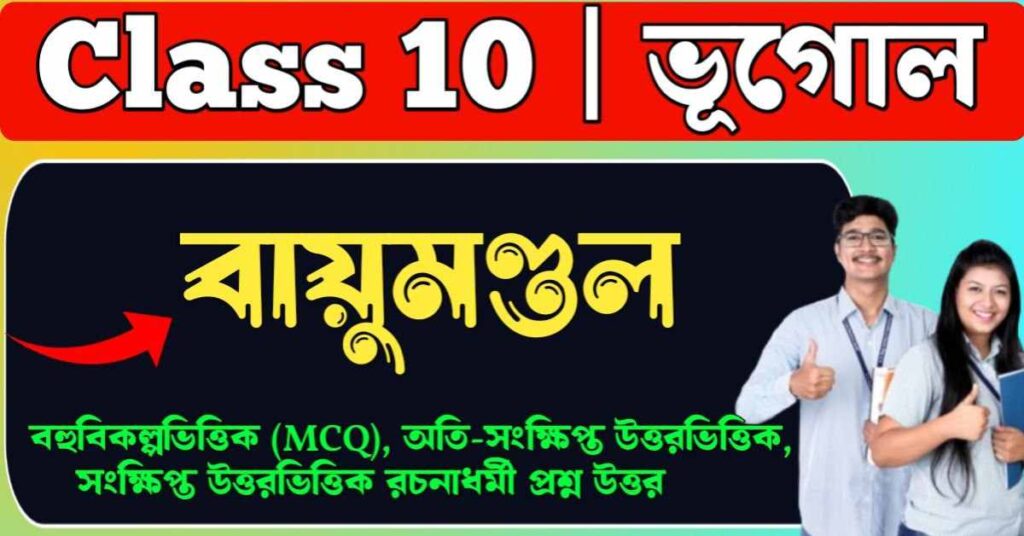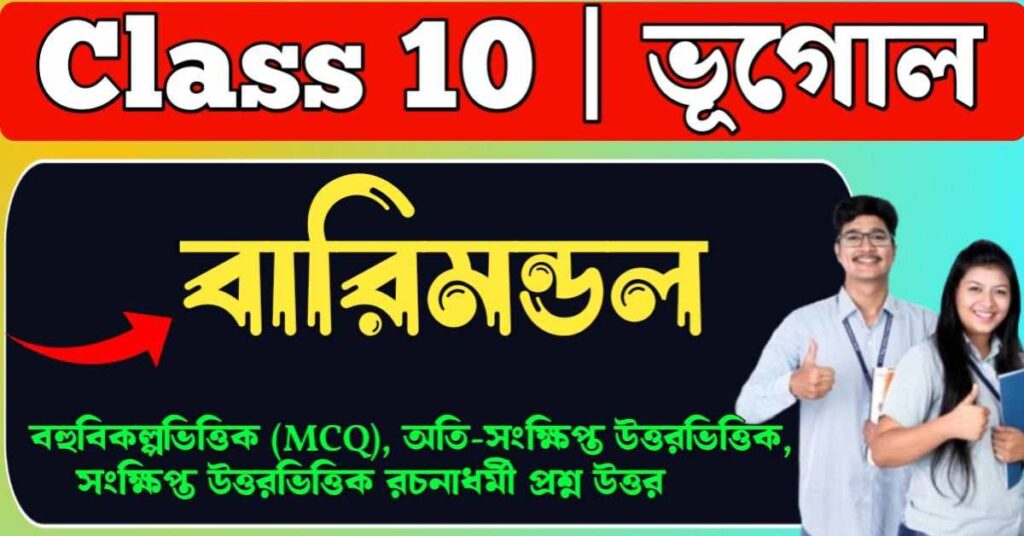বহির্জাত প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট ভূমিরূপ Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, তাকে বলে –
২. অবরোহণ ও আরোহণ প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ফল হল –
৩. শুষ্ক অঞ্চলে গিরিখাতকে বলা হয় –
৪. নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ বাড়লে তার বহনক্ষমতা বাড়ে –
৫. পাখির পায়ের মতো আকৃতির বদ্বীপ দেখা যায় –
৬. হিমবাহ দ্বারা বাহিত শিলাখণ্ডকে বলে –
৭. দুটি সার্ক বা করির মধ্যবর্তী খাড়া শৈলশিরাকে বলে –
৮. বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ হল –
৯. মরুভূমি অঞ্চলে বায়ুর অপসারণের ফলে সৃষ্ট গর্তগুলিকে বলে –
১০. পৃথিবীর বৃহত্তম নদী দ্বীপ হল –
১১. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায় নদীর –
১২. হিমবাহ ও জলধারার মিলিত সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হল –
১৩. সাহারা মরুভূমিতে প্রস্তরময় মরুভূমি পরিচিত –
১৪. ভারতের বৃহত্তম হিমবাহ হল –
১৫. নদীর জলের প্রবাহ পরিমাপের একক হল –
১৬. অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়িকে বলা হয় –
১৭. মন্থকূপ সৃষ্টি হয় যার দ্বারা, তা হলো –
১৮. একটি পিরামিড চূড়ার উদাহরণ হল –
১৯. লোয়েস সমভূমি দেখা যায় –
২০. যে প্রক্রিয়ায় শিলাসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে স্বস্থানে অবস্থান করে, তাকে বলে –
২১. পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাতটি হল –
২২. ঝুলন্ত উপত্যকায় সৃষ্টি হয় –
২৩. বায়ুর অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ব্যাঙের ছাতার মতো ভূমিরূপটি হল –
২৪. বদ্বীপ গঠিত হয় নদীর –
২৫. পর্বতের গায়ে যে সীমারেখার উপর সারা বছর বরফ জমে থাকে, তাকে বলে –
২৬. দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলে –
২৭. উলটানো নৌকার মতো ভূমিরূপ হল –
২৮. মরু অঞ্চলের শুষ্ক নদীখাতকে বলা হয় –
২৯. নায়াগ্রা জলপ্রপাতটি অবস্থিত –
৩০. Basket of Eggs Topography বলা হয় –
৩১. ইংরেজি ‘I’ আকৃতির নদী উপত্যকাকে বলে –
৩২. হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট একটি ভূমিরূপ হল –
৩৩. চলমান বালিয়াড়িকে বলে –
৩৪. পৃথিবীর বৃহত্তম পাদদেশীয় হিমবাহ হল –
৩৫. বদ্বীপ বা ‘Delta’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন –
৩৬. হিমসিঁড়ি বা ক্যাসকেড দেখা যায় –
৩৭. বায়ুর গতিপথের সাথে সমান্তরালে গড়ে ওঠা বালিয়াড়ি হল –
৩৮. ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত হল –
৩৯. দুটি বা তার বেশি হিমবাহ মিলিত হলে যে গ্রাবরেখা তৈরি হয় তা হল –
৪০. মরু অঞ্চলের লবণাক্ত জলের হ্রদকে বলে –
৪১. ‘Grade’ বা ‘পর্যায়ন’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন –
৪২. নদীর বাঁকের উত্তল অংশের সঞ্চয়কে বলে –
৪৩. ফিয়র্ড দেখা যায় –
৪৪. বায়ুর গতিপথের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে গঠিত বালিয়াড়ি হল –
৪৫. পললশঙ্কু গঠিত হয় –
৪৬. হিমবাহের ওপরের পৃষ্ঠে সৃষ্ট গভীর ফাটলগুলিকে বলে –
৪৭. বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হল –
৪৮. নদীর পুনর্যৌবন লাভের ফলে গঠিত হয় –
৪৯. একটি মহাদেশীয় হিমবাহের উদাহরণ হল –
৫০. বায়ুর কাজ সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয় –
৫১. বহির্জাত প্রক্রিয়ার মূল শক্তি হল –
৫২. পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ হল –
৫৩. পর্বতারোহীদের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রাকৃতিক ভূমিরূপ হল –
৫৪. বায়ুর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলা উল্লম্বভাবে অবস্থান করলে গঠিত হয় –
৫৫. যে প্রক্রিয়ায় ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায় তা হল –
৫৬. জলপ্রপাতের নীচে সৃষ্ট বিশাল গহ্বরকে বলে –
৫৭. একটি আদর্শ নদীর উদাহরণ হল –
৫৮. হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ত্রিকোণাকার বদ্বীপের মতো ভূমিরূপটি হল –
৫৯. বায়ুর গতিপথে কঠিন শিলার নীচে কোমল শিলা অনুভূমিকভাবে থাকলে গঠিত হয় –
৬০. নদীর গতিপথের পরিবর্তন হলে যে ভূমিরূপ তৈরি হয়, তা হল –
৬১. শার্কফিন বা হাঙ্গরের পাখনার মতো দেখতে ভূমিরূপ হল –
৬২. মরু সমপ্রায় ভূমিতে ক্ষয় প্রতিরোধী কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অবশিষ্ট পাহাড়কে বলে –
৬৩. পুঞ্জক্ষয়ের প্রধান কারণ হল –
৬৪. গঙ্গা নদীর বদ্বীপটি হল একটি –
৬৫. হিমবাহের ক্ষয় ও সঞ্চয়ের ফলে গঠিত একটি ভূমিরূপ হল –
৬৬. ‘Ship rock’ হল একটি বিখ্যাত –
৬৭. নদীর নিম্নগতিতে প্রধান কাজ হল –
৬৮. আরামকেদারার মতো দেখতে ভূমিরূপটি হল –
৬৯. মরুদান সৃষ্টি হয় –
৭০. সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপগুলির কোনটি ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. পর্যায়ন কাকে বলে?
উত্তর: ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উঁচু-নীচু স্থানের মধ্যে সমতা আনার প্রক্রিয়াকে পর্যায়ন বলে।
২. আরোহণ প্রক্রিয়া কী?
উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বাহিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, তাকে আরোহণ বলে।
৩. নগ্নীভবন কী?
উত্তর: আবহবিকার, পুঞ্জক্ষয় ও ক্ষয়ীভবন—এই তিনটি প্রক্রিয়ার সম্মিলিত কাজে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের শিলাস্তর অপসারিত হয়ে নীচের শিলাস্তর উন্মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগ্নীভবন বলে।
৪. নদীর ষষ্ঠ ঘাতের সূত্রটি কী?
উত্তর: নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলে তার বহনক্ষমতা ২^৬ বা ৬৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। এটিই নদীর ষষ্ঠ ঘাতের সূত্র।
৫. জলবিভাজিকা কাকে বলে?
উত্তর: যে উচ্চভূমি দুটি বা তার বেশি নদী অববাহিকাকে পৃথক করে, তাকে জলবিভাজিকা বলে।
৬. বিশ্বের বৃহত্তম ক্যানিয়ন কোনটি?
উত্তর: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।
৭. ভারতের নায়াগ্রা নামে পরিচিত কোন জলপ্রপাত?
উত্তর: ছত্তিশগড়ের ইন্দ্রাবতী নদীর উপর চিত্রকূট জলপ্রপাত।
৮. খাড়ি কী?
উত্তর: নদীর মোহনায় ফানেল আকৃতির প্রশস্ত অংশকে খাড়ি বলে।
৯. পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ কোনটি?
উত্তর: অ্যান্টার্কটিকার ল্যাম্বার্ট হিমবাহ।
১০. হিমশৈল কী?
উত্তর: সমুদ্রে ভাসমান বিশাল বরফের স্তূপকে হিমশৈল বলে।
১১. বার্গস্রুন্ড কী?
উত্তর: হিমবাহ ও পর্বতগাত্রের মধ্যে যে গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়, তাকে বার্গস্রুন্ড বলে।
১২. রসে মতানে-এর প্রতিবাত ঢালটি কেমন হয়?
উত্তর: রসে মতানে-এর প্রতিবাত ঢালটি অবঘর্ষের ফলে মসৃণ হয়।
১৩. বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়া কী?
উত্তর: বায়ুর দ্বারা ভূপৃষ্ঠের শিথিল বালিকণা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অপসারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অপসারণ বলে।
১৪. মরুদান কী?
উত্তর: মরু অঞ্চলে বায়ুর অপসারণের ফলে ভৌমজলস্তর উন্মুক্ত হয়ে যে জলাশয় ও সবুজ উদ্ভিদ জন্মায়, তাকে মরুদান বলে।
১৫. ভেন্টিফ্যাক্ট কী?
উত্তর: বায়ুর অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে মসৃণ ও তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত শিলাখণ্ডকে ভেন্টিফ্যাক্ট বলে।
১৬. পেডিমেন্ট কী?
উত্তর: মরু অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশে ক্ষয়জাত পদার্থ দ্বারা গঠিত মৃদু ঢালযুক্ত সমভূমিকে পেডিমেন্ট বলে।
১৭. ধারণ অববাহিকা কাকে বলে?
উত্তর: পার্বত্য অঞ্চলে মূল নদীর সঙ্গে বিভিন্ন উপনদী যে অঞ্চলের জল সংগ্রহ করে, তাকে ধারণ অববাহিকা বলে।
১৮. কিউসেক কী?
উত্তর: প্রতি সেকেন্ডে এক ঘনফুট জলপ্রবাহের পরিমাপকে কিউসেক (Cubic feet per second) বলে।
১৯. একটি জীবন্ত বদ্বীপের উদাহরণ দাও।
উত্তর: গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ।
২০. পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি?
উত্তর: ভেনেজুয়েলার সাল্টো অ্যাঞ্জেল।
২১. হিমরেখার উচ্চতা কোথায় সবচেয়ে কম?
উত্তর: মেরু অঞ্চলে (সমুদ্রপৃষ্ঠে)।
২২. নুনাটাক কী?
উত্তর: বরফমুক্ত পর্বতচূড়াকে নুনাটাক বলে।
২৩. ফিয়র্ড কী?
উত্তর: সমুদ্র-উপকূল সংলগ্ন হিমবাহ উপত্যকা যা সমুদ্রের জলে আংশিক নিমজ্জিত থাকে, তাকে ফিয়র্ড বলে।
২৪. হামাদা কী?
উত্তর: সাহারা মরুভূমির প্রস্তরময় মরুভূমিকে হামাদা বলে।
২৫. শিব বা সিফ কথার অর্থ কী?
উত্তর: আরবি ভাষায় শিব বা সিফ কথার অর্থ ‘সোজা তরোয়াল’।
২৬. বাজাদা কী?
উত্তর: মরু অঞ্চলে পেডিমেন্টের নীচে পলল সঞ্চিত হয়ে যে প্রায় সমতল ভূমি গঠিত হয়, তাকে বাজাদা বলে।
২৭. অবঘর্ষ ক্ষয় কাকে বলে?
উত্তর: নদী, হিমবাহ বা বায়ুর সঙ্গে বাহিত নুড়ি, পাথর, বালির ঘর্ষণে নদীখাত বা শিলাপৃষ্ঠ ক্ষয় হওয়াকে অবঘর্ষ ক্ষয় বলে।
২৮. সুন্দরবনের একটি নিমজ্জমান দ্বীপের নাম লেখ।
উত্তর: লোহাচরা বা নিউমুর।
২৯. ভারতের একটি করি হ্রদের উদাহরণ দাও।
উত্তর: উত্তরাখণ্ডের রূপকুণ্ড।
৩০. লোয়েস শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: জার্মান শব্দ লোয়েস-এর অর্থ ‘স্থানচ্যুত বস্তু’।
৩১. মিয়েন্ডার কী?
উত্তর: মধ্য ও নিম্নগতিতে নদী যে সর্পিল বা আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়, তাকে মিয়েন্ডার বা নদীবাঁক বলে।
৩২. ক্যাটল হ্রদ কী?
উত্তর: বহিঃধৌত সমভূমিতে বরফ গলে গিয়ে যে গর্ত বা হ্রদের সৃষ্টি হয়, তাকে ক্যাটল হ্রদ বলে।
৩৩. ‘ডিমভরতি ঝুড়ি’ কোন ভূমিরূপকে বলা হয়?
উত্তর: ড্রামলিন অধ্যুষিত অঞ্চলকে।
৩৪. ইনসেলবার্গ ক্ষয় পেয়ে গোলাকার হলে তাকে কী বলে?
উত্তর: বর্নহার্ডট।
৩৫. পুঞ্জক্ষয় কী?
উত্তর: মাধ্যাকর্ষণের টানে পর্বতের ঢাল বরাবর শিলাখণ্ডের নীচে নেমে আসাকে পুঞ্জক্ষয় বলে।
৩৬. স্বাভাবিক বাঁধ কী?
উত্তর: বন্যার সময় নদীর দুই তীরে পলি জমে যে উঁচু পাড় তৈরি হয়, তাকে স্বাভাবিক বাঁধ বলে।
৩৭. পৃথিবীর দীর্ঘতম এসকার কোনটি?
উত্তর: কানাডার অন্টারিওর ‘ব্রামpton Esker’।
৩৮. থর মরুভূমিতে চলমান বালিয়াড়িকে কী বলে?
উত্তর: ধরিয়ান।
৩৯. কোন প্রকার বদ্বীপ দেখতে অনেকটা করাতের দাঁতের মতো?
উত্তর: কাসপেট বদ্বীপ।
৪০. ক্রেগ ও টেল-এর ‘টেল’ অংশে কী সঞ্চিত হয়?
উত্তর: হিমবাহ দ্বারা বাহিত নুড়ি, বালি, কাদা ইত্যাদি।
৪১. অবরোহণ প্রক্রিয়া কী?
উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কার্যের ফলে ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায়, তাকে অবরোহণ বলে।
৪২. পলল ব্যজনী কী?
উত্তর: পর্বতের পাদদেশে নুড়ি, বালি, পলি ইত্যাদি শঙ্কুর আকারে সঞ্চিত হলে তাকে পলল ব্যজনী বলে।
৪৩. ‘Grandfather of all Deltas’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর বদ্বীপকে।
৪৪. ঝুলন্ত উপত্যকা কী?
উত্তর: মূল হিমবাহ উপত্যকার উপর ছোটো উপনদী হিমবাহের উপত্যকা ঝুলে থাকলে তাকে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে।
৪৫. কেম কী?
উত্তর: হিমবাহ বাহিত নুড়ি, বালি, কাদা ইত্যাদি হ্রদে সঞ্চিত হয়ে যে ত্রিকোণাকার ভূমিরূপ গঠন করে, তাকে কেম বলে।
৪৬. গৌর ভূমিরূপের অপর নাম কী?
উত্তর: গারা (সাহারা মরুভূমিতে) বা পিট রক (শিলা স্তম্ভ)।
৪৭. দ্রবণ ক্ষয় কী?
উত্তর: জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শিলা দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাকে দ্রবণ ক্ষয় বলে।
৪৮. মোনাডনক কী?
উত্তর: আর্দ্র সমপ্রায় ভূমিতে ক্ষয় প্রতিরোধকারী কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অবশিষ্ট পাহাড়কে মোনাডনক বলে।
৪৯. একটি কর্তিত স্পারের উদাহরণ দাও।
উত্তর: তিস্তা নদীর উচ্চগতিতে কর্তিত স্পার দেখা যায়।
৫০. কোন প্রকার উপকূলে ফিয়র্ড দেখা যায়?
উত্তর: উচ্চ অক্ষাংশের হিমবাহ অধ্যুষিত পার্বত্য উপকূলে।
৫১. রাজস্থানের প্লায়া হ্রদ কী নামে পরিচিত?
উত্তর: ধান্দ।
৫২. ঘর্ষণ ক্ষয় বা অ্যাট্রিশন কী?
উত্তর: নদীর বাহিত শিলাখণ্ডগুলি নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙে গিয়ে ছোটো হলে তাকে ঘর্ষণ ক্ষয় বলে।
৫৩. নদীমঞ্চ কী?
উত্তর: নদীর পুনর্যৌবন লাভের ফলে পুরাতন প্লাবনভূমির উপর নতুন উপত্যকা সৃষ্টি হলে পুরাতন প্লাবনভূমির অবশিষ্ট অংশকে নদীমঞ্চ বলে।
৫৪. ‘Matterhorn’ কীসের উদাহরণ?
উত্তর: পিরামিড চূড়া বা হর্নের।
৫৫. হিমদ্রোণী দেখতে কেমন?
উত্তর: ইংরেজি ‘U’ অক্ষরের মতো।
৫৬. উৎপাটন বা প্লাকিং কী?
উত্তর: হিমবাহের চাপে পর্বতের ফাটলযুক্ত শিলাস্তর উৎপাটত হয়ে হিমবাহের সঙ্গে বাহিত হলে তাকে উৎপাটন বলে।
৫৭. ‘Great Green Wall’ প্রকল্পটি কোথায় গড়ে তোলা হয়েছে?
উত্তর: সাহারা মরুভূমির প্রসার রোধ করতে আফ্রিকা মহাদেশে।
৫৮. কাসকেড বা সোপান কী?
উত্তর: হিমসিঁড়ির ধাপগুলি দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হলে তাকে ক্যাসকেড বা সোপান বলে।
৫৯. পৃথিবীর দ্রুততম হিমবাহ কোনটি?
উত্তর: গ্রিনল্যান্ডের জেকবশ্যাভন হিমবাহ।
৬০. একটি বদ্বীপবিহীন নদীর নাম লেখো।
উত্তর: নর্মদা নদী।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. পর্যায়ন ও নগ্নীভবনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
উত্তর: পর্যায়ন: এটি ক্ষয় ও সঞ্চয়ের সম্মিলিত ফল, যার দ্বারা ভূমির সমতলীকরণ হয়। নগ্নীভবন: এটি আবহবিকার, পুঞ্জক্ষয় ও ক্ষয়ীভবনের মাধ্যমে শিলাস্তরের উপরিভাগ অপসারিত হওয়ার প্রক্রিয়া। পর্যায়ন একটি গঠনমূলক ও বিনাশমূলক প্রক্রিয়া, কিন্তু নগ্নীভবন মূলত একটি বিনাশমূলক প্রক্রিয়া।
২. গিরিখাত ও ক্যানিয়নের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: গিরিখাত: আর্দ্র অঞ্চলে সৃষ্ট ইংরেজি ‘V’ আকৃতির গভীর ও সংকীর্ণ নদী উপত্যকা। ক্যানিয়ন: শুষ্ক অঞ্চলে সৃষ্ট ইংরেজি ‘I’ আকৃতির অত্যন্ত গভীর ও সংকীর্ণ নদী উপত্যকা। গিরিখাতের পার্শ্বক্ষয় বেশি, ক্যানিয়নের নিম্নক্ষয় বেশি।
৩. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ কীভাবে সৃষ্টি হয়?
উত্তর: মধ্য ও নিম্নগতিতে নদীর বাঁক খুব বেশি বেড়ে গেলে দুটি বাঁকের মধ্যবর্তী অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নদী সোজা পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর ফলে পরিত্যক্ত পুরানো বাঁকটি হ্রদে পরিণত হয়, যা দেখতে ঘোড়ার খুরের মতো হওয়ায় একে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে।
৪. সব নদীতে বদ্বীপ গড়ে ওঠে না কেন?
উত্তর: নদীতে পলির পরিমাণ কম থাকলে, মোহনায় সমুদ্রস্রোত ও জোয়ার-ভাটার প্রভাব বেশি হলে, এবং নদীর গতিবেগ বেশি থাকলে পলল সঞ্চিত হতে পারে না। এই কারণগুলির জন্য সব নদীতে বদ্বীপ গড়ে ওঠে না। যেমন – নর্মদা ও তাপ্তি নদীতে বদ্বীপ নেই।
৫. হিমরেখা সর্বত্র সমান উচ্চতায় অবস্থান করে না কেন?
উত্তর: হিমরেখার উচ্চতা অক্ষাংশ, ভূমির উচ্চতা, ঋতু পরিবর্তন, বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণতা বেশি হওয়ায় হিমরেখা অনেক উঁচুতে (প্রায় ৫৫০০ মিটার) এবং মেরু অঞ্চলে উষ্ণতা কম হওয়ায় হিমরেখা সমুদ্রপৃষ্ঠে অবস্থান করে। তাই হিমরেখা সর্বত্র সমান নয়।
৬. ক্রেভাস ও বার্গস্রুন্ডের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
উত্তর: ক্রেভাস: হিমবাহের পৃষ্ঠদেশে বা উপরিভাগে সৃষ্ট ফাটলকে ক্রেভাস বলে। বার্গস্রুন্ড: হিমবাহ ও পর্বতগাত্রের সংযোগস্থলে সৃষ্ট গভীর ফাটলকে বার্গস্রুন্ড বলে। ক্রেভাস পর্বতারোহীদের জন্য বেশি বিপজ্জনক।
৭. ড্রামলিন ও রসে মতানের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: ড্রামলিন: এটি হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত উলটানো চামচ বা নৌকার মতো ভূমিরূপ। রসে মতানে: এটি হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত একদিকে মসৃণ ও অন্যদিকে অমসৃণ ঢিবি। ড্রামলিন সঞ্চয়জাত এবং রসে মতানে ক্ষয়জাত ভূমিরূপ।
৮. ইয়ারদাং ও জিউগেনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
উত্তর: ইয়ারদাং: বায়ুর গতিপথের সমান্তরালে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর উল্লম্বভাবে থাকলে ক্ষয়ের ফলে ইয়ারদাং গঠিত হয়। জিউগেন: বায়ুর গতিপথের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর অনুভূমিকভাবে থাকলে ক্ষয়ের ফলে জিউগেন গঠিত হয়।
৯. ‘মরুভূমির সম্প্রসারণ’ রোধের দুটি উপায় লেখো।
উত্তর: ১. মরুভূমির প্রান্তে বৃক্ষরোপণ করে ‘সবুজ প্রাচীর’ বা ‘Great Green Wall’ তৈরি করা। ২. পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং জমিতে জলের সঠিক ব্যবহার করে মৃত্তিকার আর্দ্রতা বজায় রাখা।
১০. জলপ্রপাত পশ্চাদপসরণ করে কেন?
উত্তর: জলপ্রপাতের জলধারা যেখানে পড়ে, সেখানে কঠিন শিলার নীচে অবস্থিত কোমল শিলাস্তর দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর ফলে উপরের কঠিন শিলাস্তর একসময় ভেঙে পড়ে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকায় জলপ্রপাত ক্রমশ উৎসের দিকে সরে যায়, একেই জলপ্রপাতের পশ্চাদপসরণ বলে।
১১. লোয়েস সমভূমি কীভাবে গঠিত হয়?
উত্তর: মরু অঞ্চল থেকে বায়ুবাহিত অতি সূক্ষ্ম হলুদ বা ধূসর রঙের বালিকণা বহুদূরে উড়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে যে বিস্তীর্ণ সমভূমি গঠন করে, তাকে লোয়েস সমভূমি বলে। যেমন- চীনের হোয়াংহো নদীর অববাহিকায় গোবি মরুভূমি থেকে উড়ে আসা লোয়েস সঞ্চিত হয়েছে।
১২. ফিয়র্ড ও খাড়ির মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: ফিয়র্ড: হিমবাহ উপত্যকা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে ফিয়র্ড তৈরি হয়। এর দুই পাড় খুব খাড়া হয়। খাড়ি: নদীর মোহনা প্রশস্ত ও ফানেল আকৃতির হলে তাকে খাড়ি বলে। খাড়ির পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাধারণত সমতল হয়।
১৩. ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত দেখা যায় কেন?
উত্তর: মূল হিমবাহের ক্ষয়ক্ষমতা উপনদী হিমবাহের থেকে বেশি হওয়ায় মূল উপত্যকা বেশি গভীর হয়। বরফ গলে গেলে উপনদী হিমবাহের উপত্যকাটি মূল উপত্যকার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তখন উপনদীটি জলপ্রপাতের আকারে মূল নদীতে মেশে।
১৪. টিকা লেখো: পলল ব্যজনী।
উত্তর: নদীর উচ্চগতি ও মধ্যগতির সংযোগস্থলে অর্থাৎ পর্বতের পাদদেশে ভূমির ঢাল হঠাৎ কমে যাওয়ায় নদীর বহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে নুড়ি, বালি, কাঁকর ইত্যাদি পর্বতের পাদদেশে হাতপাখার মতো আকারে সঞ্চিত হয়ে যে ভূমিরূপ গঠন করে, তাকে পলল ব্যজনী বলে।
১৫. নদীর বহনকার্যের তিনটি প্রক্রিয়া কী কী?
উত্তর: নদীর বহনকার্যের তিনটি প্রক্রিয়া হল: ১. দ্রবণ প্রক্রিয়া: দ্রবীভূত পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে বাহিত হয়। ২. ভাসমান প্রক্রিয়া: সূক্ষ্ম পলি, কাদা ইত্যাদি জলের সঙ্গে ভেসে বাহিত হয়। ৩. লম্ফদান প্রক্রিয়া: অপেক্ষাকৃত বড় নুড়ি, পাথর নদীর তলদেশ বরাবর লাফিয়ে লাফিয়ে বাহিত হয়।
১৬. বার্খান ও সিফ বালিয়াড়ির পার্থক্য লেখো।
উত্তর: বার্খান: এটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং বায়ুর গতিপথের আড়াআড়ি গঠিত হয়। এর দুটি শিং থাকে। সিফ: এটি অনুদৈর্ঘ্য বা তরবারির মতো দেখতে এবং বায়ুর গতিপথের সমান্তরালে গঠিত হয়।
১৭. গ্রাবরেখা কাকে বলে? এর একটি শ্রেণিবিভাগ কর।
উত্তর: হিমবাহ পর্বতের গা থেকে ক্ষয় করা নুড়ি, পাথর, বালি, কাদা ইত্যাদি তার প্রবাহপথে বা اطرافে সঞ্চয় করে যে ভূমিরূপ গঠন করে, তাকে গ্রাবরেখা বলে। একটি শ্রেণিবিভাগ হল পার্শ্ব গ্রাবরেখা।
১৮. পেডিমেন্ট ও বাজাদার মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: পেডিমেন্ট: এটি পর্বতের পাদদেশে ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত মৃদু ঢালযুক্ত শিলাময় সমভূমি। বাজাদা: এটি পেডিমেন্টের নীচে সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত প্রায় সমতলভূমি। পেডিমেন্টের ঢাল বেশি, বাজাদার ঢাল কম।
১৯. ‘U’ আকৃতির উপত্যকা কীভাবে সৃষ্টি হয়?
উত্তর: পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় অবঘর্ষ ও উৎপাটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বের ‘V’ আকৃতির নদী উপত্যকাকে পার্শ্বক্ষয় করে চওড়া করে। এর ফলে উপত্যকাটি ইংরেজি ‘U’ অক্ষরের মতো দেখতে হয়। একেই ‘U’ আকৃতির উপত্যকা বা হিমদ্রোণী বলে।
২০. অবরোহণ ও আরোহণের পার্থক্য লেখো।
উত্তর: অবরোহণ: এটি একটি ক্ষয়মূলক প্রক্রিয়া, যার ফলে ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায়। আরোহণ: এটি একটি সঞ্চয়মূলক প্রক্রিয়া, যার ফলে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। অবরোহণের প্রধান শক্তি নদী, হিমবাহ, বায়ু এবং আরোহণের ক্ষেত্রেও তাই।
২১. টিকা লেখো: গৌর।
উত্তর: মরু অঞ্চলে বায়ুর অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে নরম শিলাস্তর বেশি এবং কঠিন শিলাস্তর কম ক্ষয় পেয়ে যখন ব্যাঙের ছাতার মতো ভূমিরূপ তৈরি করে, তখন তাকে গৌর বলে। এর ওপরের অংশ চওড়া ও নীচের অংশ সরু হয়।
২২. অপসারণ গর্ত ও মরুদ্যানের সম্পর্ক কী?উত্তর: মরু অঞ্চলে বায়ুর অপসারণ প্রক্রিয়ায় বালি অপসারিত হয়ে বিশাল গর্ত তৈরি হয়। এই গর্তগুলি যদি ভৌমজলস্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, তবে সেখানে জল বেরিয়ে এসে হ্রদ তৈরি হয় এবং গাছপালা জন্মায়। এইভাবেই অপসারণ গর্ত থেকে মরুদান সৃষ্টি হয়।
২৩. প্লাবনভূমি কীভাবে গঠিত হয়?
উত্তর: নদীর নিম্নগতিতে বর্ষাকালে বন্যা হলে নদীর জল দুই কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী নিচু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বন্যার জল সরে গেলে জলের সঙ্গে বাহিত পলি, বালি, কাদা ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে উর্বর সমভূমি তৈরি করে, তাকে প্লাবনভূমি বলে।
২৪. নদী উপত্যকা ও হিমবাহ উপত্যকার মধ্যে পার্থক্য লেখো।
উত্তর: নদী উপত্যকা সাধারণত সংকীর্ণ ও ‘V’ আকৃতির হয়। কিন্তু হিমবাহ উপত্যকা অনেক চওড়া ও ‘U’ আকৃতির হয়। নদী উপত্যকায় জলপ্রপাত, মন্থকূপ দেখা যায়, আর হিমবাহ উপত্যকায় ঝুলন্ত উপত্যকা, হিমসিঁড়ি দেখা যায়।
২৫. ওয়াদি কী? এর বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তর: মরু অঞ্চলের শুষ্ক নদীখাতকে ওয়াদি বলে। বৈশিষ্ট্য: এগুলি শুধুমাত্র প্রবল বৃষ্টির সময় জলপূর্ণ থাকে, বছরের বেশিরভাগ সময় শুকনো থাকে। ওয়াদির তলদেশ বালি ও নুড়িতে পূর্ণ থাকে।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৩ (২৫টি)
১. নদীর ক্ষয়কার্যের প্রধান তিনটি প্রক্রিয়া আলোচনা করো।
উত্তর: নদীর ক্ষয়কার্যের তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া হল:
ক) অবঘর্ষ (Abrasion): নদীর স্রোতের সঙ্গে বাহিত নুড়ি, পাথর, বালির ঘর্ষণে নদীর তলদেশ ও পার্শ্বদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এর ফলে মন্থকূপের মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়।
খ) ঘর্ষণ (Attrition): নদীর স্রোতে বাহিত শিলাখণ্ডগুলি নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙে গিয়ে আরও ছোটো ও গোলাকার হয়। এই প্রক্রিয়াকে ঘর্ষণ বলে।
গ) জলপ্রবাহজনিত ক্ষয় (Hydraulic Action): শুধুমাত্র জলের প্রবল আঘাতে নদীপাড়ের দুর্বল শিলাস্তর ভেঙে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাকে জলপ্রবাহজনিত ক্ষয় বলে।
২. হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপের বিবরণ দাও।
উত্তর: হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি প্রধান ভূমিরূপ হল:
ক) গ্রাবরেখা (Moraine): হিমবাহ বাহিত নুড়ি, বালি, পাথর ইত্যাদি তার প্রবাহপথের পাশে, সামনে বা নীচে সঞ্চিত হয়ে যে দীর্ঘ, সংকীর্ণ শৈলশিরার মতো ভূমিরূপ তৈরি করে, তাকে গ্রাবরেখা বলে। অবস্থান অনুযায়ী এগুলি পার্শ্ব, মধ্য, প্রান্ত, ভূমি গ্রাবরেখা ইত্যাদি ধরনের হয়।
খ) ড্রামলিন (Drumlin): হিমবাহ বাহিত কাদা, বালি, পাথর ইত্যাদি কোনো উঁচু ঢিবির পিছনে সঞ্চিত হয়ে উলটানো চামচ বা নৌকার মতো যে ভূমিরূপ তৈরি করে, তাকে ড্রামলিন বলে। এর হিমবাহের প্রবাহ দিকের অংশ মসৃণ এবং বিপরীত দিক অমসৃণ হয়।
গ) এসকার (Esker): হিমবাহের নীচে সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলধারার পথে নুড়ি, বালি, কাঁকর ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে বরফ গলে যাওয়ার পর যে আঁকাবাঁকা, দীর্ঘ শৈলশিরার মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে এসকার বলে।
৩. মরু অঞ্চলে বায়ুর কার্যের প্রাধান্য দেখা যায় কেন?
উত্তর: মরু অঞ্চলে বায়ুর কার্যের প্রাধান্যের কারণগুলি হল:
ক) বৃষ্টিপাতের অভাব: বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় ভূমি শুষ্ক থাকে এবং গাছপালা প্রায় জন্মায় না। ফলে মাটি আলগা থাকে এবং বায়ু সহজেই ক্ষয় ও বহন করতে পারে।
খ) উদ্ভিদহীনতা: গাছপালা মাটিকে ধরে রাখে। উদ্ভিদহীনতার কারণে বায়ু ভূপৃষ্ঠে বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হতে পারে এবং ক্ষয়কাজ চালাতে পারে।
গ) যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রাধান্য: দিন ও রাতের উষ্ণতার ব্যাপক পার্থক্যের কারণে শিলাস্তর যান্ত্রিক আবহবিকারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এই শিথিল শিলাকণা বায়ু সহজেই অপসারণ করে।
৪. চিত্রসহ একটি আদর্শ নদীর বিভিন্ন গতি ও সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপের বর্ণনা দাও।
উত্তর: একটি আদর্শ নদীর তিনটি গতিপথ দেখা যায়:
ক) উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহ: উৎস থেকে সমভূমিতে নামার আগে পর্যন্ত নদীর এই গতি দেখা যায়। এখানে ভূমির ঢাল বেশি হওয়ায় নদীর প্রধান কাজ ক্ষয়। এখানে সৃষ্ট ভূমিরূপ হল – ‘V’ আকৃতির উপত্যকা, গিরিখাত, ক্যানিয়ন, জলপ্রপাত, মন্থকূপ ইত্যাদি।
খ) মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ: সমভূমির উপর দিয়ে নদীর প্রবাহকে মধ্যগতি বলে। এখানে ভূমির ঢাল কমে যাওয়ায় নদীর প্রধান কাজ বহন ও সঞ্চয়। এখানে সৃষ্ট ভূমিরূপ হল – অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, পলল ব্যজনী, প্লাবনভূমি ইত্যাদি।
গ) নিম্নগতি বা বদ্বীপ প্রবাহ: মোহনার কাছে নদীর প্রবাহকে নিম্নগতি বলে। এখানে ভূমির ঢাল প্রায় থাকে না বললেই চলে, তাই নদীর প্রধান কাজ সঞ্চয়। এখানে সৃষ্ট ভূমিরূপ হল – বদ্বীপ, খাড়ি, স্বাভাবিক বাঁধ ইত্যাদি। (উত্তরের সাথে একটি নদীর তিন গতির ছবি আঁকলে ভালো হয়)।
৫. সুন্দরবন অঞ্চলের উপর বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব আলোচনা করো।
উত্তর: বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে:
ক) সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি: উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে এবং সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। এর ফলে সুন্দরবনের বহু দ্বীপ, যেমন – লোহাচরা, নিউমুর ইত্যাদি ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গেছে এবং সাগরদ্বীপ, ঘোড়ামারা দ্বীপও বিপন্ন।
খ) লবণাক্ততা বৃদ্ধি: সমুদ্রের জলস্তর বাড়ায় নদীর মিষ্টি জলে লবণের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে সুন্দরী, গেঁওয়া প্রভৃতি ম্যানগ্রোভ গাছের শ্বাসমূল নষ্ট হচ্ছে এবং তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।
গ) ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি: সমুদ্রের উষ্ণতা বাড়ায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা দুইই বাড়ছে, যা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করছে।
৬. হিমবাহ উপত্যকা ও নদী উপত্যকার মধ্যে তিনটি প্রধান পার্থক্য লেখো।
উত্তর: হিমবাহ উপত্যকা ও নদী উপত্যকার মধ্যে তিনটি প্রধান পার্থক্য হল:
১. আকৃতি: নদী উপত্যকা সাধারণত সংকীর্ণ ও ইংরেজি ‘V’ অক্ষরের মতো হয়। অন্যদিকে, হিমবাহ উপত্যকা অনেক চওড়া ও ইংরেজি ‘U’ অক্ষরের মতো হয়।
২. গভীরতা: নদী উপত্যকার গভীরতা ধীরে ধীরে বাড়ে। কিন্তু হিমবাহ উপত্যকা অনেক বেশি গভীর ও প্রশস্ত হয়।
৩. সৃষ্ট ভূমিরূপ: নদী উপত্যকায় জলপ্রপাত, মন্থকূপ, কর্তিত স্পার দেখা যায়। অন্যদিকে, হিমবাহ উপত্যকায় ঝুলন্ত উপত্যকা, হিমসিঁড়ি, প্যাটার্নস্টার হ্রদ ইত্যাদি দেখা যায়।
৭. চিত্রসহ রসে মতানে ও ড্রামলিনের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।
উত্তর: রসে মতানে: এটি হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট। হিমবাহের প্রবাহপথে কোনো কঠিন শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবাত ঢালটি (যেদিকে হিমবাহ আসে) অবঘর্ষের ফলে মসৃণ এবং অনুবাত ঢালটি (বিপরীত দিক) উৎপাটন প্রক্রিয়ায় অমসৃণ ও খাঁজকাটা হয়। এই ভূমিরূপকে রসে মতানে বলে।
ড্রামলিন: এটি হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট। হিমবাহ বাহিত নুড়ি, কাদা, বালি ইত্যাদি কোনো বাধা পেলে তার পিছনে সঞ্চিত হয়ে উলটানো নৌকা বা চামচের মতো যে ভূমিরূপ তৈরি করে, তাকে ড্রামলিন বলে। এর প্রতিবাত ঢাল মসৃণ এবং অনুবাত ঢাল অমসৃণ হয়। (উত্তরের সাথে দুটি ভূমিরূপের ছবি আঁকতে হবে)।
৮. বদ্বীপ গঠনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি কী কী?
উত্তর: বদ্বীপ গঠনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি হল:
ক) নদীতে পলির পরিমাণ বেশি: নদীতে প্রচুর পরিমাণে পলি, বালি, কাদা থাকলে তা মোহনায় সঞ্চিত হয়ে বদ্বীপ গঠনে সাহায্য করে।
খ) নদীর গতিবেগ কম: মোহনার কাছে নদীর গতিবেগ খুব কম হলে তবেই পলি সঞ্চিত হতে পারে।
গ) শান্ত সমুদ্র: মোহনায় সমুদ্র অগভীর ও স্রোতহীন বা শান্ত হলে পলি সহজে ভেসে যায় না এবং বদ্বীপ গড়ে ওঠে। প্রবল সমুদ্রস্রোত ও জোয়ার-ভাটা বদ্বীপ গঠনের প্রতিকূল।
৯. ঝুলন্ত উপত্যকা ও পিরামিড চূড়া কীভাবে গঠিত হয়?
উত্তর: ঝুলন্ত উপত্যকা: যখন কোনো বড় হিমবাহের সঙ্গে ছোট উপনদী হিমবাহ এসে মেশে, তখন বড় হিমবাহের ক্ষয়ক্ষমতা বেশি হওয়ায় তার উপত্যকা বেশি গভীর হয়। বরফ গলে গেলে ছোট হিমবাহের উপত্যকাটি বড়টির উপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, একে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে।
পিরামিড চূড়া: কোনো পর্বতের বিভিন্ন দিকে তিন-চারটি করি বা সার্ক পাশাপাশি গঠিত হলে তাদের মধ্যবর্তী খাড়া শীর্ষদেশটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পিরামিডের মতো তীক্ষ্ণ চূড়ায় পরিণত হয়। একে পিরামিড চূড়া বা হর্ন বলে। যেমন – আল্পস পর্বতের ম্যাটারহর্ন।
১০. মরু অঞ্চলে বায়ুর ক্ষয়কার্যের তিনটি প্রক্রিয়া আলোচনা করো।
উত্তর: মরু অঞ্চলে বায়ুর ক্ষয়কার্যের তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া হল:
ক) অপসারণ (Deflation): প্রবল বায়ুর আঘাতে মরুভূমির শিথিল, শুকনো বালিকণা এক স্থান থেকে উড়ে গিয়ে অন্য স্থানে জমা হয়। এই প্রক্রিয়াকে অপসারণ বলে। এর ফলে অপসারণ গর্ত ও মরুদান সৃষ্টি হয়।
খ) অবঘর্ষ (Abrasion): বায়ুর সঙ্গে ভাসমান কঠিন বালি, নুড়ি, পাথরকণা মরু অঞ্চলের শিলাস্তরের উপর আঘাত করে আঁচড় কাটে এবং ক্ষয় করে। এই প্রক্রিয়াকে অবঘর্ষ বলে। এর ফলে গৌর, ইয়ারদাং, জিউগেন ইত্যাদি তৈরি হয়।
গ) ঘর্ষণ (Attrition): বায়ুর সঙ্গে বাহিত শিলাখণ্ডগুলি একে অপরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙে গিয়ে আরও ছোট ও গোলাকার হয়। এই প্রক্রিয়াকে ঘর্ষণ বলে।
১১. বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপের বর্ণনা দাও।
উত্তর: বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি প্রধান ভূমিরূপ হল:
ক) বালিয়াড়ি (Sand Dune): বায়ুর গতিপথে কোনো বাধা (ঝোপ, পাথর) থাকলে সেখানে বালি জমে যে উঁচু ঢিবি তৈরি হয়, তাকে বালিয়াড়ি বলে। আকৃতি অনুসারে এগুলি বার্খান (অর্ধচন্দ্রাকৃতি) ও সিফ (অনুদৈর্ঘ্য) ইত্যাদি ধরনের হয়।
খ) লোয়েস সমভূমি (Loess Plain): মরুভূমি থেকে বায়ুবাহিত অতি সূক্ষ্ম বালিকণা বহুদূরে জমা হয়ে যে বিস্তীর্ণ, উর্বর সমভূমি তৈরি করে, তাকে লোয়েস সমভূমি বলে।
গ) বাজাদা (Bajada): মরু অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশে একাধিক পলল ব্যজনী মিলিত হয়ে যে প্রায় সমতলভূমি তৈরি করে, তাকে বাজাদা বলে।
১২. জলপ্রপাতের শ্রেণিবিভাগ করো ও উদাহরণ দাও।
উত্তর: জলপ্রপাতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) গঠন অনুসারে: কঠিন ও কোমল শিলার অনুভূমিক বা উল্লম্ব অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গঠিত জলপ্রপাত। যেমন – নায়াগ্রা।
খ) পুনর্যৌবন লাভের ফলে সৃষ্ট: নদীর পুনর্যৌবন লাভের ফলে নিক পয়েন্টে (Knick Point) জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। যেমন – সুবর্ণরেখা নদীর হুড্রু।
গ) ঝুলন্ত উপত্যকাজাত: ঝুলন্ত উপত্যকা থেকে নদী যখন মূল উপত্যকায় পড়ে, তখন জলপ্রপাত তৈরি হয়।
ঘ) চ্যুতি বা ফাটলজনিত: ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট চ্যুতি বা ফাটল বরাবর নদী প্রবাহিত হলে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। যেমন – নর্মদা নদীর ধুঁয়াধার।
১৩. টিকা লেখো: নদী মঞ্চ বা নদী সোপান।
উত্তর: নদীর গতিপথে ভূ-আলোড়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পুনর্যৌবন লাভ ঘটলে নদীর নিম্নক্ষয়ের ক্ষমতা বেড়ে যায়। তখন নদী তার পুরানো উপত্যকার মধ্যে নতুন করে গভীর খাত তৈরি করে। এর ফলে পুরানো উপত্যকার তলদেশ বা প্লাবনভূমিটি নদীর দুই পাশে সিঁড়ির ধাপের মতো উঁচু হয়ে অবস্থান করে। এই সোপান বা ধাপগুলিকে নদী মঞ্চ বলে। ভারতের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলিতে নদী মঞ্চ দেখা যায়।
১৪. টিকা লেখো: করি বা সার্ক।
উত্তর: পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের উৎপাটন ও অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে পর্বতের গায়ে যে আরামকেদারার মতো বা চামচের গর্তের মতো গভীর, খাড়া ঢালযুক্ত ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে করি (স্কটল্যান্ডে) বা সার্ক (ফ্রান্সে) বলে। এর তিনটি দিক খাড়া এবং একটি দিক খোলা থাকে। করি বা সার্কে জল জমে যে হ্রদ তৈরি হয়, তাকে করি হ্রদ বা টার্ন বলে।
১৫. নদীর মোহনায় বদ্বীপ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: নদী যখন মোহনার কাছে সমুদ্রে মেশে, তখন ভূমির ঢাল প্রায় থাকে না এবং নদীর গতিবেগ একেবারে কমে যায়। ফলে নদীর বহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তার সঙ্গে বয়ে আনা পলি, বালি, কাঁকর ইত্যাদি মোহনায় সঞ্চিত হতে থাকে। বছরের পর বছর ধরে এই সঞ্চয়ের ফলে একটি ত্রিকোণাকার বা বাংলা ‘ব’ অক্ষরের মতো ভূভাগ বা দ্বীপ জেগে ওঠে। একেই বদ্বীপ বলে। যেমন – গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ।
১৬. হিমবাহের ক্ষয়কার্যের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।
উত্তর: হিমবাহ প্রধানত দুটি প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কাজ করে:
ক) উৎপাটন বা প্লাকিং (Plucking): হিমবাহ যখন পর্বতের ঢাল বরাবর এগোয়, তখন তার চাপে পর্বতের গায়ে থাকা ফাটলযুক্ত শিলাস্তর আলগা হয়ে যায় এবং হিমবাহের সঙ্গে উৎপাটত হয়ে এগিয়ে চলে। এই প্রক্রিয়াকে উৎপাটন বলে।
খ) অবঘর্ষ (Abrasion): হিমবাহের সঙ্গে বাহিত বড় বড় পাথর, নুড়ি ইত্যাদি হিমবাহের তলদেশে ও উপত্যকার দুই পাশে ঘষা লেগে আঁচড় কাটে এবং ক্ষয় করে। এই প্রক্রিয়াকে অবঘর্ষ বলে। এর ফলে রসে মতানের মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়।
১৭. বার্খান কীভাবে সিফ বালিয়াড়িতে পরিণত হয়?
উত্তর: অর্ধচন্দ্রাকৃতি বার্খান বালিয়াড়ির প্রতিবাত ঢালে বায়ুর ঘূর্ণির ফলে দুটি শিং-এর মাঝের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বালি অপসারিত হয়। কিন্তু শিং দুটি ক্রমশ বাড়তে থাকে। একসময় মাঝের অংশটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং একটি শিং বায়ুর প্রবাহের দিকে লম্বা হয়ে তরবারির মতো অনুদৈর্ঘ্য বালিয়াড়ি বা সিফ বালিয়াড়িতে পরিণত হয়।
১৮. আবহবিকার, ক্ষয়ীভবন ও পুঞ্জক্ষয়ের মধ্যে সম্পর্ক লেখো।
উত্তর: আবহবিকার, ক্ষয়ীভবন ও পুঞ্জক্ষয়—এই তিনটি প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং একত্রে নগ্নীভবন ঘটায়। আবহবিকারের ফলে শিলাস্তর চূর্ণবিচূর্ণ ও শিথিল হয়। এই শিথিল পদার্থগুলি যখন নদী, বায়ু, হিমবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে অপসারিত হয়, তখন তাকে ক্ষয়ীভবন বলে। আবার, মাধ্যাকর্ষণের টানে যখন শিলাস্তর নীচে নেমে আসে, তখন তাকে পুঞ্জক্ষয় বলে। অর্থাৎ, আবহবিকার ক্ষয়ীভবন ও পুঞ্জক্ষয়ের পথকে প্রস্তুত করে দেয়।
১৯. ক্যানিয়ন ও গিরিখাতের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লেখো।
উত্তর: সাদৃশ্য: উভয়ই নদীর নিম্নক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট গভীর ও সংকীর্ণ উপত্যকা। উভয়ই নদীর উচ্চগতিতে বা পার্বত্য অঞ্চলে গঠিত হয়।
বৈসাদৃশ্য: ১) গিরিখাত আর্দ্র অঞ্চলে এবং ক্যানিয়ন শুষ্ক অঞ্চলে সৃষ্টি হয়। ২) গিরিখাত ‘V’ আকৃতির এবং ক্যানিয়ন ‘I’ আকৃতির হয়। ৩) গিরিখাতের পার্শ্বক্ষয় তুলনামূলকভাবে বেশি, কিন্তু ক্যানিয়নের পার্শ্বক্ষয় প্রায় হয় না বললেই চলে।
২০. বহির্জাত প্রক্রিয়া হিসেবে নদীর ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর: বহির্জাত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নদীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নদী তার প্রবাহপথে তিনটি প্রধান কাজ করে—ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয়। উচ্চগতিতে নদী ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে গিরিখাত, ক্যানিয়ন, জলপ্রপাত তৈরি করে ভূমির উচ্চতা হ্রাস করে (অবরোহণ)। মধ্যগতিতে ক্ষয়জাত পদার্থ বহন করে এবং নিম্নগতিতে তা সঞ্চয় করে প্লাবনভূমি, বদ্বীপ ইত্যাদি তৈরি করে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করে (আরোহণ)। এইভাবেই নদী অবরোহণ ও আরোহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের সমতলীকরণ বা পর্যায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে।
২১. টিকা লেখো: প্লাবনভূমি ও স্বাভাবিক বাঁধ।
উত্তর: প্লাবনভূমি: নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে বর্ষাকালে বন্যার সময় নদীর জল দুই কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বন্যার জল কমে গেলে পলি, বালি ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে উর্বর সমভূমি তৈরি হয়, তাকে প্লাবনভূমি বলে।
স্বাভাবিক বাঁধ: বন্যার সময় নদীর দুই তীরে অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী পলিরাশি সঞ্চিত হয়ে যে দীর্ঘ, অনুচ্চ বাঁধের মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে স্বাভাবিক বাঁধ বলে। এটি প্লাবনভূমির থেকে কিছুটা উঁচু হয় এবং জনবসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে।
২২. হিমবাহের শ্রেণিবিভাগ করো ও উদাহরণ দাও।
উত্তর: হিমবাহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) মহাদেশীয় হিমবাহ: বিশাল মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত বরফের আস্তরণকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে। যেমন – অ্যান্টার্কটিকার ল্যাম্বার্ট, গ্রিনল্যান্ডের বরফ চাদর।
খ) পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ: পর্বতের উঁচু অংশ থেকে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হিমবাহকে পার্বত্য হিমবাহ বলে। যেমন – ভারতের সিয়াচেন, গঙ্গোত্রী।
গ) পাদদেশীয় হিমবাহ: পর্বতের পাদদেশে একাধিক উপত্যকা হিমবাহ মিলিত হয়ে যে বরফের ক্ষেত্র তৈরি করে, তাকে পাদদেশীয় হিমবাহ বলে। যেমন – আলাস্কার মালাসপিনা।
২৩. ইনসেলবার্গ ও মোনাডনকের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
উত্তর: ইনসেলবার্গ: এটি মরু সমপ্রায় ভূমিতে ক্ষয় প্রতিরোধী কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অবশিষ্ট পাহাড়। এর পার্শ্বদেশ খুব খাড়া হয়। জার্মান শব্দ ইনসেলবার্গের অর্থ ‘দ্বীপ-শৈল’।
মোনাডনক: এটি আর্দ্র সমপ্রায় ভূমিতে ক্ষয় প্রতিরোধী কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত অবশিষ্ট পাহাড়। এর পার্শ্বদেশের ঢাল ইনসেলবার্গের মতো খাড়া হয় না। আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারের মাউন্ট মোনাডনকের নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে।
২৪. “সমস্ত জলপ্রপাতই ক্যাসকেড, কিন্তু সমস্ত ক্যাসকেড জলপ্রপাত নয়” — ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: যখন জলধারা উঁচু স্থান থেকে সরাসরি নীচে পড়ে, তখন তাকে জলপ্রপাত বলে। অন্যদিকে, যখন জলধারা সিঁড়ির ধাপের মতো ধাপে ধাপে নীচে নামে, তখন তাকে ক্যাসকেড বা সোপান বলে। সুতরাং, যেকোনো জলপ্রপাতই এক প্রকার ক্যাসকেড (এক ধাপের)। কিন্তু ক্যাসকেড মানেই ধাপে ধাপে পতন, যা সবসময় একটিমাত্র বড় জলপ্রপাত নাও হতে পারে। তাই বলা হয়, সমস্ত জলপ্রপাতই ক্যাসকেড, কিন্তু সমস্ত ক্যাসকেড জলপ্রপাত নয়।
২৫. ক্রেগ ও টেল ভূমিরূপ কীভাবে গঠিত হয়?
উত্তর: এটি হিমবাহের ক্ষয় ও সঞ্চয়ের মিলিত কার্যের ফলে গঠিত একটি বিশেষ ভূমিরূপ। হিমবাহের প্রবাহপথে কোনো কঠিন শিলা (ক্রেগ) অবস্থান করলে হিমবাহ সেটিকে ডিঙিয়ে যাওয়ার সময় তার প্রতিবাত ঢালটি ক্ষয় করে মসৃণ করে। কিন্তু কঠিন শিলার পিছনে অনুবাত ঢালে হিমবাহ বাহিত নুড়ি, বালি, কাদা ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে একটি লেজের (টেল) মতো অংশ তৈরি করে। এই ভূমিরূপকেই ক্রেগ ও টেল বলে।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৫ (১০টি)
১. নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট প্রধান তিনটি ভূমিরূপের চিত্রসহ আলোচনা করো।
উত্তর:
নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে ভূমির ঢাল কমে যাওয়ায় এবং নদীর গতিবেগ হ্রাস পাওয়ায় তার বহন ক্ষমতা কমে যায়। ফলে নদী তার সঙ্গে বয়ে আনা পলি, বালি, কাঁকর ইত্যাদি সঞ্চয় করে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠন করে। প্রধান তিনটি ভূমিরূপ হল:
ক) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Ox-bow Lake): নদীর মধ্যগতিতে সমভূমির উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে (মিয়েন্ডার) চলার সময় বাঁকের বাইরের দিকে ক্ষয় এবং ভিতরের দিকে সঞ্চয় হয়। ফলে একসময় বাঁক দুটি খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং বন্যার সময় নদী ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ দিয়ে সোজা পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর ফলে পরিত্যক্ত পুরানো বাঁকটি মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি হ্রদে পরিণত হয়, যা দেখতে ঘোড়ার খুরের মতো। একে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে। যেমন – পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের মতিঝিল।
খ) প্লাবনভূমি ও স্বাভাবিক বাঁধ (Flood Plain & Natural Levee): নিম্নগতিতে বর্ষাকালে নদীতে বন্যা হলে জল দুই কূল ছাপিয়ে যায়। বন্যার জল কমে গেলে জলের সঙ্গে বাহিত পলি, বালি ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সঞ্চিত হয়ে যে উর্বর সমভূমি তৈরি করে, তাকে প্লাবনভূমি বলে। বন্যার সময় নদীর দুই পাড়ে অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী পদার্থগুলি সঞ্চিত হয়ে যে দীর্ঘ, অনুচ্চ বাঁধের মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে স্বাভাবিক বাঁধ বলে।
গ) বদ্বীপ (Delta): নদীর মোহনায় সমুদ্রের স্রোত কম থাকলে এবং নদীতে পলির পরিমাণ বেশি হলে, সেই পলি সঞ্চিত হয়ে মাত্রাহীন বাংলা ‘ব’ বা গ্রিক অক্ষর ‘ডেল্টা’ (Δ) এর মতো যে ত্রিকোণাকার দ্বীপ বা ভূখণ্ড তৈরি হয়, তাকে বদ্বীপ বলে। আকৃতি অনুসারে বদ্বীপ বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন – ধনুকাকৃতি (গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র), পাখির পায়ের মতো (মিসিসিপি-মিসৌরি) ইত্যাদি।
(প্রতিটি ভূমিরূপের পাশে একটি করে সরল চিত্র আঁকতে হবে)।
২. হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট প্রধান তিনটি ভূমিরূপের চিত্রসহ আলোচনা করো।
উত্তর:
পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ তার উৎপাটন ও অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে। প্রধান তিনটি ভূমিরূপ হল:
ক) করি বা সার্ক (Corrie or Cirque): পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে পর্বতের গায়ে যে আরামকেদারার মতো বা চামচের গর্তের মতো গভীর, খাড়া ঢালযুক্ত ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে করি বা সার্ক বলে। এর তিনটি দিক খাড়া এবং একটি দিক খোলা থাকে। করি বা সার্কে জল জমে যে হ্রদ তৈরি হয়, তাকে করি হ্রদ বা টার্ন বলে।
খ) অ্যারেট বা অ্যারিতি (Arête): দুটি পাশাপাশি করির মধ্যবর্তী খাড়া, সংকীর্ণ ও করাতের দাঁতের মতো শৈলশিরাকে অ্যারেট বা অ্যারিতি বলে। যখন দুটি করি বিপরীত দিক থেকে ক্ষয় করে একে অপরের দিকে এগোতে থাকে, তখন মধ্যবর্তী অংশটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এই ভূমিরূপ তৈরি হয়।
গ) পিরামিড চূড়া বা হর্ন (Pyramidal Peak or Horn): কোনো পর্বতের বিভিন্ন দিকে তিন বা ততোধিক করি পাশাপাশি গঠিত হলে তাদের মধ্যবর্তী শীর্ষদেশটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পিরামিডের মতো তীক্ষ্ণ চূড়ায় পরিণত হয়। একে পিরামিড চূড়া বা হর্ন বলে। আল্পস পর্বতের ম্যাটারহর্ন এবং ভারতের হিমালয়ের নীলকন্ঠ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
(প্রতিটি ভূমিরূপের পাশে একটি করে সরল চিত্র আঁকতে হবে)।
৩. বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি প্রধান ভূমিরূপের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
উত্তর:
শুষ্ক মরু অঞ্চলে বায়ু বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে নানা ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে। প্রধান তিনটি ভূমিরূপ হল:
ক) গৌর বা গারা (Gour or Gara): মরু অঞ্চলে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর অনুভূমিকভাবে অবস্থান করলে বায়ুর অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে নীচের কোমল শিলাস্তর বেশি এবং উপরের কঠিন শিলাস্তর কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো যে ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে গৌর বলে। এর ওপরের অংশ চওড়া (টেবিলের মতো) এবং নীচের অংশ সরু হয়।
খ) জিউগেন (Zeugen): মরু অঞ্চলে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর অনুভূমিকভাবে পরপর অবস্থান করলে যান্ত্রিক আবহবিকারের ফলে উপরের কঠিন শিলাস্তরে ফাটল তৈরি হয়। সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে নীচের কোমল শিলাস্তরকে বেশি ক্ষয় করে। এর ফলে চ্যাপ্টা মাথাযুক্ত ও খাঁজকাটা দেওয়ালযুক্ত ভূমিরূপ তৈরি হয়, যাকে জিউগেন বলে। এর শীর্ষদেশ চওড়া এবং দেওয়াল খাঁজকাটা হয়।
গ) ইয়ারদাং (Yardang): মরু অঞ্চলে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর বায়ুর গতিপথের সমান্তরালে উল্লম্বভাবে অবস্থান করলে বায়ুর অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে কোমল শিলাস্তর বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লম্বাটে খাঁজ এবং কঠিন শিলাস্তর কম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তীক্ষ্ণ শৈলশিরার মতো অবস্থান করে। এই ভূমিরূপকে ইয়ারদাং বলে। এগুলিকে দেখতে অনেকটা উলটানো নৌকার মতো হয়।
(প্রতিটি ভূমিরূপের পাশে একটি করে সরল চিত্র আঁকতে হবে)।
৪. বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট প্রধান ভূমিরূপগুলি আলোচনা করো।
উত্তর:
মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলে বায়ুর কাজ প্রধান হলেও মাঝে মাঝে আকস্মিক প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট জলধারাও ভূমিরূপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মিলিত কার্যে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি হল:
ক) ওয়াদি (Wadi): মরু অঞ্চলের শুষ্ক নদীখাতকে ওয়াদি বলে। শুধুমাত্র প্রবল বৃষ্টির সময় এগুলিতে জল থাকে, অন্য সময় শুকনো থাকে।
খ) পেডিমেন্ট (Pediment): মরু অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশে জলধারা ও বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে যে মৃদু ঢালযুক্ত শিলাময় সমভূমি গঠিত হয়, তাকে পেডিমেন্ট বলে।
গ) বাজাদা (Bajada): পেডিমেন্টের নীচে জলধারা দ্বারা বাহিত পলি, বালি ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে প্রায় সমতলভূমি তৈরি হয়, তাকে বাজাদা বলে। একাধিক পলল ব্যজনী মিলিত হয়ে বাজাদা গঠন করে।
ঘ) প্লায়া (Playa): মরু অঞ্চলের অবনমিত অংশে বা দুটি বাজাদার মধ্যবর্তী নিচু স্থানে বৃষ্টির জল জমে যে লবণাক্ত জলের হ্রদ তৈরি হয়, তাকে প্লায়া বলে। এই হ্রদ শুকিয়ে গেলে লবণের আস্তরণ দেখা যায়। রাজস্থানে এগুলিকে ধান্দ বলে।
৫. নদীর মধ্যগতিতে সৃষ্ট প্রধান ভূমিরূপগুলির বিবরণ দাও।
উত্তর:
নদী যখন সমভূমিতে প্রবেশ করে, তখন তার মধ্যগতির সূচনা হয়। এখানে ভূমির ঢাল কমে যাওয়ায় নদীর প্রধান কাজ বহন, এবং সামান্য ক্ষয় ও সঞ্চয়। এই গতিতে সৃষ্ট প্রধান ভূমিরূপগুলি হল:
ক) পলল শঙ্কু ও পলল ব্যজনী: পর্বতের পাদদেশে ভূমির ঢাল হঠাৎ কমে যাওয়ায় নদী বাহিত নুড়ি, বালি, কাঁকর ইত্যাদি শঙ্কুর আকারে সঞ্চিত হয়ে পলল শঙ্কু তৈরি করে। একাধিক পলল শঙ্কু মিলিত হয়ে হাতপাখার মতো দেখতে পলল ব্যজনী গঠন করে।
খ) নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার: সমভূমিতে সামান্য বাধা পেলেই নদী এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়। এই সর্পিল বা আঁকাবাঁকা গতিপথকে নদীবাঁক বা মিয়েন্ডার বলে। তুরস্কের মিয়েন্ডারেস নদীর নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে।
গ) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ: নদীর বাঁক খুব বেশি বেড়ে গেলে একসময় দুটি বাঁক খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং নদী সোজা পথে প্রবাহিত হয়। পরিত্যক্ত বাঁকটি হ্রদে পরিণত হয়, যা দেখতে ঘোড়ার খুরের মতো। একে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে।
ঘ) প্লাবনভূমি: বন্যার সময় নদীর দুই কূলে পলি জমে যে উর্বর সমভূমি তৈরি হয়, তাকে প্লাবনভূমি বলে।
৬. হিমবাহ ও জলধারার মিলিত সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট প্রধান ভূমিরূপগুলির সচিত্র বর্ণনা দাও।
উত্তর:
হিমবাহ ও তার থেকে গলে যাওয়া জলধারার মিলিত সঞ্চয়কার্যের ফলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গঠিত হয়। প্রধান তিনটি ভূমিরূপ হল:
ক) বহিঃধৌত সমভূমি (Outwash Plain): হিমবাহ বাহিত নুড়ি, বালি, কাদা ইত্যাদি পদার্থ হিমবাহের শেষ প্রান্তে বা প্রান্ত গ্রাবরেখার সামনে জলধারা দ্বারা বাহিত ও সঞ্চিত হয়ে যে বিস্তীর্ণ, মৃদু ঢালযুক্ত সমভূমি তৈরি করে, তাকে বহিঃধৌত সমভূমি বলে।
খ) এসকার (Esker): হিমবাহের নীচে সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলধারার পথে নুড়ি, বালি, কাঁকর ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে বরফ গলে যাওয়ার পর যে দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা ও সংকীর্ণ শৈলশিরার মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে এসকার বলে।
গ) কেম (Kame): হিমবাহ ও পর্বতের মাঝে সৃষ্ট হ্রদে বা বহিঃধৌত সমভূমির উপর অবস্থিত কোনো হ্রদে হিমবাহ বাহিত নুড়ি, বালি, কাদা ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে ত্রিকোণাকার বদ্বীপের মতো বা ঢিবির মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়, তাকে কেম বলে।
(প্রতিটি ভূমিরূপের পাশে একটি করে সরল চিত্র আঁকতে হবে)।
৭. বিভিন্ন প্রকার বদ্বীপের গঠন প্রক্রিয়া উপযুক্ত উদাহরণ ও চিত্রসহ আলোচনা করো।
উত্তর:
সঞ্চয়ের আকৃতি ও গঠন অনুসারে বদ্বীপকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) ধনুকাকৃতি বদ্বীপ (Arcuate Delta): যে বদ্বীপের বাইরের দিকটা সমুদ্রের দিকে ধনুকের মতো বাঁকানো থাকে, তাকে ধনুকাকৃতি বদ্বীপ বলে। নদীতে পলির পরিমাণ খুব বেশি এবং সমুদ্রের স্রোত মাঝারি হলে এই ধরনের বদ্বীপ গড়ে ওঠে। যেমন – গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, নীলনদ, হোয়াংহো নদীর বদ্বীপ।
খ) পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ (Bird’s Foot Delta): নদীর মোহনায় সূক্ষ্ম পলির পরিমাণ বেশি এবং সমুদ্রের স্রোত খুব দুর্বল হলে নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে মেশে। এই শাখাগুলির দুই পাশে পলি জমে যে বদ্বীপ তৈরি হয়, তা দেখতে অনেকটা পাখির পায়ের মতো হয়। যেমন – আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর বদ্বীপ।
গ) কাসপেট বদ্বীপ বা করাত-দাঁত বদ্বীপ (Cuspate Delta): নদীর মোহনায় দুটি বিপরীতমুখী সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হলে বাহিত পলিরাশি সঞ্চিত হয়ে যে তীক্ষ্ণ বা করাতের দাঁতের মতো আকৃতির বদ্বীপ তৈরি হয়, তাকে কাসপেট বদ্বীপ বলে। যেমন – ইতালির টাইবার নদীর বদ্বীপ।
(প্রতিটি বদ্বীপের পাশে একটি করে সরল চিত্র আঁকতে হবে)।
৮. বহির্জাত প্রক্রিয়া কাকে বলে? এই প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক বা মাধ্যমগুলি কী কী?
উত্তর:
বহির্জাত প্রক্রিয়া: ভূপৃষ্ঠের বাইরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি (যেমন – নদী, বায়ু, হিমবাহ ইত্যাদি) দ্বারা যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় (যেমন – ক্ষয়, বহন, সঞ্চয়) ভূমিরূপের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে, তাদের একত্রে বহির্জাত প্রক্রিয়া বলে। এই প্রক্রিয়া মূলত ভূপৃষ্ঠের উপর ক্রিয়াশীল এবং এর মূল উৎস হল সূর্য।
নিয়ন্ত্রক বা মাধ্যম: বহির্জাত প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক বা মাধ্যমগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:
১. স্থিতিশীল মাধ্যম: যেগুলি এক জায়গায় স্থির থেকে কাজ করে। যেমন – আবহবিকার (উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুচাপ)।
২. গতিশীল মাধ্যম: যেগুলি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়ে কাজ করে। প্রধান গতিশীল মাধ্যমগুলি হল:
ক) নদী: জলের প্রবাহের মাধ্যমে ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় করে। এটি সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।
খ) হিমবাহ: বরফের প্রবাহের মাধ্যমে ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় করে।
গ) বায়ু: গ্যাসীয় প্রবাহের মাধ্যমে ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় করে, বিশেষত মরু অঞ্চলে।
ঘ) সমুদ্রতরঙ্গ: উপকূল অঞ্চলে ক্ষয় ও সঞ্চয় করে।
ঙ) ভৌমজল: চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে ক্ষয় ও সঞ্চয় করে।
৯. বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদী, হিমবাহ ও বায়ুর কার্যের উপর কী প্রভাব পড়ছে, তা আলোচনা করো।
উত্তর:
বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদী, হিমবাহ ও বায়ুর কার্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে:
ক) নদীর উপর প্রভাব: উষ্ণতা বাড়ার ফলে বাষ্পীভবন বাড়ছে এবং বৃষ্টিপাতের ধরন बदलছে। কোথাও অনাবৃষ্টির ফলে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার কোথাও অতিবৃষ্টির ফলে বিধ্বংসী বন্যা হচ্ছে। হিমবাহগলা জলে পুষ্ট নদীগুলিতে বরফ দ্রুত গলে যাওয়ায় প্রথমে জলের পরিমাণ বাড়ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে হিমবাহ নিঃশেষিত হলে সেগুলি শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
খ) হিমবাহের উপর প্রভাব: বিশ্ব উষ্ণায়নের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে হিমবাহের উপর। মেরু অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলের হিমবাহগুলি দ্রুত গলে যাচ্ছে, যা সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি করছে। এর ফলে হিমবাহের ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্ষমতাতেও পরিবর্তন আসছে।
গ) বায়ুর উপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মরু অঞ্চলের বিস্তার বাড়ছে (মরুভবন)। এর ফলে বায়ুর ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় কার্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডোর মতো বিধ্বংসী বায়ুর প্রকোপ বাড়ছে, যা ভূমিরূপের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।
১০. অবরোহণ ও আরোহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করো।
উত্তর:
অবরোহণ ও আরোহণ হল পর্যায়ন প্রক্রিয়ার দুটি অংশ। এদের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল:
| বৈশিষ্ট্য | অবরোহণ (Degradation) | আরোহণ (Aggradation) |
|—|—|—|
| **সংজ্ঞা** | যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়কার্যের ফলে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা হ্রাস পায়। | যে প্রক্রিয়ায় ক্ষয়জাত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে ভূপৃষ্ঠের নীচু স্থানের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। |
| **প্রকৃতি** | এটি একটি ক্ষয়মূলক বা বিনাশমূলক প্রক্রিয়া। | এটি একটি সঞ্চয়মূলক বা গঠনমূলক প্রক্রিয়া। |
| **ফল** | এর ফলে ভূমির বন্ধুরতা হ্রাস পায় এবং ভূমিভাগ নিচু হয়। | এর ফলে নীচু স্থান ভরাট হয়ে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। |
| **সৃষ্ট ভূমিরূপ** | গিরিখাত, ক্যানিয়ন, করি, গৌর, ইনসেলবার্গ ইত্যাদি ক্ষয়জাত ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। | প্লাবনভূমি, বদ্বীপ, গ্রাবরেখা, বালিয়াড়ি ইত্যাদি সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। |
| **উদাহরণ** | নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে গিরিখাত সৃষ্টি হওয়া একটি অবরোহণ প্রক্রিয়া। | নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে মোহনায় বদ্বীপ সৃষ্টি হওয়া একটি আরোহণ প্রক্রিয়া। |
অবরোহণ ও আরোহণ প্রক্রিয়া দুটি বিপরীতমুখী হলেও একে অপরের পরিপূরক। অবরোহণের ফলে সৃষ্ট পদার্থই আরোহণের মাধ্যমে সঞ্চিত হয় এবং এই দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে সমতা আসে।
বহির্জাত প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট ভূমিরূপ class 10 প্রশ্ন উত্তর, MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 Geography বহির্জাত প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট ভূমিরূপ Question Ans