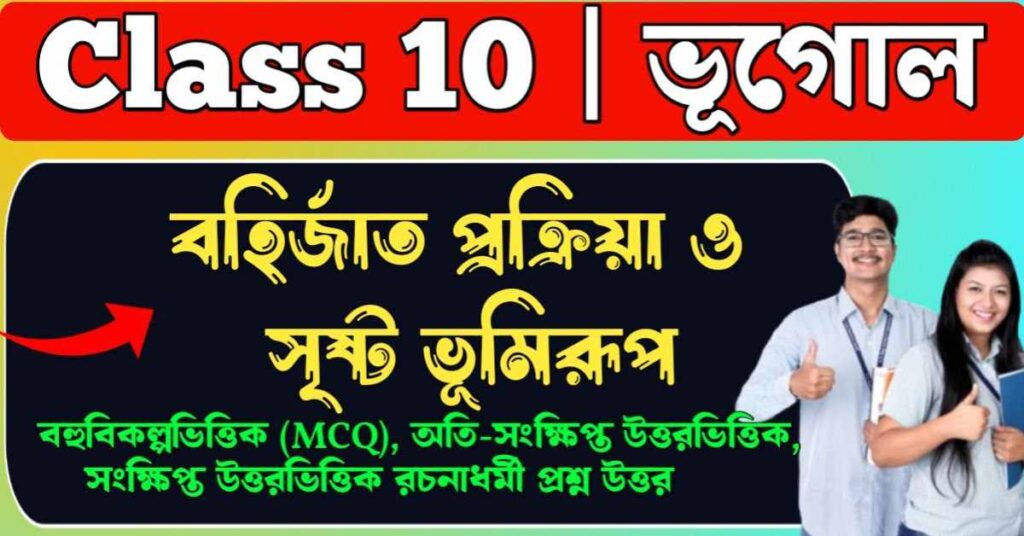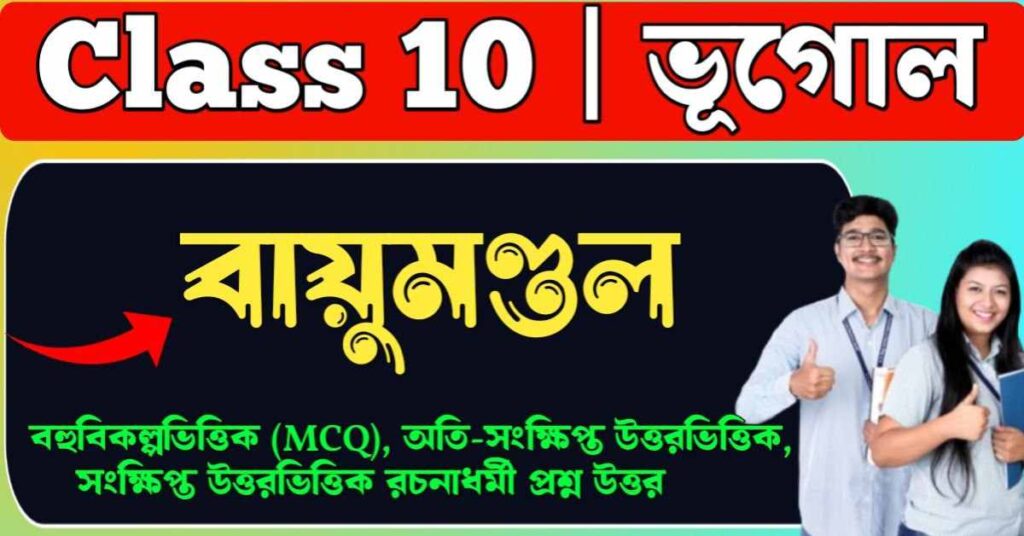ভারতের জলসম্পদ Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী হল –
২. ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হল –
৩. ভারতের একটি পশ্চিমবাহিনী নদী হল –
৪. ভারতে জলসেচের যে পদ্ধতিটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়, তা হল –
৫. শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতটি অবস্থিত –
৬. গঙ্গার প্রধান উপনদী হল –
৭. বৃষ্টির জল সংরক্ষণে ভারতের কোন রাজ্য প্রথম?
৮. ভারতের উচ্চতম বাঁধ হল –
৯. ভারতের একটি অন্তর্বাহিনী নদী হল –
১০. হিরাকুদ বাঁধটি যে নদীর উপর অবস্থিত, তা হল –
১১. দক্ষিণ ভারতে জলাশয়ের মাধ্যমে জলসেচ বেশি প্রচলিত কারণ –
১২. সিন্ধু নদের উৎপত্তি হয়েছে –
১৩. ভারতের বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ হল –
১৪. ভারতের ‘দুঃখের নদ’ বলা হয় –
১৫. ‘দক্ষিণের গঙ্গা’ বলা হয় –
১৬. নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে যে নদীর উপর, তা হল –
১৭. ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য জলবিভাজিকা হল –
১৮. ভারতের দীর্ঘতম সেচখাল হল –
১৯. একটি নিত্যবহ নদী হল –
২০. কোন নদীর মোহনায় বদ্বীপ নেই?
২১. ভারতের যে নদীর নাম একটি পুরুষ চরিত্র অনুসারে, তা হল –
২২. ‘গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান’ কর্মসূচিটি গৃহীত হয় –
২৩. ভারতের একটি গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী হল –
২৪. ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ কোনটি?
২৫. কপিলধারা জলপ্রপাতটি অবস্থিত –
২৬. উত্তর ভারতে কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে জলসেচ বেশি হয় কারণ –
২৭. গঙ্গা নদীর উৎস হল –
২৮. স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হল –
২৯. যে নদীটি অরুণাচল প্রদেশে ‘ডিহং’ নামে পরিচিত, তা হল –
৩০. ভারতের কোন রাজ্যে জলাশয়ের মাধ্যমে জলসেচ সবচেয়ে বেশি হয়?
৩১. ভারতের বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ হল –
৩২. পাঞ্জাবে প্লাবন খালকে বলা হয় –
৩৩. ভারতের কোন নদী উপত্যকা কয়লা সমৃদ্ধ?
৩৪. ‘জলবিভাজিকা উন্নয়ন’ হল একটি পদ্ধতি –
৩৫. ‘বৃদ্ধগঙ্গা’ বলা হয় কোন নদীকে?
৩৬. কাবেরী নদীর একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত হল –
৩৭. বৃষ্টির জল ধরে রেখে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বলে –
৩৮. ভারতের কোন রাজ্যে সর্বাধিক সংখ্যক নদী রয়েছে?
৩৯. ভাকরা বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত?
৪০. ভারতের একটি আদর্শ নদীর উদাহরণ হল –
৪১. ‘পঞ্চনদের দেশ’ বলা হয় –
৪২. ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত হল –
৪৩. কোন নদীর তীরে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল অবস্থিত?
৪৪. নিম্নলিখিত কোনটি সেচের আধুনিক পদ্ধতি?
৪৫. গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল হল –
৪৬. দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি –
৪৭. ভারতের কোন নদী সর্বাধিক রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে?
৪৮. কানপুর শহরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৪৯. ‘National Waterway-1’ কোন নদীর উপর অবস্থিত?
৫০. ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী পরিকল্পনার জলাধারটি হল –
৫১. ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতে কী নামে পরিচিত?
৫২. কোন প্রকার সেচ পদ্ধতিতে জলের অপচয় সবচেয়ে কম হয়?
৫৩. কোন নদীর তীরে রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা অবস্থিত?
৫৪. ‘তেলেগু গঙ্গা’ প্রকল্পটি কোন দুটি রাজ্যের যৌথ উদ্যোগ?
৫৫. ভারতের গভীরতম হ্রদ কোনটি?
৫৬. ‘হুড্রু’ জলপ্রপাতটি কোন নদীর উপর অবস্থিত?
৫৭. কোন নদীতে মাজুলি দ্বীপ অবস্থিত?
৫৮. ভারতের কোন রাজ্যে ভৌমজলের ব্যবহার সর্বাধিক?
৫৯. যমুনা নদীর উৎস কোথায়?
৬০. একটি অনিত্যবহ খালের উদাহরণ হল –
৬১. অলকানন্দা ও ভাগীরথীর মিলিত প্রবাহ কী নামে পরিচিত?
৬২. ভারতের জলসংকটের প্রধান কারণ কী?
৬৩. ‘মেত্তুর’ বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত?
৬৪. নিম্নলিখিত কোনটি পবিত্র নদী হিসেবে পরিচিত?
৬৫. সিন্ধুর দীর্ঘতম উপনদী হল –
৬৬. ভারতের কোন রাজ্যে খালের মাধ্যমে জলসেচ সর্বাধিক?
৬৭. কোন নদীকে ‘ত্রাসের নদী’ বলা হয়?
৬৮. কোলেরু হ্রদটি হল একটি –
৬৯. কোন নদীর তীরে আহমেদাবাদ শহর অবস্থিত?
৭০. ভারতের কোন রাজ্যে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ‘ছাদ-জল’ (Rooftop harvesting) বাধ্যতামূলক?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. ভারতের দীর্ঘতম নদীর নাম কী?
উত্তর: গঙ্গা (ভারতে প্রবাহপথ অনুসারে)।
২. বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কাকে বলে?
উত্তর: যে নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ, জলবিদ্যুৎ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল সরবরাহ ইত্যাদি একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করা হয়, তাকে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলে।
৩. ভারতের একটি নিত্যবহ নদীর নাম লেখো।
উত্তর: গঙ্গা বা সিন্ধু।
৪. জলবিভাজিকা উন্নয়ন কী?
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট নদী অববাহিকার প্রাকৃতিক সম্পদের (বিশেষত জল ও ভূমির) সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোকে জলবিভাজিকা উন্নয়ন বলে।
৫. ভারতের বৃহত্তম সেচখালের নাম কী?উত্তর: ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল বা রাজস্থান খাল।
৬. দক্ষিণ ভারতের শস্য ভান্ডার কোন অঞ্চলকে বলে?
উত্তর: কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলকে।
৭. ভারতের কোন রাজ্যে সর্বাধিক নলকূপের মাধ্যমে জলসেচ হয়?
উত্তর: উত্তরপ্রদেশ।
৮. ভারতের একটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের নাম লেখো।
উত্তর: পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব ঢাল (যেমন – কর্নাটক মালভূমির পূর্বাংশ)।
৯. ভারতের একটি লবণাক্ত জলের হ্রদের উদাহরণ দাও।
উত্তর: রাজস্থানের সম্বর হ্রদ।
১০. ‘দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা’ কোন নদীকে বলা হয়?
উত্তর: কাবেরী নদীকে (পবিত্রতার জন্য)।
১১. ভারতের কোন রাজ্যে খালের মাধ্যমে জলসেচ সবচেয়ে বেশি হয়?
উত্তর: উত্তরপ্রদেশ।
১২. ভারতের কোন নদী উপত্যকা ‘ভারতের রুর’ নামে পরিচিত?
উত্তর: দামোদর নদী উপত্যকা।
১৩. গঙ্গার একটি বাম তীরের ও একটি ডান তীরের উপনদীর নাম লেখো।
উত্তর: বাম তীরের উপনদী – গোমতী; ডান তীরের উপনদী – যমুনা।
১৪. ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি?
উত্তর: কুঞ্চিকল জলপ্রপাত (বরাহী নদীর উপর)।
১৫. ভারতের একটি আন্তর্জাতিক নদীর নাম লেখো।
উত্তর: সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র।
১৬. ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা কোন নদীর উপর গড়ে উঠেছে?
উত্তর: শতদ্রু নদীর উপর।
১৭. বৃষ্টির জল সংরক্ষণের একটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: ভৌমজলের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা এবং শুষ্ক ঋতুতে জলের চাহিদা মেটানো।
১৮. ভারতের কোন রাজ্যে জলাশয়ের মাধ্যমে জলসেচ সবচেয়ে বেশি প্রচলিত?
উত্তর: তামিলনাড়ু।
১৯. ভারতের একটি আদর্শ নদীর নাম লেখো।
উত্তর: গঙ্গা।
২০. কোন সেচ পদ্ধতি দক্ষিণ ভারতে বেশি দেখা যায়?
উত্তর: জলাশয়ের মাধ্যমে সেচ।
২১. DVC-এর পুরো নাম কী?
উত্তর: Damodar Valley Corporation.
২২. নর্মদা নদীর উৎস কোথায়?
উত্তর: মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গ থেকে।
২৩. ভারতের একটি পূর্ববাহিনী নদীর নাম লেখো।
উত্তর: গোদাবরী বা কৃষ্ণা।
২৪. কোন শহরকে ‘ভারতের হ্রদনগরী’ বলা হয়?
উত্তর: উদয়পুর (রাজস্থান)।
২৫. ‘সাংপো’ নদী ভারতে কী নামে প্রবেশ করেছে?
উত্তর: ডিহং নামে।
২৬. ভারতের কোন রাজ্যে জলসংকট সবচেয়ে তীব্র?
উত্তর: রাজস্থান।
২৭. নিত্যবহ খাল কী?
উত্তর: যে সেচখালে নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করে সারাবছর জল সরবরাহ করা হয়, তাকে নিত্যবহ খাল বলে।
২৮. যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহরের নাম লেখো।
উত্তর: দিল্লি বা আগ্রা।
২৯. ভারতের একটি বিখ্যাত কয়াল-এর নাম লেখো।
উত্তর: ভেম্বানাদ কয়াল।
৩০. ভারতের দীর্ঘতম উপনদী কোনটি?
উত্তর: যমুনা।
৩১. কোন নদীর তীরে কলকাতা বন্দর অবস্থিত?
উত্তর: হুগলি নদীর তীরে।
৩২. ‘জল সংরক্ষণের’ একটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির নাম লেখো।
উত্তর: রাজস্থানের জোহাদ বা টাঁকা।
৩৩. ভারতের কোন নদীকে ‘জৈব মরুভূমি’ বলা হয়?
উত্তর: দামোদর নদকে।
৩৪. প্লাবন খাল কী?
উত্তর: যে সেচখালে সরাসরি নদী থেকে খাল কেটে জল আনা হয় এবং শুধুমাত্র বর্ষাকালে বা নদীতে বন্যা হলে জল পাওয়া যায়, তাকে প্লাবন খাল বলে।
৩৫. গঙ্গার দুটি প্রধান শাখার নাম কী?
উত্তর: ভাগীরথী-হুগলি এবং পদ্মা।
৩৬. কাবেরী নদীর জলবন্টন নিয়ে কোন দুটি রাজ্যের মধ্যে বিবাদ রয়েছে?
উত্তর: কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু।
৩৭. বৃষ্টির জল সংরক্ষণে তামিলনাড়ু রাজ্যের সাফল্যর কারণ কী?
উত্তর: এখানে প্রতিটি বাড়িতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
৩৮. ভারতের কোন নদীর জল সর্বাধিক দূষিত?
উত্তর: যমুনা।
৩৯. সেচের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি কোন ঋতুতে?
উত্তর: শুষ্ক শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে।
৪০. ভারতের কোন নদী উপত্যকাকে ‘দক্ষিণ ভারতের শস্যভান্ডার’ বলে?
উত্তর: কাবেরী নদী উপত্যকাকে।
৪১. ‘National Water Grid’ কী?
উত্তর: ভারতের বন্যাপ্রবণ নদীগুলিকে খরাপ্রবণ নদীগুলির সঙ্গে খাল দ্বারা যুক্ত করার একটি বৃহৎ পরিকল্পনা।
৪২. ভারতের কোন রাজ্যে সর্বাধিক ভৌমজল উত্তোলন করা হয়?
উত্তর: উত্তরপ্রদেশ।
৪৩. ‘Ganga Action Plan’ (GAP) কবে শুরু হয়?
উত্তর: ১৯৮৬ সালে।
৪৪. ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে কী নামে পরিচিত?
উত্তর: যমুনা।
৪৫. ভারতের কোন রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের মাত্রা সর্বাধিক?
উত্তর: পশ্চিমবঙ্গ।
৪৬. ‘সর্দার সরোবর’ প্রকল্প কোন নদীর উপর অবস্থিত?
উত্তর: নর্মদা নদীর উপর।
৪৭. বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ কোনটি?
উত্তর: মাজুলি (ব্রহ্মপুত্র নদের উপর)।
৪৮. ভারতের কোন নদীকে ‘লাল নদী’ বলা হয়?
উত্তর: ব্রহ্মপুত্র নদকে।
৪৯. দক্ষিণ ভারতের কোন নদীকে ‘পবিত্র নদী’ বলা হয়?
উত্তর: কাবেরী নদীকে।
৫০. ভারতের একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম লেখো।
উত্তর: শিবসমুদ্রম (কর্নাটক) বা শ্রীশৈলম (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৫১. কোন নদীর তীরে দিল্লি শহর অবস্থিত?
উত্তর: যমুনা নদীর তীরে।
৫২. ভারতের কোন হ্রদ উল্কাপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে?
উত্তর: মহারাষ্ট্রের লোনার হ্রদ।
৫৩. ভারতের কোন দুটি নদী মোহনায় মিলিত না হয়ে খাম্বাত উপসাগরে পড়েছে?
উত্তর: নর্মদা ও তাপ্তি।
৫৪. কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলসেচকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়?
উত্তর: প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।
৫৫. ‘তেহরি’ বাঁধ কোন দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে নির্মিত?
উত্তর: ভাগীরথী ও ভিলগঙ্গা।
৫৬. ভারতের একটি মনুষ্যসৃষ্ট হ্রদের নাম লেখো।
উত্তর: গোবিন্দ সাগর (ভাকরা-নাঙ্গাল)।
৫৭. ‘স্প্রিংকলার’ কী?
উত্তর: এটি একটি আধুনিক জলসেচ পদ্ধতি যেখানে ফোয়ারার মাধ্যমে বৃষ্টির মতো করে জমিতে জল ছড়ানো হয়।
৫৮. ভারতের কোন রাজ্যে ‘জোড়’ প্রথার মাধ্যমে জল সংরক্ষণ করা হয়?
উত্তর: রাজস্থান।
৫৯. গঙ্গার দূষণ রোধে গৃহীত একটি প্রকল্পের নাম লেখো।
উত্তর: নমামি গঙ্গে।
৬০. ‘সপ্তনদীর দেশ’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: পাঞ্জাবকে।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর দুটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: উত্তর ভারত: এখানকার নদীগুলি বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়ায় নিত্যবহা এবং এগুলি দীর্ঘ ও বৃহৎ অববাহিকাযুক্ত। দক্ষিণ ভারত: এখানকার নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় অনিত্যবহা এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও সংকীর্ণ অববাহিকাযুক্ত।
২. বহুমুখী নদী পরিকল্পনার দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: ১. বাঁধ নির্মাণ করে জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং কৃষির উন্নতি ঘটানো। ২. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে শিল্প ও গৃহস্থালির চাহিদা মেটানো।
৩. বৃষ্টির জল সংরক্ষণের গুরুত্ব কী?
উত্তর: ১. এর মাধ্যমে ভৌমজলের স্তর বৃদ্ধি পায়, যা পানীয় জলের সংকট মেটায়। ২. শুষ্ক ঋতুতে এই সঞ্চিত জল সেচ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়।
৪. ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি কেন?
উত্তর: ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদীগুলি (যেমন – নর্মদা, তাপ্তি) স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং খরস্রোতা। এরা কঠিন শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় পলির পরিমাণ খুব কম। তাই মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে বদ্বীপ গড়ে উঠতে পারেনি, পরিবর্তে খাড়ি সৃষ্টি হয়েছে।
৫. জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: ১. জল ও ভূমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা এবং ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা। ২. বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ভৌমজলের ভাণ্ডার বাড়ানো এবং শুষ্ক ঋতুতে জলের জোগান দেওয়া।
৬. দক্ষিণ ভারতে জলাশয়ের মাধ্যমে জলসেচ বেশি প্রচলিত কেন?
উত্তর: দক্ষিণ ভারতের ভূপ্রকৃতি কঠিন ও অপ্রবেশ্য শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় কূপ বা নলকূপ খনন করা কঠিন ও ব্যয়বহুল। এছাড়া এখানকার বন্ধুর ভূপ্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ছোট-বড় জলাশয় গড়ে উঠেছে। তাই এখানে জলাশয়ের মাধ্যমে জলসেচ বেশি প্রচলিত।
৭. ভারতের জলসংকটের দুটি প্রধান কারণ লেখো।
উত্তর: ১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও জলের চাহিদা বৃদ্ধি: জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প ও গৃহস্থালির কাজে জলের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়েছে। ২. জলের অপচয় ও দূষণ: কৃষিক্ষেত্রে ও গার্হস্থ্য কাজে প্রচুর জলের অপচয় হয় এবং শিল্প ও পৌর আবর্জনা জলকে দূষিত করে ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলছে।
৮. খালের মাধ্যমে জলসেচের দুটি সুবিধা ও দুটি অসুবিধা লেখো।
উত্তর: সুবিধা: ১. এর মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একসঙ্গে জলসেচ করা যায়। ২. সেচের পাশাপাশি জল পরিবহণ ও মৎস্য চাষও করা সম্ভব। অসুবিধা: ১. খাল খনন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ২. অতিরিক্ত জলসেচের ফলে অনেক সময় মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে।
৯. ‘নিত্যবহ’ ও ‘অনিত্যবহ’ নদীর মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: নিত্যবহ নদী: যে নদীতে বরফগলা ও বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় সারাবছর জল থাকে। যেমন – গঙ্গা। অনিত্যবহ নদী: যে নদী শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় শুধুমাত্র বর্ষাকালে জল থাকে, অন্য সময় শুকিয়ে যায়। যেমন – লুনি।
১০. উত্তর ভারতে কূপ ও নলকূপ খনন সহজ কেন?
উত্তর: উত্তর ভারতের সমভূমি নরম পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত, তাই এখানে সহজেই কূপ বা নলকূপ খনন করা যায়। এছাড়া এখানকার ভৌমজলের স্তর ভূপৃষ্ঠের অনেক কাছে থাকায় অল্প খরচেই জল উত্তোলন করা সম্ভব হয়।
১১. বৃষ্টির জল সংরক্ষণে তামিলনাড়ু রাজ্যের ভূমিকা লেখো।
উত্তর: তামিলনাড়ু সরকার ভারতে প্রথম বৃষ্টির জল সংরক্ষণকে বাধ্যতামূলক করেছে। এখানে প্রতিটি নতুন বাড়ি তৈরির সময় ছাদে বৃষ্টির জল ধরার ও ভূগর্ভে পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক। এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের ভৌমজলের স্তর অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জলের সংকট কমেছে।
১২. ‘করমণ্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়’ – কারণ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: করমণ্ডল উপকূলে (তামিলনাড়ু) বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয়। একবার গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরব সাগরীয় শাখার প্রভাবে। দ্বিতীয়বার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এখানে বৃষ্টিপাত ঘটায়।
১৩. বহুমুখী নদী পরিকল্পনার দুটি অসুবিধা লেখো।
উত্তর: ১. বড় বাঁধ নির্মাণের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যায়, যার ফলে অনেক মানুষকে উচ্ছেদ হতে হয় এবং বনভূমি ও কৃষিজমি নষ্ট হয়। ২. বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
১৪. ভারতের অন্তর্বাহিনী নদীগুলির বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর: ভারতের অন্তর্বাহিনী নদীগুলি (যেমন – লুনি) কোনো সাগর বা মহাসাগরে না পড়ে দেশের মধ্যেই কোনো হ্রদ বা মরুভূমিতে বিলীন হয়ে যায়। এগুলি মূলত অনিত্যবহা এবং এদের দৈর্ঘ্য খুব কম হয়।
১৫. ‘অমৃতসর’ নামকরণের কারণ কী?
উত্তর: শিখদের চতুর্থ গুরু রামদাস এখানে একটি পবিত্র সরোবর বা জলাশয় খনন করিয়েছিলেন। এই ‘অমৃত সরোবর’ থেকেই শহরটির নাম হয়েছে অমৃতসর।
১৬. উত্তর ভারতের নদীগুলি বন্যাপ্রবণ কেন?
উত্তর: উত্তর ভারতের নদীগুলি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এবং এদের অববাহিকা বিশাল। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং গ্রীষ্মকালে বরফগলা জলের কারণে নদীতে জলের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়। এছাড়া, নদীর পলি জমে নাব্যতা কমে যাওয়ায় জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে সহজেই বন্যা হয়।
১৭. ‘দক্ষিণের গঙ্গা’ ও ‘দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা’ – এই দুটি নদীর নাম লেখো।
উত্তর: দৈর্ঘ্যে বড় হওয়ায় গোদাবরী নদীকে ‘দক্ষিণের গঙ্গা’ বলা হয়। অন্যদিকে, গঙ্গার মতো পবিত্র নদী হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় কাবেরী নদীকে ‘দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা’ বলা হয়।
১৮. ফালি চাষ (Strip Cropping) ও ধাপ চাষ (Terrace Farming) কী?
উত্তর: ফালি চাষ: ঢালু জমিতে আড়াআড়িভাবে ফালি বা স্ট্রিপ তৈরি করে শস্য চাষ করা হয়, যা জলপ্রবাহকে বাধা দেয় এবং মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করে। ধাপ চাষ: পার্বত্য অঞ্চলে সিঁড়ির ধাপের মতো জমি তৈরি করে চাষ করাকে ধাপ চাষ বলে।
১৯. ‘নমামি গঙ্গে’ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: ‘নমামি গঙ্গে’ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করা এবং এর পুনরুজ্জীবন ঘটানো। এর অন্তর্গত কাজগুলি হল – নিকাশি জলের পরিশোধন, শিল্পবর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ।
২০. সেচখাল ও নদীর মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: সেচখাল: এটি মনুষ্যসৃষ্ট এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য জলসেচ। নদী: এটি প্রাকৃতিক এবং এর নিজস্ব উৎস ও মোহনা রয়েছে। খালের জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু নদীর জলপ্রবাহ প্রাকৃতিক।
২১. জল সংরক্ষণে আমাদের কর্তব্য কী?
উত্তর: জল সংরক্ষণে আমাদের কর্তব্য হল – ১. দৈনন্দিন জীবনে জলের অপচয় বন্ধ করা (যেমন – অপ্রয়োজনে ট্যাপ বন্ধ রাখা)। ২. বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং অন্যদেরও এই বিষয়ে সচেতন করা।
২২. ‘দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী কেন?
উত্তর: কারণ দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূমির ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। এই ঢাল অনুসরণ করেই গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর মতো বেশিরভাগ নদী পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।
২৩. হ্রদ ও উপহ্রদের মধ্যে পার্থক্য কী?উত্তর: হ্রদ: এটি চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত একটি স্বাভাবিক জলাশয়। উপহ্রদ (লেগুন): এটি সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত একটি লবণাক্ত জলাশয়, যা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে সমুদ্র থেকে একটি বালির বাঁধ দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। যেমন – চিল্কা।
২৪. ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হিরাকুদ কোন নদীর উপর এবং কোন রাজ্যে অবস্থিত?
উত্তর: ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হিরাকুদ মহানদীর উপর ওড়িশা রাজ্যে অবস্থিত।
২৫. ভৌমজল অতিরিক্ত উত্তোলনের দুটি কুফল লেখো।
উত্তর: ১. ভৌমজলের স্তর অনেক নীচে নেমে যায়, ফলে পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়। ২. ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইডের মতো ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ঘনত্ব বেড়ে যায়।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৩ (২৫টি)
১. ভারতে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।
উত্তর: ভারত একটি কৃষিনির্ভর দেশ এবং এখানে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম:
ক) মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তা: ভারতের বৃষ্টিপাত মূলত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল, যা অত্যন্ত খামখেয়ালি ও অনিশ্চিত। কখনও দেরিতে আসে, কখনও আগে চলে যায়, যা কৃষিকাজকে ব্যাহত করে।
খ) বৃষ্টিপাতের অসম বন্টন: ভারতের সর্বত্র সমান বৃষ্টিপাত হয় না। রাজস্থানের মতো অঞ্চলে বৃষ্টি কম হওয়ায় এবং মেঘালয়ের মতো অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি হওয়ায় জলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেচ প্রয়োজন।
গ) শুষ্ক ঋতুতে চাষাবাদ: শীত ও গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। এই সময়ে রবি ও জায়িদ শস্য চাষের জন্য জলসেচ অপরিহার্য।
ঘ) উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার: আধুনিক উচ্চ ফলনশীল (HYV) বীজ চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়, যা শুধুমাত্র বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব নয়।
২. উত্তর ভারতের নদনদীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
উত্তর: উত্তর ভারতের নদনদীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:
১. উৎস ও প্রকৃতি: এই নদীগুলির উৎস হল হিমালয়ের বরফগলা জল, তাই এগুলি সারাবছর জলপূর্ণ থাকে অর্থাৎ নিত্যবহা।
২. দৈর্ঘ্য ও অববাহিকা: এই নদীগুলি (যেমন – গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র) দীর্ঘ এবং এদের অববাহিকা অত্যন্ত সুবিশাল।
৩. বন্যাপ্রবণতা: বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং গ্রীষ্মকালে বরফগলা জলের কারণে এই নদীগুলিতে প্রায়ই বন্যা দেখা যায়।
৪. গতিপথ: পার্বত্য অঞ্চলে এগুলি খরস্রোতা এবং সমভূমিতে এদের গতি ধীর। সমভূমিতে এরা প্রশস্ত ও গভীর এবং নৌচলাচলের উপযোগী।
৩. দক্ষিণ ভারতের নদনদীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
উত্তর: দক্ষিণ ভারতের নদনদীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:
১. উৎস ও প্রকৃতি: এই নদীগুলির উৎস হল উপদ্বীপীয় মালভূমির বৃষ্টির জল, তাই এগুলি অনিত্যবহা। শুধুমাত্র বর্ষাকালে এগুলিতে জল থাকে।
২. দৈর্ঘ্য ও অববাহিকা: উত্তর ভারতের নদীর তুলনায় এগুলি কম দীর্ঘ এবং এদের অববাহিকাও ছোট ও সংকীর্ণ।
৩. গতিপথ: এগুলি কঠিন শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এদের উপত্যকা সংকীর্ণ ও গভীর এবং এরা খরস্রোতা। তাই নৌচলাচলের বিশেষ উপযোগী নয়।
৪. জলপ্রপাত: বন্ধুর ভূপ্রকৃতির উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এই নদীগুলিতে অনেক জলপ্রপাত দেখা যায়, যা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আদর্শ।
৪. ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব লেখো।
উত্তর: এটি ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, যা শতদ্রু নদীর উপর নির্মিত।
উদ্দেশ্য:
১. জলসেচের মাধ্যমে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের কৃষিজমির উন্নতি ঘটানো।
২. প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা।
৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানীয় জল সরবরাহ করা।
গুরুত্ব:
এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় সবুজ বিপ্লব সম্ভব হয়েছে এবং এই রাজ্য দুটি ভারতের ‘শস্য ভাণ্ডারে’ পরিণত হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ দিল্লি, চণ্ডীগড় সহ উত্তর ভারতের শিল্প ও কৃষিতে সহায়তা করে। এটি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৫. জল সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।
উত্তর: জল সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতিগুলি হল:
ক) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ: বাড়ি বা অফিসের ছাদে বৃষ্টির জল ধরে পাইপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে বা সরাসরি ভূগর্ভে পাঠিয়ে ভৌমজলের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা হয়।
খ) জলবিভাজিকা উন্নয়ন: একটি নির্দিষ্ট নদী অববাহিকায় ছোট ছোট বাঁধ, চেক ড্যাম, পুকুর ইত্যাদি তৈরি করে বৃষ্টির জলকে আটকে রাখা হয়। এর মাধ্যমে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ হয় এবং ভৌমজলের স্তর বাড়ে।
গ) জলের পুনর্ব্যবহার: শিল্প বা গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত জলকে পরিশোধন করে পুনরায় সেচ বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা।
ঘ) আধুনিক সেচ পদ্ধতির ব্যবহার: বিন্দু সেচ বা স্প্রিংকলার সেচের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে জলের অপচয় কমানো।
৬. কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে জলসেচের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী?
উত্তর: সুবিধা:
১. এটি একটি সহজ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা যায় এমন পদ্ধতি, যার প্রাথমিক খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
২. কৃষক নিজের প্রয়োজনমতো যেকোনো সময় জলসেচ করতে পারে।
৩. ভৌমজল খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ হওয়ায় তা জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে।
অসুবিধা:
১. অতিরিক্ত জল উত্তোলনের ফলে ভৌমজলের স্তর নীচে নেমে যায় এবং জলের সংকট দেখা দেয়।
২. এর মাধ্যমে খুব বেশি জমিতে জলসেচ করা সম্ভব নয়।
৩. ভৌমজলে আর্সেনিক বা ফ্লোরাইডের মতো ক্ষতিকারক পদার্থ থাকলে তা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।
৭. গঙ্গা নদীর গতিপথ বর্ণনা করো।
উত্তর: গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম ও প্রধান নদী। এর গতিপথকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:
১. উচ্চগতি: উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ তুষারগুহা থেকে উৎপন্ন হয়ে হরিদ্বার পর্যন্ত অংশটি হল উচ্চগতি। এখানে নদীর প্রধান কাজ ক্ষয়। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ও ভাগীরথীর মিলনের পর এটি ‘গঙ্গা’ নামে পরিচিত হয়।
২. মধ্যগতি: হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গের ধুলিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত এই অংশে নদীর প্রধান কাজ বহন। এখানে যমুনা, গোমতী, ঘাঘরা, শোন প্রভৃতি উপনদী এসে মিশেছে।
৩. নিম্নগতি: ধুলিয়ান থেকে মোহনা পর্যন্ত অংশটি হল নিম্নগতি। এখানে নদী ‘ভাগীরথী-হুগলি’ ও ‘পদ্মা’ নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই অংশে নদী সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে সুবিশাল বদ্বীপ তৈরি করেছে।
৮. ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব আলোচনা করো।
উত্তর: ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অপরিসীম, তাই ভারতকে ‘মৌসুমী জলবায়ুর দেশ’ বলা হয়:
১. ঋতু পরিবর্তন: মৌসুমী বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের উপর ভিত্তি করে ভারতে প্রধানত চারটি ঋতু (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত) সৃষ্টি হয়েছে।
২. বৃষ্টিপাতের বন্টন: ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০% হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। এই বায়ুর কারণেই ভারতের কোথাও প্রচুর বৃষ্টি হয় (মৌসিনরাম), আবার কোথাও বৃষ্টি কম হয় (বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল)।
৩. অর্থনৈতিক প্রভাব: ভারতের কৃষি সম্পূর্ণরূপে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। সময়মতো বৃষ্টি হলে ফসল ভালো হয়, আবার অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে খরা বা বন্যা হয়, যা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।
৯. ভারতের জলসংকটের কারণগুলি লেখো।
উত্তর: ভারতে জলসংকটের প্রধান কারণগুলি হল:
১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পানীয় জল, কৃষিকাজ ও শিল্পের জন্য জলের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।
২. ভৌমজলের অতিরিক্ত ব্যবহার: কৃষিক্ষেত্রে ও শহরে অপরিকল্পিতভাবে ভৌমজল উত্তোলনের ফলে জলের স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে।
৩. জলের অপচয় ও দূষণ: কৃষিক্ষেত্রে ও গৃহস্থালির কাজে প্রচুর জলের অপচয় হয়। শিল্প ও পৌর বর্জ্য নদী ও হ্রদের জলকে দূষিত করে ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলছে।
৪. মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তা: অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক অঞ্চলে খরা দেখা দেয়, যা জলের সংকটকে তীব্র করে।
১০. DVC বা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার পরিচয় দাও।
উত্তর: এটি স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, যা ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়। আমেরিকার ‘ টেনেসি ভ্যালি অথরিটি’ (TVA)-এর অনুকরণে এটি তৈরি করা হয়েছে।
উদ্দেশ্য:
১. দামোদর নদের বিধ্বংসী বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা।
২. জলসেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৩. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে শিল্পায়নে সহায়তা করা।
৪. নৌচলাচল, মৎস্য চাষ ও পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো।
অবস্থান: এই পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে দামোদর ও তার উপনদীগুলির উপর গড়ে উঠেছে। এর অধীনে তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত, কোনার প্রভৃতি বাঁধ এবং দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে।
১১. বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি কী কী?
উত্তর: বৃষ্টির জল সংরক্ষণের দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে:
ক) ছাদ-জল সংরক্ষণ (Rooftop Rainwater Harvesting): এই পদ্ধতিতে বাড়ি বা অফিসের ছাদে পড়া বৃষ্টির জলকে পাইপের মাধ্যমে নীচে নামিয়ে এনে ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে বা গর্তে জমা করা হয়। এই সঞ্চিত জল পরে ব্যবহার করা যায় অথবা সরাসরি ভূগর্ভে পাঠিয়ে ভৌমজলের স্তর বাড়ানো যায়।
খ) ভূপৃষ্ঠের জল সংরক্ষণ (Surface Runoff Harvesting): প্রবাহিত বৃষ্টির জলকে ছোট ছোট চেক ড্যাম, পুকুর, খাত বা জলাশয় তৈরি করে আটকে রাখা হয়। এই পদ্ধতিটি মূলত গ্রামীণ অঞ্চলে জলসেচ ও ভৌমজল পুনर्भরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
১২. উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন সেচ পদ্ধতির প্রচলনের কারণ কী?
উত্তর: উত্তর ভারত: এখানে কূপ ও নলকূপ এবং খালের মাধ্যমে সেচ বেশি প্রচলিত। কারণ –
১. এখানকার ভূপ্রকৃতি নরম পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় কূপ ও খাল খনন করা সহজ।
২. ভৌমজলের স্তর ভূপৃষ্ঠের কাছে অবস্থিত।
৩. হিমালয় থেকে সৃষ্ট নিত্যবহ নদীগুলি খালে সারাবছর জলের জোগান দেয়।
দক্ষিণ ভারত: এখানে জলাশয়ের মাধ্যমে সেচ বেশি প্রচলিত। কারণ –
১. এখানকার ভূপ্রকৃতি কঠিন ও অপ্রবেশ্য শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় কূপ বা খাল খনন করা কঠিন।
২. বন্ধুর ভূপ্রকৃতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ছোট-বড় জলাশয় গড়ে উঠেছে।
৩. এখানকার নদীগুলি অনিত্যবহা হওয়ায় খালে সারাবছর জল পাওয়া যায় না।
১৩. খালের মাধ্যমে জলসেচের সুবিধা ও অসুবিধা লেখো।
উত্তর: সুবিধা:
১. খালের মাধ্যমে একটি বিশাল এলাকা জুড়ে একসঙ্গে জলসেচ করা সম্ভব হয়, যা বড় আকারের কৃষিকাজের জন্য উপযোগী।
২. নিত্যবহ খালগুলি সারাবছর ধরে জলের জোগান দেয়।
৩. সেচ ছাড়াও এই খালগুলি জল পরিবহন, মৎস্য চাষ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও সাহায্য করে।
অসুবিধা:
১. খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি এবং এটি সময়সাপেক্ষ।
২. অতিরিক্ত জলসেচের ফলে অনেক সময় জমির লবণাক্ততা বেড়ে গিয়ে উর্বরতা নষ্ট হয়।
৩. খাল থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হয়ে অপচয় হয়।
১৪. সিন্ধু নদের গতিপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
উত্তর: সিন্ধু নদ ভারতের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক নদী।
উৎস: এটি তিব্বতের কৈলাস পর্বতমালার কাছে অবস্থিত সিন্ধু খাবাব বা চেমায়ুং-দুং হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
গতিপথ: উৎস থেকে এটি উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে ভারতের লাদাখে প্রবেশ করেছে। এরপর এটি গিলগিট-বালটিস্তান অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এটি করাচির কাছে আরব সাগরে পড়েছে।
উপনদী: এর প্রধান উপনদীগুলি হল – শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা (পঞ্চনদ) এবং শায়ক, গিলগিট ইত্যাদি।
১৫. ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
উত্তর: ব্রহ্মপুত্র নদ তিনটি দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একটি আন্তর্জাতিক নদী।
উৎস: এটি তিব্বতের কৈলাস পর্বতমালার কাছে অবস্থিত চেমায়ুং-দুং হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
গতিপথ: তিব্বতে এটি ‘সাংপো’ নামে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের অরুণাচল প্রদেশে ‘ডিহং’ নামে প্রবেশ করেছে। এরপর আসাম উপত্যকায় এটি ‘ব্রহ্মপুত্র’ নামে পরিচিত। সবশেষে, এটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে ‘যমুনা’ নামে পরিচিত হয় এবং পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়ে।
বৈশিষ্ট্য: এই নদের জলধারণ ক্ষমতা খুব বেশি এবং এটি প্রায়ই বন্যা ঘটায়। বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ ‘মাজুলি’ এই নদের উপরেই অবস্থিত।
১৬. উত্তর ভারতের নদীগুলি নৌপরিবহনের উপযোগী কেন?
উত্তর: উত্তর ভারতের নদীগুলি নৌপরিবহনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী কারণ:
১. এই নদীগুলি বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়ায় সারাবছর জলপূর্ণ থাকে (নিত্যবহা)।
২. সমভূমি অংশে এই নদীগুলির স্রোত ধীর এবং গভীরতা বেশি, যা বড় নৌকা ও স্টিমার চলাচলের জন্য আদর্শ।
৩. এদের অববাহিকা অত্যন্ত উর্বর ও ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় জলপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের চাহিদা বেশি।
এই কারণগুলির জন্যেই National Waterway-1 গঙ্গা নদীর উপর গড়ে উঠেছে।
১৭. ‘জল সংরক্ষণ’ বলতে কী বোঝায়? এর প্রয়োজনীয়তা কী?
উত্তর: জল সংরক্ষণ: ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য জলসম্পদের সঠিক, পরিকল্পিত ও মিতব্যয়ী ব্যবহার এবং জলের অপচয় ও দূষণ রোধ করাকে জল সংরক্ষণ বলে। এর মধ্যে বৃষ্টির জল সংগ্রহ, জলের পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।
প্রয়োজনীয়তা:
১. ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তাই পানীয় জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য জল সংরক্ষণ জরুরি।
২. ভৌমজলের স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে, যা পূরণ করার জন্য জল সংরক্ষণ প্রয়োজন।
৩. শুষ্ক ঋতুতে কৃষি ও শিল্পে জলের জোগান নিশ্চিত করতে জল সংরক্ষণ অপরিহার্য।
১৮. বহুমুখী নদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি বিস্তারিতভাবে লেখো।
উত্তর: বহুমুখী নদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি হল:
১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ: নদীতে বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল ধরে রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা।
২. জলসেচ: জলাধারের জল খালের মাধ্যমে কৃষিজমিতে পৌঁছে দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা।
৩. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন: বাঁধ থেকে জল ছেড়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।
৪. জল সরবরাহ: শিল্প ও শহরগুলিতে পানীয় ও ব্যবহার্য জল সরবরাহ করা।
৫. অন্যান্য: এছাড়া মৎস্য চাষ, নৌচলাচল, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
১৯. ভারতের প্রধান প্রধান জলবিভাজিকাগুলির নাম লেখো ও তাদের ভূমিকা লেখো।
উত্তর: ভারতের প্রধান জলবিভাজিকাগুলি হল:
১. হিমালয় পর্বতমালা: এটি ভারতের বৃহত্তম জলবিভাজিকা, যা সিন্ধু নদ प्रणालीকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ प्रणाली থেকে পৃথক করেছে।
২. আরাবল্লী পর্বত ও দিল্লি শৈলশিরা: এটি সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর অববাহিকাকে পৃথক করেছে।
৩. বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত: এটি উত্তরের গাঙ্গেয় নদীগুলিকে দক্ষিণের উপদ্বীপীয় নদীগুলি থেকে পৃথক করেছে।
৪. পশ্চিমঘাট পর্বতমালা: এটি উপদ্বীপীয় ভারতের প্রধান জলবিভাজিকা, যা পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী নদীগুলিকে পৃথক করেছে।
২০. সেচ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করো।
উত্তর: সুবিধা:
১. সেচের সাহায্যে শুষ্ক অঞ্চলেও কৃষিকাজ করা সম্ভব হয়।
২. এটি মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তার উপর নির্ভরতা কমায় এবং বছরে একাধিকবার ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে।
৩. উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহারে সেচ অপরিহার্য, যা খাদ্য উৎপাদন বাড়ায়।
অসুবিধা:
১. অতিরিক্ত জলসেচের ফলে জমির লবণাক্ততা ও ক্ষারত্ব বেড়ে গিয়ে উর্বরতা নষ্ট হয়।
২. অপরিকল্পিত সেচের ফলে প্রচুর জলের অপচয় হয়।
৩. খাল খনন বা সেচ প্রকল্প নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এর জন্য অনেক জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়।
২১. গঙ্গা দূষণের কারণ ও ফলাফল কী?
উত্তর: কারণ:
১. গঙ্গার তীরে অবস্থিত বড় বড় শহরগুলির নিকাশি নালার অপরিশোধিত জল সরাসরি গঙ্গায় মেশে।
২. কানপুর, বারাণসীর মতো শিল্প শহরগুলির কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য গঙ্গাকে দূষিত করে।
৩. কৃষিজমি থেকে ধুয়ে আসা কীটনাশক ও রাসায়নিক সার জলে মেশে।
৪. নদীতে মৃতদেহ, প্রতিমা নিরঞ্জন ও অন্যান্য কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ করা হয়।
ফলাফল:
১. গঙ্গার জল পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং জলবাহিত রোগের (কলেরা, টাইফয়েড) প্রকোপ বাড়ছে।
২. জলের অক্সিজেন কমে যাওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে, বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
২২. ভারতের উপদ্বীপীয় নদীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর: উপদ্বীপীয় নদীগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) পূর্ববাহিনী নদী: এই নদীগুলি পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং মোহনায় বদ্বীপ তৈরি করেছে। প্রধান নদীগুলি হল – মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী।
খ) পশ্চিমবাহিনী নদী: এই নদীগুলি মধ্য ভারতের উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে আরব সাগরে পড়েছে। এগুলি খরস্রোতা এবং মোহনায় বদ্বীপের পরিবর্তে খাড়ি তৈরি করেছে। প্রধান নদীগুলি হল – নর্মদা ও তাপ্তি।
২৩. খরা ও বন্যার কারণ হিসেবে ভারতের জলসম্পদের ভূমিকা কী?
উত্তর: বন্যার কারণ: উত্তর ভারতের নদীগুলি (যেমন – গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র) বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বরফগলা জলের কারণে ফুলেফেঁপে ওঠে। এছাড়া নদীখাতে পলি জমে নাব্যতা কমে যাওয়ায় জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে সহজেই বন্যা হয়।
খরার কারণ: ভারতের বৃষ্টিপাত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল, যা অত্যন্ত অনিশ্চিত। সময়মতো বৃষ্টি না হলে বা কম পরিমাণে হলে খরা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এছাড়া, অপরিকল্পিতভাবে ভৌমজল উত্তোলনের ফলে জলের স্তর নীচে নেমে গিয়েও খরা দেখা দেয়।
২৪. হ্রদ ও কয়াল-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।
উত্তর: হ্রদ: এটি স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাশয়। এটি মিষ্টি বা লবণাক্ত উভয় প্রকারের হতে পারে। যেমন – উলার হ্রদ (মিষ্টি), সম্বর হ্রদ (লবণাক্ত)।
কয়াল: এটি সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত একটি বিশেষ ধরনের উপহ্রদ বা লেগুন, যা বালির বাঁধ দ্বারা সমুদ্র থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকে। এগুলি সাধারণত লবণাক্ত হয়। কয়াল শব্দটি বিশেষভাবে কেরালার মালাবার উপকূলে ব্যবহৃত হয়। যেমন – ভেম্বানাদ কয়াল।
২৫. বৃষ্টির জল সংরক্ষণে ছাদের ব্যবহার কীভাবে করা হয়?
উত্তর: বৃষ্টির জল সংরক্ষণে ছাদের ব্যবহার একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে:
১. বাড়ির ছাদকে পরিষ্কার করে জল সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
২. ছাদের জলকে পাইপের মাধ্যমে নীচে নামিয়ে আনা হয়।
৩. প্রথম বৃষ্টির জল, যা ছাদের ময়লা পরিষ্কার করে, সেটিকে একটি ফিল্টারের মাধ্যমে ছেঁকে নেওয়া হয়।
৪. এরপর বিশুদ্ধ জলকে হয় ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে জমা করে রাখা হয়, অথবা একটি গর্ত (Percolation Pit) খুঁড়ে সরাসরি ভূগর্ভে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যা ভৌমজলের স্তরকে পুনर्भরণ করে।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৫ (১০টি)
১. উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করো।
উত্তর:
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর মধ্যে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অনেক পার্থক্য দেখা যায়:
| বৈশিষ্ট্য | উত্তর ভারতের নদনদী | দক্ষিণ ভারতের নদনদী |
|—|—|—|
| **উৎস** | হিমালয় পর্বতমালার বরফগলা জল ও বৃষ্টির জল। | উপদ্বীপীয় মালভূমির বৃষ্টির জল। |
| **প্রকৃতি** | বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়ায় এগুলি নিত্যবহা (সারাবছর জল থাকে)। | বৃষ্টির জলে পুষ্ট হওয়ায় এগুলি অনিত্যবহা (বর্ষাকাল ছাড়া জল কমে যায়)। |
| **অববাহিকা** | এদের অববাহিকা অত্যন্ত সুবিশাল ও উর্বর। | এদের অববাহিকা অপেক্ষাকৃত ছোট ও সংকীর্ণ। |
| **দৈর্ঘ্য** | নদীগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ (যেমন – গঙ্গা, সিন্ধু)। | নদীগুলি তুলনামূলকভাবে কম দীর্ঘ (যেমন – নর্মদা, কাবেরী)। |
| **গতিপথ ও উপত্যকা** | পার্বত্য অঞ্চলে এরা খরস্রোতা এবং সমভূমিতে ধীরগতির ও প্রশস্ত। এদের উপত্যকা চওড়া। | এগুলি কঠিন শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় খরস্রোতা এবং এদের উপত্যকা সংকীর্ণ ও গভীর (V-আকৃতির)। |
| **বদ্বীপ গঠন** | মোহনায় সুবিশাল বদ্বীপ (যেমন – গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ) তৈরি করেছে। | পূর্ববাহিনী নদীগুলি ছোট বদ্বীপ তৈরি করলেও, পশ্চিমবাহিনী নদীগুলি খাড়ি তৈরি করেছে। |
| **নৌপরিবহণ** | সমভূমি অংশে নৌপরিবহণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। | জলপ্রপাত ও খরস্রোতের জন্য নৌপরিবহণের অযোগ্য। |
| **বন্যা** | বর্ষাকালে ও গ্রীষ্মকালে (বরফ গলার জন্য) প্রায়ই বন্যা হয়। | শুধুমাত্র বর্ষাকালে বন্যার সম্ভাবনা থাকে। |
২. ভারতে জলসেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির বিবরণ দাও এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এদের বণ্টনের কারণ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর:
ভারতে কৃষিকাজের জন্য প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়:
ক) কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে সেচ: এটি ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় সেচ পদ্ধতি। ভূগর্ভ থেকে কূপ বা নলকূপের মাধ্যমে জল তুলে সেচ দেওয়া হয়।
খ) খালের মাধ্যমে সেচ: নদী থেকে খাল কেটে কৃষিজমিতে জল নিয়ে যাওয়া হয়। এগুলি নিত্যবহ (বাঁধ থেকে জল আসে) বা প্লাবন খাল (সরাসরি নদী থেকে) হতে পারে।
গ) জলাশয়ের মাধ্যমে সেচ: নিচু জমিতে বা ছোট নদীতে বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির জল ধরে রেখে সেই জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়।
বণ্টনের কারণ:
উত্তর ভারতে কূপ, নলকূপ ও খালের প্রাধান্য:
১. উত্তর ভারতের সমভূমি নরম পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত, তাই এখানে সহজেই কূপ, নলকূপ ও খাল খনন করা যায়।
২. ভৌমজলের স্তর ভূপৃষ্ঠের অনেক কাছে থাকায় জল উত্তোলন সহজ ও কম ব্যয়বহুল।
৩. গঙ্গা, যমুনার মতো নিত্যবহ নদীগুলি খালে সারাবছর জলের জোগান দেয়।
দক্ষিণ ভারতে জলাশয়ের প্রাধান্য:
১. দক্ষিণ ভারতের ভূপ্রকৃতি কঠিন ও অপ্রবেশ্য আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত, তাই এখানে কূপ বা খাল খনন করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ।
২. এখানকার বন্ধুর ভূপ্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ছোট-বড় গর্ত বা নিচু জায়গা রয়েছে, যেখানে বৃষ্টির জল জমে জলাশয় তৈরি হয়।
৩. এখানকার নদীগুলি অনিত্যবহা হওয়ায় খালে সারাবছর জল পাওয়া যায় না, তাই জলাশয়ে জল সঞ্চয় করে রাখা হয়।
৩. ভারতে জলসংকটের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করো।
উত্তর:
জলসংকটের কারণ:
১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ন: দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নগরায়নের ফলে পানীয় জল ও ব্যবহার্য জলের চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে, যা জলসম্পদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে।
২. ভৌমজলের অতিরিক্ত উত্তোলন: কৃষিক্ষেত্রে (বিশেষত সবুজ বিপ্লবের পর) এবং শহরগুলিতে অপরিকল্পিতভাবে ভৌমজল উত্তোলনের ফলে জলের স্তর দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে।
৩. জলদূষণ: শিল্প, কৃষি ও পৌর বর্জ্য সরাসরি নদী ও হ্রদে মেশায় জলের গুণমান নষ্ট হচ্ছে এবং তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।
৪. মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তা: ভারতের বৃষ্টিপাত খামখেয়ালি মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। অনাবৃষ্টি বা কম বৃষ্টির কারণে অনেক অঞ্চলে খরা দেখা দেয়।
৫. জলের অপচয়: কৃষিক্ষেত্রে পুরনো সেচ পদ্ধতি এবং গৃহস্থালির কাজে সচেতনতার অভাবে প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয় হয়।
প্রতিকারের উপায়:
১. জল সংরক্ষণ: বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting) এবং জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভৌমজলের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে হবে।
২. জলের পুনর্ব্যবহার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ: ব্যবহৃত জলকে পরিশোধন করে পুনরায় সেচ বা শিল্পের কাজে লাগাতে হবে। কঠোর আইনের মাধ্যমে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
৩. আধুনিক সেচ পদ্ধতির ব্যবহার: বিন্দু সেচ, স্প্রিংকলার সেচের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে জলের অপচয় কমাতে হবে।
৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধি: জলের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং জলের অপচয় বন্ধ করতে উৎসাহিত করতে হবে।
৪. ভারতের প্রধান প্রধান বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলির একটি বিবরণ দাও।
উত্তর:
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রধান কয়েকটি পরিকল্পনা হল:
ক) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (DVC): এটি স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা। আমেরিকার TVA-এর অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে দামোদর নদের উপর এটি গড়ে উঠেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচ। তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত এর প্রধান বাঁধ।
খ) ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা: এটি ভারতের বৃহত্তম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা। পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে শতদ্রু নদীর উপর ভাকরা ও নাঙ্গাল নামে দুটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। এই পরিকল্পনার ফলেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় সবুজ বিপ্লব সম্ভব হয়েছে।
গ) হিরাকুদ পরিকল্পনা: এটি ওড়িশায় মহানদীর উপর অবস্থিত। হিরাকুদ বাঁধটি ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ। এর প্রধান উদ্দেশ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন।
ঘ) নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা: এটি অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় কৃষ্ণা নদীর উপর গড়ে উঠেছে। এর মূল লক্ষ্য হল জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন।
ঙ) তেহরি বাঁধ পরিকল্পনা: উত্তরাখণ্ডে ভাগীরথী নদীর উপর নির্মিত তেহরি বাঁধ ভারতের উচ্চতম বাঁধ। এর প্রধান উদ্দেশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও পানীয় জল সরবরাহ।
৫. গঙ্গা নদীর গতিপথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? প্রতিটি ভাগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
উত্তর:
গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম ও পবিত্রতম নদী। এর গতিপথকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:
১. উচ্চগতি:
বিস্তার: উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ তুষারগুহা থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত প্রায় ২৮০ কিমি অংশ।
বৈশিষ্ট্য: এই অংশে নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল এবং প্রধান কাজ হল ক্ষয়। এখানে নদী গভীর গিরিখাত ও ক্যানিয়ন তৈরি করেছে। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ও ভাগীরথীর মিলিত প্রবাহ ‘গঙ্গা’ নামে পরিচিত হয়েছে।
২. মধ্যগতি:
বিস্তার: হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পর্যন্ত প্রায় ১৭০০ কিমি অংশ।
বৈশিষ্ট্য: এই অংশে নদী সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এর স্রোত কমে যায় এবং প্রধান কাজ হয় বহন ও সামান্য সঞ্চয়। এখানে যমুনা, গোমতী, घाघरा, গন্ডক, কোশী, শোন প্রভৃতি উপনদী এসে মিশেছে। এই অংশে নদী বড় বড় বাঁক বা মিয়েন্ডার তৈরি করেছে।
৩. নিম্নগতি:
বিস্তার: ধুলিয়ান থেকে বঙ্গোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত প্রায় ৫২০ কিমি অংশ।
বৈশিষ্ট্য: এই অংশে ভূমির ঢাল প্রায় নেই বললেই চলে, তাই নদীর স্রোত খুব ধীর এবং প্রধান কাজ হল সঞ্চয়। এখানে নদী ‘ভাগীরথী-হুগলি’ (পশ্চিমবঙ্গের শাখা) ও ‘পদ্মা’ (বাংলাদেশের প্রধান শাখা) নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই অংশে নদী সঞ্চয়কার্যের মাধ্যমে পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ (গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ) তৈরি করেছে।
৬. জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে জলসংকট মোকাবিলা করা সম্ভব? উদাহরণসহ লেখো।
উত্তর:
জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা হল একটি নির্দিষ্ট নদী অববাহিকার সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের (জল, ভূমি, উদ্ভিদ) বিজ্ঞানসম্মত ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা। এটি জলসংকট মোকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
জলসংকট মোকাবিলার পদ্ধতি:
১. জল সংরক্ষণ: এই ব্যবস্থাপনায় ছোট ছোট চেক ড্যাম, পুকুর, খাত ইত্যাদি নির্মাণ করে বৃষ্টির প্রবাহিত জলকে আটকে দেওয়া হয়। এর ফলে জল চুঁইয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ভৌমজলের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।
২. মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ: জলবিভাজিকা অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ, ধাপ চাষ, ফালি চাষ ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা হয়। এর ফলে মাটি জল ধরে রাখতে পারে এবং জলের অপচয় কমে।
৩. জলের সঠিক ব্যবহার: এই পদ্ধতিতে স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জলের সঠিক ও মিতব্যয়ী ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়। বিন্দু সেচ ও স্প্রিংকলার সেচের মতো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জলের চাহিদা কমানো হয়।
৪. শুষ্ক ঋতুতে জলের জোগান: সঞ্চিত জল শুষ্ক ঋতুতে পানীয় ও সেচের কাজে ব্যবহার করে জলের সংকট দূর করা হয়।
উদাহরণ: রাজস্থানের আরভারি নদীর অববাহিকায় ‘তরুণ ভারত সংঘ’ নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নেতৃত্বে জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি মৃত নদীকে पुनরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে। মহারাষ্ট্রের রালেগাঁও সিদ্ধি গ্রামে আন্না হাজারের নেতৃত্বে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ দেখা যায়।
৭. ভারতের জলসেচ ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।
উত্তর:
ভারতে প্রচলিত প্রধান তিনটি সেচ ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা নিচে দেওয়া হল:
| বৈশিষ্ট্য | কূপ ও নলকূপ সেচ | খাল সেচ | জলাশয় সেচ |
|—|—|—|—|
| **প্রচলন** | এটি ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি (প্রায় ৬২%)। উত্তর ভারত (উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব) ও গুজরাটে বেশি প্রচলিত। | এটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশে বেশি প্রচলিত। | এটি মূলত দক্ষিণ ভারতে (তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক) প্রচলিত। |
| **সুবিধা** | ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা যায়, খরচ কম এবং প্রয়োজনমতো জল পাওয়া যায়। | বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসেচ করা যায় এবং নৌচলাচল ও মৎস্য চাষেও সাহায্য করে। | বন্ধুর অঞ্চলে যেখানে খাল বা কূপ খনন সম্ভব নয়, সেখানে এটি কার্যকর। |
| **অসুবিধা** | অতিরিক্ত জল উত্তোলনে ভৌমজলের স্তর নীচে নেমে যায় এবং জলের সংকট দেখা দেয়। | নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি এবং অতিরিক্ত সেচে জমির লবণাক্ততা বাড়ে। | বর্ষার উপর নির্ভরশীল এবং প্রচুর পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হয়ে অপচয় হয়। |
| **উপযুক্ততা** | নরম পাললিক শিলা ও উঁচু ভৌমজলস্তরযুক্ত অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত। | নিত্যবহ নদী ও সমতল ভূমিযুক্ত অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত। | কঠিন, অপ্রবেশ্য শিলা ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত। |
৮. গঙ্গা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করো।
উত্তর:
গঙ্গা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধান ব্যবস্থাগুলি হল:
১. গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (GAP): এটি ছিল গঙ্গা দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ, যা ১৯৮৬ সালে শুরু হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শহরের নিকাশি জল এবং শিল্প বর্জ্যকে শোধন করে তবেই নদীতে ফেলার ব্যবস্থা করা। এর অধীনে বিভিন্ন শহরে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) স্থাপন করা হয়।
২. জাতীয় নদী সংরক্ষণ পরিকল্পনা (NRCP): গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের পরিধি বাড়িয়ে ১৯৯৫ সালে এই পরিকল্পনা চালু করা হয়, যার অধীনে গঙ্গা ছাড়াও অন্যান্য প্রধান নদীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
৩. জাতীয় গঙ্গা নদী অববাহিকা কর্তৃপক্ষ (NGRBA): ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল গঙ্গা নদীকে একটি ‘জাতীয় নদী’ হিসেবে ঘোষণা করে এর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
৪. নমামি গঙ্গে প্রকল্প: ২০১৪ সালে ভারত সরকার এই সমন্বিত গঙ্গা সংরক্ষণ মিশনটি চালু করে। এটি বর্তমানে গঙ্গা দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রধান প্রকল্প। এর উদ্দেশ্যগুলি হল – নিকাশি পরিকাঠামো তৈরি, নদীর ঘাটগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ, নদীর উপরিভাগ পরিষ্কার রাখা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৯. ভারতের একটি প্রধান পশ্চিমবাহিনী নদী হিসাবে নর্মদা নদীর গতিপথ ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
গতিপথ:
উৎস: নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশের মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গ (১০৫৭ মিটার) থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
প্রবাহ: উৎস থেকে এটি বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যবর্তী গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রায় ১৩১২ কিমি পথ অতিক্রম করে এটি গুজরাটের ভারুচ শহরের কাছে খাম্বাত উপসাগরে পড়েছে।
জলপ্রপাত: এর গতিপথে জব্বলপুরের কাছে ‘ধুঁয়াধার’ এবং ‘কপিলধারা’র মতো বিখ্যাত জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।
গুরুত্ব:
১. জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ: নর্মদা নদীর উপর ‘সর্দার সরোবর’ এবং ‘ইন্দিরা সাগর’-এর মতো বৃহৎ বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়েছে, যা গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসেচ করে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
২. পানীয় জল: এই নদী মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের বহু শহর ও গ্রামের প্রধান পানীয় জলের উৎস।
৩. ধর্মীয় গুরুত্ব: নর্মদা ভারতের অন্যতম পবিত্র নদী হিসেবে বিবেচিত এবং এর তীরে অনেক তীর্থক্ষেত্র রয়েছে।
৪. পর্যটন: ধুঁয়াধার জলপ্রপাত এবং সর্দার সরোবর বাঁধ (স্ট্যাচু অফ ইউনিটি) পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
১০. বৃষ্টির জল সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতিগুলি বিস্তারিতভাবে লেখো।
উত্তর:
গুরুত্ব:
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জলের অপচয় ও দূষণের কারণে ভারতে জলসংকট একটি বড় সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ:
১. এটি পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।
২. ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারকে পুনर्भরিত করে ভৌমজলের স্তর উপরে তোলে।
৩. শুষ্ক ঋতুতে কৃষিকাজে সেচের জলের জোগান দেয়।
৪. এটি মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে।
৫. শহরাঞ্চলে বৃষ্টির জল নিকাশি ব্যবস্থার উপর চাপ কমায়।
পদ্ধতি:
১. ছাদ-জল সংরক্ষণ (Rooftop Harvesting): এটি শহরাঞ্চলে জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। বাড়ির ছাদে পড়া বৃষ্টির জলকে পাইপের মাধ্যমে নীচে এনে ফিল্টার করে ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে বা সরাসরি একটি গর্তের মাধ্যমে ভূগর্ভে পাঠানো হয়।
২. ভূপৃষ্ঠের জল সংরক্ষণ: গ্রামীণ অঞ্চলে বৃষ্টির প্রবাহিত জলকে ছোট ছোট বাঁধ (চেক ড্যাম), পুকুর, খাত বা জলাশয় তৈরি করে আটকে রাখা হয়।
৩. ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি: রাজস্থানের জোহাদ, টাঁকা বা মহারাষ্ট্রের ট্যাঙ্কের মতো ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিগুলিও জল সংরক্ষণে অত্যন্ত কার্যকর। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে জলসম্পদের সঠিক ও স্থিতিশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।
ভারতের জলসম্পদ class 10 প্রশ্ন উত্তর MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 Geography ভারতের জলসম্পদ Question Answer