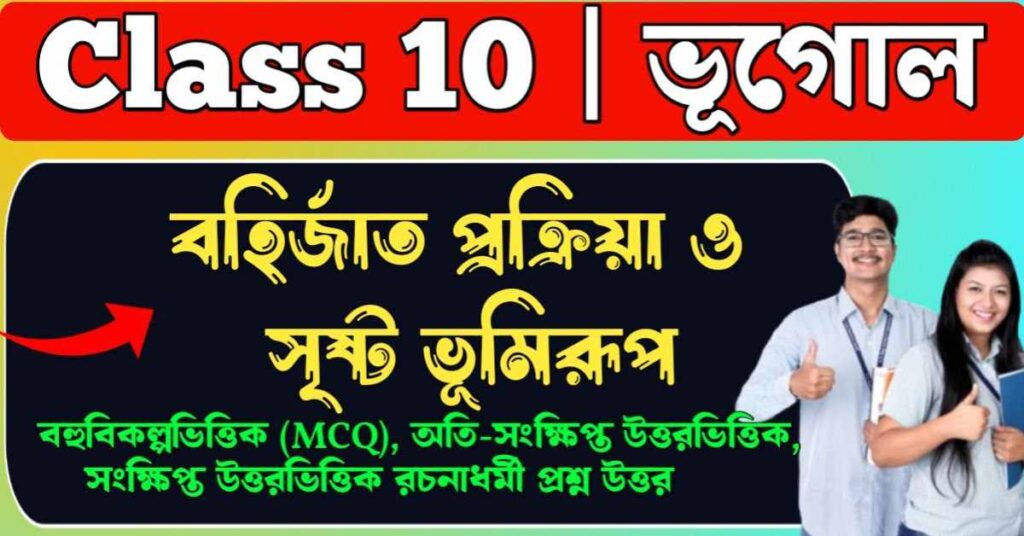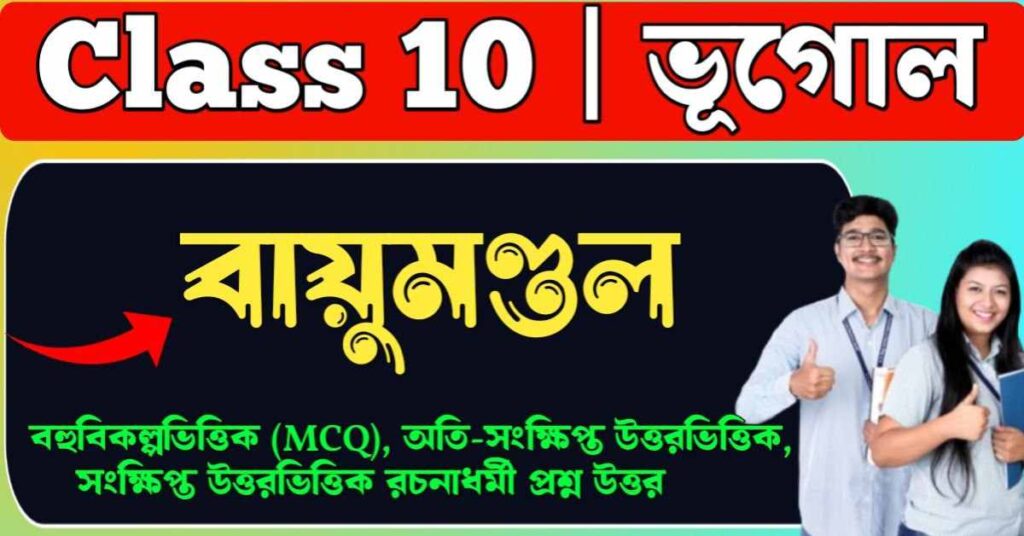ভারতের শিল্প Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. ভারতের বৃহত্তম লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র হল –
২. ভারতের ‘ম্যাঞ্চেস্টার’ বলা হয় –
৩. ভারতের ‘ডেট্রয়েট’ নামে পরিচিত –
৪. ভারতের বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকেন্দ্র হল –
৫. ভারতের প্রথম পাটকলটি স্থাপিত হয় –
৬. একটি বিশুদ্ধ কাঁচামালের উদাহরণ হল –
৭. ভারতের ‘রুর’ বলা হয় –
৮. SAIL-এর পুরো নাম হল –
৯. ভারতের বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাণ কেন্দ্রটি হল –
১০. দক্ষিণ ভারতের ‘ম্যাঞ্চেস্টার’ বলা হয় –
১১. ভারতের প্রথম সফল লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রটি হল –
১২. শিকড়-আলগা শিল্প বলা হয় –
১৩. একটি অবিশুদ্ধ কাঁচামালের উদাহরণ হল –
১৪. ভারতের ‘সিলিকন ভ্যালি’ বলা হয় –
১৫. কোন শিল্পকে ‘উদীয়মান শিল্প’ বলা হয়?
১৬. দুর্গাপুর লৌহ ইস্পাত কেন্দ্রটি যে দেশের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে, তা হল –
১৭. ভারতের বৃহত্তম পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র হল –
১৮. ভারতের একটি শুল্কমুক্ত বন্দর হল –
১৯. ভারতের প্রথম কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্রটি স্থাপিত হয় –
২০. কোন শিল্পকে ‘সকল শিল্পের মেরুদণ্ড’ বলা হয়?
২১. ভিলাই লৌহ ইস্পাত কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে যে দেশের সহযোগিতায়, তা হল –
২২. উত্তর ভারতের ‘ম্যাঞ্চেস্টার’ বলা হয় –
২৩. ভারতের বৃহত্তম সরকারি লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র হল –
২৪. আধুনিক শিল্পদানব বলা হয় –
২৫. ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র হল –
২৬. ভারতের সর্বাধিক কাপড়কল রয়েছে –
২৭. ভারতের প্রথম পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্রটি স্থাপিত হয় –
২৮. রাউরকেলা ইস্পাত কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে যে দেশের সহযোগিতায় –
২৯. যে কাঁচামালের পণ্যসূচক (Material Index) ১-এর কম, সেটি হল –
৩০. ভারতের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হল –
৩১. কোন শিল্পকে ‘শিল্পের শিল্প’ বলা হয়?
৩২. ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র হল –
৩৩. ভারতের প্রথম কাগজকলটি স্থাপিত হয় –
৩৪. একটি ওজনহ্রাসশীল কাঁচামাল হল –
৩৫. কোন শহরকে ‘ভারতের গ্লাসগো’ বলা হয়?
৩৬. দক্ষিণ ভারতের একমাত্র লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রটি হল –
৩৭. পূর্ব ভারতের বৃহত্তম পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র হল –
৩৮. ভারতের একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প হল –
৩৯. মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড হল একটি –
৪০. ভারতের কোন রাজ্যে সর্বাধিক পাটকল রয়েছে?
৪১. ‘TISCO’ প্রতিষ্ঠিত হয় –
৪২. ভারতের বৃহত্তম বিমানপোত নির্মাণ কেন্দ্রটি হল –
৪৩. কোন শিল্পে ন্যাপথা একটি প্রধান কাঁচামাল?
৪৪. ভারতের রেলওয়াগন নির্মাণ কেন্দ্রটি হল –
৪৫. একটি বনজভিত্তিক শিল্প হল –
৪৬. ভারতের বৃহত্তম Software Park কোথায় অবস্থিত?
৪৭. সালেম ইস্পাত কেন্দ্রটি বিখ্যাত –
৪৮. ভারতের কোন রাজ্যে কার্পাস বয়ন শিল্পের সর্বাধিক কেন্দ্রীভবন ঘটেছে?
৪৯. কোন শহরকে ‘ভারতের টেক্সটাইল সিটি’ বলা হয়?
৫০. ভারতের একটি খনিজভিত্তিক শিল্প হল –
৫১. দুর্গাপুর ইস্পাত কেন্দ্রটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৫২. তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মূল উপাদান হল –
৫৩. ভারতের বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থা হল –
৫৪. কোন শিল্পকে ‘Sunrise Industry’ বলা হয়?
৫৫. বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কেন্দ্রটি হল ভারতের একমাত্র –
৫৬. কোন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল ব্যাগাসি?
৫৭. হলদিয়া বিখ্যাত –
৫৮. ভারতের একটি সংযোজন-ভিত্তিক শিল্প হল –
৫৯. ‘আইসোপেন’ কী?
৬০. ভারতের কোন শিল্পাঞ্চলকে ‘ভারতের খনিজ ভাণ্ডার’ বলা হয়?
৬১. কোন রাজ্যে সর্বাধিক চিনিকল রয়েছে?
৬২. ভারতের প্রথম আধুনিক কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র কোথায় গড়ে ওঠে?
৬৩. পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র হল –
৬৪. একটি অস্থানু শিল্পের উদাহরণ হল –
৬৫. ‘ISCO’-এর পুরো নাম কী?
৬৬. ভারতের কোন শহরে ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস অবস্থিত?
৬৭. একটি হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উদাহরণ হল –
৬৮. ওয়েবারের শিল্প স্থানিকতার তত্ত্বে কোন বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
৬৯. ভারতের বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন কেন্দ্রটি হল –
৭০. ভারতের কোন শিল্পাঞ্চলকে ‘ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী’ বলা হয়?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. ভারতের ‘রুর’ কাকে বলে?
উত্তর: দুর্গাপুরকে।
২. একটি বিশুদ্ধ কাঁচামালের উদাহরণ দাও।
উত্তর: তুলা বা কার্পাস।
৩. ভারতের ‘সিলিকন ভ্যালি’ কোন শহরকে বলা হয়?
উত্তর: বেঙ্গালুরুকে।
৪. SAIL-এর পুরো নাম কী?
উত্তর: Steel Authority of India Limited.
৫. শিকড়-আলগা শিল্প কাকে বলে?
উত্তর: যে শিল্পের কাঁচামাল বিশুদ্ধ প্রকৃতির হওয়ায় শিল্পকেন্দ্রটি কাঁচামালের উৎস বা বাজারের কাছাকাছি যেকোনো স্থানে গড়ে উঠতে পারে, তাকে শিকড়-আলগা শিল্প বলে। যেমন – কার্পাস বয়ন শিল্প।
৬. ভারতের প্রথম পাটকল কোথায় স্থাপিত হয়?
উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায়।
৭. ভারতের বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র কোনটি?
উত্তর: হরিয়ানার গুরগাঁও।
৮. একটি অবিশুদ্ধ কাঁচামালের উদাহরণ দাও।
উত্তর: আকরিক লোহা বা আঁখ।
৯. ভারতের ‘ম্যাঞ্চেস্টার’ কোন শহরকে বলা হয়?
উত্তর: আহমেদাবাদকে।
১০. TISCO-র পুরো নাম কী?
উত্তর: Tata Iron and Steel Company.
১১. কোন শিল্পকে ‘উদীয়মান শিল্প’ বলা হয়?
উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পকে।
১২. ভারতের ‘ডেট্রয়েট’ কাকে বলে?
উত্তর: চেন্নাইকে।
১৩. একটি কৃষিভিত্তিক শিল্পের নাম লেখো।
উত্তর: চিনি শিল্প বা পাট শিল্প।
১৪. ভারতের বৃহত্তম পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র কোনটি?
উত্তর: গুজরাটের জামনগর।
১৫. কোন শিল্পকে ‘সকল শিল্পের মেরুদণ্ড’ বলা হয়?
উত্তর: লৌহ ইস্পাত শিল্পকে।
১৬. দক্ষিণ ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার কাকে বলে?
উত্তর: কোয়েম্বাটুরকে।
১৭. পণ্যসূচক (Material Index) কী?
উত্তর: কাঁচামালের ওজন ও উৎপাদিত পণ্যের ওজনের অনুপাতকে পণ্যসূচক বলে।
১৮. ভারতের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্রের নাম লেখো।
উত্তর: চিত্তরঞ্জন (রেল ইঞ্জিন) বা বেঙ্গালুরু (বিমান)।
১৯. একটি বনজভিত্তিক শিল্পের নাম লেখো।
উত্তর: কাগজ শিল্প বা দেশলাই শিল্প।
২০. ভারতের প্রথম কার্পাস বয়ন মিল কোথায় গড়ে ওঠে?
উত্তর: হাওড়ার ঘুসুড়িতে।
২১. বিশুদ্ধ কাঁচামালের পণ্যসূচক কত?
উত্তর: ১ বা ১-এর কম।
২২. ভারতের বৃহত্তম লৌহ ইস্পাত কারখানা কোনটি?
উত্তর: ভিলাই (উৎপাদনের দিক থেকে)।
২৩. কোন শিল্পকে ‘আধুনিক শিল্পদানব’ বলা হয়?
উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পকে।
২৪. ভারতের একটি তথ্যপ্রযুক্তি পার্কের নাম লেখো।
উত্তর: বেঙ্গালুরুর ইলেকট্রনিক সিটি বা কলকাতার সল্টলেক সেক্টর ফাইভ।
২৫. আউটসোর্সিং কী?
উত্তর: কোনো সংস্থা যখন তার নিজের কাজ বাইরের অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে করিয়ে নেয়, তখন তাকে আউটসোর্সিং বলে।
২৬. ভারতের একটি উপকূলভিত্তিক লৌহ ইস্পাত কেন্দ্রের নাম লেখো।
উত্তর: বিশাখাপত্তনম।
২৭. কোন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল ন্যাপথা?
উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পের।
২৮. দুর্গাপুরকে ‘ভারতের রুর’ বলা হয় কেন?
উত্তর: জার্মানির রুর শিল্পাঞ্চলের মতো দুর্গাপুরও কয়লাখনি অঞ্চলের কাছে অবস্থিত একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র হওয়ায় একে ভারতের রুর বলা হয়।
২৯. ভারতের প্রথম সফল কাগজকল কোনটি?
উত্তর: বালিতে অবস্থিত বালি পেপার মিল।
৩০. কোন শিল্পকে ‘Sunrise Industry’ বলা হয়?
উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্প বা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প।
৩১. ভারতের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোনটি?
উত্তর: বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড।
৩২. ভারতের একটি সংকর ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রের নাম লেখো।
উত্তর: সালেম বা দুর্গাপুর।
৩৩. BPO-এর পুরো নাম কী?
উত্তর: Business Process Outsourcing.
৩৪. হোসিয়ারি শিল্পে ভারতের কোন শহর প্রথম?
উত্তর: লুধিয়ানা।
৩৫. কোন শিল্পকে ‘অনুসারী শিল্প’ বলা হয়?
উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পকে।
৩৬. ভারতের রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে।
৩৭. একটি স্থানু শিল্পের উদাহরণ দাও।
উত্তর: লৌহ ইস্পাত শিল্প বা চিনি শিল্প।
৩৮. একটি প্রাণিজভিত্তিক শিল্পের নাম লেখো।
উত্তর: দুগ্ধ শিল্প বা পশম শিল্প।
৩৯. কোন শিল্পের বর্জ্য পদার্থ ব্যাগাসি?
উত্তর: চিনি শিল্পের।
৪০. ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানপোত নির্মাণ কেন্দ্র কোনটি?
উত্তর: বেঙ্গালুরু (HAL)।
৪১. ভারতের বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট কারখানা কোনটি?
উত্তর: মধ্যপ্রদেশের নেপানগর।
৪২. একটি অস্থানু শিল্পের উদাহরণ দাও।
উত্তর: কার্পাস বয়ন শিল্প।
৪৩. কোন শিল্পকে ‘শিল্পের শিল্প’ বলা হয়?
উত্তর: ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে।
৪৪. ভারতের বৃহত্তম সরকারি ইস্পাত কারখানা কোনটি?
উত্তর: বোকারো।
৪৫. ভারতের কোন রাজ্যে সর্বাধিক মোটরগাড়ি নির্মিত হয়?
উত্তর: হরিয়ানা।
৪৬. কাঁচামালের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে শিল্পকে কটি ভাগে ভাগ করা হয়?
উত্তর: প্রধানত তিনটি – কৃষিভিত্তিক, খনিজভিত্তিক ও বনজভিত্তিক।
৪৭. তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মূল উপাদান কী?
উত্তর: মানব সম্পদ বা মেধা।
৪৮. ভারতের কোন রাজ্যে সর্বাধিক চিনি কল আছে?
উত্তর: মহারাষ্ট্র।
৪৯. ভারতের ‘টেক্সটাইল সিটি’ কাকে বলে?
উত্তর: আহমেদাবাদকে।
৫০. আইসোটীম কী?
উত্তর: শিল্প স্থানিকতার তত্ত্বে, সমান পরিবহন ব্যয়যুক্ত স্থানগুলিকে যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়, তাকে আইসোটীম বলে।
৫১. একটি সংযোজন ভিত্তিক শিল্পের উদাহরণ দাও।
উত্তর: মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প।
৫২. HAL-এর পুরো নাম কী?
উত্তর: Hindustan Aeronautics Limited.
৫৩. ভারতের কোন শিল্পাঞ্চলকে ‘ভারতের খনিজ ভাণ্ডার’ বলা হয়?
উত্তর: ছোটনাগপুর শিল্পাঞ্চলকে।
৫৪. ভারতের কোন শহরকে ‘ইস্পাত নগরী’ বলা হয়?
উত্তর: জামশেদপুরকে।
৫৫. একটি ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উদাহরণ দাও।
উত্তর: জাহাজ নির্মাণ শিল্প।
৫৬. কোন নদীর তীরে অধিকাংশ পাটকল গড়ে উঠেছে?
উত্তর: হুগলি নদীর তীরে।
৫৭. ভারতের দুটি প্রধান কার্পাস বয়ন কেন্দ্রের নাম লেখো।
উত্তর: আহমেদাবাদ ও মুম্বাই।
৫৮. কোন শিল্পে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পে।
৫৯. ভারতের কোন রাজ্যে কাগজকলের সংখ্যা সর্বাধিক?
উত্তর: মহারাষ্ট্র।
৬০. ভারতের কোন রাজ্যকে ‘সিলিকন রাজ্য’ বলা হয়?উত্তর: কর্ণাটককে।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ কাঁচামালের পার্থক্য কী?
উত্তর: বিশুদ্ধ কাঁচামাল: যে কাঁচামালের ওজন এবং তা থেকে উৎপাদিত পণ্যের ওজন প্রায় সমান হয়। যেমন – তুলা। অবিশুদ্ধ কাঁচামাল: যে কাঁচামালের ওজন উৎপাদিত পণ্যের ওজনের চেয়ে বেশি হয়, অর্থাৎ উৎপাদনে ওজন হ্রাস পায়। যেমন – আকরিক লোহা, আঁখ।
২. শিকড়-আলগা শিল্প বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে শিল্পের কাঁচামাল বিশুদ্ধ প্রকৃতির (পণ্যসূচক ১ বা তার কম) হওয়ায় শিল্পকেন্দ্রটি কাঁচামালের উৎস, বাজার বা অন্য যেকোনো স্থানে গড়ে উঠতে পারে এবং পরিবহন ব্যয় তেমন প্রভাব ফেলে না, তাকে শিকড়-আলগা শিল্প বলে।
উদাহরণ: কার্পাস বয়ন শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প।
৩. অনুসারী শিল্প কী?
উত্তর: কোনো একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত দ্রব্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে যখন তার চারপাশে আরও অনেক ছোট ছোট শিল্প গড়ে ওঠে, তখন সেই শিল্পগুলিকে অনুসারী শিল্প বলে। যেমন – পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্রকে ভিত্তি করে প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু, ডিটারজেন্ট শিল্প গড়ে ওঠে।
৪. ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
উত্তর: ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প: যেখানে ভারী যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। যেমন – রেল ইঞ্জিন, জাহাজ, খনন যন্ত্রপাতি নির্মাণ।
খ) হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প: যেখানে হালকা ও ছোট যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। যেমন – বৈদ্যুতিক পাখা, সেলাই মেশিন, সাইকেল নির্মাণ।
৫. ভারতের ‘রুর’ ও ‘ম্যাঞ্চেস্টার’ কাকে এবং কেন বলা হয়?
উত্তর: ভারতের রুর: দুর্গাপুরকে বলা হয়। কারণ জার্মানির রুর শিল্পাঞ্চলের মতো দুর্গাপুরও কয়লাখনি অঞ্চলের কাছে অবস্থিত একটি বৃহৎ লৌহ ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্র।
ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার: আহমেদাবাদকে বলা হয়। কারণ ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের মতো আহমেদাবাদও কার্পাস বয়ন শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র।
৬. পণ্যসূচক (Material Index) কী? এর গুরুত্ব কী?
উত্তর: কোনো শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওজন এবং উৎপাদিত পণ্যের ওজনের অনুপাতকে পণ্যসূচক বলে।
গুরুত্ব: পণ্যসূচকের মান ১-এর বেশি হলে শিল্পটি কাঁচামালের উৎসের কাছে এবং ১ বা তার কম হলে বাজারের কাছে গড়ে ওঠে। এটি শিল্পের স্থানিকতা নির্ধারণে সাহায্য করে।
৭. পেট্রোরসায়ন শিল্পকে ‘উদীয়মান শিল্প’ বলা হয় কেন?উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এই শিল্প থেকে উৎপাদিত দ্রব্য (যেমন – প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু, পলিমার) বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এবং অন্যান্য অনেক শিল্পের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও গুরুত্বের কারণেই একে ‘উদীয়মান শিল্প’ বা ‘Sunrise Industry’ বলা হয়।
৮. ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের দুটি গুরুত্ব লেখো।
উত্তর: ১. এই শিল্প প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। ২. এটি বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
৯. সংযোজন-ভিত্তিক শিল্প কী? উদাহরণ দাও।উত্তর: যে শিল্পে বিভিন্ন স্থান থেকে আনা নানা ধরনের যন্ত্রাংশকে একত্রিত বা সংযোজন করে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্রব্য তৈরি করা হয়, তাকে সংযোজন-ভিত্তিক শিল্প বলে।
উদাহরণ: মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প, কম্পিউটার নির্মাণ শিল্প।
১০. দুর্গাপুর ইস্পাত কেন্দ্র গড়ে ওঠার দুটি কারণ লেখো।উত্তর: ১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা এবং সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের আকরিক লোহা সহজে পাওয়া যায়। ২. পরিকাঠামো: দামোদর নদ থেকে জল এবং দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এছাড়া উন্নত সড়ক ও রেলপথের সুবিধা রয়েছে।
১১. কৃষিভিত্তিক ও খনিজভিত্তিক শিল্পের দুটি পার্থক্য লেখো।উত্তর: কৃষিভিত্তিক শিল্প: এর প্রধান কাঁচামাল আসে কৃষি থেকে। যেমন – চিনি শিল্প, পাট শিল্প। খনিজভিত্তিক শিল্প: এর প্রধান কাঁচামাল খনি থেকে পাওয়া যায়। যেমন – লৌহ ইস্পাত শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প। কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল পচনশীল হতে পারে, কিন্তু খনিজভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল সাধারণত পচনশীল নয়।
১২. ভারতের পাট শিল্পের দুটি প্রধান সমস্যা কী?
উত্তর: ১. কাঁচামালের অভাব: দেশভাগের ফলে বেশিরভাগ উন্নত মানের পাট উৎপাদক অঞ্চল বাংলাদেশে চলে গেছে। ২. বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার: প্লাস্টিক ও পলিথিনের মতো সস্তা বিকল্প দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাট শিল্প পিছিয়ে পড়ছে।
১৩. ভারতে মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পে উন্নতির দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: ১. দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে এবং গাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২. বিদেশি সংস্থাগুলির বিনিয়োগ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে।
১৪. ‘আধুনিক শিল্পদানব’ ও ‘সকল শিল্পের মেরুদণ্ড’ – কোন শিল্পকে এবং কেন বলা হয়?উত্তর: আধুনিক শিল্পদানব: পেট্রোরসায়ন শিল্পকে বলা হয়, কারণ এই শিল্প থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য আধুনিক জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সকল শিল্পের মেরুদণ্ড: লৌহ ইস্পাত শিল্পকে বলা হয়, কারণ অন্যান্য সমস্ত শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামো এই শিল্প থেকেই আসে।
১৫. আউটসোর্সিং ও অফশোরিং-এর পার্থক্য কী?
উত্তর: আউটসোর্সিং: কোনো সংস্থা যখন তার কাজ বাইরের অন্য কোনো সংস্থাকে দিয়ে করায়, তা দেশের ভেতরে বা বাইরে হতে পারে। অফশোরিং: যখন কোনো সংস্থা তার কাজ বা উৎপাদন কেন্দ্র অন্য কোনো দেশে স্থানান্তর করে, তাকে অফশোরিং বলে।
১৬. আহমেদাবাদে কার্পাস বয়ন শিল্প গড়ে ওঠার দুটি কারণ লেখো।উত্তর: ১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: নিকটবর্তী কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল থেকে সহজেই উন্নত মানের তুলা পাওয়া যায়। ২. অনুকূল জলবায়ু: এখানকার আর্দ্র জলবায়ু সুতো ছেঁড়ার সমস্যা কমায়।
১৭. ‘তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প’ বলতে কী বোঝায়?উত্তর: যে শিল্পে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান করা হয়, তাকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বা IT (Information Technology) শিল্প বলে।
১৮. ভারী ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পার্থক্য কী?
উত্তর: ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প: এই শিল্পে বড় ও ভারী যন্ত্রপাতি (যেমন – রেল ইঞ্জিন, জাহাজ) তৈরি হয় এবং এর জন্য প্রচুর কাঁচামাল ও মূলধন প্রয়োজন। হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প: এই শিল্পে ছোট ও হালকা যন্ত্রপাতি (যেমন – পাখা, সেলাই মেশিন) তৈরি হয় এবং এতে কম কাঁচামাল ও মূলধন লাগে।
১৯. কেন পেট্রোরসায়ন শিল্পকে ‘Sunrise Industry’ বলা হয়?উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও গুরুত্বের কারণে একে ‘Sunrise Industry’ বা ‘উদীয়মান শিল্প’ বলা হয়। এই শিল্প থেকে উৎপাদিত দ্রব্য আধুনিক জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
২০. ভারতের দুটি প্রধান শিল্পাঞ্চলের নাম লেখো।
উত্তর: ভারতের দুটি প্রধান শিল্পাঞ্চল হল:
১. মুম্বাই-পুনে শিল্পাঞ্চল (পশ্চিম ভারত)।
২. হুগলি শিল্পাঞ্চল (পূর্ব ভারত)।
২১. বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে শিল্পের অবস্থান কীভাবে নির্ধারিত হয়?উত্তর: বিশুদ্ধ কাঁচামাল: এর পণ্যসূচক ১ বা তার কম হওয়ায় পরিবহন ব্যয় তেমন প্রভাব ফেলে না। তাই এই শিল্প কাঁচামাল উৎস, বাজার বা যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে গড়ে উঠতে পারে (শিকড়-আলগা শিল্প)। অবিশুদ্ধ কাঁচামাল: এর পণ্যসূচক ১-এর বেশি হওয়ায় পরিবহন ব্যয় কমাতে শিল্পটি কাঁচামালের উৎসের কাছে গড়ে ওঠে।
২২. কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামালগুলি কী কী?
উত্তর: কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামালগুলি হল – সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম কাঠ, বাঁশ, সাবাই ঘাস, আখের ছিবড়ে (ব্যাগাসি) এবং পুরোনো কাগজ।
২৩. ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামালগুলি কী কী?উত্তর: ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামালগুলি হল – আকরিক লোহা, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট এবং চুনাপাথর।
২৪. বেঙ্গালুরুকে ‘ভারতের সিলিকন ভ্যালি’ বলা হয় কেন?
উত্তর: আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালির মতো বেঙ্গালুরুও ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এখানে অসংখ্য দেশি-বিদেশি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, দক্ষ মানব সম্পদ এবং উন্নত পরিকাঠামো রয়েছে। এই কারণেই বেঙ্গালুরুকে ‘ভারতের সিলিকন ভ্যালি’ বলা হয়।
২৫. ‘শিল্পের অবস্থান’ বলতে কী বোঝায়?উত্তর: কোনো শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য যে স্থানে কাঁচামাল, পরিবহন, বাজার, শ্রমিক, মূলধন ইত্যাদি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সবচেয়ে কম খরচে পাওয়া যায়, সেই আদর্শ স্থানটিকে নির্বাচন করাকে ‘শিল্পের অবস্থান’ বা ‘Location of Industry’ বলে।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৩ (২৫টি)
১. পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি আলোচনা করো।
উত্তর: ভারতের পশ্চিম অংশে, বিশেষত মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে, কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের প্রধান কারণগুলি হল:
ক) কাঁচামালের সহজলভ্যতা: এই অঞ্চলের কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুর মাটি তুলা চাষের জন্য আদর্শ। তাই শিল্পকেন্দ্রগুলি সহজেই স্থানীয়ভাবে উন্নত মানের তুলা পায়।
খ) আর্দ্র জলবায়ু: সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার আর্দ্র জলবায়ু সুতো ছেঁড়ার সমস্যা কমায়, যা বয়ন শিল্পের জন্য উপযোগী।
গ) উন্নত পরিবহন ও বন্দর: মুম্বাই ও কান্ডালার মতো বড় বন্দর এবং উন্নত সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে কাঁচামাল আনা ও উৎপাদিত দ্রব্য পাঠানো সহজ।
ঘ) মূলধন ও বাজার: এই অঞ্চলটি ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হওয়ায় এখানে মূলধনের কোনো অভাব নেই এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাও প্রচুর।
২. পূর্ব ও মধ্য ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের একদেশীভবনের কারণগুলি কী কী?
উত্তর: ভারতের বেশিরভাগ লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র পূর্ব ও মধ্য ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এর কারণগুলি হল:
১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: এই অঞ্চলে লৌহ ইস্পাত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল – আকরিক লোহা (সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ), কয়লা (রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো), ম্যাঙ্গানিজ ও ডলোমাইট কাছাকাছি পাওয়া যায়।
২. জলের প্রাচুর্য: দামোদর, সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী নদীর মতো নদীগুলি থেকে শিল্পে প্রয়োজনীয় জল সহজেই পাওয়া যায়।
৩. শক্তির উৎস: কয়লাখনি অঞ্চলের কাছে হওয়ায় তাপবিদ্যুৎ এবং দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (DVC) থেকে জলবিদ্যুৎ সহজে পাওয়া যায়।
৪. সুলভ শ্রমিক ও উন্নত পরিবহন: এই অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায় এবং উন্নত সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধাজনক।
৩. ভারতের পাট শিল্পের সমস্যা ও তার সমাধান আলোচনা করো।
উত্তর: সমস্যা:
১. কাঁচামালের অভাব: দেশভাগের ফলে বেশিরভাগ উন্নত মানের পাট উৎপাদক অঞ্চল বাংলাদেশে চলে যাওয়ায় ভারতে কাঁচামালের সংকট দেখা দিয়েছে।
২. বিকল্প দ্রব্যের প্রতিযোগিতা: প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বাড়ায় পাটের তৈরি দ্রব্যের চাহিদা কমে গেছে।
৩. পুরানো যন্ত্রপাতি: ভারতের বেশিরভাগ পাটকলের যন্ত্রপাতি পুরানো, যা উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।
৪. শ্রমিক সমস্যা: শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট প্রায়শই উৎপাদন ব্যাহত করে।
সমাধান:
১. উন্নত মানের পাট চাষে উৎসাহ দেওয়া।
২. পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সরকারি নীতি গ্রহণ ও প্রচার চালানো।
৩. পাটকলগুলির আধুনিকীকরণ করা।
৪. ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নতির কারণগুলি কী কী?
উত্তর: সাম্প্রতিককালে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের দ্রুত উন্নতির কারণগুলি হল:
ক) দক্ষ মানব সম্পদ: ভারতে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মেধাবী যুবক-যুবতী রয়েছে, যা এই শিল্পের প্রধান চালিকাশক্তি।
খ) সরকারি নীতি: ভারত সরকার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (STP) স্থাপন, কর ছাড় এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই শিল্পের প্রসারে সহায়তা করেছে।
গ) কম উৎপাদন ব্যয়: উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক কম হওয়ায় আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অনেক বিদেশি সংস্থা ভারতে তাদের কাজ পাঠাচ্ছে।
ঘ) উন্নত পরিকাঠামো: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট এই শিল্পের বিকাশে সাহায্য করেছে।
৫. ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটির উদাহরণসহ পরিচয় দাও।
উত্তর: ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প:
সংজ্ঞা: যে শিল্পে বড় ও ভারী যন্ত্রপাতি তৈরি হয় এবং প্রচুর কাঁচামাল ও মূলধন প্রয়োজন হয়, তাকে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলে।
উদাহরণ:
১. রেল ইঞ্জিন নির্মাণ: পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জন।
২. জাহাজ নির্মাণ: বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড।
৩. মোটরগাড়ি নির্মাণ: হরিয়ানার গুরগাঁও।
খ) হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প:
সংজ্ঞা: যে শিল্পে অপেক্ষাকৃত ছোট ও হালকা যন্ত্রপাতি তৈরি হয় এবং কম কাঁচামাল ও মূলধন লাগে, তাকে হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলে।
উদাহরণ:
১. বৈদ্যুতিক পাখা নির্মাণ: কলকাতা।
২. সেলাই মেশিন নির্মাণ: কলকাতা, লুধিয়ানা।
৩. সাইকেল নির্মাণ: লুধিয়ানা, সোনিপত।
৬. হুগলি নদীর তীরে পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি লেখো।
উত্তর: হুগলি নদীর উভয় তীরে পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি হল:
১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: পশ্চিমবঙ্গ ভারতের প্রধান পাট উৎপাদক রাজ্য হওয়ায় সহজেই কাঁচামাল পাওয়া যায়।
২. জলের প্রাচুর্য: পাট পচানোর (জাগ দেওয়া) জন্য এবং শিল্পে ব্যবহারের জন্য হুগলি নদী থেকে প্রচুর জল পাওয়া যায়।
৩. সুলভ শ্রমিক: পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি (বিহার, ওড়িশা) থেকে প্রচুর সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায়।
৪. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে কাঁচাপাট আমদানি ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির সুবিধা রয়েছে। এছাড়া সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমেও পরিবহন সুবিধাজনক।
৫. শক্তির উৎস ও মূলধন: নিকটবর্তী রানীগঞ্জ থেকে কয়লা এবং কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মূলধনের জোগান পাওয়া যায়।
৭. ভারতের অর্থনীতিতে মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর: ভারতের অর্থনীতিতে মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম:
১. কর্মসংস্থান: এই শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।
২. অনুসারী শিল্পের বিকাশ: এই শিল্পকে কেন্দ্র করে টায়ার, কাচ, ব্যাটারি, ইস্পাত, প্লাস্টিকের মতো অনেক অনুসারী শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।
৩. জিডিপিতে অবদান: মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনে (GDP) একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
৪. রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: ভারত থেকে উৎপাদিত গাড়ি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।
৫. পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি: এই শিল্পের উন্নতির ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নত ও গতিশীল হয়েছে।
৮. শিল্প স্থাপনে কাঁচামালের ভূমিকা উদাহরণসহ আলোচনা করো।
উত্তর: শিল্প স্থাপনে কাঁচামালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাঁচামালের प्रकृति শিল্পের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে।
ক) অবিশুদ্ধ বা ওজনহ্রাসশীল কাঁচামাল: যে কাঁচামালের ওজন উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে বেশি হয় (যেমন – আকরিক লোহা, আঁখ), সেই শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যয় কমানোর জন্য শিল্পকেন্দ্রটি কাঁচামালের উৎসের কাছে গড়ে ওঠে। যেমন – বেশিরভাগ লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র কয়লা ও আকরিক লোহার খনির কাছে অবস্থিত।
খ) বিশুদ্ধ কাঁচামাল: যে কাঁচামালের ওজন এবং উৎপাদিত পণ্যের ওজন প্রায় সমান থাকে (যেমন – তুলা, পাট), সেই শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পকেন্দ্রটি কাঁচামালের উৎস, বাজার বা যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে গড়ে উঠতে পারে। যেমন – কার্পাস বয়ন শিল্প।
সুতরাং, কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও প্রকৃতি শিল্পের অবস্থান নির্ধারণের একটি প্রধান নিয়ামক।
৯. পেট্রোরসায়ন শিল্পের গুরুত্ব কী?
উত্তর: পেট্রোরসায়ন শিল্পকে ‘আধুনিক শিল্পদানব’ ও ‘উদীয়মান শিল্প’ বলা হয়। এর গুরুত্ব হল:
১. বৈচিত্র্যময় উৎপাদন: এই শিল্প থেকে প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু (নাইলন, পলিয়েস্টার), কৃত্রিম রাবার, ডিটারজেন্ট, কীটনাশক, রং, সার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদিত হয়, যা আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।
২. অনুসারী শিল্পের বিকাশ: এই শিল্পকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোট-বড় অনুসারী শিল্পের বিকাশ ঘটে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
৩. কৃষিতে সহায়তা: এই শিল্প থেকে উৎপাদিত সার ও কীটনাশক কৃষিজ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
৪. বিকল্পের জোগান: এটি কাঠ, ধাতু, প্রাকৃতিক রাবারের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প জোগান দিয়ে বনভূমি ও পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে।
১০. ভারতের শিল্পায়নের প্রধান সমস্যাগুলি কী কী?উত্তর: ভারতে শিল্পায়নের পথে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে:
১. মূলধনের অভাব: শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ মূলধনের অভাব একটি প্রধান সমস্যা।
২. পরিকাঠামোগত দুর্বলতা: অনেক অঞ্চলে এখনো নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, উন্নত রাস্তাঘাট, বন্দর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।
৩. কাঁচামালের সমস্যা: অনেক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত মানের কাঁচামালের অভাব রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।
৪. কারিগরি জ্ঞানের অভাব: আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত এখনো অনেক উন্নত দেশের থেকে পিছিয়ে আছে।
৫. সরকারি নীতি ও শ্রমিক সমস্যা: অনেক সময় সরকারের জটিল নীতি, দুর্নীতি এবং শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট শিল্পের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।
১১. কাঁচামালের উৎস অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ করো।
উত্তর: কাঁচামালের উৎস অনুসারে শিল্পকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) কৃষিভিত্তিক শিল্প: যে শিল্পের কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। যেমন – কার্পাস বয়ন শিল্প, পাট শিল্প, চিনি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
খ) খনিজভিত্তিক শিল্প: যে শিল্পের কাঁচামাল খনি থেকে পাওয়া যায়। যেমন – লৌহ ইস্পাত শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, সিমেন্ট শিল্প।
গ) বনজভিত্তিক শিল্প: যে শিল্পের কাঁচামাল অরণ্য থেকে আসে। যেমন – কাগজ শিল্প, দেশলাই শিল্প, আসবাবপত্র শিল্প।
ঘ) প্রাণিজভিত্তিক শিল্প: যে শিল্পের কাঁচামাল প্রাণী থেকে আসে। যেমন – দুগ্ধ শিল্প, পশম শিল্প, চর্ম শিল্প।
১২. দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর: দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল।
প্রধান শিল্প: এটি মূলত লৌহ ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (DSP) এবং অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট (ASP) ভারতের অন্যতম প্রধান ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র।
গড়ে ওঠার কারণ:
১. রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা এবং সিংভূমের আকরিক লোহার সহজলভ্যতা।
২. দামোদর নদ থেকে জল এবং দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বিদ্যুতের জোগান।
৩. কলকাতা বন্দরের নৈকট্য এবং উন্নত সড়ক ও রেলপথের সুবিধা।
এই সমস্ত সুবিধার জন্য দুর্গাপুরকে ‘ভারতের রুর’ বলা হয়।
১৩. পণ্যসূচক ১-এর কম হলে শিল্পটি বাজারের কাছে গড়ে ওঠে কেন?
উত্তর: যখন কোনো শিল্পের কাঁচামাল বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয়, তখন তার পণ্যসূচক (কাঁচামালের ওজন ÷ উৎপাদিত পণ্যের ওজন) ১ বা তার কম হয়। এর অর্থ হল, কাঁচামালকে পণ্যে পরিণত করার সময় তার ওজন প্রায় একই থাকে বা কমে না।
এই ক্ষেত্রে, কাঁচামালকে শিল্পকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরিবহন ব্যয় এবং উৎপাদিত পণ্যকে বাজারে নিয়ে যাওয়ার পরিবহন ব্যয় প্রায় সমান হয়। তাই শিল্প মালিকরা পরিবহন ব্যয় কমানোর জন্য শিল্পকেন্দ্রটি কাঁচামালের উৎসের পরিবর্তে বিশাল বাজারের কাছে স্থাপন করা পছন্দ করেন, যাতে উৎপাদিত দ্রব্য সহজেই ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই কারণেই কার্পাস বয়ন শিল্পের মতো শিল্পগুলি বাজারের কাছে গড়ে ওঠে।
১৪. ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখো।
উত্তর: ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং এর সম্ভাবনা অপার।
১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মেশিন লার্নিং: এই ক্ষেত্রগুলিতে ভারত দ্রুত উন্নতি করছে, যা ভবিষ্যতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
২. ডিজিটাল ইন্ডিয়া: সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির ফলে দেশের অভ্যন্তরেই তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবার চাহিদা বাড়ছে।
৩. আউটসোর্সিং হাব: ভারত বিশ্বের প্রধান আউটসোর্সিং কেন্দ্র হিসেবে নিজের স্থান আরও মজবুত করবে।
৪. স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম: বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদের মতো শহরগুলি বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্টার্ট-আপ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।
তবে, সাইবার নিরাপত্তা এবং দক্ষ মানব সম্পদের জোগান বজায় রাখা এই শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
১৫. ভারতের অর্থনীতিতে কার্পাস বয়ন শিল্পের গুরুত্ব কী?
উত্তর: ভারতের অর্থনীতিতে কার্পাস বয়ন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম:
১. বৃহত্তম শিল্প: এটি ভারতের বৃহত্তম সুসংগঠিত শিল্প।
২. কর্মসংস্থান: এই শিল্প কৃষির পর ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান ক্ষেত্র। এটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ করে।
৩. জিডিপিতে অবদান: এটি দেশের শিল্প উৎপাদন ও মোট জাতীয় আয়ে (GDP) একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
৪. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান বস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। উৎপাদিত সুতো, কাপড় ও পোশাক বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।
১৬. আহমেদাবাদকে ‘ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার’ বলা হয় কেন?উত্তর: ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহর কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। ভারতের আহমেদাবাদ শহরেও কার্পাস বয়ন শিল্পের অসাধারণ উন্নতি ঘটেছে। এর কারণগুলি হল:
১. নিকটবর্তী কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল থেকে উন্নত মানের তুলার সহজলভ্যতা।
২. সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় জলের জোগান।
৩. আর্দ্র জলবায়ু, যা সুতো কাটার জন্য উপযোগী।
৪. মুম্বাই ও কান্ডালা বন্দরের নৈকট্য এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা।
৫. স্থানীয় উদ্যোগপতিদের মূলধন বিনিয়োগ।
এই সমস্ত অনুকূল পরিবেশের জন্য আহমেদাবাদ ভারতের প্রধান কার্পাস বয়ন শিল্প কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাই একে ‘ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার’ বলা হয়।
১৭. ভারতের চিনি শিল্পের সমস্যাগুলি কী কী?
উত্তর: ভারতের চিনি শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি হল:
১. নিম্ন মানের কাঁচামাল: ভারতের আঁখে সুক্রোজ বা চিনির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম।
২. পুরানো যন্ত্রপাতি: উত্তর ভারতের বেশিরভাগ চিনি কলের যন্ত্রপাতি পুরানো, যা উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।
৩. মৌসুমী উৎপাদন: আঁখ একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে পাওয়া যায় বলে চিনি কলগুলি বছরের মাত্র ৪-৫ মাস চালু থাকে, বাকি সময় বন্ধ থাকে।
৪. ব্যাগাসির সমস্যা: আঁখের ছিবড়ে বা ব্যাগাসিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে।
১৮. ভারী ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
উত্তর: | বৈশিষ্ট্য | ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প | হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প | |—|—|—| | **উৎপাদিত দ্রব্য** | বড় ও ভারী যন্ত্রপাতি তৈরি হয়, যেমন – রেল ইঞ্জিন, জাহাজ, খনন যন্ত্রপাতি। | ছোট ও হালকা যন্ত্রপাতি তৈরি হয়, যেমন – বৈদ্যুতিক পাখা, সেলাই মেশিন, সাইকেল। | | **কাঁচামাল** | প্রচুর পরিমাণে ভারী কাঁচামাল (লোহা, ইস্পাত) প্রয়োজন হয়। | কম পরিমাণে হালকা কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। | | **মূলধন** | প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। | তুলনামূলকভাবে কম মূলধন লাগে। | | **উদাহরণ** | দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, বিশাখাপত্তনম। | কলকাতা, লুধিয়ানা, মুম্বাই। |
১৯. কেন দক্ষিণ ভারতে চিনি শিল্পের প্রসার ঘটছে?উত্তর: সম্প্রতি উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে (বিশেষত মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু) চিনি শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটছে। এর কারণগুলি হল:
১. উন্নত মানের আঁখ: দক্ষিণ ভারতের আঁখে সুক্রোজ বা চিনির পরিমাণ বেশি, তাই একই পরিমাণ আঁখ থেকে বেশি চিনি পাওয়া যায়।
২. অনুকূল জলবায়ু: এখানকার সামুদ্রিক জলবায়ু আঁখ চাষের জন্য আদর্শ এবং ফলনও বেশি।
৩. আধুনিক চিনিকল: এখানকার বেশিরভাগ চিনিকল নতুন এবং আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত, ফলে উৎপাদন ব্যয় কম।
৪. সমবায় ব্যবস্থা: সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে এখানকার চিনি শিল্প অত্যন্ত সুসংগঠিত।
২০. ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলির নাম লেখো।উত্তর: ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি হল:
১. পশ্চিমাঞ্চল: আহমেদাবাদ (ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার), মুম্বাই, পুনে, সুরাট, নাগপুর।
২. দক্ষিণাঞ্চল: কোয়েম্বাটুর (দক্ষিণ ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার), মাদুরাই, সালেম, চেন্নাই।
৩. উত্তরাঞ্চল: কানপুর (উত্তর ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার), দিল্লি, আগ্রা, লুধিয়ানা।
৪. পূর্বাঞ্চল: কলকাতা, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ।
২১. ভারতের প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রগুলির নাম ও তাদের অবস্থান লেখো।
উত্তর: ভারতের প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রগুলি হল:
১. TISCO (টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি): জামশেদপুর (ঝাড়খণ্ড)।
২. IISCO (ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি): বার্নপুর-কুলটি (পশ্চিমবঙ্গ)।
৩. দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (DSP): দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)।
৪. রাউরকেলা স্টিল প্ল্যান্ট (RSP): রাউরকেলা (ওড়িশা)।
৫. ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট (BSP): ভিলাই (ছত্তিশগড়)।
৬. বোকারো স্টিল প্ল্যান্ট (BSL): বোকারো (ঝাড়খণ্ড)।
২২. ভারতের কাগজ শিল্পের সমস্যাগুলি কী কী?
উত্তর: ভারতের কাগজ শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি হল:
১. কাঁচামালের অভাব: সরলবর্গীয় নরম কাঠের অভাব থাকায় বাঁশ ও সাবাই ঘাসের উপর নির্ভর করতে হয়, যা যথেষ্ট নয়।
২. রাসায়নিকের অভাব: কাগজ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।
৩. পরিবেশগত সমস্যা: কাগজ শিল্প একটি অন্যতম দূষণকারী শিল্প। এর বর্জ্য জল ও বায়ুকে দূষিত করে।
৪. অধিক উৎপাদন ব্যয়: পুরানো যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল ও রাসায়নিকের উচ্চ মূল্যের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেশি।
২৩. শিল্প স্থাপনে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর: শিল্প স্থাপনে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য:
১. কাঁচামাল সংগ্রহ: উৎস অঞ্চল থেকে শিল্পকেন্দ্রে কাঁচামাল নিয়ে আসার জন্য উন্নত সড়ক, রেল বা জলপথ প্রয়োজন।
২. উৎপাদিত দ্রব্য প্রেরণ: উৎপাদিত পণ্যকে দ্রুত ও কম খরচে বাজারে বা বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা দরকার।
৩. শ্রমিক ও যন্ত্রপাতি আনা-নেওয়া: শ্রমিকদের যাতায়াত এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ শিল্পকেন্দ্রে আনার জন্যও উন্নত পরিবহন প্রয়োজন।
ওয়েবারের শিল্প স্থানিকতার তত্ত্বেও পরিবহন ব্যয়কে শিল্প স্থাপনের প্রধান নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
২৪. শিল্প স্থাপনে বাজারের ভূমিকা কী?
উত্তর: শিল্প স্থাপনে বাজারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:
১. চাহিদা সৃষ্টি: বাজারই কোনো দ্রব্যের চাহিদা তৈরি করে, যা উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি। বাজারের আকার যত বড় হবে, শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাও তত বাড়বে।
২. অবস্থান নির্ধারণ: পচনশীল দ্রব্য (যেমন – দুগ্ধ, বেকারি) বা ভঙ্গুর দ্রব্যের (যেমন – কাচ) শিল্প বাজারের কাছে গড়ে ওঠে। বিশুদ্ধ কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্পগুলিও পরিবহন ব্যয় কমাতে বাজারের কাছে গড়ে উঠতে পারে।
৩. মূলধন সরবরাহ: বড় শহর বা বাজার অঞ্চলগুলি মূলধন বিনিয়োগ এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রধান কেন্দ্র, যা শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে।
২৫. ‘শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: যখন কোনো শিল্প একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ বলে।
উদাহরণ: ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্প প্রথমে মুম্বাই-আহমেদাবাদ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি কোয়েম্বাটুর, কানপুর, কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে।
কারণ: সরকারি নীতি, বিভিন্ন অঞ্চলে কাঁচামালের উৎপাদন, নতুন বাজারের সৃষ্টি এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৫ (১০টি)
১. পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।
উত্তর:
ভারতের পশ্চিম অংশে, বিশেষত মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে, কার্পাস বয়ন শিল্পের অসাধারণ কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। এর প্রধান কারণগুলি হল:
১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: এই অঞ্চলের কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুর মাটি তুলা চাষের জন্য অত্যন্ত আদর্শ। তাই শিল্পকেন্দ্রগুলি সহজেই স্থানীয়ভাবে উন্নত মানের তুলা পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়, যা কাঁচামাল সংগ্রহের পরিবহন ব্যয় কমিয়ে দেয়।
২. আর্দ্র জলবায়ু: সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার আর্দ্র জলবায়ু সুতো কাটার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আর্দ্রতার কারণে সুতো সহজে ছিঁড়ে যায় না, ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় না।
৩. উন্নত পরিবহন ও বন্দর সুবিধা: মুম্বাই, কান্ডালা, নভসেবার মতো বড় বন্দর এবং উন্নত সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি, যন্ত্রপাতি আনা এবং উৎপাদিত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করা অত্যন্ত সুবিধাজনক।
৪. শক্তির উৎস: নিকটবর্তী পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ট্রম্বে ও তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের জোগান পাওয়া যায়।
৫. মূলধন ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা: মুম্বাই ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী হওয়ায় এবং আহমেদাবাদ একটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হওয়ায় এখানে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের কোনো অভাব নেই। উন্নত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও শিল্প বিকাশে সহায়ক।
৬. সুলভ শ্রমিক ও বাজার: এই অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক সহজেই পাওয়া যায়। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে কার্পাস বস্ত্রের বিশাল বাজার রয়েছে।
২. পূর্ব ও মধ্য ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের একদেশীভবনের কারণগুলি সবিস্তারে আলোচনা করো।
উত্তর:
ভারতের বেশিরভাগ বৃহৎ ও সুসংহত লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র পূর্ব ও মধ্য ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই একদেশীভবনের প্রধান কারণগুলি হল:
১. কাঁচামালের সমাবেশ: লৌহ ইস্পাত একটি ভারী ও অবিশুদ্ধ কাঁচামাল-নির্ভর শিল্প। এই অঞ্চলে শিল্পের প্রধান কাঁচামাল – উচ্চ মানের আকরিক লোহা (ঝাড়খণ্ডের সিংভূম, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ও কেন্দুঝর), কোক কয়লা (রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো), চুনাপাথর ও ডলোমাইট (ওড়িশার সুন্দরগড়) এবং ম্যাঙ্গানিজ (ওড়িশার কেন্দুঝর, ঝাড়খণ্ডের সিংভূম) সবই কাছাকাছি পাওয়া যায়। এর ফলে পরিবহন ব্যয় অনেক কমে যায়।
২. জলের প্রাচুর্য: শিল্পে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ জল দামোদর, সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী, মহানদীর মতো নদীগুলি থেকে সহজেই পাওয়া যায়।
৩. শক্তির পর্যাপ্ত জোগান: কয়লাখনি অঞ্চলের কাছে হওয়ায় তাপবিদ্যুৎ এবং দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (DVC) ও হিরাকুদ প্রকল্প থেকে জলবিদ্যুৎ সহজে পাওয়া যায়।
৪. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: এই অঞ্চলটি সড়ক ও রেলপথ দ্বারা সুসংযুক্ত। কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানি এবং উৎপাদিত ইস্পাত রপ্তানির সুবিধা রয়েছে।
৫. সুলভ শ্রমিক ও বাজার: পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মতো ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যগুলি থেকে প্রচুর সস্তা ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। এছাড়া, নিকটবর্তী কলকাতা এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্রগুলি ইস্পাতের একটি বড় বাজার।
৩. ভারতের পেট্রোরসায়ন শিল্পের পরিচয় দাও এবং এর গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
পরিচয়:
যে শিল্পে খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্য (যেমন – ন্যাপথা, ইথেন, প্রোপেন) ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা হয়, তাকে পেট্রোরসায়ন শিল্প বলে। এই শিল্প থেকে উৎপাদিত দ্রব্যগুলি হল – প্লাস্টিক, পলিমার, কৃত্রিম তন্তু (নাইলন, টেরিলিন), কৃত্রিম রাবার, ডিটারজেন্ট, কীটনাশক, রং ইত্যাদি।
ভারতের প্রধান পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্রগুলি হল – জামনগর (বৃহত্তম), ট্রম্বে (প্রথম), কয়ালি, হলদিয়া, বরোনি ইত্যাদি।
গুরুত্ব:
পেট্রোরসায়ন শিল্পকে ‘আধুনিক শিল্পদানব’ ও ‘উদীয়মান শিল্প’ বলা হয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম:
১. বৈচিত্র্যময় ব্যবহার: এই শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে (যেমন – পোশাক, আসবাবপত্র, মোড়ক, গাড়ি) ব্যবহৃত হয়।
২. অনুসারী শিল্পের বিকাশ: এই শিল্পকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোট-বড় অনুসারী (প্লাস্টিক, রং, ঔষধ) শিল্পের বিকাশ ঘটে, যা প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
৩. কৃষিতে সহায়তা: এই শিল্প থেকে উৎপাদিত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কৃষিজ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
৪. প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প: কৃত্রিম তন্তু, প্লাস্টিক, কৃত্রিম রাবার ইত্যাদি কাঠ, ধাতু, তুলা, প্রাকৃতিক রাবারের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প হিসেবে কাজ করে, যা পরিবেশ সংরক্ষণে সাহায্য করে।
৫. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়: এই শিল্পের উন্নতির ফলে অনেক রাসায়নিক দ্রব্য আর বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না, ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়।
৪. ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নতির কারণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা করো।
উত্তর:
উন্নতির কারণ:
বিগত কয়েক দশকে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি (IT) শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। এর প্রধান কারণগুলি হল:
১. দক্ষ মানব সম্পদ: ভারতে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদ রয়েছে, যা এই জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পের প্রধান চালিকাশক্তি।
২. সরকারি নীতি ও উৎসাহ: ভারত সরকার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (STP) স্থাপন, কর ছাড়, রপ্তানিতে উৎসাহ এবং ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র মতো বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই শিল্পের প্রসারে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে।
৩. কম উৎপাদন ব্যয় ও আউটসোর্সিং: উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে শ্রমিকের পারিশ্রমিক অনেক কম। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা, ইউরোপের অনেক বড় বড় সংস্থা তাদের কাজ (Business Process Outsourcing – BPO) ভারতে পাঠাচ্ছে।
৪. উন্নত পরিকাঠামো: প্রধান শহরগুলিতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে।
৫. বিশ্বায়ন: বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বেড়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:
ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।
১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং, ডেটা সায়েন্স, ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT)-এর মতো নতুন ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের সম্ভাবনা অপার।
২. ভারত বিশ্বের প্রধান সফটওয়্যার ও পরিষেবা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নিজের স্থান আরও মজবুত করবে।
৩. ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।
৪. বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, পুনের মতো শহরগুলি বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্টার্ট-আপ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে, যা নতুন নতুন উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।
৫. ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রেণিবিভাগ করে প্রত্যেকটির বিবরণ দাও।
উত্তর:
ইঞ্জিনিয়ারিং বা যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পকে ‘শিল্পের শিল্প’ বলা হয়। এটিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:
ক) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প:
সংজ্ঞা: যে শিল্পে বড়, ভারী ও জটিল যন্ত্রপাতি তৈরি হয় এবং প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল (লোহা, ইস্পাত) ও মূলধন প্রয়োজন হয়, তাকে ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলে।
উদাহরণ ও কেন্দ্র:
১. রেল ইঞ্জিন নির্মাণ: পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হয়।
২. রেল বগি নির্মাণ: তামিলনাড়ুর পেরাম্বুর এবং পাঞ্জাবের কাপুরথালায় রেলের বগি তৈরি হয়।
৩. জাহাজ নির্মাণ: বিশাখাপত্তনম, কোচি, মুম্বাই ও কলকাতায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কারখানা রয়েছে।
৪. বিমানপোত নির্মাণ: কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (HAL) বিমানপোত তৈরি করে।
খ) হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প:
সংজ্ঞা: যে শিল্পে অপেক্ষাকৃত ছোট ও হালকা যন্ত্রপাতি তৈরি হয় এবং এতে কম কাঁচামাল ও মূলধন লাগে, তাকে হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলে।
উদাহরণ ও কেন্দ্র:
১. বৈদ্যুতিক সামগ্রী: পাখা, মোটর, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি কলকাতায়, ভোপালে ও হরিদ্বারে তৈরি হয়।
২. সেলাই মেশিন: কলকাতা, লুধিয়ানা, মুম্বাইয়ে সেলাই মেশিন তৈরি হয়।
৩. সাইকেল: লুধিয়ানা, সোনিপত, চেন্নাই সাইকেল শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
৪. বিভিন্ন যন্ত্রপাতি: কৃষি যন্ত্রপাতি, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্রে তৈরি হয়।
৬. শিল্প স্থাপনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকগুলির ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর:
কোনো স্থানে শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠার জন্য একাধিক প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকের প্রয়োজন হয়।
প্রাকৃতিক নিয়ামক:
১. কাঁচামাল: এটি শিল্প স্থাপনের প্রধান ভিত্তি। অবিশুদ্ধ কাঁচামাল-নির্ভর শিল্প (যেমন – লৌহ ইস্পাত, চিনি) কাঁচামালের উৎসের কাছে গড়ে ওঠে। বিশুদ্ধ কাঁচামাল-নির্ভর শিল্প (যেমন – কার্পাস বয়ন) যেকোনো স্থানে গড়ে উঠতে পারে।
২. শক্তি সম্পদ: শিল্পের যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন শক্তির জোগান অপরিহার্য। তাই শিল্পকেন্দ্রগুলি কয়লাখনি, বিদ্যুৎকেন্দ্র বা তৈল শোধনাগারের কাছে গড়ে ওঠে।
৩. জল: যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা রাখা, কাঁচামাল ধোয়া এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য শিল্পে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। তাই শিল্পকেন্দ্রগুলি নদী বা জলাশয়ের তীরে গড়ে ওঠে।
৪. অনুকূল ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু: সমতল জমিতে কারখানা ও পরিকাঠামো নির্মাণ করা সহজ। কিছু শিল্পের জন্য বিশেষ জলবায়ুর প্রয়োজন হয় (যেমন – কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ু)।
অর্থনৈতিক নিয়ামক:
১. সুলভ শ্রমিক: শিল্পের জন্য দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাই ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে সুলভ শ্রমিক পাওয়ার আশায় শিল্প গড়ে ওঠে।
২. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: কাঁচামাল আনা এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে পাঠানোর জন্য উন্নত সড়ক, রেল, জল ও বিমানপথ অপরিহার্য।
৩. বাজার: উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা এবং বিক্রির জন্য বাজারের নৈকট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৪. মূলধন: শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়, যা ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যায়।
৫. সরকারি নীতি: সরকারের অনুকূল নীতি, কর ছাড়, পরিকাঠামোগত সহায়তা ইত্যাদিও শিল্প স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৭. ভারতের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
উত্তর:
ভারতে কয়েকটি প্রধান শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে:
১. মুম্বাই-পুনে শিল্পাঞ্চল: এটি ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল। কার্পাস বয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রোরসায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, চলচ্চিত্র শিল্প এখানকার প্রধান শিল্প।
২. হুগলি শিল্পাঞ্চল: এটি ভারতের প্রাচীনতম শিল্পাঞ্চল। পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ, রাসায়নিক, কার্পাস বয়ন এখানকার প্রধান শিল্প।
৩. বেঙ্গালুরু-চেন্নাই শিল্পাঞ্চল: এটি দক্ষিণ ভারতের প্রধান শিল্পাঞ্চল। তথ্যপ্রযুক্তি, মোটরগাড়ি নির্মাণ, কার্পাস বয়ন ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পে এটি উন্নত।
৪. গুজরাট শিল্পাঞ্চল: আহমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট অঞ্চল জুড়ে এটি বিস্তৃত। কার্পাস বয়ন, পেট্রোরসায়ন ও হীরা শিল্প এখানকার প্রধান শিল্প।
৫. ছোটনাগপুর শিল্পাঞ্চল: এটি ভারতের খনিজ ভাণ্ডার। লৌহ ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট শিল্প এখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।
৬. দিল্লি-গুরগাঁও-মীরাট শিল্পাঞ্চল: মোটরগাড়ি, ইলেকট্রনিক্স এবং বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য শিল্পে এই অঞ্চল উন্নত।
৮. ভারতের পাট শিল্পের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভারতের পাট শিল্পের সমস্যা:
১. কাঁচামালের অভাব ও নিম্নমান: দেশভাগের ফলে বেশিরভাগ উন্নত মানের পাট উৎপাদক অঞ্চল বাংলাদেশে চলে যাওয়ায় ভারতে কাঁচামালের সংকট দেখা দেয়।
২. বিকল্প দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা: পাটের তৈরি বস্তা, দড়ির পরিবর্তে প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বাড়ায় পাটের চাহিদা বিশ্ব বাজারে কমে গেছে।
৩. পুরানো যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি: ভারতের বেশিরভাগ পাটকলের যন্ত্রপাতি পুরানো, যার ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশি এবং পণ্যের মানও আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় কম।
৪. শ্রমিক সমস্যা: শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট এবং কম পারিশ্রমিক প্রায়শই উৎপাদন ব্যাহত করে।
৫. আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা হ্রাস: বিশ্ব বাজারে পাটের চাহিদা ক্রমশ কমছে।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:
এত সমস্যা সত্ত্বেও ভারতের পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে:
১. পরিবেশবান্ধব তন্তু: পাট একটি প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব তন্তু। প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় পাটের তৈরি দ্রব্যের চাহিদা পুনরায় বাড়তে পারে।
২. বৈচিত্র্যময় ব্যবহার: বর্তমানে পাট থেকে শুধুমাত্র বস্তা বা দড়ি নয়, কার্পেট, ব্যাগ, পোশাক, আসবাবপত্র, গাড়ির যন্ত্রাংশ এমনকি কাগজও তৈরি হচ্ছে। এই বৈচিত্র্যময় ব্যবহার শিল্পের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
৩. সরকারি উদ্যোগ: ভারত সরকার পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং পাট চাষ ও শিল্পের আধুনিকীকরণে সহায়তা করছে। সঠিক পরিকল্পনা ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে এই শিল্প পুনরায় তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে।
৯. ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের বিকেন্দ্রীভবনের কারণগুলি কী কী?
উত্তর:
কার্পাস বয়ন একটি শিকড়-আলগা শিল্প হওয়ায় এটি প্রথমে মুম্বাই-আহমেদাবাদ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকলেও, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিকেন্দ্রীভবনের কারণগুলি হল:
১. কাঁচামালের সহজলভ্যতা: বর্তমানে তুলা শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র বা গুজরাটেই নয়, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চাষ হচ্ছে। ফলে স্থানীয় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে অনেক নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।
২. বাজারের বিস্তার: ভারতের বিশাল জনসংখ্যা কার্পাস বস্ত্রের একটি বিরাট বাজার। তাই বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য সেইসব অঞ্চলে নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।
৩. উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা: সড়ক ও রেলপথের উন্নতির ফলে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে কাঁচামাল আনা এবং উৎপাদিত দ্রব্য পাঠানো সহজ হয়েছে।
৪. বিদ্যুতের সহজলভ্যতা: জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান সহজ হয়েছে।
৫. সরকারি নীতি: সরকার পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কর ছাড় ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করছে, যা বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করেছে।
৬. শ্রমিকের জোগান: ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে সুলভ শ্রমিক পাওয়ার আশায় অনেক শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যেমন – কানপুর।
১০. আলফ্রেড ওয়েবারের শিল্প স্থানিকতার নূন্যতম ব্যয় তত্ত্বটি আলোচনা করো।
উত্তর:
জার্মান অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড ওয়েবার ১৯০৯ সালে তাঁর ‘Theory of the Location of Industries’ গ্রন্থে শিল্প স্থাপনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের একটি তত্ত্ব দেন, যা ‘নূন্যতম ব্যয় তত্ত্ব’ নামে পরিচিত।
মূল বক্তব্য: ওয়েবারের মতে, শিল্প স্থাপনের জন্য সেই স্থানটিই সবচেয়ে উপযুক্ত যেখানে উৎপাদন ব্যয় (কাঁচামাল ও পণ্যের পরিবহন ব্যয়, শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি) সবচেয়ে কম হবে এবং শিল্পপতির লাভ সর্বাধিক হবে।
প্রধান নিয়ামক: তিনি শিল্প স্থাপনের জন্য তিনটি প্রধান নিয়ামককে গুরুত্ব দিয়েছেন:
১. পরিবহন ব্যয় (Transport Cost): এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। শিল্পের অবস্থান এমন হবে যেখানে কাঁচামাল আনা ও উৎপাদিত পণ্য বাজারে পাঠানোর মোট পরিবহন ব্যয় সর্বনিম্ন হবে। এর জন্য তিনি ‘পণ্যসূচক’ (Material Index) এবং ‘আইসোডাপেন’ (Isodapane – সম পরিবহন ব্যয় রেখা) এর ধারণা ব্যবহার করেন।
২. শ্রমিকের ব্যয় (Labour Cost): যদি কোনো স্থানে সুলভ শ্রমিক পাওয়ার ফলে সাশ্রয় হওয়া অর্থ পরিবহন ব্যয়ের বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হয়, তবে শিল্পটি সর্বনিম্ন পরিবহন ব্যয়ের স্থান থেকে সরে এসে সুলভ শ্রমিকের উৎসের কাছে গড়ে উঠবে।
৩. একদেশীভবনের সুবিধা (Agglomeration Benefits): যখন অনেক শিল্প এক জায়গায় গড়ে ওঠে, তখন তারা উন্নত পরিকাঠামো, তথ্য আদান-প্রদান এবং অন্যান্য অনেক সুবিধা পায়। যদি এই সুবিধা থেকে হওয়া লাভ অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়, তবে শিল্পগুলি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হবে।
ওয়েবারের তত্ত্বটি শিল্প স্থানিকতা বোঝার একটি প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ মডেল, যদিও এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।
ভারতের শিল্প class 10 প্রশ্ন উত্তর MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 Geography ভারতের শিল্প Question Answer