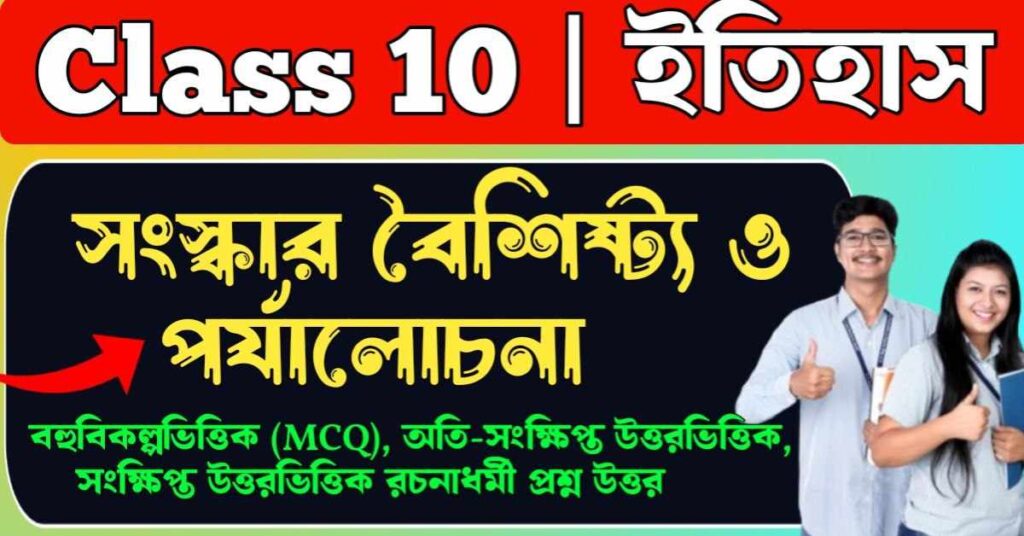ইতিহাসের ধারণা Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা শুরু হয় কবে?
২. ‘Historiography’ কথাটির অর্থ কী?
৩. মোহনবাগান ক্লাব কবে আই.এফ.এ. শিল্ড জয় করে?
৪. ‘জীবনস্মৃতি’ কার আত্মজীবনী?
৫. ‘সত্তর বৎসর’ নামক আত্মজীবনীটি কার লেখা?
৬. ‘একাত্তরের ডায়েরী’ নামক স্মৃতিকথাটির রচয়িতা কে?
৭. ‘সোমপ্রকাশ’ ছিল একটি—
৮. ‘বঙ্গদর্শন’ সাময়িকপত্রটি কে প্রবর্তন করেন?
৯. ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়—
১০. ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ পালিত হয়—
১১. ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থটি হল একটি—
১২. ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র কোনটি?
১৩. ‘Subaltern’ গোষ্ঠীর একজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন—
১৪. ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র কোনটি?
১৫. ‘Silent Spring’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
১৬. ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠিগুলির হিন্দি অনুবাদ কে করেন?
১৭. ‘লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার’-এর পত্র সংখ্যা ছিল—
১৮. ভারতের প্রথম কোথায় হকি খেলা শুরু হয়?
১৯. ‘পথের পাঁচালী’ ছবির পরিচালক কে?
২০. রসগোল্লার আবিষ্কারক কে?
২১. ভারতে ফুটবল খেলার প্রবর্তন করে—
২২. ‘নবান্ন’ নাটকটির রচয়িতা কে?
২৩. ‘সরকারি নথিপত্র’ সংরক্ষণ করা হয়—
২৪. প্রথম বাঙালি ফোটোগ্রাফার কে ছিলেন?
২৫. ‘Annales School’ বা অ্যানাল গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়—
২৬. ‘সেদিনের কথা’ নামক স্মৃতিকথাটি কার লেখা?
২৭. কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কবে?
২৮. ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ কে করেন?
২৯. ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কে ছিলেন?
৩০. ‘হিস্টোরিয়া’ শব্দটি একটি—
৩১. ক্রিকেট খেলার উদ্ভব হয় কোন দেশে?
৩২. ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
৩৩. ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাব কোনটি?
৩৪. ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক কাকে বলা হয়?
৩৫. ‘The Story of My Experiments with Truth’ কার আত্মজীবনী?
৩৬. প্রথম কোন পত্রিকায় ফটোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়?
৩৭. ‘কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
৩৮. ‘বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—
৩৯. কোন বিষয়টি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়?
৪০. ‘চিপকো আন্দোলন’ ছিল একটি—
৪১. ভারতে প্রথম আদমশুমারি ( مردم شماری ) হয় কবে?
৪২. ‘কেরলের কথাকলি’ কোন ধরণের শিল্পের উদাহরণ?
৪৩. ‘ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, তার বেশিও নয়, কমও নয়’ – উক্তিটি কার?
৪৪. ‘A History of Hindu Chemistry’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
৪৫. ‘The Annals of Rural Bengal’ কার লেখা?
৪৬. ‘গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন খ্যাতনামা—
৪৭. ‘ইকো-ফেমিনিজম’ (Eco-feminism) কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?
৪৮. ভারতের ডাকটিকিট প্রথম কবে চালু হয়?
৪৯. ‘ইতিহাসের জনক’ কাকে বলা হয়?
৫০. ‘ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৫১. উদয়শঙ্কর বিখ্যাত ছিলেন কোন শিল্পে?
৫২. নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার জনক কে?
৫৩. ‘জীবনের ঝরাপাতা’ কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
৫৪. ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—
৫৫. ‘পাবনা জেলার ইতিহাস’ গ্রন্থটি কী ধরনের ইতিহাসের উদাহরণ?
৫৬. ‘What is History?’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
৫৭. ‘বোমা তৈরির কৌশল’ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হত?
৫৮. ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?
৫৯. ‘Food in History’ গ্রন্থটি কার লেখা?
৬০. ভারতে প্রথম কবে জনগণনা (Census) শুরু হয়?
৬১. ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
৬২. ‘কলকাতা: কাঠের খোদাই’ (Calcutta: Wood and Wood Engraving) গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
৬৩. নারী দিবস পালিত হয়—
৬৪. ‘The Indian War of Independence’ গ্রন্থটি কার লেখা?
৬৫. ‘ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ’ (IPL) কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?
৬৬. ‘দাগেরোটাইপ’ (Daguerreotype) পদ্ধতি যুক্ত ছিল—
৬৭. পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চাকে কী বলা হয়?
৬৮. ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—
৬৯. কোনটিকে আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপাদান বলে গণ্য করা হয়?
৭০. ‘Annales’ পত্রিকাটি কোন দেশ থেকে প্রকাশিত হত?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. নতুন সামাজিক ইতিহাস কী?
উত্তর: রাজা-মহারাজাদের কাহিনীর পরিবর্তে সাধারণ মানুষের জীবনচর্চার ইতিহাসই হল নতুন সামাজিক ইতিহাস।
২. ‘জীবনের ঝরাপাতা’ কার আত্মজীবনী?
উত্তর: ‘জীবনের ঝরাপাতা’ সরলাদেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী।
৩. খেলার ইতিহাস চর্চা কবে শুরু হয়?
উত্তর: ১৯৭০-এর দশকে ইংল্যান্ডে প্রথম খেলার ইতিহাস চর্চা শুরু হয়।
৪. সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
৫. দুটি পরিবেশ-বিষয়ক আন্দোলনের নাম লেখো।
উত্তর: চিপকো আন্দোলন ও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন।
৬. ভারতে প্রথম কবে রেলপথ চালু হয়?
উত্তর: ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে।
৭. সরকারি নথিপত্র কোথায় সংরক্ষণ করা হয়?
উত্তর: মহাফেজখানা বা লেখ্যাগারে (Archives)।
৮. আত্মজীবনী কীভাবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: আত্মজীবনী থেকে সমসাময়িক কালের সমাজ ও রাজনীতির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ পাওয়া যায়।
৯. ফটোগ্রাফির জনক কাকে বলা হয়?
উত্তর: লুই দাগের ও নিয়েপসকে।
১০. নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত একজন ঐতিহাসিকের নাম লেখো।
উত্তর: রণজিৎ গুহ।
১১. ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১২. ‘Letters from a Father to his Daughter’-এর লেখক কে?
উত্তর: জওহরলাল নেহরু।
১৩. একটি স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর: রাধারমণ সাহার ‘পাবনা জেলার ইতিহাস’।
১৪. ‘Indian Women: From Purdah to Modernity’ কার লেখা?
উত্তর: বি. আর. নন্দা।
১৫. ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র কে তৈরি করেন?
উত্তর: দাদাসাহেব ফালকে।
১৬. সামরিক ইতিহাসের একটি বিষয় উল্লেখ করো।
উত্তর: যুদ্ধের কারণ, কৌশল এবং ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র।
১৭. খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস থেকে কী জানা যায়?
উত্তর: কোনো অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যের বিবর্তন এবং তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য জানা যায়।
১৮. ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি কে রচনা করেন?
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।
১৯. ‘ইতিহাসমালা’ কে রচনা করেন?
উত্তর: উইলিয়াম কেরি।
২০. ‘IFA’-এর পুরো নাম কী?
উত্তর: ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।
২১. শহরের ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্ব লেখো।
উত্তর: শহরের ইতিহাস চর্চা থেকে কোনো শহরের উৎপত্তি, বিকাশ এবং তার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন জানা যায়।
২২. ‘সত্তর বৎসর’ আত্মজীবনীটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়।
২৩. ‘হিস্টোরিয়া’ শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: অনুসন্ধান বা গবেষণা।
২৪. ভারতে প্রথম কোথায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: গোয়ায়।
২৫. নারী ইতিহাস চর্চার একজন ঐতিহাসিকের নাম লেখো।
উত্তর: জেরাল্ডিন ফোর্বস।
২৬. ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ কার লেখা?
উত্তর: কালীপ্রসন্ন সিংহ।
২৭. একজন বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর নাম লেখো।
উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৮. ‘দিল্লি দরবার’ কীসের জন্য বিখ্যাত?
উত্তর: ব্রিটিশ রাজাদের অভিষেক অনুষ্ঠান এবং ফটোগ্রাফির ব্যবহারের জন্য।
২৯. টপ্পা গানের প্রবর্তক কে?
উত্তর: রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)।
৩০. ‘Imperialism of Free Trade’ তত্ত্বটি কার?
উত্তর: জন গ্যালাহার ও রোনাল্ড রবিনসন।
৩১. দুটি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর: ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ (দক্ষিণারঞ্জন বসু) ও ‘একাত্তরের ডায়েরী’ (সুফিয়া কামাল)।
৩২. ‘অ্যানাল স্কুল’-এর দুজন ঐতিহাসিকের নাম লেখো।
উত্তর: লুসিয়েন ফেবর ও মার্ক ব্লখ।
৩৩. ‘The History of British India’ কার লেখা?
উত্তর: জেমস মিল।
৩৪. ভারতীয়রা আলুর ব্যবহার কাদের কাছ থেকে শেখে?
উত্তর: পোর্তুগিজদের কাছ থেকে।
৩৫. ‘বীরাষ্টমী ব্রত’ কে চালু করেন?
উত্তর: সরলাদেবী চৌধুরাণী।
৩৬. ‘টোটাল হিস্ট্রি’ বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কী?
উত্তর: অ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রবর্তিত সামগ্রিক ইতিহাস চর্চাই হল টোটাল হিস্ট্রি।
৩৭. ‘কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত’ কে রচনা করেন?
উত্তর: বিনয় ঘোষ।
৩৮. ‘The Cambridge School’-এর একজন ঐতিহাসিকের নাম লেখো।
উত্তর: অনিল শীল।
৩৯. পোশাক পরিচ্ছদের ইতিহাস থেকে কী জানা যায়?
উত্তর: কোনো সমাজের মানুষের রুচি, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় জানা যায়।
৪০. বাংলায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা কোনটি?
উত্তর: সমাচার দর্পণ।
৪১. ‘রাজতরঙ্গিনী’ গ্রন্থ থেকে কোন অঞ্চলের ইতিহাস জানা যায়?
উত্তর: কাশ্মীরের ইতিহাস।
৪২. ‘রাজতরঙ্গিনী’ কে রচনা করেন?
উত্তর: কলহন।
৪৩. ‘India Wins Freedom’ কার আত্মজীবনী?
উত্তর: মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।
৪৪. ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: উমেশচন্দ্র দত্ত।
৪৫. ইন্টারনেট ব্যবহারের একটি অসুবিধা লেখো।
উত্তর: ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা কঠিন এবং অনেক সময় ভুল তথ্য থাকে।
৪৬. ‘কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
৪৭. ‘জীববৈচিত্র্য’ বা ‘Biodiversity’ শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?
উত্তর: ওয়াল্টার জি. রোজেন।
৪৮. ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা কবে চালু হয়?
উত্তর: ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে।
৪৯. ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: সরলাদেবী চৌধুরাণী।
৫০. ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে।
৫১. ‘History from Below’ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: নীচ থেকে দেখা ইতিহাস বা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস চর্চা।
৫২. একটি পরিবেশগত ইতিহাস গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর: র্যাচেল কারসনের ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ (Silent Spring)।
৫৩. ‘ভারতের তোতাপাখি’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: আমির খসরুকে।
৫৪. ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে।
৫৫. ‘বিষ্ণুপুর ঘরানা’ কীসের জন্য বিখ্যাত?
উত্তর: ধ্রুপদী সঙ্গীতের জন্য।
৫৬. ‘The Police in British India’ কার লেখা?
উত্তর: আনন্দস্বরূপ গুপ্ত।
৫৭. ‘Past and Present’ পত্রিকাটি কোন গোষ্ঠীর মুখপত্র ছিল?
উত্তর: ব্রিটেনের মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর।
৫৮. ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।
৫৯. ‘ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল’ (ICC) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে।
৬০. ‘জাতীয় মহাফেজখানা’ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: দিল্লিতে।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. নতুন সামাজিক ইতিহাস বলতে কী বোঝো?
উত্তর: যে ইতিহাসচর্চায় রাজা-মহারাজা বা অভিজাতদের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মানুষ, যেমন – কৃষক, শ্রমিক, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাকে নতুন সামাজিক ইতিহাস বলে। এর ফলে ইতিহাস সর্বসাধারণের ইতিহাস হয়ে ওঠে।
২. ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার গুরুত্ব কী?
উত্তর: আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এগুলি থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিকোণ সমসাময়িক ঘটনাকে নতুনভাবে বুঝতে সাহায্য করে।
৩. সরকারি নথিপত্র বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: সরকারি নথিপত্র বলতে সরকারি আদেশ, নির্দেশ, পুলিশ ও গোয়েন্দা রিপোর্ট, চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের প্রতিবেদনকে বোঝায়। এগুলি আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান, যদিও এগুলি প্রায়শই একপেশে হয়।
৪. স্থানীয় ইতিহাস চর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
উত্তর: স্থানীয় ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় ইতিহাসে তার অবদান সম্পর্কে জানা যায়। এটি বৃহত্তর ইতিহাস রচনার ফাঁকফোকর পূরণ করতে এবং সাধারণ মানুষকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করে।
৫. পরিবেশের ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব কী?
উত্তর: পরিবেশের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশের উপর মানুষের কার্যকলাপের প্রভাব এবং বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যার ঐতিহাসিক কারণ জানা যায়। এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিবেশ নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে।
৬. ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা সমকালীন সমাজে কী ভূমিকা পালন করেছিল?
উত্তর: দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক ও রাজনৈতিক चेतना বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে।
৭. নারী ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব লেখো।
উত্তর: নারী ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে ইতিহাসে নারীদের অবদান, তাদের সামাজিক অবস্থান, অধিকার এবং বঞ্চনার কথা জানা যায়। এটি ইতিহাসে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসকে আরও সম্পূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে।
৮. নিম্নবর্গের ইতিহাস (Subaltern Studies) বলতে কী বোঝো?
উত্তর: যে ইতিহাসচর্চায় সমাজের অভিজাত বা উচ্চবর্গের পরিবর্তে কৃষক, শ্রমিক, দলিত, আদিবাসী প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখা হয় এবং ইতিহাসে তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বলে।
৯. ফটোগ্রাফ কীভাবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সমাজ, ঘটনা, ব্যক্তিত্ব বা স্থাপত্যের একটি জীবন্ত দৃশ্যপট তুলে ধরে। এর মাধ্যমে পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায়, যা ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে।
১০. খেলাধুলার ইতিহাস চর্চা থেকে কী জানা যায়?
উত্তর: খেলাধুলার ইতিহাস চর্চা থেকে কোনো সমাজের অবসর যাপন, শারীরিক সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, ১৯১১ সালে মোহনবাগানের আই.এফ.এ. শিল্ড জয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হয়।
১১. ব্রিটিশ সরকার কেন ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিল?
উত্তর: ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা নির্ভীকভাবে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, শোষণ এবং দেশীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা করত। লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন অনুসারে সরকারের সমালোচনার অপরাধে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
১২. ইন্টারনেট ব্যবহারের দুটি সুবিধা ও দুটি অসুবিধা লেখো।
উত্তর: সুবিধা: (১) ঘরে বসে সহজেই বিপুল পরিমাণ তথ্য পাওয়া যায়। (২) বিভিন্ন দেশের মহাফেজখানা ও গ্রন্থাগারের উপাদান ব্যবহার করা যায়। অসুবিধা: (১) ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা কঠিন। (২) অনেক সময় ভুল ও বিকৃত তথ্য থাকে।
১৩. শিল্পচর্চার ইতিহাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: সংগীত, নৃত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও চিত্রকলা প্রভৃতির ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে একটি যুগের সাংস্কৃতিক মান, মানুষের রুচিবোধ এবং সামাজিক প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে জানা যায়। এই শিল্পগুলি সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির প্রতিফলন ঘটায়, যা ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান।
১৪. শহরের ইতিহাস চর্চা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: কোনো একটি শহরের উৎপত্তি, বিকাশ, তার গঠন, জনসংখ্যা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে শহরের ইতিহাস চর্চা বলে। যেমন – কলকাতার ইতিহাস, দিল্লির ইতিহাস ইত্যাদি।
১৫. ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব কী?
উত্তর: সংবাদপত্র থেকে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, সামাজিক সমস্যা, জনমত এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। উনিশ শতকে ‘সোমপ্রকাশ’, ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’-এর মতো পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা এবং জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
১৬. জওহরলাল নেহরু তাঁর কন্যাকে চিঠি লিখেছিলেন কেন?
উত্তর: জওহরলাল নেহরু যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত থাকার কারণে জেলে বন্দি ছিলেন, তখন তাঁর দশ বছর বয়সী কন্যা ইন্দিরাকে ইতিহাস, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলি ‘Letters from a Father to his Daughter’ নামে পরিচিত।
১৭. পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কেন?
উত্তর: পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মানুষের সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গভেদ, জাতিভেদ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এটি বিভিন্ন সময়ের রুচি ও ফ্যাশনের পরিবর্তনকেও তুলে ধরে।
১৮. খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস চর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
উত্তর: খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস চর্চা থেকে একটি সমাজের খাদ্যের প্রকার, খাদ্যের বিবর্তন, খাদ্যের সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। যেমন, ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসে পোর্তুগিজদের আনা আলু ও লঙ্কার প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
১৯. ‘অ্যানাল স্কুল’ কী?
উত্তর: ‘অ্যানাল স্কুল’ হলো ফ্রান্সে গড়ে ওঠা একটি ইতিহাস চর্চার গোষ্ঠী, যা গতানুগতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিকতার ইতিহাস চর্চার উপর জোর দেয়। লুসিয়েন ফেবর ও মার্ক ব্লখ ছিলেন এর প্রধান প্রবক্তা।
২০. সরকারি নথিপত্রের সীমাবদ্ধতা কী?
উত্তর: সরকারি নথিপত্র মূলত ব্রিটিশ বা ঔপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, তাই এগুলি একপেশে হয়। শাসকরা প্রায়শই নিজেদের সাফল্যকে বড় করে দেখায় এবং ব্যর্থতা বা অত্যাচারের ঘটনাকে চেপে যায়, যা ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করে।
২১. ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহে চিঠিপত্রের গুরুত্ব কী?
উত্তর: ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে কোনো ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, মানসিকতা এবং বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত জানা যায়। এগুলি প্রায়শই অনেক অকথিত বা গোপন তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে, যা সরকারি নথিতে পাওয়া যায় না।
২২. ‘গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র’ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি বাবু সমাজের ইংরেজি অনুকরণপ্রিয়তা, সামাজিক ভণ্ডামি এবং ঔপনিবেশিক শাসনের নানা অসঙ্গতিকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছে। এগুলি সমকালীন সমাজের এক জীবন্ত দলিল।
২৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস চর্চা করা হয় কেন?
উত্তর: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা, বিভিন্ন আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট এবং সমাজে তার প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। এটি বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশেও সাহায্য করে।
২৪. ‘একাত্তরের ডায়েরী’ থেকে কী জানা যায়?
উত্তর: সুফিয়া কামালের লেখা ‘একাত্তরের ডায়েরী’ থেকে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত বিবরণ পাওয়া যায়।
২৫. সামরিক ইতিহাস বলতে কী বোঝো?
উত্তর: ইতিহাসের যে শাখায় যুদ্ধের কারণ, প্রকৃতি, রণকৌশল, অস্ত্রশস্ত্রের বিবর্তন, সামরিক বাহিনীর গঠন এবং সমাজে যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে সামরিক ইতিহাস বলা হয়।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবনস্মৃতি’-র গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবনস্মৃতি’ আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর গুরুত্বগুলি হল:
১. উনিশ শতকের সমাজচিত্র: এই গ্রন্থ থেকে উনিশ শতকের কলকাতার অভিজাত ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলের কথা, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।
২. শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয়: তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, যেমন—ঘরের শিক্ষকদের কাছে পড়া, নরম্যাল স্কুলে ভর্তি এবং সাধারণ স্কুলের প্রতি কবির অনীহার বিবরণ থেকে সে যুগের শিক্ষার স্বরূপ বোঝা যায়।
৩. ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব: ঠাকুর পরিবারের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের একটি চিত্র এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে।
৪. জাতীয়তাবাদের উন্মেষ: স্বদেশী ভাবধারার উন্মেষ, ‘হিন্দুমেলা’র মতো সংগঠনের কার্যকলাপ এবং জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশের কথা ‘জীবনস্মৃতি’ থেকে জানা যায়।
তবে এটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা হওয়ায় এখানে সব তথ্য নিরপেক্ষভাবে পাওয়া যায় না, যা এর একটি সীমাবদ্ধতা।
২. ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সরলাদেবী চৌধুরাণীর ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থটির মূল্যায়ন করো।
উত্তর:
সরলাদেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ‘জীবনের ঝরাপাতা’ উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের প্রথমভাগের বাংলার ইতিহাস জানার জন্য একটি মূল্যবান উপাদান।
১. নারীর দৃষ্টিকোণ: এই গ্রন্থটি ঠাকুরবাড়ির এক বিদূষী নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রসার এবং অন্তঃপুরের নারীদের আত্মবিকাশের কথা জানা যায়।
২. রাজনৈতিক কার্যকলাপ: সরলাদেবী নিজে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘বীরাষ্টমী ব্রত’, ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’ এবং ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলায় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রসারের কথা জানা যায়।
৩. কংগ্রেসের অন্দরমহল: জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাই এই গ্রন্থ থেকে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ এবং নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
৪. সামাজিক চিত্র: তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান, বিধিনিষেধ এবং তার বিরুদ্ধে সরলাদেবীর মতো নারীদের সংগ্রামের একটি জীবন্ত ছবি এই আত্মজীবনীতে রয়েছে।
৩. আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে সরকারি নথিপত্রের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা লেখো।
উত্তর:
আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনায় সরকারি নথিপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
গুরুত্ব:
১. প্রামাণ্য তথ্য: সরকারি চিঠিপত্র, পুলিশ ও গোয়েন্দা রিপোর্ট, জেলাশাসকদের প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা, আইনকানুন এবং বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়।
২. পরিসংখ্যান: জনগণনা, ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি পরিসংখ্যানমূলক নথি থেকে তৎকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভ করা যায়।
৩. বিদ্রোহের তথ্য: বিভিন্ন কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও দমননীতির বিস্তারিত বিবরণ এই নথিগুলিতে পাওয়া যায়।
সীমাবদ্ধতা:
১. একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি: এই নথিগুলি ব্রিটিশদের স্বার্থে এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, তাই এগুলি পক্ষপাতদুষ্ট।
২. তথ্য গোপন: শাসকরা প্রায়শই নিজেদের ব্যর্থতা ও অত্যাচারের ঘটনাগুলিকে গোপন করত বা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করত।
৩. সাধারণ মানুষের অনুপস্থিতি: এই নথিগুলিতে সাধারণ মানুষের ভাবনা, যন্ত্রণা বা মতামত প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে।
৪. ইতিহাসের তথ্য হিসেবে চিঠিপত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
আধুনিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।
১. ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ: চিঠিপত্র থেকে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা যায়, যা সরকারি নথিতে পাওয়া যায় না।
২. গোপন তথ্যের উৎস: অনেক সময় চিঠিপত্রে এমন সব গোপন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনার উল্লেখ থাকে যা অন্য কোনো উপাদানে মেলে না।
৩. সমাজচিত্রের প্রতিফলন: চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের পারিপার্শ্বিক সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে ওঠে।
৪. উদাহরণ: জওহরলাল নেহরুর তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে লেখা চিঠিগুলি (‘Letters from a Father to his Daughter’) থেকে যেমন তৎকালীন বিশ্ব ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে নেহরুর ভাবনা জানা যায়, তেমনই এটি এক পিতা-কন্যার সম্পর্কেরও দলিল।
৫. ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর:
আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা উভয়ই ব্যক্তিগত রচনা হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।
১. বিষয়বস্তু: আত্মজীবনীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হল লেখকের নিজের জীবন। লেখক নিজের জন্ম, বেড়ে ওঠা, কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির বিস্তারিত বিবরণ দেন। অন্যদিকে, স্মৃতিকথার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল লেখকের জীবনের সঙ্গে জড়িত কোনো বিশেষ ঘটনা বা সময়। এখানে লেখকের নিজের জীবনের চেয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনাই বেশি প্রাধান্য পায়।
২. পরিধি: আত্মজীবনীর পরিধি সাধারণত ব্যাপক হয়, যা লেখকের সমগ্র জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু স্মৃতিকথার পরিধি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ এবং এটি জীবনের একটি বিশেষ পর্বকে কেন্দ্র করে রচিত হয়।
৩. উদাহরণ: রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’ একটি আত্মজীবনী। অন্যদিকে, সুফিয়া কামালের ‘একাত্তরের ডায়েরী’ বা মণিকুন্তলা সেনের ‘সেদিনের কথা’ হল স্মৃতিকথা।
৬. উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিত্র ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকায় কীভাবে ফুটে উঠেছে?
উত্তর:
উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা ছিল মূলত নারীদের জন্য প্রকাশিত একটি পত্রিকা। এতে উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
১. নারীশিক্ষার প্রসার: পত্রিকাটি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করত এবং বিভিন্ন শিক্ষিতা নারীর জীবনী ও রচনা প্রকাশ করে অন্যদের উৎসাহিত করত।
২. সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা: ‘বামাবোধিনী’ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথার মতো সামাজিক কুপ্রথাগুলির তীব্র বিরোধিতা করত এবং জনমত গঠনে সহায়তা করত।
৩. বিধবাবিবাহকে সমর্থন: এই পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে wholeheartedly সমর্থন জানিয়েছিল এবং এই বিষয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করত।
৪. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা: নারীদের স্বাস্থ্য, গৃহকর্ম এবং সন্তান পালন বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে ‘বামাবোধিনী’ নারীদের স্বাবলম্বী ও সচেতন করে তুলতে চেয়েছিল। এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে নারীর অবহেলিত অবস্থান এবং তাদের উন্নতির প্রচেষ্টার একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।
৭. বিপিনচন্দ্র পালের ‘সত্তর বৎসর’ কীভাবে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর:
চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী ‘সত্তর বৎসর’ আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার একটি মূল্যবান উপাদান।
১. জাতীয়তাবাদের বিবর্তন: এই গ্রন্থে বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তন অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসি নেতা এবং পরিশেষে চরমপন্থী নেতা হয়ে ওঠার বিবরণ রয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের একটি ধারা বোঝা যায়।
২. উনিশ শতকের সমাজ: এই গ্রন্থ থেকে উনিশ শতকের গ্রাম বাংলার সামাজিক জীবন, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়।
৩. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট: ‘সত্তর বৎসর’-এ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিরোধ এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ পাওয়া যায়।
৪. വ്യക്തിగత అభిప్రాయాలు: ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাঁর মনোভাব এবং সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ইতিহাসকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে সাহায্য করে।
৮. নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
উত্তর:
নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:
১. নিম্নবর্গের গুরুত্ব: এই ইতিহাস চর্চায় রাজা-মহারাজা বা অভিজাতদের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মানুষ যেমন – কৃষক, শ্রমিক, নারী, দলিত ও প্রান্তিক মানুষদের গুরুত্ব দেওয়া হয়।
২. নতুন বিষয়বস্তু: রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের বদলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, যেমন – খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু করা হয়েছে।
৩. সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি: নতুন সামাজিক ইতিহাস কোনো একটি বিশেষ দিকের পরিবর্তে সমাজের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে চায়।
৪. ইতিহাসকে গণতান্ত্রিক করা: এর মূল লক্ষ্য হল ইতিহাসকে শুধুমাত্র精英দের কাহিনী থেকে মুক্ত করে সর্বসাধারণের ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
৯. আধুনিক ইতিহাস চর্চায় ফটোগ্রাফির গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
আধুনিক ইতিহাস চর্চায় ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র একটি অপরিহার্য উপাদান। এর গুরুত্বগুলি হল:
১. প্রামাণ্য দলিল: ফটোগ্রাফ কোনো ঘটনা, ব্যক্তি বা স্থানের একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে। ছবির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা সহজ হয়।
২. জীবন্ত প্রতিচ্ছবি: এটি অতীতকে জীবন্ত করে তোলে। এর মাধ্যমে উনিশ শতকের শহর, গ্রাম, মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব এবং স্থাপত্যের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়।
৩. সামাজিক বিশ্লেষণ: ফটোগ্রাফ থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক স্তরবিন্যাস, লিঙ্গ সম্পর্ক এবং cultural practices সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যেমন, ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের আলাদাভাবে ছবি তোলা তৎকালীন বর্ণবিদ্বেষের পরিচায়ক।
৪. ঘটনার সাক্ষী: বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন – দিল্লি দরবার, স্বাধীনতা সংগ্রাম বা দুর্ভিক্ষের ছবি সেই ঘটনাগুলির ভয়াবহতা বা জাকজমককে সরাসরি পাঠকের সামনে তুলে ধরে।
১০. টিকা লেখো: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা (Subaltern Studies)।
উত্তর:
‘Subaltern’ কথাটির অর্থ হল নিম্নবর্গীয় বা অধীনস্থ। যে ইতিহাসচর্চায় সমাজের উচ্চবর্গ বা অভিজাতদের পরিবর্তে কৃষক, শ্রমিক, মজুর, নারী, দলিত, আদিবাসী প্রভৃতি সাধারণ বা নিম্নবর্গের মানুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকেই নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বলা হয়।
১৯৮০-র দশকে রণজিৎ গুহর নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ায় এই ধারার সূত্রপাত হয়। এই গোষ্ঠীর মতে, প্রচলিত ইতিহাসে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও অবদানকে অভিজাতদের সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তাদের নিজস্ব ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পার্থ চ্যাটার্জি, শাহিদ আমিন, গৌতম ভদ্র প্রমুখ এই ধারার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক। এই চর্চা ইতিহাসকে আরও গণতান্ত্রিক ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে।
১১. টিকা লেখো: খেলার ইতিহাস।
উত্তর:
নতুন সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল খেলার ইতিহাস। ১৯৭০-এর দশকে ইংল্যান্ডে এর চর্চা শুরু হয়। খেলার ইতিহাস শুধুমাত্র খেলার নিয়মকানুন বা রেকর্ডের বিবরণ নয়, এর মাধ্যমে একটি সমাজের সংস্কৃতি, অবসর যাপন, অর্থনীতি এবং রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।
গুরুত্ব:
১. জাতীয়তাবাদ: খেলাধুলার মাধ্যমে অনেক সময় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে। যেমন, ১৯১১ সালে মোহনবাগানের আই.এফ.এ. শিল্ড জয় পরাধীন ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক নৈতিক জয় হিসেবে বিবেচিত হয়।
২. সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ: ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে খেলাধুলার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হত এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হত।
৩. সামাজিকীকরণ: খেলাধুলা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করে এবং সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে রিচার্ড হোল্ট, জে. এ. ম্যাঙ্গান এবং ভারতীয়দের মধ্যে রামচন্দ্র গুহ, বোরিয়া মজুমদার প্রমুখের নাম করা যায়।
১২. টীকা লেখো: পরিবেশের ইতিহাস।
উত্তর:
পরিবেশের ইতিহাস হল ইতিহাসের একটি আধুনিক শাখা যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়।
বিষয়বস্তু: এর বিষয়বস্তু হল বনভূমি, নদী, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য এবং এগুলির উপর মানুষের কার্যকলাপের প্রভাব। শিল্পায়ন, নগরায়ন, কৃষির বিস্তার কীভাবে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তা এই চর্চার মূল বিষয়।
গুরুত্ব:
১. সমস্যার উৎস নির্ণয়: এটি বর্তমান পরিবেশগত সমস্যাগুলির (যেমন – দূষণ, অরণ্য ধ্বংস) ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধানে সাহায্য করে।
২. পরিবেশ আন্দোলন: চিপকো বা নর্মদা বাঁচাও-এর মতো পরিবেশ আন্দোলনগুলির প্রেক্ষাপট বুঝতে পরিবেশের ইতিহাস চর্চা অপরিহার্য।
৩. নীতি নির্ধারণ: অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পরিবেশ নীতি নির্ধারণে এই চর্চা সাহায্য করে।
র্যাচেল কারসনের ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ এই ধারার একটি দিকনির্দেশক গ্রন্থ।
১৩. ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ‘ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠি’র গুরুত্ব কী?
উত্তর:
জওহরলাল নেহরু তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি ‘Letters from a Father to his Daughter’ নামে সংকলিত হয়েছে। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এর গুরুত্ব হল:
১. বিশ্ব ইতিহাসের সহজপাঠ: এই চিঠিগুলিতে অত্যন্ত সহজ ভাষায় পৃথিবীর উৎপত্তি, মানব সভ্যতার বিকাশ এবং বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি কিশোর-কিশোরীদের ইতিহাস পাঠে আগ্রহী করে তোলে।
২. নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি: এর মাধ্যমে ইতিহাস, সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নেহরুর আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।
৩. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা: নেহরু এই চিঠিগুলিতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন জাতির মুক্তি সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন।
৪. সরল ভাষার ব্যবহার: কোনো জটিল তত্ত্ব বা তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত না করে, সহজ ও ঘরোয়া ভাষায় ইতিহাসকে তুলে ধরা এই চিঠিগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
১৪. নারী ইতিহাসের উপর একটি টীকা লেখো।
উত্তর:
ইতিহাসের যে শাখায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা, তাদের সামাজিক অবস্থান, অধিকার, বঞ্চনা এবং অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে নারী ইতিহাস বলা হয়। ১৯৭০-এর দশক থেকে এই ধারার চর্চা জনপ্রিয়তা লাভ করে।
উদ্দেশ্য:
১. প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করা এবং ইতিহাসে নারীর উপেক্ষিত ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করা।
২. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া।
৩. অতীতে নারীদের উপর হওয়া অত্যাচার ও বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করা।
৪. ইতিহাসের লিঙ্গীয় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।
ভারতে নারী ইতিহাস চর্চায় জেরাল্ডিন ফোর্বস, বন্দনা শিবা, নীরা দেশাই প্রমুখের অবদান উল্লেখযোগ্য। সরলাদেবী চৌধুরাণীর ‘জীবনের ঝরাপাতা’ বা মণিকুন্তলা সেনের ‘সেদিনের কথা’ নারী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
১৫. আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চায় চলচ্চিত্রের ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর:
আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চায় চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য-শ্রাব্য উপাদান (audio-visual source)।
১. সামাজিক প্রতিচ্ছবি: চলচ্চিত্র সমকালীন সমাজের রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, মানুষের জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন সমস্যার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। যেমন – ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে গ্রামীণ বাংলার এক নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।
২. ঐতিহাসিক ঘটনার দলিল: অনেক চলচ্চিত্র নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়, যা সেই ঘটনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। যেমন – ‘গান্ধী’ বা ‘সর্দার’।
৩. জনমত গঠন: চলচ্চিত্র অনেক সময় সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গঠনে সাহায্য করে। ‘নবান্ন’ নাটক (এবং পরে চলচ্চিত্র) পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহতা তুলে ধরেছিল।
৪. সীমাবদ্ধতা: তবে চলচ্চিত্র যেহেতু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়, তাই অনেক সময় পরিচালক ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করেন বা কাহিনিকে অতিরঞ্জিত করেন। তাই চলচ্চিত্রকে ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
১৬. টীকা লেখো: স্থানীয় ইতিহাস।
উত্তর:
কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র অঞ্চলের (যেমন – গ্রাম, শহর বা জেলা) ইতিহাসকে স্থানীয় ইতিহাস বলা হয়। এটি জাতীয় ইতিহাসের একটি অংশ হলেও এর নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে।
গুরুত্ব:
১. জাতীয় ইতিহাসের পরিপূরক: স্থানীয় ইতিহাস জাতীয় ইতিহাসের অনেক অজানা বা উপেক্ষিত অধ্যায়কে তুলে ধরে এবং ইতিহাসের ফাঁক পূরণ করে।
২. আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সন্ধান: এর মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের বিশেষ সামাজিক প্রথা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোকশিল্প এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়।
৩. সাধারণ মানুষের ইতিহাস: স্থানীয় ইতিহাস মূলত সাধারণ মানুষের কথা বলে, যা জাতীয় স্তরের ইতিহাসে প্রায়শই উপেক্ষিত থাকে।
৪. উদাহরণ: রাধারমণ সাহার ‘পাবনা জেলার ইতিহাস’, কুমুদনাথ মল্লিকের ‘নদীয়া কাহিনী’ বা বিনয় ঘোষের ‘কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত’ উল্লেখযোগ্য স্থানীয় ইতিহাসের গ্রন্থ।
১৭. ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনগুলি আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর:
ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনগুলি আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
১. বিপ্লবী কার্যকলাপের তথ্য: ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য তাদের উপর নজরদারি চালাত। গোয়েন্দা রিপোর্টগুলি থেকে বিভিন্ন বিপ্লবী দল, তাদের সদস্য, কার্যকলাপ এবং গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।
২. নেতাদের মূল্যায়ন: এই রিপোর্টগুলিতে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতার কার্যকলাপ ও তাদের প্রভাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব মূল্যায়ন থাকে, যা থেকে সেই নেতাদের গুরুত্ব বোঝা যায়।
৩. কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের তথ্য: সরকার বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখত। গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে এই আন্দোলনগুলির সংগঠন ও নেতাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।
৪. সীমাবদ্ধতা: তবে এই রিপোর্টগুলি ব্রিটিশদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এবং প্রায়শই অতিরঞ্জিত। বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে এখানে ‘ষড়যন্ত্র’ বা ‘সন্ত্রাস’ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা এর প্রধান সীমাবদ্ধতা।
১৮. টীকা লেখো: যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস।
উত্তর:
যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস আধুনিক ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তন বোঝা যায়।
১. অর্থনৈতিক প্রভাব: রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ডাক ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতির ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন সহজ হয়, যা অর্থনীতির বিকাশে সাহায্য করে। ব্রিটিশরা মূলত তাদের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থেই ভারতে রেলপথ নির্মাণ করেছিল।
২. সামাজিক প্রভাব: যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের মধ্যে যাতায়াত বাড়ে, যা সামাজিক ভেদাভেদ কমাতে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে সাহায্য করে।
৩. রাজনৈতিক প্রভাব: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্রিটিশদের পক্ষে ভারতের বিশাল সাম্রাজ্যকে শাসন করা এবং বিদ্রোহ দমন করা সহজ করে দিয়েছিল। আবার, همین ব্যবস্থা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের পক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে জনমত গঠন করাও সহজ করে দিয়েছিল।
১৯. টীকা লেখো: দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস।
উত্তর:
ইতিহাসের যে শাখায় চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি দৃশ্যশিল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস বলে।
গুরুত্ব:
১. সামাজিক প্রতিফলন: দৃশ্যশিল্পে সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। যেমন, উনিশ শতকের পটচিত্রে বা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রে তৎকালীন বাবু সংস্কৃতির সমালোচনা দেখা যায়।
২. রাজনৈতিক বার্তা: অনেক সময় শিল্পীরা তাদের ছবির মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা দেন। যেমন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ ছবিটি স্বদেশী যুগে জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল।
৩. ঐতিহাসিক দলিল: ফটোগ্রাফি বা বিভিন্ন চিত্রকলা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে।
দৃশ্যশিল্পের ইতিহাস আমাদের কেবল শিল্পের নান্দনিক দিকটিই নয়, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝতেও সাহায্য করে।
২০. সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর:
সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:
১. প্রকাশের সময়: সংবাদপত্র সাধারণত দৈনিক প্রকাশিত হয় এবং প্রতিদিনের টাটকা খবর পরিবেশন করে। অন্যদিকে, সাময়িকপত্র একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর (যেমন – সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক) প্রকাশিত হয়।
২. বিষয়বস্তু: সংবাদপত্রের মূল বিষয় হল সাম্প্রতিক ঘটনা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও খেলার খবর। সাময়িকপত্রে খবরের পাশাপাশি সাহিত্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা, গল্প, কবিতা ইত্যাদি গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা স্থান পায়।
৩. স্থায়িত্ব: সংবাদপত্রের আবেদন সাময়িক এবং এর আয়ু একদিন। কিন্তু সাময়িকপত্রের সাহিত্যমূল্য ও গভীর আলোচনার জন্য এর আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৪. উদাহরণ: ‘The Times of India’ একটি সংবাদপত্র, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ একটি সাময়িকপত্র।
২১. ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী?
উত্তর:
আধুনিক ইতিহাস চর্চায় ইন্টারনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি হল:
সুবিধা:
১. সহজলভ্যতা: ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের লাইব্রেরি, মহাফেজখানা বা জাদুঘরের ডিজিটাল উপাদান (বই, নথি, ছবি) সহজেই পাওয়া যায়।
২. তথ্যের প্রাচুর্য: যেকোনো বিষয়ে বিপুল পরিমাণ তথ্য ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া সম্ভব।
অসুবিধা:
১. নির্ভরযোগ্যতার অভাব: ইন্টারনেটে প্রাপ্ত সব তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়। এখানে প্রচুর ভুল, বিকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য থাকে, যা যাচাই করা কঠিন।
২. তথ্যের স্থায়িত্বহীনতা: অনেক সময় ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে মূল্যবান তথ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
২২. ‘ইতিহাসের ধারণা’ অধ্যায়টি পাঠের গুরুত্ব কী?
উত্তর:
‘ইতিহাসের ধারণা’ অধ্যায়টি পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম:
১. ইতিহাসের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা: এই অধ্যায়টি আমাদের জানায় যে, ইতিহাস শুধু রাজা-বাদশাহর যুদ্ধ বা বংশাবলীর কাহিনী নয়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, খেলাধুলা, খাদ্যাভ্যাস, শিল্পচর্চা—সবকিছুই ইতিহাসের অন্তর্গত।
২. নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ: এটি আমাদের প্রচলিত ইতিহাস চর্চার সীমাবদ্ধতাগুলি ধরিয়ে দেয় এবং নারী, নিম্নবর্গ বা পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখার একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।
৩. উপাদানের বৈচিত্র্য: ইতিহাস রচনার জন্য কী কী ধরনের উপাদান (যেমন- আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ) ব্যবহার করা যায় এবং সেগুলির সুবিধা-অসুবিধা কী, তা জানতে সাহায্য করে।
৪. ইতিহাস পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি: বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে ইতিহাস পাঠ আরও আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।
২৩. টীকা লেখো: খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস।
উত্তর:
খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস হল নতুন সামাজিক ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় শাখা। এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের খাদ্যের প্রকার, রান্নার পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তন এবং তার সঙ্গে জড়িত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
গুরুত্ব:
১. সাংস্কৃতিক পরিচয়: খাদ্যাভ্যাস একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন, বাঙালির মাছ-ভাত বা রসগোল্লা তার পরিচয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।
২. সামাজিক স্তরবিন্যাস: কী ধরনের খাবার খাওয়া হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করে অতীতে সামাজিক স্তরবিন্যাস বোঝা যেত।
৩. অর্থনৈতিক অবস্থা: কোনো অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস থেকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।
৪. বিশ্বায়ন ও বিনিময়: এর মাধ্যমে জানা যায় কীভাবে এক দেশের খাবার অন্য দেশে জনপ্রিয় হয়েছে। যেমন, ভারতে পোর্তুগিজদের মাধ্যমে আলু, লঙ্কা বা চিনা খাবারের আগমন।
২৪. উনিশ শতকের বাংলায় নাট্যচর্চার ইতিহাস কীভাবে সমকালীন সমাজের প্রতিফলন ঘটায়?
উত্তর:
উনিশ শতকের বাংলায় নাট্যচর্চা ছিল সমকালীন সমাজের এক জীবন্ত দর্পণ।
১. সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন: তৎকালীন নাটকগুলিতে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন—কুলীন প্রথা, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে আসত। যেমন, রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’।
২. ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা: অনেক নাটকে ব্রিটিশ শাসনের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক, যা নীলকরদের অত্যাচারের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছিল।
৩. জাতীয়তাবাদের প্রচার: বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাটক, যেমন—গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘সিরাজদ্দৌলা’ বা ‘মীরকাশিম’ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করা হত এবং মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত।
এইভাবে, উনিশ শতকের নাটকগুলি শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, সেগুলি ছিল সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের এক শক্তিশালী হাতিয়ার।
২৫. বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব কী?
উত্তর:
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস চর্চা আধুনিক ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর গুরুত্ব হল:
১. সভ্যতার অগ্রগতি বোঝা: এই চর্চার মাধ্যমে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগান্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কীভাবে মানুষের জীবনযাত্রাকে বদলে দিয়েছে, তা বোঝা যায়।
২. ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট: ঔপনিবেশিক ভারতে কীভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ঘটেছিল এবং তার ফলে দেশীয় জ্ঞানচর্চা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা জানা যায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা এর একটি উদাহরণ।
৩. ভারতীয়দের অবদান: এই ইতিহাস চর্চা থেকে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহার মতো ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতিকূলতার মধ্যে গবেষণার কথা জানা যায়, যা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।
৪. জনস্বাস্থ্যের বিবর্তন: বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, তার চিকিৎসা এবং সরকারি জনস্বাস্থ্য নীতির বিবর্তন সম্পর্কে জানতে চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস অপরিহার্য।
Class 10 Class 10 History chapter 1
ইতিহাসের ধারণা class 10 প্রশ্ন উত্তর MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 History ইতিহাসের ধারণা Question Answer