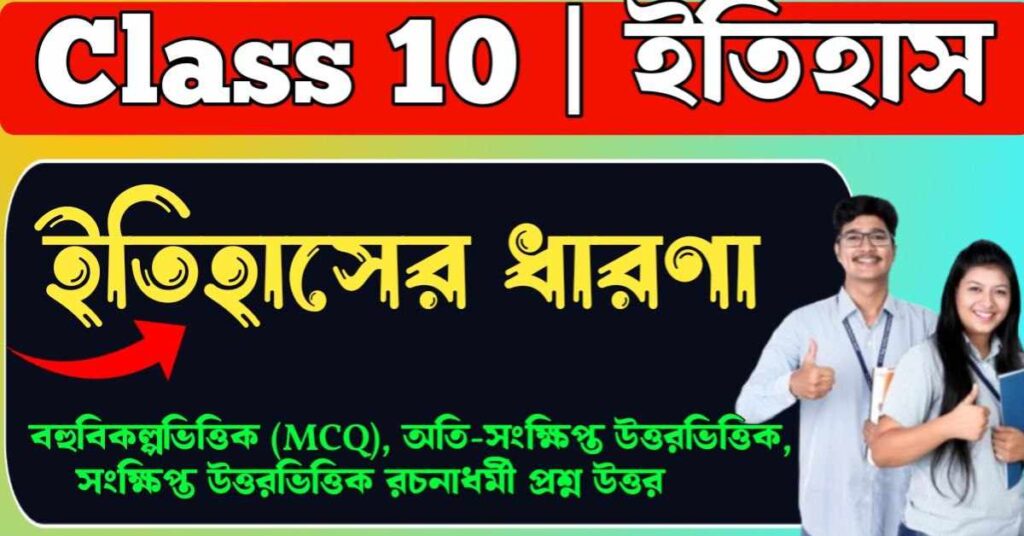সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. সতীদাহ প্রথা রদ হয়—
২. ‘ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৩. ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—
৪. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৫. ‘নববিধান ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৬. ‘সর্বধর্ম সমন্বয়ের’ আদর্শ প্রচার করেন—
৭. বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়—
৮. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন—
৯. ‘যত মত তত পথ’— উক্তিটি কার?
১০. ‘নব্যবঙ্গ’ বা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠীর প্রবর্তক ছিলেন—
১১. ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
১২. ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন—
১৩. ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ‘ম্যাগনাকার্টা’ বলা হয়—
১৪. শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ যোগদান করেন—
১৫. ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’র সম্পাদক ছিলেন—
১৬. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কার আমলে?
১৭. ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন—
১৮. ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন—
১৯. ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি কার রচনা?
২০. ভারতে প্রথম মহিলা স্নাতক ছিলেন—
২১. ‘চুঁইয়ে পড়া নীতি’ (Downward Filtration Theory)র প্রবক্তা ছিলেন—
২২. ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন—
২৩. ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ’-এর নেতা ছিলেন—
২৪. শ্রীরামপুরের ‘ত্রয়ী’ নামে পরিচিত ছিলেন—
২৫. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন—
২৬. ‘The publisher of Nil Durpan’ নামে কার বিচার হয়েছিল?
২৭. ‘নব্য বেদান্ত’ প্রচার করেন—
২৮. ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
২৯. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন—
৩০. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী ছিলেন—
৩১. ‘ভারত পথিক’ বলা হয়—
৩২. ‘তিন আইন’ (Act III) পাস হয়—
৩৩. ‘প্রাচ্য’ ও ‘পাশাত্যবাদী’ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান—
৩৪. ‘ব্রাহ্মিকা শাড়ি’ পরার রীতি চালু করেন—
৩৫. ‘Academic Association’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৩৬. ‘হিন্দু কলেজের’ বর্তমান নাম কী?
৩৭. ‘লালন ফকির’ ছিলেন একজন—
৩৮. ‘হুতোম’ কার ছদ্মনাম ছিল?
৩৯. ‘হিন্দু মেলার’ অপর নাম কী ছিল?
৪০. ‘বেথুন স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৪১. ‘বামাবোধিনী’ একটি —
৪২. ‘কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৪৩. ‘ব্রাহ্ম ধর্মের অনুষ্ঠান’ পদ্ধতি কে রচনা করেন?
৪৪. স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটি বই হল—
৪৫. ‘শিক্ষা সমন্বয়’-এর আদর্শ কার?
৪৬. ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ রচনা করেন—
৪৭. ‘ধর্মসভার’ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—
৪৮. বাংলার নবজাগরণকে ‘তথাকথিত নবজাগরণ’ বলেছেন—
৪৯. ‘দিকদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—
৫০. সতীদাহ প্রথা রদ করেন—
৫১. ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৫২. ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
৫৩. ‘এনকোয়ারার’ (Enquirer) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—
৫৪. ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়—
৫৫. ‘পটলডাঙা অ্যাকাডেমি’র বর্তমান নাম হল—
৫৬. ‘সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি’ (GCPI) গঠিত হয়—
৫৭. ‘কেরানির সংস্কৃতি’ (Clerk Culture) গড়ে ওঠে যার ফলে, তা হল—
৫৮. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা এম. এ. ছিলেন—
৫৯. ‘বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী’ যুক্ত ছিলেন—
৬০. ‘আলালের ঘরের দুলাল’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
৬১. ‘বেদান্ত কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৬২. ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়—
৬৩. শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন—
৬৪. ‘মেকলে মিনিটস’ পেশ করা হয়—
৬৫. ‘হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদে’র অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন—
৬৬. ‘হরিনাথ মজুমদারে’র ছদ্মনাম ছিল—
৬৭. ‘বেঙ্গল গেজেট’ প্রকাশ করেন—
৬৮. ‘নবজাগরণ’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন—
৬৯. ‘দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়’ যুক্ত ছিলেন—
৭০. ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনটি রচনা করেন—
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. কবে সতীদাহ প্রথা রদ হয়?
উত্তর: ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে।
২. ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।
৩. ‘বামাবোধিনী’ কী ধরনের পত্রিকা ছিল?
উত্তর: এটি ছিল একটি নারী বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।
৪. হিন্দু কলেজের বর্তমান নাম কী?
উত্তর: প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: কেশবচন্দ্র সেন।
৬. সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ কে প্রচার করেন?
উত্তর: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।
৭. বিধবা বিবাহ আইন কে পাস করেন?
উত্তর: লর্ড ডালহৌসি (লর্ড ক্যানিং-এর আমলে কার্যকরী হয়)।
৮. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য কে ছিলেন?
উত্তর: তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং।
৯. ‘যত মত তত পথ’— কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: সব ধর্মই সত্য এবং সব ধর্মের লক্ষ্যই এক— ईश्वर प्राप्ति।
১০. ডিরোজিওর অনুগামীদের কী বলা হত?
উত্তর: নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল।
১১. ‘হুতুম’ কার ছদ্মনাম ছিল?
উত্তর: কালীপ্রসন্ন সিংহের।
১২. ‘নীলদর্পণ’ নাটকের বিষয়বস্তু কী ছিল?
উত্তর: নীলকর সাহেবদের দ্বারা বাঙালি নীলচাষিদের উপর অত্যাচার ও শোষণ।
১৩. উডের ডেসপ্যাচ কবে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে।
১৪. স্বামী বিবেকানন্দের আসল নাম কী ছিল?
উত্তর: নরেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৫. ‘কাঙাল হরিনাথ’ কার ছদ্মনাম ছিল?
উত্তর: হরিনাথ মজুমদারের।
১৬. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে।
১৭. ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে।
১৮. ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: অক্ষয়কুমার দত্ত।
১৯. ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দ।
২০. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক কে ছিলেন?
উত্তর: কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু।
২১. ‘চুঁইয়ে পড়া নীতি’ কী?
উত্তর: উচ্চবিত্ত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করলে তাদের মাধ্যমে তা ক্রমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে—এই নীতি।
২২. ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকা কেন বিখ্যাত?
উত্তর: সাঁওতাল বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহকে সমর্থন করার জন্য।
২৩. ব্রাহ্ম সমাজের একটি বিভাজনের নাম লেখো।
উত্তর: আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।
২৪. শ্রীরামপুর মিশন কারা প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড।
২৫. ‘নব্য বেদান্ত’ কী?
উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্তের আধুনিক, যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী ব্যাখ্যা।
২৬. আত্মীয় সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।
২৭. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: ভারতে আগত ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য।
২৮. ‘তিন আইন’ কী?
উত্তর: কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে পাস হওয়া বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ এবং অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকৃতিদানকারী আইন।
২৯. প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে মূল বিতর্ক কী ছিল?
উত্তর: ভারতে দেশীয় প্রাচ্য শিক্ষা না কি ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে— এই নিয়ে বিতর্ক।
৩০. ‘সমাচার দর্পণ’ কে প্রকাশ করেন?
উত্তর: শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন (সম্পাদক: জন ক্লার্ক মার্শম্যান)।
৩১. ‘প্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদী’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে।
৩২. বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় কে সহযোগিতা করেছিলেন?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৩৩. ‘নবজাগরণ’ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: নবজাগরণ বা রেনেসাঁস কথাটির অর্থ হল ‘পুনর্জন্ম’ বা নতুন করে জেগে ওঠা।
৩৪. ‘ব্রাহ্মিকা শাড়ি’ কী?
উত্তর: জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রবর্তিত আধুনিক রুচিসম্মত শাড়ি পরার একটি বিশেষ রীতি।
৩৫. নব্যবঙ্গের একজন সদস্যের নাম লেখো।
উত্তর: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামতনু লাহিড়ী।
৩৬. ‘সিমলা ডেপুটেশন’ কী?
উত্তর: শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য উডের ডেসপ্যাচের আগে লর্ড ডালহৌসির কাছে একটি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ। (এটি শিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়ের বিষয়)।
৩৭. লালন ফকির কে ছিলেন?
উত্তর: উনিশ শতকের একজন মানবতাবাদী ও মরমী বাউল সাধক।
৩৮. ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ কার ছদ্মনাম ছিল?
উত্তর: প্যারিচাঁদ মিত্রের।
৩৯. ‘হিন্দু মেলা’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: নবগোপাল মিত্র।
৪০. কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে।
৪১. ‘ব্রাহ্ম ধর্মের অনুষ্ঠান’ কী?
উত্তর: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রাহ্মদের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ।
৪২. ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ কে রচনা করেন?
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।
৪৩. ‘ধর্মসভা’ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: সতীদাহ প্রথা রদ আইনের বিরোধিতা করতে এবং সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে।
৪৪. বাংলার নবজাগরণকে ‘এলিস্ট আন্দোলন’ কে বলেছেন?
উত্তর: অনিল শীল।
৪৫. ‘দিকদর্শন’ কী ধরনের পত্রিকা ছিল?
উত্তর: এটি ছিল বাংলা ভাষার প্রথম মাসিক সাময়িকপত্র।
৪৬. সতীদাহ প্রথা রদে কোন ভারতীয়র ভূমিকা প্রধান ছিল?
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়ের।
৪৭. রামকৃষ্ণ মিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে।
৪৮. ‘বর্ণপরিচয়’ এর লেখক কে?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৪৯. ‘পার্থেনন’ (Parthenon) পত্রিকাটি কারা প্রকাশ করত?
উত্তর: নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী।
৫০. ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক কে ছিলেন?
উত্তর: রেভারেন্ড জেমস লঙ।
৫১. ডেভিড হেয়ার কে ছিলেন?
উত্তর: স্কটল্যান্ডের একজন ঘড়ি-ব্যবসায়ী, যিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।
৫২. ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: কেশবচন্দ্র সেন।
৫৩. ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’— এই আদর্শ কার?
উত্তর: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের।
৫৪. ‘মেকলে মিনিটস’ কী?
উত্তর: টমাস ব্যাবিংটন মেকলের নেতৃত্বে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে লেখা বিখ্যাত প্রতিবেদন।
৫৫. বিধবা বিবাহ আন্দোলনে কার ভূমিকা প্রধান ছিল?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের।
৫৬. ‘সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি’র সভাপতির নাম কী ছিল?
উত্তর: টমাস ব্যাবিংটন মেকলে।
৫৭. ‘চলতি বাংলা গদ্যের জনক’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: প্যারিচাঁদ মিত্রকে (টেকচাঁদ ঠাকুর)।
৫৮. ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: স্যার উইলিয়াম জোনস।
৫৯. ‘গদর’ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উত্তর: লালা হরদয়াল। (বিপ্লবী কার্যকলাপ অধ্যায়ের প্রশ্ন)।
৬০. ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং তাদের বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন করা। এর মাধ্যমে নারীদের লেখা প্রকাশ করে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলাও একটি লক্ষ্য ছিল।
২. ‘নব্যবঙ্গ’ বা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ কাদের বলা হত?
উত্তর: উনিশ শতকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুগামী একদল যুক্তিবাদী তরুণ ছাত্রদের ‘নব্যবঙ্গ’ বা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ বলা হত। তারা প্রচলিত কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির তীব্র বিরোধী ছিলেন।
৩. ‘ব্রাহ্মসমাজ’ কেন বিভক্ত হয়েছিল?
উত্তর: কেশবচন্দ্র সেনের কিছু কার্যকলাপ, যেমন—নিজের নাবালিকা কন্যার সঙ্গে কোচবিহারের রাজার বিবাহ দেওয়া (তিন আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে) এবং নিজেকে ‘অবতার’ হিসেবে দাবি করা নিয়ে মতবিরোধের জেরে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়েছিল।
৪. উডের ডেসপ্যাচকে (১৮৫৪) ‘ম্যাগনাকার্টা’ বলা হয় কেন?
উত্তর: উডের ডেসপ্যাচে ভারতে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি সুসংহত শিক্ষানীতির রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। এর সুপারিশ অনুসারেই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই একে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার ‘মহাসনদ’ বা ‘ম্যাগনাকার্টা’ বলা হয়।
৫. শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ‘সর্বধর্ম সমন্বয়’ আদর্শটি কী?
উত্তর: শ্রীরামকৃষ্ণের ‘সর্বধর্ম সমন্বয়’ আদর্শের মূল কথা হল, সব ধর্মই সত্য এবং ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র (‘যত মত, তত পথ’)। তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে এক সমন্বয়বাদী বার্তা প্রচার করেছিলেন।
৬. ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থটির গুরুত্ব কী?
উত্তর: কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ উনিশ শতকের কলকাতার বাবু সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। এর মাধ্যমে লেখক ব্যঙ্গ ও শ্লেষের দ্বারা তৎকালীন সমাজের ভণ্ডামি, নৈতিক অবক্ষয় এবং ইংরেজি অনুকরণপ্রিয়তাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন।
৭. নারীশিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কী ছিল?
উত্তর: নারীশিক্ষায় বিদ্যাসাগরের অবদান অপরিসীম। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে ‘বেথুন স্কুল’ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন।
৮. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক কী?
উত্তর: ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আগে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ দেশীয় ভাষায় প্রাচ্য জ্ঞানচর্চায় ব্যয় হবে, না কি ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চায় ব্যয় হবে— এই নিয়ে ‘সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি’র সদস্যদের মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল, তাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক নামে পরিচিত।
৯. ডেভিড হেয়ার স্মরণীয় কেন?
উত্তর: ডেভিড হেয়ার ছিলেন বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) এবং পটলডাঙা অ্যাকাডেমি (হেয়ার স্কুল) প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
১০. ‘নীলদর্পণ’ নাটক সমাজে কী প্রভাব ফেলেছিল?
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক নীলকরদের অত্যাচারের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে শিক্ষিত বাঙালি समाजকে নাড়া দিয়েছিল। এটি নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করে এবং নীল বিদ্রোহের সমর্থনে জনমত গঠনে সহায়তা করেছিল।
১১. মেকলে মিনিটস কী?
উত্তর: ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ‘সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি’র সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে যে জোরালো সুপারিশপত্র বা প্রতিবেদন পেশ করেন, তাই ‘মেকলে মিনিটস’ নামে পরিচিত। এর ভিত্তিতেই ভারতে ইংরেজি শিক্ষা নীতি গৃহীত হয়।
১২. স্বামী বিবেকানন্দের ‘নব্য বেদান্ত’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়ে যে নতুন মানবতাবাদী ও প্রয়োগমূলক বেদান্তের ধারণা দেন, তাই ‘নব্য বেদান্ত’ নামে পরিচিত। এর মূল কথা হল ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’।
১৩. উনিশ শতকের নবজাগরণের দুটি সীমাবদ্ধতা লেখো।
উত্তর: (১) এই নবজাগরণ মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক এবং উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। (২) মুসলিম সমাজ এবং গ্রামের সাধারণ মানুষ এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়নি।
১৪. ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ ছিল গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। এই পত্রিকা নির্ভীকভাবে গ্রামীণ মানুষের উপর জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করত, যা সে যুগে বিরল ছিল।
১৫. ‘তিন আইন’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে একটি আইন পাস করে, যা ‘তিন আইন’ নামে পরিচিত। এর দ্বারা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং অসবর্ণ বিবাহকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
১৬. লালন ফকির কে ছিলেন?
উত্তর: লালন ফকির ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও গীতিকার। তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতাবাদের কথা প্রচার করেন।
১৭. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্রদের ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক শিক্ষাদান করা।
১৮. ‘ধর্মসভা’ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ‘ধর্মসভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধিতা করা এবং সতীদাহ প্রথা রদ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা।
১৯. ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিভাজনের কারণ কী ছিল?
উত্তর: কেশবচন্দ্র সেন তাঁর নাবালিকা কন্যার সঙ্গে কোচবিহারের নাবালক রাজার বিবাহ দিলে ‘তিন আইন’ লঙ্ঘিত হয়। এর প্রতিবাদে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসুর মতো নবীন ব্রাহ্ম নেতারা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন।
২০. ‘চুঁইয়ে পড়া নীতি’ (Filtration Theory) ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
উত্তর: এই নীতি ব্যর্থ হয়েছিল কারণ উচ্চবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করে নিজেদের আখের গোছাতেই বেশি আগ্রহী ছিল।
২১. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অবদান কী?
উত্তর: বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন অন্যতম প্রচারক, যিনি প্রথম ব্রাহ্ম সমাজে ‘নগর সংকীর্তন’ প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাহ্ম ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।
২২. পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন, চার্চ মিশনারি সোসাইটি প্রভৃতি খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থাগুলি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তারা অসংখ্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এবং ছাপাখানার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে, যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার।
২৩. ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনটির বিষয়বস্তু কী?
উত্তর: মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনটির বিষয়বস্তু হল উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একদল তরুণের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও নৈতিক অধঃপতন। এর মাধ্যমে তিনি নব্যশিক্ষিত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে কটাক্ষ করেছেন।
২৪. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় মধুসূদন গুপ্তের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় হিসেবে শবব্যবচ্ছেদ (dissection) করেন। এর ফলে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যায় আধুনিক শরীরবিদ্যা চর্চার পথ খুলে যায় এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর হয়।
২৫. ‘ক্যালাইডোস্কোপ’ (Kaleidoscope) পত্রিকাটি কারা প্রকাশ করত?
উত্তর: এটি ছিল ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামী নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর একটি ইংরেজি পত্রিকা। এর মাধ্যমে তারা তাদের যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা প্রকাশ করত।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. নারীশিক্ষার প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করো।
উত্তর:
উনিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অবিস্মরণীয়।
ভূমিকা: তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীসমাজের উন্নতি ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়।
অবদান:
১. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: সরকারি শিক্ষা পরিদর্শক হিসেবে তিনি নিজের ক্ষমতায় ও খরচে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
২. বেথুন স্কুলকে সাহায্য: তিনি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে ‘হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়’ (পরে বেথুন স্কুল) প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৩. সামাজিক বাধা অতিক্রম: তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন করা সহজ ছিল না। বিদ্যাসাগর সমস্ত সামাজিক বাধা ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করে এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।
উপসংহার: তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই বাংলায় নারীশিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত করে।
২. ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থে সমকালীন কলকাতার সমাজচিত্র কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
উত্তর:
কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনামে লেখা ‘হুতুম প্যাঁচার নকশা’ উনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবনের এক অনবদ্য দলিল।
সমাজচিত্র:
১. বাবু সংস্কৃতি: এই গ্রন্থে কলকাতার নব্য-ধনী ‘বাবু’ সম্প্রদায়ের বিলাসব্যসন, ইংরেজি অনুকরণপ্রিয়তা এবং অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করা হয়েছে।
২. ধর্মীয় ভণ্ডামি: তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, যেমন – চড়ক, বারোয়ারি পূজা, রথযাত্রা ইত্যাদির আড়ালে যে ভণ্ডামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা চলত, তার নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে।
৩. চলিত ভাষার ব্যবহার: হুতোমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে কথ্য বা চলিত ভাষাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। তাঁর ভাষা ছিল সহজ, সরল এবং শ্লেষাত্মক।
৪. সামাজিক পরিবর্তন: পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কলকাতার সমাজে যে দ্রুত পরিবর্তন আসছিল, তার একটি জীবন্ত ছবি এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এটি নিছক ব্যঙ্গ রচনা নয়, এটি একটি মূল্যবান সমাজ-নথি।
৩. স্বামী বিবেকানন্দের ‘নব্য বেদান্ত’ সম্পর্কে আলোচনা করো।
উত্তর:
স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়ে এক নতুন, যুগোপযোগী ও মানবতাবাদী দর্শন প্রচার করেন, যা ‘নব্য বেদান্ত’ নামে পরিচিত।
বৈশিষ্ট্য:
১. মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা: নব্য বেদান্তের মূল কথা হল, ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’। বিবেকানন্দ মনে করতেন, ঈশ্বর শুধুমাত্র মন্দিরে বা মূর্তিতে সীমাবদ্ধ নন, তিনি প্রতিটি জীবের মধ্যে বিরাজমান। তাই দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত মানুষের সেবাই হল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর উপাসনা।
২. আত্মবিশ্বাসের বার্তা: তিনি বেদান্তের ‘আমিই ব্রহ্ম’ (অহং ব্রহ্মাস্মি) তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেন।
৩. বাস্তববাদী ও প্রয়োগমূলক: তিনি বেদান্তকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক আলোচনার বিষয় না রেখে দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের কাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন।
৪. জাতিভেদ বিরোধিতা: নব্য বেদান্ত জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে এবং সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা বলে।
৪. উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের চরিত্র বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
উনিশ শতকে বাংলায় যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটেছিল, তার চরিত্র বা প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।
প্রকৃতি:
১. যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ: এই নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ। এর প্রভাবে মানুষ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে শেখে।
২. পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সংস্পর্শে এসেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ আধুনিক মনন ও চেতনার অধিকারী হয়।
৩. সংস্কার আন্দোলন: এই জাগরণের ফলে সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারীশিক্ষার প্রসারের মতো বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।
সীমাবদ্ধতা:
তবে এই নবজাগরণের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এটি মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম সমাজ বা গ্রামীণ जनता এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়নি। তাই অনেকে একে ‘শহুরে精英দের আন্দোলন’ বলে সমালোচনা করেন।
৫. টীকা লেখো: নব্যবঙ্গ আন্দোলন।
উত্তর:
উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁর অনুগামী একদল তরুণ ছাত্র যে প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তাই নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন নামে পরিচিত।
বৈশিষ্ট্য:
১. যুক্তিবাদ: তারা কোনো কিছু বিনা বিচারে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না এবং সব কিছুকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতেন।
২. কুসংস্কার বিরোধিতা: তারা হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা, পৌত্তলিকতা এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করতেন।
৩. সংগঠন: তারা ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘পার্থেনন’, ‘এনকোয়ারার’ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করতেন।
ব্যর্থতার কারণ: তবে তাদের আন্দোলন 지나치게 নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক ছিল। গঠনমূলক কাজের অভাব এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়।
৬. বাংলার সমাজ সংস্কারে ব্রাহ্মসমাজের অবদান কী ছিল?
উত্তর:
উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ সংস্কারে ব্রাহ্মসমাজের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অবদান:
১. একেশ্বরবাদ প্রচার: রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে এবং উপনিষদের উপর ভিত্তি করে একেশ্বরবাদের প্রচার করে।
২. সতীদাহ প্রথা রদ: রামমোহনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে, যার ফলে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এই প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ হয়।
৩. নারীশিক্ষার প্রসার: কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির পক্ষে জোরালো সওয়াল করে। ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশ এর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।
৪. অন্যান্য সংস্কার: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন জানান। এইভাবেই ব্রাহ্মসমাজ বাংলার আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৭. শিক্ষা বিস্তারে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক কী? এই বিতর্কের অবসান কীভাবে হয়?
উত্তর:
বিতর্ক: ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলে, সেই টাকা প্রাচ্য অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে, না কি পাশ্চাত্য অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে— এই নিয়ে ‘সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি’র (GCPI) সদস্যদের মধ্যে যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়, তাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক নামে পরিচিত। এইচ. টি. প্রিন্সেপ প্রমুখ প্রাচ্য শিক্ষার এবং আলেকজান্ডার ডাফ, সন্ডার্স প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন।
অবসান: এই বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে টমাস ব্যাবিংটন মেকলকে নিয়োগ করেন। মেকলে তাঁর বিখ্যাত ‘মিনিটস’-এ (১৮৩৫) জোরালোভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মত দেন। বেন্টিঙ্ক মেকলের প্রস্তাব গ্রহণ করলে এই বিতর্কের অবসান ঘটে এবং ভারতে সরকারি শিক্ষানীতি হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষাই গৃহীত হয়।
৮. চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভারতে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার প্রসারে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা ছিল যুগান্তকারী।
ভূমিকা:
১. পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রসার: এই কলেজই প্রথম ভারতে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এবং ইংরেজি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে।
২. শবব্যবচ্ছেদ প্রবর্তন: ভারতীয় সমাজে শবব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। এই কলেজের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৬ সালে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেন, যা আধুনিক শরীরবিদ্যা (Anatomy) চর্চার পথ খুলে দেয়।
৩. কুসংস্কার দূরীকরণ: মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং এর কার্যকলাপ ভারতীয়দের মন থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা কুসংস্কার দূর করতে সাহায্য করে।
৪. দক্ষ চিকিৎসক তৈরি: এই কলেজ থেকে বহু কৃতি ও দক্ষ চিকিৎসক তৈরি হন, যারা পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান এবং জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে সাহায্য করেন।
৯. ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকায় উনিশ শতকের গ্রামীণ বাংলার কী রূপ চিত্র ফুটে উঠেছে?
উত্তর:
হরিনাথ মজুমদার বা ‘কাঙাল হরিনাথ’ সম্পাদিত ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ উনিশ শতকের গ্রামীণ বাংলার এক বিশ্বস্ত দলিল।
গ্রামীণ চিত্র:
১. শোষণ ও অত্যাচার: এই পত্রিকায় গ্রামীণ সমাজের উপর জমিদার, মহাজন, নীলকর এবং ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীদের শোষণ ও অত্যাচারের বাস্তব চিত্র নির্ভীকভাবে তুলে ধরা হত।
২. কৃষকদের দুর্দশা: এতে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা, ফসলের অবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর নিয়মিত প্রকাশিত হত।
৩. সামাজিক সমস্যা: ‘গ্রামবার্ত্তা’ গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন—অশিক্ষা, কুসংস্কার, দলাদলি ইত্যাদির কথাও প্রকাশ করত।
৪. প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর: এটি শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন করত না, অসহায় গ্রামবাসীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল। এর ফলে হরিনাথকে বহুবার জমিদার ও নীলকরদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল।
১০. বাংলার নবজাগরণ কি শুধুই কলকাতা-কেন্দ্রিক ছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর:
উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক ছিল— এই মত বহুলাংশে সত্য।
যুক্তি:
১. কেন্দ্রস্থল: নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। হিন্দু কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাহ্মসমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানই কলকাতায় অবস্থিত ছিল।
২. অংশগ্রহণকারী: এই জাগরণের প্রধান কারিগর—রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা। অংশগ্রহণকারীরাও ছিলেন মূলত কলকাতার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণি।
৩. গ্রামীণ সমাজের বিচ্ছিন্নতা: এই জাগরণের ঢেউ বাংলার বিশাল গ্রামীণ অঞ্চলে পৌঁছায়নি। গ্রামের সাধারণ কৃষক, কারিগর এবং মুসলিম সমাজ এর দ্বারা প্রায় অস্পৃষ্ট ছিল। তাই ঐতিহাসিক অনিল শীল একে ‘A limited elist movement’ বা ‘সীমিত精英দের আন্দোলন’ বলে অভিহিত করেছেন। তবে, ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’র মতো কিছু ব্যতিক্রমও ছিল, যা গ্রামীণ সমস্যা তুলে ধরেছিল।
১১. ধর্মসংস্কার আন্দোলনে রামমোহন রায়ের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
রাজা রামমোহন রায় ছিলেন উনিশ শতকের ভারতের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ।
ভূমিকা:
১. একেশ্বরবাদ প্রচার: তিনি হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা ও বহু-ঈশ্বরবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। উপনিষদের উপর ভিত্তি করে তিনি এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন।
২. ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা: তাঁর একেশ্বরবাদী মতবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য তিনি ১৮২৮ সালে ‘ব্রাহ্মসভা’ (পরে ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল একটি সর্বজনীন উপাসনা গৃহ।
৩. শাস্ত্রের ব্যাখ্যা: তিনি বেদ-উপনিষদের ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ করে প্রমাণ করতে চান যে, হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হল একেশ্বরবাদ এবং সতীদাহের মতো প্রথার কোনো শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই।
৪. সমন্বয়বাদ: তিনি অন্যান্য ধর্ম, যেমন—ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ভালো দিকগুলিকেও গ্রহণ করার কথা বলেন।
১২. ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
দীনবন্ধু মিত্র রচিত ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০) নাটকটি উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।
ঐতিহাসিক গুরুত্ব:
১. নীলকরদের অত্যাচারের দলিল: এই নাটকটি নীলকর সাহেবদের অমানবিক শোষণ, অত্যাচার এবং নীলচাষিদের অসহায়তার এক জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী দলিল।
২. জনমত গঠন: নাটকটি শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে নীলচাষিদের দুর্দশার বিষয়ে সচেতন করে তোলে এবং তাদের সমর্থনে শক্তিশালী জনমত গঠনে সাহায্য করে।
৩. নীল বিদ্রোহে প্রভাব: এটি নীল বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাদের মনোবল বাড়িয়েছিল।
৪. আন্তর্জাতিক প্রভাব: মাইকেল মধুসূদন দত্তের করা ইংরেজি অনুবাদ ইউরোপেও আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে সরকার ‘নীল কমিশন’ গঠন করতে বাধ্য হয়।
১৩. টীকা লেখো: উডের প্রতিবেদন (Wood’s Despatch)।
উত্তর:
বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে বিস্তারিত প্রতিবেদন বা সুপারিশমালা পেশ করেন, তাই ‘উডের প্রতিবেদন’ বা ‘উডের ডেসপ্যাচ’ নামে পরিচিত।
সুপারিশসমূহ:
১. পৃথক শিক্ষাদপ্তর: প্রতিটি প্রদেশে একটি করে পৃথক জনশিক্ষা দপ্তর খোলার সুপারিশ করা হয়।
২. বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।
৩. শিক্ষার স্তরবিন্যাস: প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়—এই চারটি স্তরে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।
৪. নারীশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা: নারীশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
এই ব্যাপক ও সুসংহত পরিকল্পনার জন্য একে ‘ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার ম্যাগনাকার্টা’ বলা হয়।
১৪. শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল?
উত্তর:
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ধর্মীয় চিন্তাধারা ছিল সহজ, সরল এবং সমন্বয়বাদী।
বৈশিষ্ট্য:
১. সর্বধর্ম সমন্বয়: তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়। তিনি নিজে ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মমত সাধনা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সব ধর্মই সত্য এবং ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল ‘যত মত, তত পথ’।
২. মানবসেবা: তিনি বলতেন, ‘জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা’। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের সেবা করাই হল ঈশ্বরের সেবা। এই আদর্শ তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।
৩. সহজ ভাষায় ধর্মব্যাখ্যা: তিনি কোনো জটিল দর্শন বা শাস্ত্রীয় তর্কের পরিবর্তে সহজ-সরল গ্রাম্য উপমার মাধ্যমে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হত।
৪. মূর্তিপূজার সমর্থন: তিনি নিরাকার ঈশ্বরের পাশাপাশি সাকার বা মূর্তিপূজাকেও ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একটি পথ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
১৫. বাংলার নবজাগরণকে ‘ব্যর্থ রেনেসাঁস’ বলা হয় কেন?
উত্তর:
অনেক ঐতিহাসিক উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে ‘ব্যর্থ রেনেসাঁস’ বলে অভিহিত করেছেন কারণ এর কিছু গভীর সীমাবদ্ধতা ছিল।
ব্যর্থতার কারণ:
১. শহর-কেন্দ্রিকতা: এই জাগরণ ছিল মূলত কলকাতা শহর-কেন্দ্রিক এবং এর প্রভাব বাংলার বিশাল গ্রামাঞ্চলে পৌঁছায়নি।
২. হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধতা: এটি প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার বিশাল মুসলিম সমাজ এই জাগরণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল।
৩. মৌলিক চিন্তার অভাব: সমালোচকদের মতে, এই জাগরণে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ঘটেনি। এটি ছিল মূলত পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুকরণ।
৪. ব্রিটিশনির্ভরতা: সংস্কারকরা প্রায়শই ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করতেন এবং গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে আবেদন-নিবেদনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারণগুলির জন্য একে একটি ‘অসম্পূর্ণ’ বা ‘ব্যর্থ রেনেসাঁস’ বলা হয়।
১৬. সমাজ সংস্কারে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারে ডিরোজিওর অনুগামী নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল মূলত প্রথাবিরোধী ও সমালোচনামূলক।
ভূমিকা:
১. কুসংস্কারের বিরোধিতা: তারা হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা, পুরোহিততন্ত্র এবং অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন।
২. যুক্তিবাদ ও নারীস্বাধীনতার প্রচার: তারা যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নারীস্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেন। তারা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন।
৩. মত প্রকাশের স্বাধীনতা: ‘পার্থেনন’, ‘এনকোয়ারার’ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে তারা নির্ভীকভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন।
সীমাবদ্ধতা: তবে তাদের কার্যকলাপ মূলত ধ্বংসাত্মক বা নেতিবাচক সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোনো গঠনমূলক কর্মসূচি বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় তাদের আন্দোলন বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।
১৭. উনিশ শতকে নারী সমাজের উন্নয়নে ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
উনিশ শতকে নারী সমাজের উন্নয়নে উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।
ভূমিকা:
১. নারীশিক্ষার প্রচার: এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্যই ছিল নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো। এতে নিয়মিতভাবে শিক্ষিতা নারীদের কাহিনী, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরামর্শ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহজ আলোচনা প্রকাশিত হত।
২. আত্মপ্রকাশের সুযোগ: ‘বামাবোধিনী’ নারীদের নিজেদের লেখা প্রকাশের একটি মঞ্চ (platform) তৈরি করে দিয়েছিল, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করত।
৩. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি: এটি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করত।
৪. আধুনিক মনন গঠন: এই পত্রিকা বাঙালি নারীদের ঘরের কোণ থেকে বের করে এনে আধুনিক জগৎ সম্পর্কে জানতে এবং একটি আধুনিক মনন গঠনে সাহায্য করেছিল। প্রায় ষাট বছর ধরে এটি নারী জাগরণের অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে।
১৮. ‘তিন আইন’ (Act III of 1872) কী ছিল এবং এর গুরুত্ব কী?
উত্তর:
‘তিন আইন’: ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সক্রিয় উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যে আইনটি পাস করে, তা ‘তিন আইন’ বা ‘Native Marriage Act’ নামে পরিচিত। এই আইনের তিনটি প্রধান ধারা ছিল:
১. বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং বিয়ের জন্য পাত্রীর ন্যূনতম বয়স ১৪ ও পাত্রের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা।
২. বহুবিবাহ প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করা।
৩. অসবর্ণ বা ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া।
গুরুত্ব: এই আইনটি ছিল নারীমুক্তি এবং সামাজিক প্রগতিশীলতার পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি বিবাহ ব্যবস্থাকে একটি আধুনিক ও মানবিক রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। তবে দুঃখের বিষয়, স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন তাঁর নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিয়ে এই আইন লঙ্ঘন করেন, যার ফলে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়ে যায়।
১৯. টীকা লেখো: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ।
উত্তর:
রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম আন্দোলন যখন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার হাল ধরেন।
ভূমিকা:
১. তত্ত্ববোধিনী সভা: দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে ১৮৩৯ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র মাধ্যমে ব্রাহ্ম ভাবধারা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার শুরু করেন।
২. নতুন প্রাণসঞ্চার: ১৮৪৩ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে এই মৃতপ্রায় সংগঠনে নতুন প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ একটি সুসংগঠিত রূপ লাভ করে।
৩. ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা: তিনি ‘ব্রাহ্মধর্ম’ গ্রন্থ রচনা করেন এবং ব্রাহ্মদের জন্য নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি ও অনুশাসন চালু করেন। তিনিই প্রথম বেদকে অভ্রান্ত বলে মানতে অস্বীকার করেন।
৪. আদি ব্রাহ্মসমাজ: কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হলে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন অংশটি ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ’ নামে পরিচিত হয়।
২০. পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
রাজা রামমোহন রায়কে ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তক বলা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।
ভূমিকা:
১. পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থন: তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্কে জোরালোভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষ নেন এবং লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার দাবি জানান।
২. প্রতিষ্ঠান স্থাপন: তিনি কলকাতায় ‘অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল’ নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ডেভিড হেয়ারকে ‘হিন্দু কলেজ’ প্রতিষ্ঠায় এবং আলেকজান্ডার ডাফকে ‘জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন’ (স্কটিশ চার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন।
৩. বেদান্ত কলেজ: তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় সাধনের জন্য ১৮২৬ সালে ‘বেদান্ত কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করেন।
এভাবেই রামমোহন ভারতে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।
২১. টীকা লেখো: ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা।
উত্তর:
প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট: ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’-এর নেতা কেশবচন্দ্র সেনের কিছু কার্যকলাপ, যেমন—নিজের নাবালিকা কন্যার সঙ্গে কোচবিহারের নাবালক রাজার বিবাহ দেওয়া এবং তাঁর একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মতো নবীন ও গণতান্ত্রিকপন্থী ব্রাহ্ম নেতারা তাঁর বিরোধিতা করেন।
প্রতিষ্ঠা: এই মতবিরোধের জেরেই তাঁরা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গ ত্যাগ করে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন।
বৈশিষ্ট্য:
১. এটি ছিল একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন, যেখানে সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হত।
২. এই সমাজ নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা এবং সামাজিক সাম্যের উপর বিশেষ জোর দেয়।
৩. ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
২২. ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকা কীভাবে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেছিল?
উত্তর:
‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকা, বিশেষ করে সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।
ভূমিকা:
১. নির্ভীক সাংবাদিকতা: এই পত্রিকা নির্ভীকভাবে নীলকর সাহেবদের শোষণ, বেআইনিভাবে চাষিদের জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করা, দাদন প্রথার কুফল এবং চাষিদের উপর শারীরিক অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ করত।
২. আইনি সহায়তা: হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারিত নীলচাষিদের আইনি পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা দিতেন এবং তাদের কলকাতায় আশ্রয় দিতেন।
৩. শিক্ষিত সমাজের সমর্থন: পত্রিকার এই ভূমিকার ফলে কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীলচাষিদের দুর্দশার কথা জানতে পারে এবং তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে।
এভাবেই ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ নীল বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল এবং শক্তিশালী জনমত গঠনে সক্ষম হয়েছিল।
২৩. উনিশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনে বামাবোধিনী গোষ্ঠীর অবদান কী ছিল?
উত্তর:
উনিশ শতকে বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনে উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখের নেতৃত্বে ‘বামাবোধিনী গোষ্ঠী’র অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অবদান:
১. ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশ: এই গোষ্ঠীর প্রধান কাজ ছিল ১৮৬৩ সাল থেকে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশ করা। এই পত্রিকা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে নারীদের অবহিত করত।
২. সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা: তাঁরা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো প্রথার তীব্র সমালোচনা করতেন এবং নারীস্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করতেন।
৩. উচ্চশিক্ষার দাবি: দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের উচ্চশিক্ষার অধিকারের জন্য আন্দোলন করেন। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা স্নাতক হতে সক্ষম হন।
৪. রাজনৈতিক সচেতনতা: এই গোষ্ঠী নারীদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়েও সচেতন করার চেষ্টা করত।
২৪. বাংলার সমাজ জীবনে লালন ফকিরের প্রভাব আলোচনা করো।
উত্তর:
উনিশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনে বাউল সাধক লালন ফকিরের প্রভাব ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী।
প্রভাব:
১. মানবতাবাদের প্রচার: লালন তাঁর গানের মাধ্যমে জাতপাত, ধর্মীয় ভেদাভেদ ও আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে উঠে মানবধর্মের কথা প্রচার করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল, ‘জাত গেল জাত গেল বলে এ কী আজব কারখানা’।
২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন।
৩. সামাজিক গোঁড়ামিতে আঘাত: তাঁর সহজ-সরল কিন্তু গভীর অর্থবহ গানগুলি সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানে।
৪. বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রভাব: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বহু বুদ্ধিজীবী লালনের মানবতাবাদী দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন।
২৫. ডিরোজিও কেন তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত হন?
উত্তর:
হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ ছিল।
কারণসমূহ:
১. ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আঘাত: ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামীরা হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, জাতিভেদ প্রথা এবং অন্যান্য আচারের তীব্র সমালোচনা করতেন। তাঁরা নিষিদ্ধ মাংস খাওয়া এবং পৈতা ছিঁড়ে ফেলার মতো কাজ করে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে ক্ষুব্ধ করে তোলেন।
২. অভিভাবকদের অভিযোগ: ছাত্রদের এই ‘উচ্ছৃঙ্খল’ আচরণের জন্য তাদের অভিভাবকরা ডিরোজিওকে দায়ী করেন এবং হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান।
৩. কর্তৃপক্ষের চাপ: কলেজের পরিচালক সমিতি, বিশেষ করে রক্ষণশীল হিন্দু সদস্যরা, এই চাপের মুখে নতিস্বীকার করেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, ডিরোজিওর প্রভাবে কলেজের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে।
এই সমস্ত কারণে, ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিকতা প্রচার ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করার অভিযোগে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয়।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৮ (১০টি)
১. উনিশ শতকে বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের ভারতে সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই ভারতীয় সমাজ মধ্যযুগীয় জড়তা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ‘ভারত পথিক’ বলে অভিহিত করেছেন।
অবদান:
১. সতীদাহ প্রথা রদ: রামমোহনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন। তিনি শাস্ত্র উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে, এই প্রথার কোনো ধর্মীয় ভিত্তি নেই। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন এবং গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে আইন পাস করতে প্রভাবিত করেন। এর ফলে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ‘সপ্তদশ বিধি’ দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়।
২. একেশ্বরবাদ প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা: তিনি হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা ও বহু-ঈশ্বরবাদের বিরোধিতা করে উপনিষদের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮১৫ সালে ‘আত্মীয় সভা’ এবং ১৮২৮ সালে ‘ব্রাহ্মসভা’ (পরে ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করেন।
৩. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা: তিনি নারীর সমানাধিকারের পক্ষে ছিলেন। তিনি নারীদের সম্পত্তির অধিকার এবং শিক্ষার অধিকারের দাবি জানান। তিনি বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার মতো কুপ্রথারও বিরোধিতা করেন।
৪. জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা: রামমোহন জাতিভেদ প্রথাকে সামাজিক অনৈক্যের মূল কারণ বলে মনে করতেন এবং এর তীব্র বিরোধিতা করেন।
উপসংহার: রামমোহন রায় ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, ধর্ম সংস্কারক এবং আধুনিক ভারতের প্রবক্তা। তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।
২. শিক্ষাসংস্কার ও সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর অবদান মূলত দুটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল—শিক্ষাসংস্কার ও সমাজ সংস্কার।
শিক্ষাসংস্কারে অবদান:
১. বাংলা গদ্যের জনক: তিনি বাংলা গদ্যকে প্রথম শৈল্পিক ও সুগঠিত রূপ দেন। তাঁর রচিত ‘বর্ণপরিচয়’, ‘কথামালা’, ‘বোধোদয়’ প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা ভাষাশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে।
২. নারীশিক্ষার প্রসার: তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার অক্লান্ত প্রচারক। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন।
৩. সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার: সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি সেখানে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের পরিবর্তে সকল বর্ণের হিন্দুদের ভর্তির অধিকার দেন এবং ইংরেজি শিক্ষাকে আবশ্যিক করেন।
সমাজ সংস্কারে অবদান:
১. বিধবা বিবাহ প্রবর্তন: তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। তিনি শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তাঁর অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সরকার ‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাস করে।
২. বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা: তিনি বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, যদিও এক্ষেত্রে তিনি আইন পাস করাতে সফল হননি।
উপসংহার: বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন প্রকৃত মানবতাবাদী, যিনি তাঁর জ্ঞান ও কর্ম দিয়ে বাঙালি সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত ও আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর অবদান বাঙালি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।
৩. উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাংলার ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই ‘বাংলার নবজাগরণ’ বা ‘Bengal Renaissance’ বলা হয়।
চরিত্র বা প্রকৃতি:
১. মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ: এই নবজাগরণের মূল ভিত্তি ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ। এর প্রভাবে মানুষ ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে শেখে।
২. কলকাতাকেন্দ্রিকতা: এই জাগরণের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। হিন্দু কলেজ, ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বদের কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা।
৩. সমন্বয়বাদী ধারা: রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান গ্রহণ করলেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ বর্জন করেননি।
সীমাবদ্ধতা:
১. শহর ও精英দের মধ্যে সীমাবদ্ধ: ঐতিহাসিকদের মতে, এই নবজাগরণ মূলত কলকাতা শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
২. মুসলিম সমাজের অনুপস্থিতি: বাংলার বিশাল মুসলিম সমাজ এই জাগরণ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। রক্ষণশীলতা ও ব্রিটিশদের প্রতি недоверие এর অন্যতম কারণ।
৩. গণসংযোগের অভাব: নবজাগরণের নেতারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের আন্দোলন মূলত আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
উপসংহার: এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের নবজাগরণই আধুনিক বাংলার ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল।
৪. উনিশ শতকে বাংলায় ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে বাংলার ধর্ম ও সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে বিকশিত হয়।
ভূমিকা:
১. একেশ্বরবাদ প্রচার ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা: ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি ছিল উপনিষদের একেশ্বরবাদ। এটি হিন্দুধর্মের বহু-ঈশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা এবং জটিল আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধিতা করে এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলে।
২. সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা: ব্রাহ্মসমাজ শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। রামমোহনের নেতৃত্বে এটি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হন।
৩. নারীমুক্তি: ব্রাহ্মসমাজ নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশ এবং নারীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন নারীমুক্তির পথকে প্রশস্ত করে।
৪. বিভাজন ও তার প্রভাব: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ’, ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ এবং ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’— এই তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভাজন আন্দোলনকে কিছুটা দুর্বল করলেও, প্রতিটি শাখাই নিজ নিজ উপায়ে সংস্কারের কাজ চালিয়ে যায়। ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নারীশিক্ষা ও সামাজিক সাম্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
উপসংহার: ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এক নতুন যুক্তিবাদী ও আধুনিক মানসিকতা তৈরি করেছিল, যা বাংলার নবজাগরণকে সার্থক করে তুলেছিল।
৫. উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে বিদেশি ও দেশীয় উদ্যোগের এক মেলবন্ধন ঘটেছিল। এক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ারের যুগ্ম প্রচেষ্টা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
রামমোহন রায়ের ভূমিকা:
১. পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক: রামমোহন রায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া ভারতের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্কে জোরালোভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষ নেন এবং লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখে ভারতে গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যার মতো আধুনিক বিষয় পড়ানোর দাবি জানান।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন: তিনি নিজে কলকাতায় ‘অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল’ নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ডেভিড হেয়ারকে ‘হিন্দু কলেজ’ এবং আলেকজান্ডার ডাফকে ‘জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন’ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন।
ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা:
১. নিঃস্বার্থ শিক্ষাব্রতী: স্কটল্যান্ডের একজন ঘড়ি-ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও ডেভিড হেয়ার তাঁর জীবনের সমস্ত অর্থ ও সময় এদেশের মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।
২. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা: তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর উদ্যোগেই এই কলেজের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং তিনি এর পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন।
৩. অন্যান্য প্রতিষ্ঠান: তিনি ১৮১৭ সালে ‘কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করে স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি ‘পটলডাঙা অ্যাকাডেমি’ (যা পরে ‘হেয়ার স্কুল’ নামে পরিচিত হয়) প্রতিষ্ঠা করেন।
উপসংহার: রামমোহন ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পথপ্রদর্শক ও তাত্ত্বিক রূপকার, আর ডেভিড হেয়ার ছিলেন তার নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্মী। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলায় আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।
৬. উনিশ শতকের বাংলায় সমাজসংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্যাবলী ও তার সীমাবদ্ধতা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার এক যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল একজন শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে।
কার্যাবলী:
১. বিধবা বিবাহ প্রবর্তন: বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। তিনি পরাশর সংহিতা সহ বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তাঁর অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে এবং বহু মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্রের চাপে সরকার ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ‘বিধবা বিবাহ আইন’ (Act XV) পাস করে। তিনি নিজের খরচে বহু বিধবার বিবাহও দেন।
২. বহুবিবাহের বিরোধিতা: তিনি বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে একাধিক পুস্তিকা রচনা করেন এবং সরকারের কাছে আইন পাসের জন্য আবেদন জানান, যদিও এক্ষেত্রে তিনি সফল হননি।
৩. বাল্যবিবাহের বিরোধিতা: তিনি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। তিনি মনে করতেন, বাল্যবিবাহই বহু মেয়ের বৈধব্যের কারণ।
সীমাবদ্ধতা:
১. আইন কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ: বিধবা বিবাহ আইন পাস হলেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতার কারণে তা বাস্তবে খুব বেশি সাফল্য লাভ করেনি। বিদ্যাসাগর নিজে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে পারলেও এর প্রচলন করতে পারেননি।
২. অন্যান্য সংস্কারে ব্যর্থতা: বহুবিবাহ রদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে তিনি সরকারের কাছ থেকে আইন পাস করাতে ব্যর্থ হন।
উপসংহার: কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টা হিন্দুসমাজের গভীরে নাড়া দিয়েছিল এবং নারীমুক্তির পথে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। তাঁর অদম্য জেদ ও মানবিকতাই তাঁকে ‘করুণাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করেছে।
৭. ‘নব্যবঙ্গ আন্দোলন’-এর ব্যর্থতার কারণগুলি কী ছিল? এই আন্দোলনের গুরুত্ব কী?
উত্তর:
ভূমিকা: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে ‘নব্যবঙ্গ’ বা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ আন্দোলন উনিশ শতকের বাংলায় এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়।
ব্যর্থতার কারণ:
১. নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি: নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী মূলত হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে সমালোচনাই করত। তাদের কোনো গঠনমূলক বা ইতিবাচক কর্মসূচি ছিল না, যা দিয়ে তারা সমাজের উন্নতি করতে পারে।
২. সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগহীনতা: তাদের আন্দোলন ছিল পুরোপুরি শহর-কেন্দ্রিক এবং উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলার বিশাল গ্রামীণ জনতা বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ ছিল না।
৩. বাস্তবতাবিবর্জিত চরমপন্থা: তাদের কার্যকলাপ, যেমন—নিষিদ্ধ মাংস খাওয়া, পৈতা ছেঁড়া ইত্যাদি ছিল কিছুটা চরমপন্থী ও বাস্তবতাবিবর্জিত। এর ফলে তারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
৪. ডিরোজিওর অকালমৃত্যু: ১৮৩১ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে ডিরোজিওর অকালমৃত্যুর ফলে এই আন্দোলন যোগ্য নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।
গুরুত্ব:
ব্যর্থতা সত্ত্বেও, নব্যবঙ্গ আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তারাই প্রথম বাংলার যুবসমাজকে যুক্তিবাদী, সমালোচনামূলক ও আধুনিক মননের অধিকারী হতে শিখিয়েছিল। তারাই প্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়ের কথা বলেছিল। তাদের চিন্তাভাবনা পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।
৮. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ দ্বিধাগ্রস্ত এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের আবেদনও হ্রাস পাচ্ছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক নতুন আধ্যাত্মিক ও সমন্বয়বাদী বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন।
প্রভাব:
১. সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা: শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান অবদান হল তাঁর ‘সর্বধর্ম সমন্বয়’-এর আদর্শ। তিনি নিজে বিভিন্ন ধর্ম সাধনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ‘যত মত, তত পথ’—অর্থাৎ সব ধর্মই সত্য। তাঁর এই বার্তা তৎকালীন ধর্মীয় বিবাদ ও সংকীর্ণতার আবহে এক ঐক্যের বাণী নিয়ে আসে।
২. হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাবে যে শিক্ষিত হিন্দুরা নিজের ধর্মের প্রতি আস্থা হারাচ্ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজ-সরল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও ভক্তিবাদের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের গরিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।
৩. শিক্ষিত সমাজের উপর প্রভাব: তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং সহজ-সরল ধর্মব্যাখ্যা কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো ব্রাহ্ম নেতা এবং নরেন্দ্রনাথ দত্তের (বিবেকানন্দ) মতো বহু শিক্ষিত তরুণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
৪. বিবেকানন্দের উত্থান: শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেন তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি গুরুর ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’র আদর্শকে এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও মানবসেবার কাজ করে চলেছে।
উপসংহার: শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো সংগঠন বা গ্রন্থ রচনা না করেও শুধুমাত্র তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও সমন্বয়বাদী বার্তার মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক নীরব কিন্তু গভীর বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।
৯. টীকা লেখো: ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ এবং ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’।
উত্তর:
উনিশ শতকের বাংলায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল ‘বামাবোধিনী’ এবং ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’।
বামাবোধিনী পত্রিকা:
উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মূলত নারীদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা।
গুরুত্ব:
১. এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং নারীদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার করা।
২. এটি নারীদের লেখা প্রকাশের একটি মঞ্চ তৈরি করে দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল।
৩. এতে স্বাস্থ্য, গৃহকর্ম, সন্তান পালন এবং সামাজিক নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, যা নারীদের সার্বিক বিকাশে সাহায্য করত।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট:
‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ ছিল একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর প্রথম সম্পাদক হলেও, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনাতেই এটি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছায়।
গুরুত্ব:
১. এই পত্রিকা নির্ভীকভাবে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমালোচনা করত।
২. সাঁওতাল বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়ে এটিই প্রথম কোনো ইংরেজি পত্রিকা যা বিদ্রোহীদের পক্ষে লেখে।
৩. নীল বিদ্রোহের সময় এটি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং নীলচাষিদের সমর্থনে জনমত গঠনে প্রধান ভূমিকা নেয়। হরিশচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবেও চাষিদের সাহায্য করতেন।
১০. বাংলার নবজাগরণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ও তার সীমাবদ্ধতা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলার নবজাগরণে এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ভূমিকা:
১. পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্র: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে বাঙালিরা ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়, যা তাদের মধ্যে এক নতুন যুক্তিবাদী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।
২. শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি: এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে বাংলায় এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির উদ্ভব হয়, যারা পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল।
৩. নারীশিক্ষার প্রসার: দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মতো ব্যক্তিদের আন্দোলনের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নারীদের জন্য তার দরজা খুলে দেয়। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসুর মতো নারীরা এখান থেকেই স্নাতক হয়ে নারীশিক্ষার ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।
৪. জাতীয়তাবাদের উন্মেষ: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচারিত হলে, তা তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে সাহায্য করে।
সীমাবদ্ধতা:
১. কেরানি তৈরির কারখানা: সমালোচকদের মতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য স্বল্প বেতনের কেরানি তৈরি করা, মৌলিক গবেষণা বা চিন্তার বিকাশ ঘটানো নয়।
২. শহরকেন্দ্রিকতা: এর সুফল মূলত কলকাতা ও অন্যান্য শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
উপসংহার: এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে আধুনিক বাংলা তথা ভারতের পথপ্রদর্শক এক শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি করেছিল, তা অনস্বীকার্য।
Class 10 History সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা Question Answer MCQ,অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : class 10 সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা প্রশ্ন উত্তর