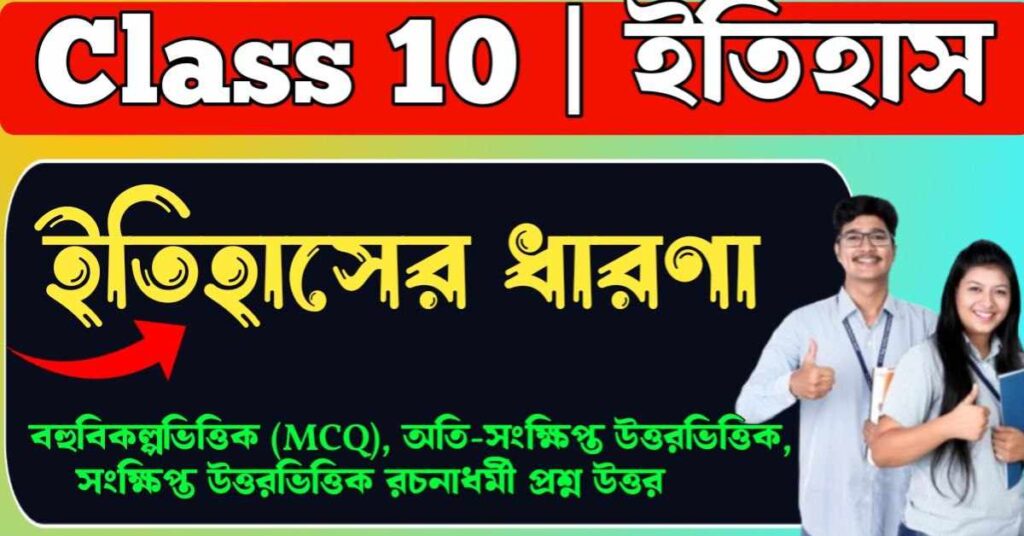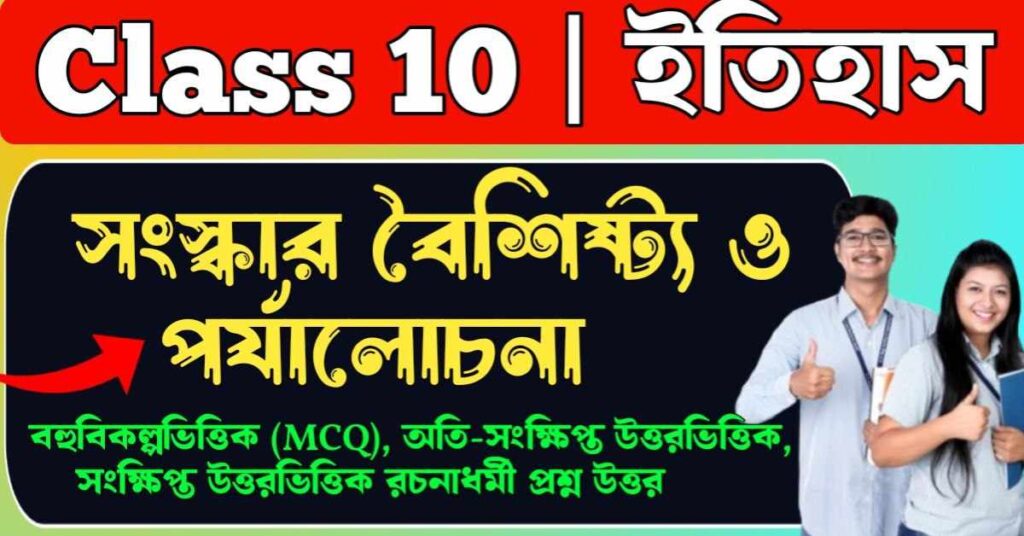প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. ‘হুল’ কথাটির অর্থ হল—
২. সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন—
৩. তিতুমীরের প্রকৃত নাম ছিল—
৪. মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা ছিলেন—
৫. ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন—
৬. ‘দামিন-ই-কোহ’ কথাটির অর্থ হল—
৭. ‘উলগুলান’ নামে পরিচিত ছিল কোন বিদ্রোহ?
৮. নীল বিদ্রোহ হয়েছিল—
৯. সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন—
১০. ‘খুঁৎকাঠি প্রথা’ প্রচলিত ছিল কোন সমাজে?
১১. ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—
১২. ‘ধরতী আবা’ নামে পরিচিত ছিলেন—
১৩. কোল বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল—
১৪. ‘বাংলার নানা সাহেব’ বলা হয়—
১৫. চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন—
১৬. ভারতে প্রথম অরণ্য আইন পাস হয়—
১৭. নীল বিদ্রোহের সময় বড়লাট ছিলেন—
১৮. ‘দার-উল-হারব’ কথাটির অর্থ—
১৯. ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি রচনা করেন—
২০. পাবনা কৃষক বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন—
২১. বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন—
২২. ‘বিপ্লব’ কথাটির অর্থ হল—
২৩. রংপুর বিদ্রোহের নেতা ছিলেন—
২৪. ভিল বিদ্রোহ হয়েছিল—
২৫. ‘জমি আল্লাহর দান’— এই উক্তিটি কার?
২৬. সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের উল্লেখ আছে কোন উপন্যাসে?
২৭. নীল বিদ্রোহকে ‘এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান’ বলেছেন—
২৮. মেদিনীপুরের ‘লক্ষ্মীবাই’ নামে পরিচিত ছিলেন—
২৯. ‘দিকু’ কাদের বলা হত?
৩০. ‘Tarikh-i-Muhammadiya’ আন্দোলনের অপর নাম ছিল—
৩১. নীল কমিশন গঠিত হয়—
৩২. ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি কোন বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে লেখা?
৩৩. নীল বিদ্রোহের প্রথম শহীদ কে ছিলেন?
৩৪. পাগলপন্থী বিদ্রোহের নেতা ছিলেন—
৩৫. ‘উলগুলান’ কথাটির অর্থ হল—
৩৬. ‘বারাসাত বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত—
৩৭. সাঁওতাল পরগনা জেলা গঠিত হয়—
৩৮. ‘দাদন’ কথাটির অর্থ হল—
৩৯. ব্রিটিশরা চুয়াড়দের বলত—
৪০. ‘The Santhals of Santhal Parganas’ গ্রন্থটি কার লেখা?
৪১. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের পটভূমি ছিল—
৪২. ‘জঙ্গলমহল’ জেলাটি গঠিত হয় কোন বিদ্রোহের পর?
৪৩. ‘হাজি শরিয়তুল্লাহ’ মারা যান—
৪৪. তিতুমীরের সেনাপতির নাম ছিল—
৪৫. পাবনা বিদ্রোহ ছিল মূলত—
৪৬. ‘সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি’ গঠিত হয় কোন বিদ্রোহের পর?
৪৭. ‘ফরাজ’ শব্দের অর্থ হল—
৪৮. বিরসা মুন্ডার मृत्यू হয়—
৪৯. ‘আমরা মহারানির প্রজা হতে চাই’— এই স্লোগানটি ছিল কোন বিদ্রোহের?
৫০. ‘খেরওয়ার’ নামে পরিচিত ছিল কোন আদিবাসী গোষ্ঠী?
৫১. দেবী চৌধুরাণী ছিলেন একজন—
৫২. ব্রিটিশ শাসনে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ কোনটি?
৫৩. ‘সাঁওতাল পরগনা’র পূর্ব নাম কী ছিল?
৫৪. ‘ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন’ পাস হয়—
৫৫. ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল—
৫৬. ‘বালাকোটের যুদ্ধ’ হয়েছিল—
৫৭. নীল বিদ্রোহকে ‘প্রথম সার্থক কৃষক বিদ্রোহ’ বলেছেন—
৫৮. ‘দামিন’ কথাটির অর্থ হল—
৫৯. ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকটি রচনা করেন—
৬০. রংপুর বিদ্রোহের কারণ ছিল—
৬১. পাগলপন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—
৬২. মুন্ডা বিদ্রোহের সময় বড়লাট ছিলেন—
৬৩. ‘খেরওয়ারি হুল’ নামে পরিচিত ছিল—
৬৪. ‘বিদ্রোহ’ ও ‘অভ্যুত্থান’-এর মধ্যে পার্থক্য হল—
৬৫. ‘বে-এলাকা চাষ’ কথাটি যুক্ত ছিল—
৬৬. ‘দুদু মিঞা’ যে আন্দোলনের নেতা ছিলেন—
৬৭. কোল বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন—
৬৮. ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটির লেখক কে?
৬৯. চুয়াড় বিদ্রোহের অপর নাম কী?
৭০. ‘অচল সিংহ’ কোন বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. ‘হুল’ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: ‘হুল’ একটি সাঁওতালি শব্দ, যার অর্থ হল বিদ্রোহ।
২. সাঁওতাল বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: সিধু ও কানু।
৩. তিতুমীরের আসল নাম কী ছিল?
উত্তর: মীর নিসার আলি।
৪. মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর: বিরসা মুন্ডা।
৫. ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তক কে?
উত্তর: হাজি শরিয়তুল্লাহ।
৬. ‘দামিন-ই-কোহ’ কী?
উত্তর: ‘দামিন-ই-কোহ’ কথার অর্থ ‘পাহাড়ের প্রান্তদেশ’। এটি ছিল সাঁওতালদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি এলাকা।
৭. ‘উলগুলান’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ‘উলগুলান’ একটি মুন্ডা শব্দ, যার অর্থ ‘ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা’ বা ‘বিরাট তোলপাড়’।
৮. নীল বিদ্রোহ কবে হয়েছিল?
উত্তর: ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে।
৯. সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের একজন নেত্রীর নাম লেখো।
উত্তর: দেবী চৌধুরাণী।
১০. ‘খুঁৎকাঠি প্রথা’ কী?
উত্তর: মুন্ডাদের চিরাচরিত যৌথ মালিকানাধীন জমি চাষের প্রথা।
১১. ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা কে করেন?
উত্তর: রায়বেরিলির সৈয়দ আহমেদ।
১২. বিরসা মুন্ডা নিজেকে কী বলে ঘোষণা করেন?
উত্তর: ‘ধরতী আবা’ বা ‘পৃথিবীর পিতা’।
১৩. কোল বিদ্রোহ কবে হয়েছিল?
উত্তর: ১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে।
১৪. ‘বাংলার নানা সাহেব’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: রামরতন মল্লিককে।
১৫. চুয়াড় বিদ্রোহের একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: দুর্জন সিংহ বা রানী শিরোমণি।
১৬. ভারতে প্রথম অরণ্য আইন কবে পাস হয়?
উত্তর: ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে।
১৭. ‘দার-উল-ইসলাম’ কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: ইসলামের দেশ বা শান্তিস্থল।
১৮. ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি কে রচনা করেন?
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র।
১৯. পাবনা বিদ্রোহের একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: ঈশানচন্দ্র রায় বা শম্ভুপাল।
২০. তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন?
উত্তর: বারাসাতের নারকেলবেড়িয়া গ্রামে।
২১. বিপ্লব ও বিদ্রোহের মধ্যে একটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: বিদ্রোহ হল কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সীমিত প্রতিবাদ, আর বিপ্লব হল সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।
২২. রংপুর বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর: নুরুলউদ্দিন।
২৩. ‘জমি আল্লাহর দান’— উক্তিটি কার?
উত্তর: ফরাজি নেতা দুদু মিঞার।
২৪. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের পটভূমি কী ছিল?
উত্তর: সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ।
২৫. ‘দিকু’ কাদের বলা হত?
উত্তর: সাঁওতাল বা মুন্ডা অধ্যুষিত অঞ্চলে বহিরাগত জমিদার ও মহাজনদের ‘দিকু’ বলা হত।
২৬. নীল কমিশন কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে।
২৭. ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি কার লেখা?
উত্তর: মহাশ্বেতা দেবীর।
২৮. নীল বিদ্রোহের প্রথম শহীদ কে ছিলেন?
উত্তর: বিশ্বনাথ সর্দার।
২৯. পাগলপন্থী বিদ্রোহ কোথায় হয়েছিল?
উত্তর: ময়মনসিংহ জেলার শেরপুরে।
৩০. ‘বারাসাত বিদ্রোহ’ কার নেতৃত্বে হয়েছিল?
উত্তর: তিতুমীরের নেতৃত্বে।
৩১. ‘দাদন’ কী?
উত্তর: নীলকররা চাষিদের নীল চাষ করতে বাধ্য করার জন্য যে অগ্রিম অর্থ দিত, তাকে ‘দাদন’ বলা হত।
৩২. ‘জঙ্গলমহল’ জেলাটি কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।
৩৩. দুদু মিঞার আসল নাম কী ছিল?
উত্তর: মহম্মদ মহসিন।
৩৪. তিতুমীরের সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: গোলাম মাসুম।
৩৫. ‘সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি’ কেন গঠিত হয়?
উত্তর: কোল বিদ্রোহের পর কোলদের শান্ত করার জন্য এই প্রশাসনিক ইউনিট গঠিত হয়।
৩৬. ‘ফরাজ’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য।
৩৭. বিরসা মুন্ডা কবে মারা যান?
উত্তর: ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে।
৩৮. পাবনা বিদ্রোহের একটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তর: এই বিদ্রোহ জমিদারদের বিরুদ্ধে হলেও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ছিল না।
৩৯. ‘খেরওয়ার’ কী?
উত্তর: সাঁওতালদের প্রাচীন নাম। এটি তাদের একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্রোহের রূপকেও বোঝায়।
৪০. একজন ফকির নেতার নাম লেখো।
উত্তর: মজনু শাহ।
৪১. ‘ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন’ কবে পাস হয়?
উত্তর: ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে।
৪২. ‘বালাকোটের যুদ্ধ’ কবে হয়?
উত্তর: ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে (শিখদের সঙ্গে ওয়াহাবিদের)।
৪৩. নীল বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।
৪৪. ‘বে-এলাকা চাষ’ কী?
উত্তর: নীলকরদের নিজেদের জমিতে মজুর দিয়ে নীল চাষ করানোকে ‘নিজ আবাদি’ বা ‘বে-এলাকা চাষ’ বলা হত।
৪৫. ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকটির রচয়িতা কে?
উত্তর: মীর মোশাররফ হোসেন।
৪৬. রংপুর বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে হয়েছিল?
উত্তর: ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে।
৪৭. পাগলপন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উত্তর: করিম শাহ।
৪৮. মুন্ডা বিদ্রোহের অপর নাম কী?
উত্তর: উলগুলান।
৪৯. ঔপনিবেশিক অরণ্য আইনের একটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: বনজ সম্পদ, বিশেষ করে মূল্যবান কাঠকে সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত করা।
৫০. ‘সাঁওতাল পরগনা’ জেলাটি কেন গঠন করা হয়েছিল?
উত্তর: সাঁওতাল বিদ্রোহের পর তাদের শান্ত করতে এবং তাদের জন্য একটি পৃথক প্রশাসনিক এলাকা তৈরি করতে।
৫১. ভিল বিদ্রোহের একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: শিউরাম।
৫২. ওয়াহাবি আন্দোলনের লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তর: ভারতকে ‘দার-উল-হারব’ (বিধর্মীর দেশ) থেকে ‘দার-উল-ইসলাম’ (ইসলামের দেশ)-এ পরিণত করা।
৫৩. ‘পাইক’ কাদের বলা হত?
উত্তর: মেদিনীপুরের জমিদারদের অধীনে কর্মরত বেতনভোগী সৈনিকদের ‘পাইক’ বলা হত।
৫৪. ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি কোথা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ঢাকা থেকে।
৫৫. ‘তারিকা-ই-মহম্মদীয়া’ কথার অর্থ কী?
উত্তর: মহম্মদ প্রদর্শিত পথ।
৫৬. ‘সুই মুন্ডা’ কোন বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উত্তর: কোল বিদ্রোহ।
৫৭. ‘পঞ্চম আইন’ কী?
উত্তর: ১৮৫৯ সালের একটি আইন, যা নীলচাষিদের দাদন নিয়ে চুক্তিভঙ্গ করলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার অধিকার নীলকরদের দেয়।
৫৮. ‘মারাঠা গোর্কি’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে-কে।
৫৯. ‘সিংবোঙা’ কে?
উত্তর: মুন্ডাদের প্রধান দেবতা বা সূর্যদেবতা।
৬০. ‘নীল বাঁদরে সোনার বাংলা নষ্ট করছে’— এই উক্তিটি কোন পত্রিকায় করা হয়েছিল?
উত্তর: ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকায়।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন প্রণয়নের দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: (১) ভারতীয় বনভূমির মূল্যবান কাঠ, যেমন—শাল ও সেগুন দখল করে রেললাইন তৈরি ও জাহাজ নির্মাণে ব্যবহার করা। (২) অরণ্যবাসী আদিবাসীদের বনভূমির উপর চিরাচরিত অধিকার কেড়ে নিয়ে বনজ সম্পদের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।
২. ‘বিদ্রোহ’, ‘অভ্যুত্থান’ ও ‘বিপ্লব’-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: বিদ্রোহ: কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সীমিত প্রতিবাদ। অভ্যুত্থান: যখন কোনো বিদ্রোহে ব্যাপক জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। বিপ্লব: যখন কোনো সংগ্রামের মাধ্যমে প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।
৩. ‘খুঁৎকাঠি প্রথা’ কী?
উত্তর: ‘খুঁৎকাঠি প্রথা’ হল মুন্ডা সমাজে প্রচলিত একটি চিরাচরিত প্রথা, যেখানে গ্রামের জমি কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বরং সমগ্র গ্রাম বা খিলির (গোষ্ঠী) যৌথ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত।
৪. তিতুমীর কেন বিখ্যাত?
উত্তর: তিতুমীর বা মীর নিসার আলি বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিখ্যাত। তিনি জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বারাসাতের কাছে নারকেলবেড়িয়া গ্রামে একটি ‘বাঁশের কেল্লা’ নির্মাণ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
৫. ফরাজি আন্দোলন কি নিছকই একটি ধর্মীয় আন্দোলন ছিল?
উত্তর: না, ফরাজি আন্দোলন শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। হাজি শরিয়তুল্লাহর নেতৃত্বে এটি ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণের আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও, তাঁর পুত্র দুদু মিঞার নেতৃত্বে এটি জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়।
৬. ‘দাদন প্রথা’ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: নীলকর সাহেবরা বাংলার গরিব চাষিদের নীল চাষ করতে বাধ্য করার জন্য যে স্বল্প পরিমাণ অর্থ অগ্রিম বা ‘দাদন’ দিত, সেই প্রথাই ‘দাদন প্রথা’ নামে পরিচিত। এই দাদনের জালে জড়িয়ে চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়ে যেত।
৭. ‘দামিন-ই-কোহ’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ‘দামিন-ই-কোহ’ একটি ফারসি শব্দ, যার অর্থ ‘পাহাড়ের প্রান্তদেশ’। ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের জন্য রাজমহল পাহাড়ের প্রান্তবর্তী একটি বিশাল এলাকাকে নির্দিষ্ট করে দেয়, যা ‘দামিন-ই-কোহ’ নামে পরিচিত।
৮. রানী শিরোমণি স্মরণীয় কেন?
উত্তর: রানী শিরোমণি ছিলেন মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহের একজন অন্যতম নেত্রী। ব্রিটিশরা তাঁর জমিদারি কেড়ে নিলে তিনি পাইক বা চুয়াড়দের নিয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই কারণে তাঁকে ‘মেদিনীপুরের লক্ষ্মীবাই’ বলা হয়।
৯. নীল বিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: নীল বিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এবং দীনবন্ধু মিত্র ‘নীলদর্পণ’ নাটক রচনা করে নীলচাষিদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন ও জনমত গঠন করেন।
১০. ‘উলগুলান’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ‘উলগুলান’ একটি মুন্ডা শব্দ, যার অর্থ ‘ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা’ বা ‘বিরাট তোলপাড়’। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে পরিচালিত মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০) ‘উলগুলান’ নামে পরিচিত।
১১. ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: (১) ওয়াহাবি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সারা ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করা, আর ফরাজি আন্দোলন ছিল মূলত পূর্ব বাংলা-কেন্দ্রিক। (২) ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল বেশি সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু ফরাজি আন্দোলন দুদু মিঞার মৃত্যুর পর দুর্বল হয়ে পড়ে।
১২. পাবনা বিদ্রোহের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তর: (১) এই বিদ্রোহ ছিল মূলত জমিদারদের বেআইনি কর বৃদ্ধি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নয়। (২) বিদ্রোহীরা আইন মেনে চলত এবং তাদের প্রধান দাবি ছিল শান্তিপূর্ণভাবে শুধুমাত্র মহারানির প্রজা হয়ে থাকা।
১৩. ব্রিটিশ সরকার কেন ‘সাঁওতাল পরগনা’ জেলা গঠন করে?
উত্তর: ১৮৫৫-৫৬ সালের ভয়ঙ্কর সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, সাঁওতালদের অসন্তোষ দূর না করলে শাসন চালানো কঠিন। তাই তাদের শান্ত করার জন্য এবং তাদের নিজস্ব আইনকানুন ও সংস্কৃতির সুরক্ষার আশ্বাস দিয়ে একটি পৃথক ‘সাঁওতাল পরগনা’ জেলা গঠন করা হয়।
১৪. ‘বে-এলাকা’ ও ‘রায়তি’ চাষের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: বে-এলাকা চাষ: নীলকররা নিজেদের খাস জমিতে বাইরের মজুর দিয়ে যে নীল চাষ করত, তাকে বে-এলাকা বা নিজ-আবাদি চাষ বলে। রায়তি চাষ: চাষিদের নিজেদের জমিতে দাদন দিয়ে নীল চাষ করতে বাধ্য করাকে রায়তি চাষ বলে।
১৫. দুদু মিঞা কীভাবে ফরাজি আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন?
উত্তর: পিতার মৃত্যুর পর দুদু মিঞা ফরাজি আন্দোলনকে একটি কৃষক আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি ‘জমি আল্লাহর দান’ বলে খাজনা বন্ধের ডাক দেন এবং জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী ও গুপ্তচর ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।
১৬. কোল বিদ্রোহের দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: (১) ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে কোলদের চিরাচরিত জমির অধিকার নষ্ট হয়। (২) বহিরাগত বা ‘দিকু’ মহাজন ও জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার কোলদের বিদ্রোহী করে তোলে।
১৭. সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কেন?
উত্তর: (১) এই বিদ্রোহের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা সুসংহত পরিকল্পনা ছিল না। (২) যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে এটি ব্যর্থ হয়।
১৮. ‘ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন’ (১৯০৮) কেন পাস হয়?
উত্তর: মুন্ডা বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার আদিবাসীদের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য ‘ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন’ পাস করে। এই আইনের দ্বারা মুন্ডাদের ‘খুঁৎকাঠি’ প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং বেগার শ্রম বা বেট-বেগারি প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।
১৯. ‘বারাসাত বিদ্রোহ’ কী?
উত্তর: তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত ওয়াহাবি আন্দোলন ‘বারাসাত বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত অঞ্চলে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
২০. ‘বিপ্লব’ শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়?
উত্তর: ‘বিপ্লব’ শব্দটি দ্বারা কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত ও আমূল পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। যেমন— ফরাসি বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব।
২১. ‘পাইক’ ও ‘বরকন্দাজ’ কারা ছিল?
উত্তর: ‘পাইক’ ছিল মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জমিদারদের অধীনে কর্মরত একপ্রকার বেতনভোগী সৈনিক। ‘বরকন্দাজ’ ছিল জমিদারদের অধীনে কর্মরত বন্দুকধারী রক্ষী বা সিপাই।
২২. নীল বিদ্রোহকে ‘প্রথম আধুনিক কৃষক বিদ্রোহ’ বলা হয় কেন?
উত্তর: নীল বিদ্রোহে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একযোগে নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থন লাভ করেছিল। এর সুসংগঠিত রূপ ও ব্যাপকতার জন্য একে ‘প্রথম আধুনিক কৃষক বিদ্রোহ’ বলা হয়।
২৩. তারিকা-ই-মহম্মদীয়া কী?
উত্তর: ‘তারিকা-ই-মহম্মদীয়া’ কথার অর্থ ‘মহম্মদ প্রদর্শিত পথ’। ভারতে সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে পরিচালিত ওয়াহাবি আন্দোলন এই নামেও পরিচিত ছিল।
২৪. পাগলপন্থী বিদ্রোহের আদর্শ কী ছিল?
উত্তর: পাগলপন্থী বিদ্রোহের আদর্শ ছিল ধর্মীয় সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এর নেতা করিম শাহ ও টিপু শাহ ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষ সমান—এই নীতি প্রচার করে জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।
২৫. ‘জঙ্গলমহল’ বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝানো হত?
উত্তর: ব্রিটিশ শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং ছোটনাগপুরের কিছু অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলকে একত্রে ‘জঙ্গলমহল’ বলা হত। এই অঞ্চলেই চুয়াড় বিদ্রোহ হয়েছিল।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগুলি কী ছিল?
উত্তর:
১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ বা ‘হুল’ ছিল ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম ভয়ঙ্কর উপজাতি বিদ্রোহ। এর কারণগুলি হল:
১. অর্থনৈতিক শোষণ: ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে সাঁওতালদের উপর চড়া হারে কর চাপানো হয়। বহিরাগত ‘দিকু’ মহাজনরা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে তাদের জমি কেড়ে নিত।
২. ব্যবসায়ীদের প্রতারণা: ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে কম দামে ফসল কিনত এবং কেনারাম ও বেচারাম নামক দু’রকম বাটখারা ব্যবহার করে তাদের ঠকাতো।
৩. বিচারব্যবস্থার ব্যর্থতা: ব্রিটিশ আইন ও আদালত ছিল জটিল ও ব্যয়বহুল। বিচারকরা প্রায়শই মহাজন ও জমিদারদের পক্ষ নিতেন, ফলে সাঁওতালরা কোনো ন্যায়বিচার পেত না।
৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ: ব্রিটিশ কর্মচারী, মিশনারি এবং অন্যান্য বহিরাগতরা সাঁওতালদের সরল জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ করত, যা তাদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। এই সম্মিলিত শোষণের বিরুদ্ধেই সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
২. নীল বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মনোভাব কেমন ছিল?
উত্তর:
নীল বিদ্রোহ ছিল এমন একটি কৃষক বিদ্রোহ, যা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যাপক সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেছিল।
মনোভাব:
১. সংবাদপত্রের ভূমিকা: ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং নীলচাষিদের পক্ষে জনমত গঠন করেন। ‘সোমপ্রকাশ’-এর মতো পত্রিকাও এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে।
২. ‘নীলদর্পণ’ নাটকের প্রভাব: দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি নীলচাষিদের দুর্দশার এক জীবন্ত ছবি তুলে ধরে শিক্ষিত সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের করা ইংরেজি অনুবাদ ইউরোপেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।
৩. আইনি সহায়তা: শিশিরকুমার ঘোষের মতো সাংবাদিক এবং বিভিন্ন আইনজীবী নীলচাষিদের আইনি সহায়তা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।
উপসংহার: শিক্ষিত শ্রেণির এই সক্রিয় সমর্থনের ফলেই নীল বিদ্রোহ এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে ‘নীল কমিশন’ গঠন করতে বাধ্য করে।
৩. ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন কীভাবে আদিবাসীদের অধিকার হরণ করেছিল?
উত্তর:
ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতে একাধিক অরণ্য আইন (১৮৬৫, ১৮৭৮) প্রণয়ন করে, যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।
অধিকার হরণ:
১. চিরাচরিত অধিকার বিলোপ: এই আইনগুলির দ্বারা অরণ্যের উপর আদিবাসীদের চিরাচরিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। জঙ্গল থেকে কাঠ, মধু, ফলমূল সংগ্রহ এবং পশুচারণ নিষিদ্ধ করা হয়।
২. সংরক্ষিত অরণ্য ঘোষণা: মূল্যবান বনজ সম্পদযুক্ত অরণ্যগুলিকে ‘সংরক্ষিত’ ও ‘সুরক্ষিত’—এই দুই ভাগে ভাগ করে সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।
৩. ঝুম চাষে বাধা: অরণ্য আইনের ফলে আদিবাসীদের চিরাচরিত ‘ঝুম’ বা স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতি বেআইনি ঘোষিত হয়, যা তাদের জীবিকার উপর সরাসরি আঘাত হানে।
৪. বনকর্মী ও পুলিশের অত্যাচার: বন বিভাগের কর্মচারী ও পুলিশ অরণ্য আইন প্রয়োগের নামে আদিবাসীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত। এর ফলেই কোল, মুন্ডা, সাঁওতালের মতো বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
৪. ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি লেখো।
উত্তর:
উনিশ শতকে বাংলায় ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন দুটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সংস্কার আন্দোলন হলেও এদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই ছিল।
সাদৃশ্য:
১. দুটি আন্দোলনই ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণের আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়েছিল এবং কোরান-নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে চলার উপর জোর দিয়েছিল।
২. উভয় আন্দোলনই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ-বিরোধী এবং জমিদার-মহাজন বিরোধী কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।
বৈসাদৃশ্য:
১. ওয়াহাবি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সারা ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে, ফরাজি আন্দোলনের ক্ষেত্র মূলত পূর্ব বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
২. ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল অনেক বেশি সংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী এবং এর একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল। ফরাজি আন্দোলন মূলত স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং দুদু মিঞার মৃত্যুর পর দুর্বল হয়ে পড়ে।
৫. টীকা লেখো: মুন্ডা বিদ্রোহ (উলগুলান)।
উত্তর:
ভূমিকা: বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে যে শক্তিশালী উপজাতি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, তা মুন্ডা বিদ্রোহ বা ‘উলগুলান’ (ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা) নামে পরিচিত।
কারণ:
১. ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে মুন্ডাদের চিরাচরিত ‘খুঁৎকাঠি’ বা যৌথ মালিকানার প্রথা ভেঙে যায়।
২. বহিরাগত ‘দিকু’ জমিদার ও মহাজনদের শোষণ এবং বেগার শ্রম বা ‘বেট-বেগারি’ প্রথা মুন্ডাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।
৩. খ্রিস্টান মিশনারিরা মুন্ডাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করলে তাদের সংস্কৃতি সংকটের মুখে পড়ে।
নেতৃত্ব ও লক্ষ্য: বিরসা মুন্ডা নিজেকে ‘ধরতী আবা’ বা ‘পৃথিবীর পিতা’ বলে ঘোষণা করেন এবং এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দিকু ও ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে এক স্বাধীন ‘মুন্ডা রাজ’ প্রতিষ্ঠা করা।
ফলাফল: ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে এবং বিরসাকে গ্রেপ্তার করে। জেলে কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর ফলে সরকার ‘ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন’ (১৯০৮) পাস করতে বাধ্য হয়।
৬. নীল বিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দের নীল বিদ্রোহ ছিল বাংলার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়।
কারণ:
১. দাদন প্রথার শোষণ: নীলকররা চাষিদের নামমাত্র অগ্রিম বা ‘দাদন’ দিয়ে তাদের সবচেয়ে উর্বর জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। একবার দাদন নিলে চাষিরা বংশপরম্পরায় নীলকরদের ক্রীতদাসে পরিণত হত।
২. কম মূল্য প্রদান: নীলকররা বাজার দরের অনেক কম দামে চাষিদের কাছ থেকে নীল কিনত, ফলে চাষিরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত।
৩. শারীরিক অত্যাচার: কোনো চাষি নীল চাষ করতে অস্বীকার করলে তাদের উপর অবর্ণনীয় শারীরিক অত্যাচার চালানো হত, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হত।
৪. আইনের অপপ্রয়োগ: ১৮৫৯ সালের ‘পঞ্চম আইন’ অনুযায়ী, দাদনের চুক্তিভঙ্গ করলে চাষিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যেত, যা নীলকরদের অত্যাচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।
গুরুত্ব:
এই বিদ্রোহের চাপে সরকার ‘নীল কমিশন’ গঠন করতে বাধ্য হয়। কমিশনের সুপারিশে বাংলায় বলপূর্বক নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। এটি ছিল বাংলার কৃষকদের প্রথম সংগঠিত ও সফল প্রতিরোধ।
৭. চুয়াড় বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: ব্রিটিশ শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল (মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ধলভূম) অঞ্চলের আদিবাসী চুয়াড়রা যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাই চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধগুলির অন্যতম।
কারণ:
১. ব্রিটিশরা জঙ্গলমহলের জমিদারদের উপর চড়া হারে রাজস্ব চাপায়। সেই রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদাররা তাদের অধীনে কর্মরত পাইকদের জমি কেড়ে নেয়।
২. ব্রিটিশদের নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও অরণ্য আইনের ফলে চুয়াড়দের চিরাচরিত জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।
নেতৃত্ব ও বিস্তার: এই বিদ্রোহের প্রধান নেতারা ছিলেন ধলভূমের দুর্জন সিংহ, গোবর্ধন দিকপতি এবং মেদিনীপুরের রানী শিরোমণি। বিদ্রোহীরা সরকারি খাজনাখানা লুট করে এবং ব্রিটিশ বাহিনীকে একাধিকবার পরাজিত করে।
ফলাফল: ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করলেও, চুয়াড়দের শান্ত করার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ‘জঙ্গলমহল’ নামে একটি পৃথক জেলা গঠন করে।
৮. ফরাজি আন্দোলনের আদর্শ ও কর্মসূচি কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের পূর্ব বাংলায় হাজি শরিয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিঞার নেতৃত্বে পরিচালিত ফরাজি আন্দোলন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও কৃষক আন্দোলন।
আদর্শ:
ফরাজি আন্দোলনের মূল আদর্শ ছিল ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণ। ‘ফরাজ’ কথার অর্থ ‘ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য’। শরিয়তুল্লাহ ইসলাম-বিরোধী সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে কোরান-নির্দেশিত পথে চলার কথা বলেন।
কর্মসূচি:
১. ধর্মীয় সংস্কার: শরিয়তুল্লাহ পিরের প্রতি ভক্তি, মহরম উৎসব পালন ইত্যাদি অ-ইসলামীয় বলে মনে করতেন এবং এগুলি বর্জনের ডাক দেন।
২. অর্থনৈতিক প্রতিবাদ: তাঁর পুত্র দুদু মিঞার নেতৃত্বে আন্দোলনটি কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি ঘোষণা করেন, ‘জমি আল্লাহর দান’, তাই জমির উপর কর বা খাজনা নেওয়ার অধিকার জমিদারদের নেই।
৩. সাংগঠনিক শক্তি: দুদু মিঞা একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন এবং জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন।
৯. টীকা লেখো: তিতুমীরের বিদ্রোহ (বারাসাত বিদ্রোহ)।
উত্তর:
ভূমিকা: বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা মীর নিসার আলি বা তিতুমীর পরিচালিত ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম ‘বারাসাত বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত।
কারণ:
১. তিতুমীর ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন।
২. স্থানীয় জমিদার, বিশেষ করে কৃষ্ণদেব রায়, তিতুমীরের অনুগামীদের উপর ‘দাড়ির উপর কর’ চাপালে বিরোধ শুরু হয়।
৩. জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশদের সম্মিলিত শোষণের বিরুদ্ধে তিতুমীর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।
বাঁশের কেল্লা: তিতুমীর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের কাছে নারকেলবেড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং নিজেকে ‘বাদশাহ’ বলে ঘোষণা করেন।
পতন: ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের পাঠানো বিশাল ব্রিটিশ বাহিনীর গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লার পতন ঘটে এবং তিতুমীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তা পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
১০. পাবনা কৃষক বিদ্রোহের কারণ ও বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তর:
১৮৭০-এর দশকে পূর্ব বাংলার পাবনা জেলায় জমিদারদের বিরুদ্ধে যে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তা পাবনা বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
কারণ:
১. ১৮৫৯ সালের ‘দশম আইন’ (Act X) অনুযায়ী কৃষকদের জমিতে যে স্বত্ব জন্মেছিল, জমিদাররা তা অস্বীকার করত।
২. জমিদাররা বেআইনিভাবে কর বা ‘আবওয়াব’ বৃদ্ধি করত এবং কৃষকদের উচ্ছেদ করত।
৩. জমির মাপ ও হিসাবপত্রে কারচুপি করে জমিদাররা কৃষকদের ঠকাতো।
বৈশিষ্ট্য:
১. এই বিদ্রোহ ছিল মূলত জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নয়। বিদ্রোহীরা বলত, ‘আমরা মহারানির প্রজা হতে চাই’।
২. এটি ছিল একটি শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ আন্দোলন। কৃষকরা নিজেদের ইউনিয়ন গঠন করে এবং আইনি লড়াই চালায়।
৩. এই বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিয়েছিল, তাই এর কোনো সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছিল না।
১১. টীকা লেখো: সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ।
উত্তর:
ভূমিকা: ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০) পর থেকে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সন্ন্যাসী ও ফকিররা যে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়েছিল, তাই সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
কারণ:
১. ব্রিটিশ সরকার তীর্থযাত্রার উপর কর বসালে সন্ন্যাসী ও ফকিররা ক্ষুব্ধ হয়।
২. কোম্পানির চড়া রাজস্বনীতির ফলে বহু কৃষক ও কারিগর সর্বস্বান্ত হয়ে বিদ্রোহে যোগ দেয়।
৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহতা সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়িয়ে তোলে।
নেতৃত্ব ও প্রকৃতি: এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য নেতারা ছিলেন মজনু শাহ, মুশা শাহ, ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণী। এটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম প্রতিরোধগুলির অন্যতম। তবে এর কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সুসংগঠিত পরিকল্পনা না থাকায় শেষ পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন।
১২. কোল বিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোল উপজাতির মানুষেরা যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তা কোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
কারণ:
১. ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে কোলদের চিরাচরিত জমির অধিকার নষ্ট হয়।
২. বহিরাগত ‘দিকু’ (হিন্দু, মুসলিম, শিখ) মহাজন ও জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার চরমে ওঠে।
৩. ব্রিটিশ আইন ও আদালত কোলদের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।
৪. তাদের প্রিয় পানীয় হাঁড়িয়ার উপর কর বসানো হলে তারা ক্ষুব্ধ হয়।
গুরুত্ব:
বুদ্ধু ভগত, জোয়া ভগত, সুই মুন্ডার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। ব্রিটিশ সরকার কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করলেও এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই বিদ্রোহের পরেই সরকার কোলদের জন্য ‘সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি’ নামে একটি পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট গঠন করে এবং তাদের চিরাচরিত আইনকানুনকে স্বীকৃতি দেয়।
১৩. ব্রিটিশ সরকার কেন উপজাতি বিদ্রোহ দমনে কঠোর নীতি নিয়েছিল?
উত্তর:
ব্রিটিশ সরকার উপজাতি বিদ্রোহ দমনে কঠোর নীতি নিয়েছিল কারণ:
১. সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব রক্ষা: উপজাতি বিদ্রোহগুলি প্রায়শই অত্যন্ত হিংসাত্মক হত এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিত। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য এই বিদ্রোহগুলি কঠোরভাবে দমন করা জরুরি ছিল।
২. অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা: উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক স্বার্থ, যেমন—রেলপথ নির্মাণ, খনিজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য এই অঞ্চলগুলিকে শান্ত রাখা প্রয়োজন ছিল।
৩. অন্যান্যদের জন্য উদাহরণ তৈরি: একটি বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করে সরকার অন্যান্য সম্ভাব্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির কাছে একটি বার্তা পাঠাতে চাইত যে, ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করলে তার ফল ভয়ঙ্কর হবে।
৪. সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা: নিজেদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতীয়দের মনে ভয় তৈরি করাও এই কঠোর নীতির অন্যতম কারণ ছিল।
১৪. বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে সম্পর্ক কী?
উত্তর:
বিদ্রোহ ও বিপ্লব শব্দদুটি প্রায়শই একসঙ্গে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ও সম্পর্ক রয়েছে।
সম্পর্ক:
১. কারণ ও ফল: বিদ্রোহকে অনেক সময় বিপ্লবের পূর্বশর্ত বা প্রথম ধাপ হিসেবে দেখা হয়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছোটখাটো বিদ্রোহ জমতে জমতে একসময় তা বড় আকার নিয়ে বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে।
২. উদ্দেশ্যের রূপান্তর: একটি আন্দোলন বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হয়েও পরবর্তীকালে তার লক্ষ্য ও কর্মসূচির পরিবর্তনের মাধ্যমে বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন, ফরাসি বিপ্লব প্রথমে ছিল শুধুমাত্র রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পরে তা সমগ্র সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের বিপ্লবে পরিণত হয়।
পার্থক্য: বিদ্রোহের লক্ষ্য সীমিত (যেমন—কর কমানো), কিন্তু বিপ্লবের লক্ষ্য ব্যাপক (যেমন—শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন)। বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু সফল হলে তা বিপ্লব হয়ে ওঠে।
১৫. সাঁওতাল বিদ্রোহকে কি ‘শ্রেণি সংগ্রাম’ বলা যায়?
উত্তর:
হ্যাঁ, সাঁওতাল বিদ্রোহকে অনেকাংশে ‘শ্রেণি সংগ্রাম’ বলা যেতে পারে।
যুক্তি:
১. শোষক ও শোষিতের লড়াই: এই বিদ্রোহ ছিল মূলত শোষিত সাঁওতাল কৃষক শ্রেণির সঙ্গে শোষক শ্রেণির (বহিরাগত জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী) লড়াই। সাঁওতালরা তাদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধেই অস্ত্র তুলে নিয়েছিল।
২. জমির অধিকারের প্রশ্ন: সাঁওতালদের চিরাচরিত যৌথ মালিকানার জমি কেড়ে নিয়ে ব্রিটিশরা যে ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা চালু করে, তা ছিল সরাসরি সাঁওতাল কৃষক শ্রেণির উপর ভূস্বামী শ্রেণির আক্রমণ।
৩. ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ: এই বিদ্রোহে সাঁওতালরা একটি শোষিত শ্রেণি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তাদের শত্রু ছিল একটি নির্দিষ্ট শোষক শ্রেণি, কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাতির মানুষ নয়।
তবে এটি শুধুমাত্র শ্রেণি সংগ্রাম ছিল না, এর সঙ্গে জাতিগত পরিচয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নও জড়িত ছিল। তাই একে একটি ‘শ্রেণি-জাতিগত সংগ্রাম’ (class-cum-ethnic struggle) বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।
১৬. টীকা লেখো: রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩)।
উত্তর:
ভূমিকা: ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের রংপুর বিদ্রোহ।
কারণ:
ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে রংপুরের ইজারাদার দেবী সিংহ প্রজাদের উপর চড়া হারে রাজস্ব চাপান এবং তা আদায়ের জন্য অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করেন। রাজস্ব দিতে না পারলে কৃষকদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। এই ভয়াবহ শোষণের বিরুদ্ধেই কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
নেতৃত্ব ও ঘটনা: এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন নুরুলউদ্দিন। তিনি নিজেকে ‘নবাব’ বলে ঘোষণা করেন এবং দয়ারাম শীলকে তাঁর ‘দেওয়ান’ নিযুক্ত করেন। বিদ্রোহীরা সম্মিলিতভাবে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং দেবী সিংহের অনুচরদের আক্রমণ করে।
ফলাফল: ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে। বহু কৃষক নিহত হয় এবং নুরুলউদ্দিন আহত হয়ে পালিয়ে যান। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এটি প্রমাণ করে যে, কৃষকরা संगठितভাবে অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে পারে।
১৭. উনিশ শতকের কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহগুলির ব্যর্থতার সাধারণ কারণ কী ছিল?
উত্তর:
উনিশ শতকে একাধিক কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও সেগুলি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এর সাধারণ কারণগুলি হল:
১. স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন চরিত্র: বিদ্রোহগুলি ছিল মূলত স্থানীয় এবং একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সমন্বয় ছিল না। এগুলির কোনো সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল না।
২. সনাতন অস্ত্রশস্ত্র: বিদ্রোহীরা মূলত তীর, ধনুক, তরোয়াল, বল্লমের মতো সনাতন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। অন্যদিকে, ব্রিটিশ বাহিনী আধুনিক বন্দুক ও কামান ব্যবহার করত।
৩. যোগ্য নেতৃত্বের অভাব: বেশিরভাগ বিদ্রোহের কোনো দূরদর্শী ও সুসংগঠিত নেতৃত্ব ছিল না। নেতারা আবেগপ্রবণ হলেও রণকৌশলে পারদর্শী ছিলেন না।
৪. নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব: বিদ্রোহগুলির কোনো সুস্পষ্ট বা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল না। স্থানীয় অত্যাচারীদের বিতাড়ন করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না।
১৮. নীল বিদ্রোহে ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার ভূমিকা লেখো।
উত্তর:
১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহের সমর্থনে জনমত গঠনে ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।
ভূমিকা:
১. নির্ভীক সাংবাদিকতা: পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নীলকর সাহেবদের শোষণ, বেআইনি কার্যকলাপ এবং চাষিদের উপর অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ করতেন।
২. শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ: এই পত্রিকার মাধ্যমেই কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম নীলচাষিদের দুর্দশার কথা জানতে পারে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।
৩. প্রতিবাদের ভাষা: পত্রিকাটি নীলকরদের ‘নীল বাঁদর’ বলে কটাক্ষ করে এবং তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করে।
৪. চাষিদের আশ্রয়স্থল: হরিশচন্দ্র শুধুমাত্র লেখালিখিই করেননি, তিনি তাঁর বাড়িতে অত্যাচারিত নীলচাষিদের আশ্রয় দিতেন এবং তাদের আইনি পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তাও করতেন। এক কথায়, ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ ছিল নীলচাষিদের প্রধান মুখপাত্র।
১৯. ‘আমরা মহারানির প্রজা হতে চাই’— এই উক্তিটির তাৎপর্য কী?
উত্তর:
এই উক্তিটি পাবনা কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭০-এর দশক) প্রধান স্লোগান ছিল। এর তাৎপর্য হল:
১. ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য: এই স্লোগান থেকে বোঝা যায় যে, পাবনার কৃষকদের বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ছিল না। তারা মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকে মেনে নিয়েছিল।
২. জমিদার-বিরোধী মনোভাব: তাদের মূল ক্ষোভ ছিল স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে, যারা বেআইনিভাবে কর বৃদ্ধি করত এবং তাদের উপর অত্যাচার চালাত। কৃষকরা মনে করত, মহারানির শাসনে থাকলে তারা জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তি পাবে।
৩. আইনানুগ মানসিকতা: এটি বিদ্রোহীদের আইনানুগ ও শান্তিপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়। তারা হিংসার পথে না গিয়ে শুধুমাত্র জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তি চেয়ে সরাসরি মহারানির প্রজা হতে চেয়েছিল। এই কারণেই এই বিদ্রোহ অন্যান্য হিংসাত্মক বিদ্রোহ থেকে স্বতন্ত্র ছিল।
২০. সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলাফল কী হয়েছিল?
উত্তর:
সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) ব্রিটিশ সরকার কঠোরভাবে দমন করলেও এর কিছু সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল।
ফলাফল:
১. পৃথক সাঁওতাল পরগনা গঠন: বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, সাঁওতালদের ক্ষোভ প্রশমিত করা প্রয়োজন। তাই সরকার ভাগলপুর ও বীরভূমের কিছু অংশ নিয়ে ‘সাঁওতাল পরগনা’ নামে একটি পৃথক নন-রেগুলেশন জেলা গঠন করে।
২. পৃথক আইন প্রবর্তন: এই নতুন জেলায় ব্রিটিশদের সাধারণ আইনকানুন কার্যকর না করে সাঁওতালদের নিজস্ব সামাজিক ও বিচারব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
৩. বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ: সাঁওতাল পরগনায় বহিরাগত মহাজন ও ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
৪. অনুপ্রেরণা: এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরবর্তীকালের বহু কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
২১. টীকা লেখো: দেবী সিংহ।
উত্তর:
দেবী সিংহ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে রংপুর ও দিনাজপুরের একজন অত্যাচারী ইজারাদার।
কার্যাবলী:
১. তিনি এই অঞ্চলের কৃষকদের উপর অত্যন্ত চড়া হারে রাজস্ব চাপান।
২. রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি প্রজাদের উপর অবর্ণনীয় শারীরিক অত্যাচার চালাতেন, তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি কেড়ে নিতেন।
৩. তাঁর শোষণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের কৃষকরা নুরুলউদ্দিনের নেতৃত্বে এক ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা ‘রংপুর বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত।
দেবী সিংহ ছিলেন ব্রিটিশ শাসনামলে দেশীয় ইজারাদার ও বেনিয়ানদের প্রজাশোষণের এক নিকৃষ্ট উদাহরণ।
২২. ফরাজি আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন?
উত্তর:
ফরাজি আন্দোলন বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়েছিল:
১. যোগ্য নেতৃত্বের অভাব: ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিঞার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নোয়া মিঞা বা আব্দুল গফুরের নেতৃত্বে সেই সাংগঠনিক দৃঢ়তা ছিল না। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।
২. ব্রিটিশদের কঠোর দমননীতি: ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে তাদের শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে এবং কঠোর হস্তে দমন করে। দুদু মিঞাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করা হয়।
৩. অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা: আন্দোলনটি শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর কোনো সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল না। এছাড়া, রক্ষণশীল মুসলিমদের একাংশও এই আন্দোলনের বিরোধিতা করত।
৪. লক্ষ্যের অস্পষ্টতা: ধর্মীয় সংস্কার দিয়ে শুরু হয়ে কৃষক আন্দোলনে পরিণত হলেও, এর কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না।
২৩. ‘বিদ্রোহ’ বলতে কী বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর:
সংজ্ঞা: কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত কোনো আইন, ব্যবস্থা বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র প্রতিবাদ গড়ে তোলাকে ‘বিদ্রোহ’ বলা হয়। এটি সাধারণত কোনো ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তনের দাবি জানায়।
বৈশিষ্ট্য:
১. বিদ্রোহ সাধারণত স্থানীয় হয় এবং এর পরিধি সীমিত থাকে।
২. এটি কোনো একটি বা একাধিক নির্দিষ্ট দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যেমন—কর কমানো বা অত্যাচার বন্ধ করা।
৩. বিদ্রোহের লক্ষ্য সমগ্র ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, বরং ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা।
৪. বিদ্রোহ অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় এবং এর কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকে না।
২৪. নীলকররা কীভাবে নীলচাষিদের উপর অত্যাচার করত?
উত্তর:
নীলকর সাহেবরা নীলচাষিদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাত।
অত্যাচারের ধরন:
১. দাদনের জাল: তারা স্বল্প পরিমাণ দাদন দিয়ে চাষিদের নীল চাষের চুক্তিতে আবদ্ধ করত, যা থেকে চাষিরা আর বেরোতে পারত না।
২. শারীরিক নির্যাতন: কোনো চাষি নীল চাষ করতে অস্বীকার করলে তাদের ধরে এনে কুঠিতে আটকে রাখা হত, চাবুক দিয়ে মারা হত এবং নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হত।
৩. সম্পত্তি ধ্বংস: চাষিদের অবাধ্য করার জন্য তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হত, গবাদি পশু কেড়ে নেওয়া হত এবং পরিবারের মহিলাদের সম্মানহানি করা হত।
৪. মিথ্যা মামলা: নীলকররা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে প্রায়ই চাষিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করত এবং তাদের জেলে পাঠাত।
২৫. ‘জঙ্গলমহল’-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর:
পরিচয়: ব্রিটিশ শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং ছোটনাগপুরের (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) মানভূম ও ধলভূম পরগনার অরণ্য অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে একত্রে ‘জঙ্গলমহল’ বলা হত।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল মূলত ভূমিজ, লোধা, শবর প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়, যাদের সাধারণভাবে ‘চুয়াড়’ বলা হত। তারা বংশানুক্রমে স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কাজ করত।
বিদ্রোহ ও ফলাফল: ব্রিটিশদের নতুন রাজস্ব নীতির ফলে তাদের জীবিকা বিপন্ন হলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহের পরেই ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলকে প্রশাসনিকভাবে স্থিতিশীল করার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ‘জঙ্গলমহল’ নামে একটি পৃথক জেলা গঠন করে।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৮ (১০টি)
১. সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) কারণ, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ব্রিটিশ ভারতে সংঘটিত উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ বা ‘হুল’। সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
কারণ:
১. অর্থনৈতিক শোষণ: ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে সাঁওতালদের উপর চড়া হারে করের বোঝা চাপে। বহিরাগত ‘দিকু’ মহাজনরা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে তাদের জমিজমা আত্মসাৎ করত।
২. ব্যবসায়ীদের প্রতারণা: বহিরাগত ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে কম দামে ফসল কিনত এবং ‘কেনারাম’ (বেশি ওজনের) ও ‘বেচারাম’ (কম ওজনের) নামক দু’রকম বাটখারা ব্যবহার করে তাদের ঠকাতো।
৩. ব্রিটিশ আইন ও বিচারব্যবস্থা: ব্রিটিশ আইন ছিল জটিল ও ব্যয়বহুল। আদালত ও পুলিশ প্রায়শই মহাজন ও জমিদারদের পক্ষ নিত, ফলে সাঁওতালরা কোনো ন্যায়বিচার পেত না।
৪. সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ: ব্রিটিশ কর্মচারী ও মিশনারিরা সাঁওতালদের নিজস্ব সংস্কৃতি, উৎসব ও জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করত, যা তাদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।
বৈশিষ্ট্য:
১. এই বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত হিংসাত্মক এবং এর লক্ষ্য ছিল ‘দিকু’ ও ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করা।
২. হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরিব কামার, কুমোর, তাঁতিরাও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, যা একে এক গণসংগ্রামের চরিত্র দেয়।
গুরুত্ব:
এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে দমন করলেও এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সরকার সাঁওতালদের জন্য ‘সাঁওতাল পরগনা’ নামে একটি পৃথক জেলা গঠন করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে তাদের নিজস্ব আইনকানুনকে স্বীকৃতি দেয়। এই বিদ্রোহ পরবর্তীকালের বহু কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
২. নীল বিদ্রোহের কারণ কী ছিল? এই বিদ্রোহে বাংলার শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সংঘটিত নীল বিদ্রোহ ছিল কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এটি ছিল বিদেশি নীলকর সাহেবদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের এক संगठित প্রতিরোধ।
কারণ:
১. দাদন প্রথা: নীলকররা চাষিদের নামমাত্র অগ্রিম বা ‘দাদন’ দিয়ে তাদের সবচেয়ে উর্বর জমিতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। এই দাদনের জালে একবার জড়িয়ে পড়লে চাষিরা বংশপরম্পরায় নীলকরদের ক্রীতদাসে পরিণত হত।
২. কম মূল্য ও প্রতারণা: নীলকররা বাজার দরের অনেক কম দামে চাষিদের কাছ থেকে নীল কিনত এবং ওজন ও হিসাবে কারচুপি করত।
৩. অবর্ণনীয় অত্যাচার: কোনো চাষি নীল চাষ করতে অস্বীকার করলে নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনী তাদের উপর অবর্ণনীয় শারীরিক অত্যাচার চালাত, তাদের বাড়িঘর লুটপাট ও জ্বালিয়ে দেওয়া হত এবং পরিবারের মহিলাদের সম্মানহানি করা হত।
৪. আইনের অপব্যবহার: ১৮৫৯ সালের ‘পঞ্চম আইন’-এর মতো আইনগুলি নীলকরদের পক্ষে ছিল, যা চাষিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।
শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা:
নীল বিদ্রোহ অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহ থেকে স্বতন্ত্র ছিল কারণ এটি বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল।
১. ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’: হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করে জনমত গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন।
২. ‘নীলদর্পণ’: দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি নীলচাষিদের দুর্দশার এক জীবন্ত ছবি তুলে ধরে শিক্ষিত সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে।
৩. আইনি ও সাংগঠনিক সাহায্য: শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন ঘোষের মতো সাংবাদিক ও আইনজীবীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষিদের সংগঠিত করেন এবং তাদের আইনি সহায়তা দেন।
উপসংহার: শিক্ষিত শ্রেণির এই সক্রিয় সমর্থনের ফলেই নীল বিদ্রোহ এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে ‘নীল কমিশন’ গঠন করে বাংলায় বলপূর্বক নীল চাষ বন্ধ করতে বাধ্য করে।
৩. ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে মুসলিম সমাজে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন হল ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন। দুটিরই লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণ, কিন্তু তাদের চরিত্র, পরিধি ও কর্মসূচিতে পার্থক্য ছিল।
সাদৃশ্য:
১. ধর্মীয় উৎস: উভয় আন্দোলনের উৎস ছিল ধর্মীয়। দুটিই ইসলাম ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করা অ-ইসলামীয় রীতিনীতি দূর করে কোরান-নির্দেশিত পথে ফিরে যাওয়ার কথা বলে।
২. ব্রিটিশ-বিরোধিতা: উভয় আন্দোলনই ভারতকে ‘দার-উল-হারব’ (বিধর্মীর দেশ) বলে মনে করত এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করত।
৩. কৃষক চরিত্র: উভয় আন্দোলনই পরবর্তীকালে দরিদ্র মুসলিম কৃষক ও কারিগরদের সমর্থন লাভ করে এবং জমিদার-মহাজন-নীলকর বিরোধী কৃষক সংগ্রামে পরিণত হয়।
বৈসাদৃশ্য:
১. পরিধি: ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব ছিল সর্বভারতীয়। এর প্রধান কেন্দ্র ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিতানা এবং ভারতে পাটনা। অন্যদিকে, ফরাজি আন্দোলনের প্রভাব মূলত পূর্ব বাংলার (ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
২. লক্ষ্য: ওয়াহাবিদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে ভারতে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ফরাজিদের লক্ষ্য ছিল মূলত স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করা।
৩. সংগঠন ও স্থায়িত্ব: ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল অনেক বেশি সংগঠিত, এর একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও কর ব্যবস্থা ছিল এবং এটি প্রায় ৫০ বছর ধরে চলেছিল। ফরাজি আন্দোলন মূলত দুদু মিঞার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর এটি দুর্বল হয়ে পড়ে।
উপসংহার: এই পার্থক্য সত্ত্বেও, উভয় আন্দোলনই উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিল।
৪. উনিশ শতকে সংঘটিত কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহগুলির কারণ কী ছিল? এই বিদ্রোহগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে তাদের প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, আইনকানুন এবং শোষণ নীতির ফলে উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।
সাধারণ কারণ:
১. উচ্চহারে ভূমিরাজস্ব: কোম্পানির প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারি, মহালওয়ারি) মূল লক্ষ্য ছিল অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়। এই চড়া রাজস্বের চাপে কৃষক ও আদিবাসী সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়।
২. বহিরাগতদের শোষণ: নতুন ব্যবস্থার ফলে জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী (‘দিকু’) প্রভৃতি বহিরাগত শোষক শ্রেণির উদ্ভব হয়, যারা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বা প্রতারণা করে কৃষক ও আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিত।
৩. অরণ্য আইন: ব্রিটিশদের তৈরি অরণ্য আইন আদিবাসীদের জঙ্গলের উপর চিরাচরিত অধিকার (যেমন—কাঠ সংগ্রহ, পশুচারণ, ঝুম চাষ) কেড়ে নেয়, যা তাদের জীবন-জীবিকার উপর চরম আঘাত হানে।
৪. ব্রিটিশ আইন ও বিচারব্যবস্থা: ব্রিটিশ আদালত ছিল জটিল, ব্যয়বহুল এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। বিচারকরা প্রায়শই শোষকদের পক্ষ নিতেন, ফলে শোষিতরা কোনো ন্যায়বিচার পেত না।
বিদ্রোহগুলির চরিত্র:
১. স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন: বিদ্রোহগুলি (যেমন—চুয়াড়, কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা) ছিল মূলত স্থানীয় এবং একটির সঙ্গে অপরটির কোনো সমন্বয় ছিল না।
২. স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ: এগুলি ছিল মূলত শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এর কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের পরিকল্পনা ছিল না।
৩. ধর্মীয় অনুষঙ্গ: অনেক বিদ্রোহের সঙ্গেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষঙ্গ জড়িত ছিল। নেতারা প্রায়ই নিজেদের ঈশ্বরের দূত বলে প্রচার করতেন (যেমন—বিরসা মুন্ডা)।
৪. হিংসাত্মক রূপ: অত্যাচার চরমে উঠলে বিদ্রোহীরা প্রায়শই হিংসার পথ বেছে নিত এবং শোষক মহাজন, জমিদারদের হত্যা করত।
উপসংহার: এই বিদ্রোহগুলি ব্রিটিশদের উন্নত অস্ত্রের সামনে ব্যর্থ হলেও, এগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণের চরিত্রকে উন্মোচিত করে এবং পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করে।
৫. মুন্ডা বিদ্রোহের (উলগুলান) কারণ ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের শেষভাগে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ছোটনাগপুর অঞ্চলে যে শক্তিশালী উপজাতি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, তা মুন্ডা বিদ্রোহ বা ‘উলগুলান’ (ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা) নামে পরিচিত।
কারণ:
১. ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ও ‘খুঁৎকাঠি’ প্রথার বিলোপ: ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে মুন্ডাদের চিরাচরিত ‘খুঁৎকাঠি’ বা জমির যৌথ মালিকানার প্রথা ভেঙে যায় এবং জমির উপর তাদের অধিকার 사라 যায়।
২. ‘দিকু’দের শোষণ: বহিরাগত ‘দিকু’ (জমিদার, মহাজন, ঠিকাদার)দের শোষণ মুন্ডাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তারা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে মুন্ডাদের জমি কেড়ে নিত।
৩. বেগার শ্রম বা ‘বেট-বেগারি’: জমিদার ও ব্রিটিশ ঠিকাদাররা মুন্ডাদের বিনা পারিশ্রমিকে বা নামমাত্র পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য করত, যা ‘বেট-বেগারি’ প্রথা নামে পরিচিত।
৪. খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ: খ্রিস্টান মিশনারিরা মুন্ডাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করলে তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি সংকটের মুখে পড়ে। প্রথমদিকে মিশনারিরা সাহায্য করলেও, পরে তারা সরকারের পক্ষ নিলে মুন্ডারা হতাশ হয়।
বিরসার নেতৃত্ব: এই পরিস্থিতিতে বিরসা মুন্ডা নিজেকে ‘ধরতী আবা’ (পৃথিবীর পিতা) ও ঈশ্বরের দূত হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি এক নতুন ধর্মমত (‘বিরসাইত ধর্ম’) প্রচার করেন এবং দিকু ও ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে এক স্বাধীন ও শোষণমুক্ত ‘মুন্ডা রাজ’ প্রতিষ্ঠার ডাক দেন।
গুরুত্ব:
ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করে এবং বিরসাকে গ্রেপ্তার করে। জেলে কলেরায় তাঁর মৃত্যু হলেও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।
১. এই বিদ্রোহের ফলেই সরকার ‘ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন’ (১৯০৮) পাস করতে বাধ্য হয়।
২. এই আইনের দ্বারা মুন্ডাদের ‘খুঁৎকাঠি’ প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং বেগার শ্রম প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।
৩. এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে, আদিবাসী সমাজও সংগঠিতভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।
৬. বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলনের পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের বাংলায় ব্রিটিশ, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, তার মধ্যে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ‘বারাসাত বিদ্রোহ’ নামেও পরিচিত।
আদর্শ ও লক্ষ্য: মীর নিসার আলি বা তিতুমীর মক্কায় গিয়ে ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূর করে ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরণ। কিন্তু দেশে ফিরে তিনি জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচার দেখে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে একটি স্বাধীন ইসলামীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।
জমিদারদের সঙ্গে সংঘাত: স্থানীয় জমিদার, বিশেষ করে পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, তিতুমীরের অনুগামীদের উপর ‘দাড়ির উপর কর’ বসালে বিরোধ তীব্র হয়। তিতুমীর এই বৈষম্যমূলক কর দিতে অস্বীকার করেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন।
বারাসাত বিদ্রোহ ও বাঁশের কেল্লা: তিতুমীর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ও বসিরহাট অঞ্চলে এক বিশাল কৃষক বাহিনীকে সংগঠিত করেন। তিনি নিজেকে ‘বাদশাহ’ এবং তাঁর ভাগ্নে গোলাম মাসুমকে ‘সেনাপতি’ ঘোষণা করে ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করেন। বারাসাতের কাছে নারকেলবেড়িয়া গ্রামে তিনি একটি দুর্ভেদ্য ‘বাঁশের কেল্লা’ নির্মাণ করে তাঁর প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তোলেন।
পতন ও গুরুত্ব: ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের পাঠানো বিশাল ব্রিটিশ বাহিনীর গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লার পতন ঘটে। তিতুমীর যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও, এটি ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের এক মিলিত সংগ্রাম, যা পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
৭. ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহগুলির মূল কারণ কী ছিল? এই বিদ্রোহগুলি কেন ব্যর্থ হয়েছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একাধিক কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলির পিছনে কিছু সাধারণ কারণ বিদ্যমান ছিল এবং কিছু সাধারণ দুর্বলতার কারণে এগুলি ব্যর্থ হয়েছিল।
মূল কারণ:
১. ভূমিরাজস্ব নীতি: ব্রিটিশদের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সহ বিভিন্ন ভূমিরাজস্ব নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধিক রাজস্ব আদায়। এই নীতির ফলে কৃষকদের উপর করের বোঝা বাড়ে এবং তারা জমি হারিয়ে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়।
২. মহাজনী শোষণ: চড়া সুদে ঋণদানকারী মহাজন শ্রেণি এই সময় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কৃষক ও আদিবাসীরা একবার ঋণের জালে জড়ালে আর বেরোতে পারত না এবং অবশেষে তাদের জমি মহাজনদের হাতে চলে যেত।
৩. অরণ্য আইন: ব্রিটিশদের তৈরি অরণ্য আইন আদিবাসীদের বনভূমির উপর চিরাচরিত অধিকার কেড়ে নেয়, যা তাদের জীবন-জীবিকার উপর চরম আঘাত হানে।
৪. ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা: ব্রিটিশ আইন ও আদালত ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এটি ছিল জটিল, ব্যয়বহুল এবং প্রায়শই শোষক জমিদার ও মহাজনদের পক্ষ নিত।
ব্যর্থতার কারণ:
১. স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন চরিত্র: বিদ্রোহগুলি ছিল স্থানীয় প্রকৃতির এবং একটির সঙ্গে অপরটির কোনো যোগাযোগ বা সমন্বয় ছিল না।
২. সনাতন অস্ত্রশস্ত্র: বিদ্রোহীরা মূলত তীর, ধনুক, তরোয়ালের মতো সনাতন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত, যা ব্রিটিশদের আধুনিক বন্দুক ও কামানের সামনে অকার্যকর ছিল।
৩. নেতৃত্বের দুর্বলতা: বেশিরভাগ বিদ্রোহের কোনো দূরদর্শী ও সংগঠিত নেতৃত্ব ছিল না। নেতারা আবেগপ্রবণ হলেও আধুনিক রণকৌশলে পারদর্শী ছিলেন না।
৪. নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব: বিদ্রোহগুলির কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের কোনো সুসংহত পরিকল্পনা ছিল না।
উপসংহার: এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও, বিদ্রোহগুলি ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্রকে উন্মোচিত করে এবং ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ-বিরোধী চেতনার জন্ম দেয়।
৮. ‘আনন্দমঠ’ ও ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কীভাবে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহকে চিত্রিত করেছেন?
উত্তর:
ভূমিকা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) এবং ‘দেবী চৌধুরাণী’ (১৮৮৪) উপন্যাসে ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের পটভূমিতে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের এক নতুন আদর্শ তুলে ধরেছেন।
‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে चित्रण:
১. ‘আনন্দমঠ’-এ বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে একটি হিন্দু সন্তানের (সন্ন্যাসী) বিদ্রোহ হিসেবে দেখিয়েছেন, যার মূল লক্ষ্য হল ‘সন্তান ধর্ম’ পালন করে দেশমাতাকে বিধর্মী মুসলিম শাসনের হাত থেকে মুক্ত করা।
২. তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে কিছুটা পরিবর্তন করে বিদ্রোহের প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলিম শাসকদের দেখিয়েছেন, যদিও বাস্তবে সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।
৩. এই উপন্যাসের মাধ্যমেই তিনি ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্র প্রচার করেন, যা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্রে পরিণত হয়। এখানে ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে তিনি এক শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আখ্যান তৈরি করেছেন।
‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসে चित्रण:
১. এই উপন্যাসে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠকের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে এক আদর্শ নারী চরিত্র এবং নিষ্কাম কর্মের ধারণা তুলে ধরেছেন।
২. এখানে বিদ্রোহের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আদর্শ চরিত্র গঠন এবং কৃষ্ণ-কথিত নিষ্কাম কর্মের দর্শন। দেবী চৌধুরাণী এখানে একজন দস্যুরানি হলেও, তাঁর মূল লক্ষ্য হল আদর্শ স্থাপন করা।
৩. বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও বিদ্রোহের ঐতিহাসিকতাকে ছাপিয়ে নিজের নৈতিক ও দার্শনিক আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।
উপসংহার: বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তথ্যকে ব্যবহার করে মূলত তাঁর স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় আদর্শকেই প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাস দুটিকে খাঁটি ঐতিহাসিক রচনা না বলে, ইতিহাসের আধারে লেখা জাতীয়তাবাদী আখ্যান বলাই শ্রেয়।
৯. টীকা লেখো: (ক) চুয়াড় বিদ্রোহ (খ) কোল বিদ্রোহ।
উত্তর:
(ক) চুয়াড় বিদ্রোহ:
ভূমিকা: ব্রিটিশ শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল (মেদিনীপুর, বাঁকুড়া) অঞ্চলের আদিবাসী চুয়াড়রা যে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাই চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধগুলির অন্যতম।
কারণ: ব্রিটিশরা জঙ্গলমহলের জমিদারদের উপর চড়া হারে রাজস্ব চাপায়। সেই রাজস্ব মেটাতে জমিদাররা তাদের অধীনে কর্মরত পাইকদের নিষ্কর জমি কেড়ে নেয়। এছাড়া, ব্রিটিশদের নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও অরণ্য আইনের ফলে চুয়াড়দের চিরাচরিত জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।
নেতৃত্ব ও বিস্তার: এই বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন দুর্জন সিংহ, অচল সিংহ, গোবর্ধন দিকপতি এবং মেদিনীপুরের রানী শিরোমণি। বিদ্রোহীরা সরকারি খাজনাখানা লুট করে এবং ব্রিটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে।
ফলাফল: ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করলেও, চুয়াড়দের শান্ত করার জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ‘জঙ্গলমহল’ নামে একটি পৃথক জেলা গঠন করে এবং পাইকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।
(খ) কোল বিদ্রোহ:
ভূমিকা: ১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে ছোটনাগপুর অঞ্চলের কোল উপজাতির মানুষেরা ব্রিটিশ শাসন ও বহিরাগত শোষকদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তা কোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।
কারণ: ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফলে কোলদের চিরাচরিত জমির অধিকার নষ্ট হয়। বহিরাগত ‘দিকু’ (হিন্দু, মুসলিম, শিখ) মহাজন ও জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার, বিশেষ করে তাদের নারীদের সম্মানহানি কোলদের বিদ্রোহী করে তোলে। এছাড়া, তাদের প্রিয় পানীয় হাঁড়িয়ার উপর কর বসানো হলে তারা চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়।
নেতৃত্ব ও বিস্তার: বুদ্ধু ভগত, জোয়া ভগত, সুই মুন্ডার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ রাঁচি, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা বহিরাগত দিকুদের হত্যা করে এবং ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করে।
ফলাফল: ব্রিটিশ সরকার নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। তবে এই বিদ্রোহের পর সরকার কোলদের জন্য ‘সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি’ নামে একটি পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট গঠন করে এবং তাদের চিরাচরিত আইনকানুনকে স্বীকৃতি দেয়।
১০. উনিশ শতকের বিভিন্ন কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব কেমন ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে সংঘটিত একাধিক কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব ছিল মিশ্র এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়েছিল।
প্রাথমিক পর্বের উদাসীনতা:
চুয়াড়, কোল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো প্রাথমিক পর্বের উপজাতি বিদ্রোহগুলির প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ছিল মূলত উদাসীন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী। এর কারণগুলি হল:
১. শিক্ষিত শ্রেণি মূলত ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করত। তাই তারা ব্রিটিশ-বিরোধী যেকোনো বিদ্রোহকে সন্দেহের চোখে দেখত।
২. এই বিদ্রোহগুলি ছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরে এবং বিদ্রোহীরা ছিল মূলত অশিক্ষিত আদিবাসী। ফলে তাদের সঙ্গে শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির কোনো মানসিক বা সামাজিক যোগ ছিল না।
৩. বিদ্রোহের হিংসাত্মক প্রকৃতি শিক্ষিত শ্রেণিকে ভীত ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল।
মনোভাবের পরিবর্তন (নীল বিদ্রোহের সময়):
এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে নীল বিদ্রোহের (১৮৫৯-৬০) সময়। এই বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ব্যাপক সহানুভূতি ও সমর্থন জানায়।
১. সংবাদপত্রের সমর্থন: ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা নীলচাষিদের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে।
২. সাহিত্যের ভূমিকা: দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটক শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাদের বিবেককে জাগ্রত করে।
৩. প্রত্যক্ষ সাহায্য: বহু আইনজীবী ও সাংবাদিক গ্রামে গিয়ে চাষিদের সংগঠিত করেন ও আইনি সহায়তা দেন।
উপসংহার: সুতরাং, বলা যায় যে, প্রথমদিকে উদাসীন থাকলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্র উন্মোচিত হওয়ার পর শিক্ষিত বাঙালি সমাজ কৃষক ও উপজাতিদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল।
Class 10 History প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ Question Answer MCQ,অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : class 10 প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ প্রশ্ন উত্তর