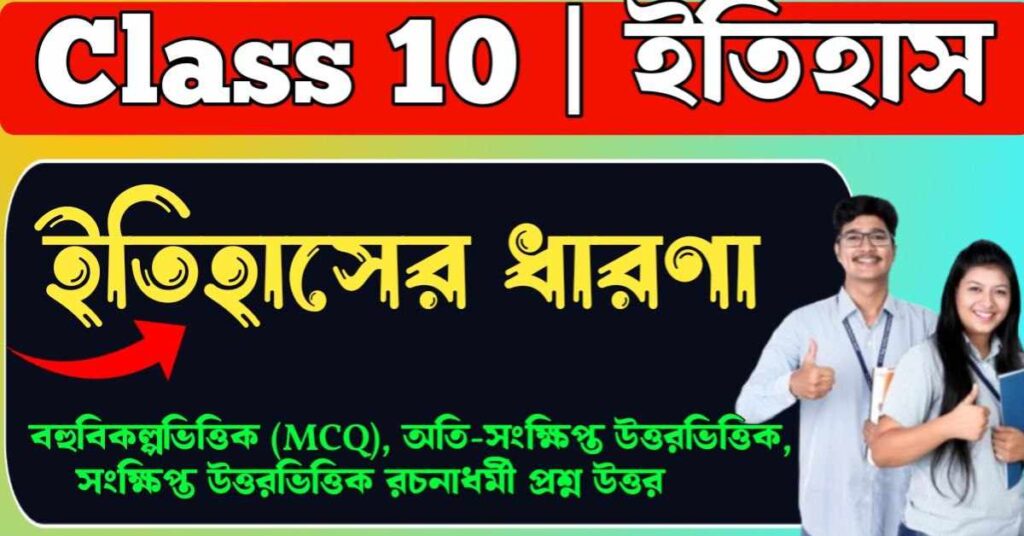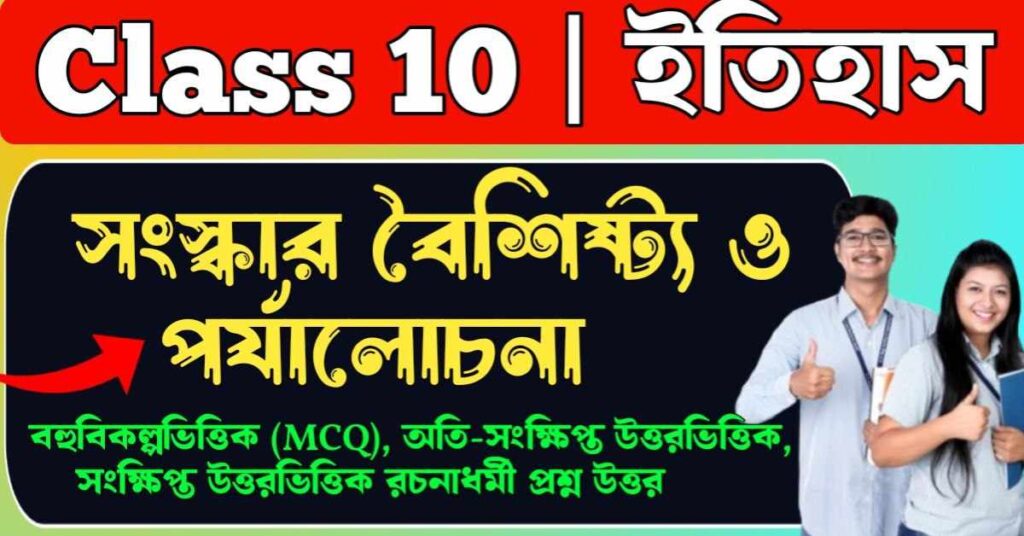সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রথম শহীদ ছিলেন—
২. ‘ভারত সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৩. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি রচনা করেন—
৪. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি অঙ্কন করেন—
৫. ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল—
৬. ‘হিন্দু মেলা’র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—
৭. ‘গোরা’ উপন্যাসটি কার লেখা?
৮. মহারানির ঘোষণাপত্র (১৮৫৮) অনুযায়ী ভারতের ‘প্রথম ভাইসরয়’ হন—
৯. ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি কোন উপন্যাসের অন্তর্গত?
১০. ‘জমিদার সভা’র সভাপতি ছিলেন—
১১. মহাবিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলেছেন—
১২. ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
১৩. ‘ইলবার্ট বিল’ বিতর্কের সঙ্গে কোন ভাইসরয় জড়িত ছিলেন?
১৪. ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন—
১৫. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটির পূর্ব নাম ছিল—
১৬. ‘ সভা-সমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন—
১৭. মহাবিদ্রোহের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—
১৮. ‘ভাইসরয়’ কথাটির অর্থ হল—
১৯. ‘The Great Rebellion’ গ্রন্থটি কার লেখা?
২০. ‘নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার জনক’ বলা হয়—
২১. কানপুরে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন—
২২. হিন্দু মেলার অপর নাম ছিল—
২৩. ‘The First Indian War of Independence, 1857-59’ গ্রন্থটি কার লেখা?
২৪. মহারানির ঘোষণাপত্র জারি করা হয়—
২৫. ‘জমিদার সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
২৬. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন—
২৭. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটিতে দেবীর হাতে ছিল—
২৮. ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়—
২৯. যে আইনের দ্বারা ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে তা হল—
৩০. ‘ন্যাশানাল পেপার’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—
৩১. ‘ভারত সভার’ প্রথম সভাপতি ছিলেন—
৩২. লর্ড লিটনের ‘অস্ত্র আইন’ পাস হয়—
৩৩. ‘জাতিয়তাবাদের গীতা’ বলা হয়—
৩৪. বিহারে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন—
৩৫. ‘Landholders’ Society’ হল—
৩৬. স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের ‘একমাত্র আশা’ হল—
৩৭. মহারানি ভিক্টোরিয়া ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি গ্রহণ করেন—
৩৮. ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’ (ইনকিলাব জিন্দাবাদ) স্লোগানটি প্রথম ব্যবহার করেন—
৩৯. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়—
৪০. ‘আধুনিক ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি’ বলা হয়—
৪১. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
৪২. ‘ইলবার্ট বিল’ পাস হয়—
৪৩. ‘ইন্ডিয়ান লীগ’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৪৪. ‘ झांसीর রানি’ লক্ষ্মীবাইয়ের আসল নাম ছিল—
৪৫. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি প্রকাশিত হত—
৪৬. ‘জাতীয় কংগ্রেস’-এর পূর্বসূরি ছিল—
৪৭. ‘বিপ্লব’ (Revolution) কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়—
৪৮. সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন—
৪৯. ‘নেটিভ প্রেস’ নামে পরিচিত ছিল—
৫০. ‘নব্য বৈষ্ণব ধর্ম’-এর কথা বলা হয়েছে—
৫১. মহাবিদ্রোহকে ‘সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া’ বলেছেন—
৫২. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক ছিলেন—
৫৩. ‘অদ্ভুত লোক’ নামক ব্যঙ্গচিত্রটি কার আঁকা?
৫৪. ‘স্বদেশী ভাবধারার জনক’ বলা হয়—
৫৫. ‘সত্যশোধন’ বইটি কার লেখা?
৫৬. ‘এনফিল্ড রাইফেল’-এর টোটার ঘটনা কোন বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত?
৫৭. ‘হিন্দু মেলার’ সম্পাদক ছিলেন—
৫৮. ‘গোরা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা শেষ পর্যন্ত যে মতবাদে বিশ্বাসী হয়—
৫৯. ‘ভারত সভা’র উদ্যোগে প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—
৬০. ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’ প্রয়োগ করেন—
৬১. ‘রাষ্ট্রগুরু’ নামে পরিচিত ছিলেন—
৬২. ‘বিরূপ বজ্র’ নামক ব্যঙ্গচিত্র গ্রন্থটি কার?
৬৩. ‘সন্তান সম্প্রদায়’ গঠিত হয় কোন উপন্যাসের আধারে?
৬৪. ‘Bengal British India Society’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৬৫. ‘The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
৬৬. ‘জাতীয় শিক্ষা’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন—
৬৭. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি কোন প্রেক্ষাপটে আঁকা হয়েছিল?
৬৮. ‘ভারত সভা’র একজন অ-বাঙালি সদস্য ছিলেন—
৬৯. মহারানির ঘোষণাপত্রটিকে ‘অধিকার ও স্বাধীনতার মহাসনদ’ বলেছেন—
৭০. ‘ভারত সচিব’ পদটি সৃষ্টি হয়—
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ কে ছিলেন?
উত্তর: মঙ্গল পাণ্ডে।
২. ভারত সভা কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু।
৩. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের রচয়িতা কে?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি কে এঁকেছেন?
উত্তর: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫. ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর: বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা।
৬. হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: নবগোপাল মিত্র।
৭. ‘গোরা’ উপন্যাসের লেখক কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮. ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন?
উত্তর: লর্ড ক্যানিং।
৯. ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি কোন উপন্যাসে আছে?
উত্তর: আনন্দমঠ।
১০. জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উত্তর: দ্বারকানাথ ঠাকুর।
১১. কে মহাবিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলেছেন?
উত্তর: বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
১২. ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: স্বামী বিবেকানন্দ।
১৩. ইলবার্ট বিল বিতর্কের সময় ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন?
উত্তর: লর্ড রিপন।
১৪. ভারতের শেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী?
উত্তর: দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর।
১৫. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটির পূর্ব নাম কী ছিল?
উত্তর: বঙ্গমাতা।
১৬. কে উনিশ শতককে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলেছেন?
উত্তর: ঐতিহাসিক অনিল শীল।
১৭. ‘ভাইসরয়’ কথার অর্থ কী?
উত্তর: রাজপ্রতিনিধি।
১৮. ‘নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার জনক’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
১৯. কানপুরে সিপাহী বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?
উত্তর: নানা সাহেব।
২০. হিন্দু মেলার অপর নাম কী ছিল?
উত্তর: চৈত্র মেলা।
২১. মহারানির ঘোষণাপত্র কবে জারি হয়?
উত্তর: ১ নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
২২. একজন ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর নাম লেখো।
উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৩. ভারত সভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে।
২৪. ভারতে কবে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে?
উত্তর: ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে।
২৫. ‘ন্যাশানাল পেপার’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: নবগোপাল মিত্র।
২৬. ‘ভারত সভার’ প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: আনন্দমোহন বসু।
২৭. অস্ত্র আইন কে পাস করেন?
উত্তর: লর্ড লিটন।
২৮. বিহারে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব কে দেন?
উত্তর: কুনওয়ার সিংহ।
২৯. ‘Landholders’ Society’-র বাংলা নাম কী?
উত্তর: জমিদার সভা।
৩০. বিবেকানন্দ কাদের ‘ভারতের একমাত্র আশা’ বলেছেন?
উত্তর: ভারতের সাধারণ মানুষ বা জনগণ’কে।
৩১. মহারানি ভিক্টোরিয়া কবে ‘ভারত সম্রাজ্ঞী’ উপাধি নেন?
উত্তর: ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে।
৩২. ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ কথার অর্থ কী?
উত্তর: বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
৩৩. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে।
৩৪. আধুনিক ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি কাকে বলা হয়?
উত্তর: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে।
৩৫. ‘ভারত সভা’র একটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: সারা ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠন করা।
৩৬. ‘ইলবার্ট বিল’ কী ছিল?
উত্তর: ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার দেওয়ার জন্য প্রস্তাবিত একটি বিল।
৩৭. ইন্ডিয়ান লীগ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: শিশিরকুমার ঘোষ।
৩৮. ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের আসল নাম কী ছিল?
উত্তর: মণিকর্ণিকা তাম্বে।
৩৯. ‘জাতীয় কংগ্রেস’-এর পূর্বসূরি কোন সংগঠনকে বলা হয়?
উত্তর: ভারত সভা’কে।
৪০. মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর-জেনারেল কে ছিলেন?
উত্তর: লর্ড ক্যানিং।
৪১. ‘গোরা’ উপন্যাসের মূল বক্তব্য কী?
উত্তর: সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমালোচনা এবং এক উদার, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী ভারতভাবনার সন্ধান।
৪২. কে মহাবিদ্রোহকে ‘সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া’ বলেছেন?
উত্তর: রজনীপাম দত্ত।
৪৩. ‘অদ্ভুত লোক’ ব্যঙ্গচিত্রটি কার আঁকা?
উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
৪৪. ‘স্বদেশী ভাবধারার জনক’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: রাজনারায়ণ বসুকে।
৪৫. এনফিল্ড রাইফেলের টোটায় কী মেশানো আছে বলে গুজব রটে?
উত্তর: গরু ও শূকরের চর্বি।
৪৬. ‘রাষ্ট্রগুরু’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
৪৭. ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’ কে প্রবর্তন করেন?
উত্তর: লর্ড ডালহৌসি।
৪৮. ভারত সভার প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে।
৪৯. ‘ভারত সচিব’ পদটি কোথায় সৃষ্টি করা হয়েছিল?
উত্তর: লন্ডনে।
৫০. ‘বিদ্রোহ’ (Revolt) ও ‘বিপ্লব’ (Revolution) শব্দ দুটির অর্থ কী?
উত্তর: বিদ্রোহ হল সীমিত প্রতিবাদ, আর বিপ্লব হল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।
৫১. ‘Eighteen Fifty-Seven’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন।
৫২. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
৫৩. ‘ভারতমাতা’ চিত্রটিতে দেবীর কয়টি হাত দেখানো হয়েছে?
উত্তর: চারটি।
৫৪. কে মহাবিদ্রোহকে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ ছাড়া আর কিছু বলতে নারাজ ছিলেন?
উত্তর: ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার।
৫৫. ‘বিপিনচন্দ্র পাল’ কোন পত্রিকায় ‘আনন্দমঠ’কে ‘জাতীয়তাবাদের বাইবেল’ বলেছেন?
উত্তর: ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায়।
৫৬. ‘ভারতমাতা’ কোন ভাবাদর্শে নির্মিত?
উত্তর: স্বদেশী ভাবাদর্শে।
৫৭. ‘Indian National Conference’ কে আহ্বান করেন?
উত্তর: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৮. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের পটভূমি কী?
উত্তর: ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ।
৫৯. ‘ভারত সভা’র সঙ্গে যুক্ত একজন অ-বাঙালি নেতার নাম লেখো।
উত্তর: এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার।
৬০. ‘জাতীয়’ শব্দটি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল?
উত্তর: হিন্দু মেলা।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. মহারানির ঘোষণাপত্রের (১৮৫৮) দুটি প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: (১) মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমিত করে তাদের আস্থা অর্জন করা। (২) ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ব্রিটিশ রাজের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করা।
২. হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। এর মাধ্যমে দেশীয় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শরীরচর্চার উন্নতি ঘটানোও একটি লক্ষ্য ছিল।
৩. ইলবার্ট বিল বিতর্ক কী?
উত্তর: ভাইসরয় লর্ড রিপনের আইন-সচিব ইলবার্ট একটি বিল আনেন, যার দ্বারা ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এর বিরুদ্ধে ভারতের শ্বেতাঙ্গরা তীব্র আন্দোলন শুরু করে, যা ‘ইলবার্ট বিল বিতর্ক’ নামে পরিচিত।
৪. ভারত সভা প্রতিষ্ঠার দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
উত্তর: (১) সারা ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠন করা। (২) ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
৫. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি কীভাবে জাতীয়তাবাদকে অনুপ্রাণিত করেছিল?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে দেশমাতাকে দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমের এক শক্তিশালী মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাস ও সংগীত পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।
৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ চিত্রটির তাৎপর্য কী?
উত্তর: ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি স্বদেশী যুগে ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। এতে ভারতমাতাকে এক শান্ত, সৌম্য, গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা দেবী রূপে দেখানো হয়েছে, যিনি তাঁর সন্তানদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও দীক্ষা দিচ্ছেন। এটি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে আত্মশক্তির প্রতীক।
৭. ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে বিবেকানন্দ কী বলতে চেয়েছেন?
উত্তর: ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং দেশের যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। তিনি শূদ্র বা সাধারণ মানুষের জাগরণের মাধ্যমে এক নতুন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন।
৮. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) দুটি প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
উত্তর: (১) এনফিল্ড রাইফেলের টোটা প্রচলন, যা গরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি বলে গুজব রটে এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সিপাহির ধর্মনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (২) সৈন্যদের সাধারণ সার্ভিস তালিকাভুক্তি আইন (General Service Enlistment Act) দ্বারা সমুদ্রপারে যেতে বাধ্য করা।
৯. ‘জমিদার সভা’ ও ‘ভারত সভা’র মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।
উত্তর: (১) জমিদার সভা ছিল মূলত জমিদারদের স্বার্থরক্ষার সংগঠন, আর ভারত সভা ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। (২) জমিদার সভার আবেদন ছিল সীমিত, কিন্তু ভারত সভার লক্ষ্য ছিল সারা ভারতে জনমত গঠন করা।
১০. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বেড়ে ওঠা ইংরেজি অনুকরণপ্রিয় ‘বাবু’ সংস্কৃতি, সামাজিক ভণ্ডামি এবং জাতিভেদ প্রথাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন।
১১. ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রকাশ করেছেন?
উত্তর: ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ, উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক গোরা শেষ পর্যন্ত তার আইরিশ পরিচয় জানতে পেরে উপলব্ধি করে যে, ভারতের আসল পরিচয় কোনো ধর্ম বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা এক মহান মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।
১২. মহাবিদ্রোহকে (১৮৫৭) কেন ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলা হয়?
উত্তর: যেহেতু এই বিদ্রোহ মূলত সিপাহিদের অসন্তোষ (যেমন—টোটার ঘটনা, বেতনে বৈষম্য) থেকে শুরু হয়েছিল এবং এর নেতৃত্বও প্রধানত সিপাহিদের হাতেই ছিল, তাই চার্লস রেক্স, জন সিলি প্রমুখ ঐতিহাসিক একে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলে অভিহিত করেছেন।
১৩. ‘বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা’কে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন?
উত্তর: কারণ এই সভাই প্রথম ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে। এটি নিষ্কর জমির উপর কর আরোপের মতো সরকারি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, যা একটি রাজনৈতিক কার্যকলাপ।
১৪. মহাবিদ্রোহের দুটি সামাজিক কারণ লেখো।
উত্তর: (১) ব্রিটিশরা সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের মতো সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করলে রক্ষণশীল হিন্দুরা মনে করে যে, সরকার তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছে। (২) জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ কার্যকলাপ ভারতীয় সমাজকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।
১৫. ‘আত্মশক্তি’র আদর্শ কী ছিল?
উত্তর: ‘আত্মশক্তি’র আদর্শ হল বিদেশি শক্তির উপর নির্ভর না করে নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশের সার্বিক উন্নতি ঘটানো। হিন্দু মেলা এই আদর্শ প্রচার করত এবং দেশীয় ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও শরীরচর্চার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের কথা বলত।
১৬. ‘ভারত সভা’র সিভিল সার্ভিস আন্দোলনের গুরুত্ব কী ছিল?
উত্তর: ভারত সভা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের বসার বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করার প্রতিবাদে সারা ভারতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত সভা প্রথম একটি সর্বভারতীয় ইস্যুতে সফলভাবে জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়।
১৭. ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’ কী?
উত্তর: লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’ অনুসারে, কোনো ব্রিটিশ আশ্রিত দেশীয় রাজ্যের রাজা পুত্রসন্তান ছাড়া মারা গেলে, সেই রাজ্যটি সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে এবং কোনো দত্তক পুত্র উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।
১৮. ‘ভারতমাতা’ চিত্রের চারটি হাতে কী কী ছিল এবং তার প্রতীকী অর্থ কী?
উত্তর: ‘ভারতমাতা’ চিত্রের চারটি হাতে ছিল পুস্তক (শিক্ষা), ধানের শিষ (অন্ন), জপের মালা (দীক্ষা) এবং শ্বেতবস্ত্র (বস্ত্র)। এর প্রতীকী অর্থ হল, ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও দীক্ষা দিচ্ছেন।
১৯. ‘Vernacular Press Act’ বা ‘দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন’ কী?
উত্তর: ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন এই আইন পাস করেন। এর দ্বারা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং বলা হয় যে, সরকারের বিরুদ্ধে কোনো লেখা প্রকাশ করলে সেই পত্রিকার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
২০. মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: (১) বিদ্রোহটি ছিল অসংগঠিত এবং এর কোনো সর্বভারতীয় প্রসার বা যোগ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। (২) ব্রিটিশদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার (টেলিগ্রাফ, রেল) কাছে বিদ্রোহীরা টিকে থাকতে পারেনি।
২১. ‘ঐতিহাসিক’ ও ‘জাতীয়তাবাদী’ ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিরপেক্ষভাবে ঘটনার বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা প্রায়শই আবেগ দ্বারা চালিত হয় এবং কোনো ঘটনাকে জাতির গৌরব বৃদ্ধি বা জাতীয়তাবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মহিমান্বিত করে তোলে।
২২. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান দাবি কী ছিল?
উত্তর: এই সংগঠনের প্রধান দাবি ছিল ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য আইনসভায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা। এছাড়া তারা সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ এবং বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণের দাবিও জানিয়েছিল।
২৩. ‘আনন্দমঠ’-এর সন্তান দলের আদর্শ কী ছিল?
উত্তর: ‘আনন্দমঠ’-এর সন্তান দলের আদর্শ ছিল আত্মসংযম, শৃঙ্খলা এবং নিঃস্বার্থ দেশসেবা। তারা দেশমাতাকে বিদেশি শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।
২৪. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ‘জাতীয় বিদ্রোহ’ বলার দুটি কারণ দেখাও।
উত্তর: (১) এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু অসামরিক মানুষ, কৃষক, কারিগর ও জমিদার এতে যোগ দিয়েছিল। (২) বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে, যা একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দেয়।
২৫. ‘সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা’ অধ্যায়টির নামকরণ কতটা সার্থক?
উত্তর: এই নামকরণ অত্যন্ত সার্থক। কারণ এই অধ্যায়ে মহাবিদ্রোহের মতো ব্যাপক গণ-অসন্তোষ থেকে শুরু করে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ভারত সভার মতো প্রাথমিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ হওয়ার শুরুর দিকের কাহিনীই আলোচনা করা হয়েছে।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. টীকা লেখো: মহারানির ঘোষণাপত্র (১৮৫৮)।
উত্তর:
ভূমিকা: মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমিত করতে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করতে ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়া একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। এলাহাবাদের দরবারে লর্ড ক্যানিং এটি পাঠ করেন।
ঘোষণার বিষয়বস্তু:
১. কোম্পানি শাসনের অবসান: এই ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো হয় এবং ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ রাজ বা মহারানির হাতে তুলে দেওয়া হয়।
২. ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি: সরকার ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
৩. স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল: দেশীয় রাজাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, স্বত্ববিলোপ নীতি আর প্রয়োগ করা হবে না এবং তাদের দত্তক গ্রহণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
৪. যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ: জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
তাৎপর্য: এই ঘোষণাপত্র ভারতীয়দের কিছু অধিকার দিলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করা। এটি ছিল ‘শিক্ষিত ভারতীয়দের জন্য রাজনৈতিক رشوة’।
২. ভারত সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘ভারত সভা’ বা ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
উদ্দেশ্য:
১. ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠন করা।
২. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করা।
৩. হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা।
৪. রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা।
কার্যাবলী:
১. সিভিল সার্ভিস আন্দোলন: সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের বসার বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করার প্রতিবাদে ভারত সভা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে।
২. দমনমূলক আইনের বিরোধিতা: এটি লর্ড লিটনের ‘অস্ত্র আইন’ ও ‘দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন’-এর তীব্র বিরোধিতা করে।
৩. ইলবার্ট বিল সমর্থন: ভারত সভা ইলবার্ট বিলকে সমর্থন জানিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করে।
উপসংহার: ভারত সভাই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করে, যা পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল।
৩. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?
উত্তর:
ভূমিকা: ঐতিহাসিক অনিল শীল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন। এই সময়ে ভারতে, বিশেষ করে বাংলায়, একাধিক রাজনৈতিক সভা-সমিতি গড়ে ওঠে, যা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়।
কারণ:
১. রাজনৈতিক চেতনার প্রসার: পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে এবং তারা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।
২. বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন: এই সময়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), পুনা সার্বজনিক সভা (১৮৭০), ইন্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), ভারত সভা (১৮৭৬), মাদ্রাজ মহাজন সভা (১৮৮৪) প্রভৃতি numerous রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে।
৩. সাংবিধানিক আন্দোলন: এই সভা-সমিতিগুলি মূলত আবেদন-নিবেদন, স্মারকলিপি প্রদান এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে নিজেদের দাবি পেশ করত।
৪. সর্বভারতীয় রূপ: ভারত সভার মতো প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করে, যা ছিল এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই এই সময়কালকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয়।
৪. টীকা লেখো: হিন্দু মেলা।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ‘হিন্দু মেলা’ বা ‘চৈত্র মেলা’ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণায় এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
উদ্দেশ্য:
১. বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব থেকে যুবসমাজকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।
২. ‘আত্মশক্তি’ বা আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার করা।
৩. দেশীয় শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, শরীরচর্চা ইত্যাদির উন্নতি সাধন করা।
৪. হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা।
কার্যাবলী:
প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। এখানে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য, দেশীয় ব্যায়াম ও কুস্তি প্রদর্শিত হত এবং দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ ও সংগীত পরিবেশন করা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিশোর বয়সে এই মেলায় কবিতা পাঠ করেন।
গুরুত্ব: হিন্দু মেলা সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হলেও, এটিই প্রথম ভারতীয়দের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল।
৫. লেখায় ও রেখায় কীভাবে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহিত্য ও শিল্পের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন লেখকের রচনা এবং শিল্পীর আঁকা ছবি দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।
লেখায় জাতীয়তাবাদ:
১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস এবং ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীত বিপ্লবীদের মূল মন্ত্রে পরিণত হয়। তিনি দেশমাতাকে দেবী রূপে কল্পনা করে দেশপ্রেমকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন।
২. স্বামী বিবেকানন্দ: তাঁর ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে তিনি যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী হতে এবং দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। তিনি শূদ্র জাগরণের মাধ্যমে এক নতুন, শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার কথা বলেন।
রেখায় জাতীয়তাবাদ:
১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: তাঁর আঁকা ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি স্বদেশী যুগে জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। এটি ছিল দেশের এক আধ্যাত্মিক ও সৌম্য প্রতিমূর্তি।
২. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর: তিনি তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সমাজ ও বাবু সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন।
এইভাবে, উনিশ শতকের লেখা ও রেখা ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছিল।
৬. ‘আনন্দমঠ’ এবং ‘বর্তমান ভারত’— এই দুটি গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ কীভাবে ফুটে উঠেছে?
উত্তর:
ভূমিকা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ‘বর্তমান ভারত’— এই দুটি গ্রন্থ উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে দুটি ভিন্ন কিন্তু শক্তিশালী ধারা তৈরি করেছিল।
‘আনন্দমঠ’-এ জাতীয়তাবাদ:
১. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমকে ধর্মের সঙ্গে একীভূত করেছেন। তিনি দেশকে ‘মা’ হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং দেশের মুক্তির জন্য সন্ন্যাসী ‘সন্তান’দের আত্মত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেছেন।
২. এই উপন্যাসের ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্রে পরিণত হয়। এটি ছিল এক আবেগময় ও আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ।
‘বর্তমান ভারত’-এ জাতীয়তাবাদ:
১. বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ছিল অনেক বেশি বাস্তববাদী ও কর্মমুখী। তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের তীব্র সমালোচনা করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কথা বলেছেন।
২. তাঁর জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ছিল মানবতাবাদ ও সেবা। তিনি দেশের দরিদ্র, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের (‘শূদ্র’) জাগরণের মাধ্যমে এক শক্তিশালী ও নতুন ভারত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।
উপসংহার: বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে আবেগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ জাগিয়েছেন, বিবেকানন্দ সেখানে কর্ম ও সেবার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী এক নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন।
৭. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব কেমন ছিল?
উত্তর:
মহাবিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব ছিল মূলত উদাসীনতা ও বিরোধিতার। এর কারণগুলি হল:
১. ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আস্থা: শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণি বা ‘ভদ্রলোক’ সমাজ মনে করত যে, ব্রিটিশ শাসনই ভারতের আধুনিকীকরণের একমাত্র পথ। তারা সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহের মতো সংস্কারের জন্য ব্রিটিশদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। তাই তারা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চায়নি।
২. বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে সংশয়: তারা এই বিদ্রোহকে প্রগতিশীল আন্দোলন হিসেবে দেখেনি। বরং এটিকে সিপাহিদের দ্বারা পরিচালিত একটি সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ বলে মনে করত।
৩. হিংসাত্মক কার্যকলাপ: বিদ্রোহের হিংসাত্মক কার্যকলাপ শিক্ষিত শ্রেণিকে ভীত ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তারা শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষে ছিল।
৪. ব্রিটিশদের পক্ষ সমর্থন: এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলি বিদ্রোহের বিরোধিতা করে এবং ব্রিটিশদের প্রতি তাদের আনুগত্য জানায়।
৮. টীকা লেখো: ইলবার্ট বিল বিতর্ক।
উত্তর:
ভূমিকা: ভাইসরয় লর্ড রিপনের আমলে সংঘটিত ইলবার্ট বিল বিতর্ক ছিল ঔপনিবেশিক ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা ব্রিটিশদের বর্ণবিদ্বেষী চরিত্রকে উন্মোচিত করে দেয়।
প্রেক্ষাপট: তৎকালীন ভারতীয় আইন অনুযায়ী, কোনো ভারতীয় বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারতেন না। এই বর্ণবিদ্বেষী আইন দূর করার জন্য রিপনের আইন-সচিব স্যার কোর্টনি ইলবার্ট ১৮৮৩ সালে একটি বিলের খসড়া তৈরি করেন।
বিতর্ক: এই বিলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতের শ্বেতাঙ্গ বা ইউরোপীয় সম্প্রদায় তীব্র আন্দোলন শুরু করে। তারা ‘ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন’ গঠন করে এবং বিলের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি ও প্রচার চালায়। তাদের চাপের মুখে সরকার বিলটি সংশোধন করতে বাধ্য হয়।
ফলাফল: সংশোধিত বিলে বলা হয়, ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারলেও, অভিযুক্ত ব্যক্তি জুরির দাবি করতে পারবেন, যেখানে অন্তত অর্ধেক সদস্য ইউরোপীয় হতে হবে। এই ঘটনা ভারতীয়দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ব্রিটিশ শাসনে ন্যায় ও সাম্যের কোনো স্থান নেই এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া অধিকার আদায় সম্ভব নয়। এটিই পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথকে ত্বরান্বিত করে।
৯. ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন?
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ উপন্যাসটি শুধুমাত্র একটি উপন্যাস নয়, এটি জাতীয়তাবাদ নিয়ে এক গভীর দার্শনিক আলোচনা। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন।
সমালোচনা:
১. উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক ‘গোরা’: উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা ছিল উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক। সে মনে করত, কঠোর হিন্দু আচার-বিচার ও ব্রাহ্মণ্যবাদের মাধ্যমেই ভারতের মুক্তি সম্ভব। সে অন্য ধর্ম, বিশেষ করে ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান ধর্মকে ঘৃণা করত।
২. সংকীর্ণতার প্রকাশ: গোরার এই হিন্দুত্ববাদ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। এটি ভারতের বিশাল মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে এক খণ্ডিত জাতীয়তাবাদের কথা বলত। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের বিভেদকামী জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।
৩. সত্যের উন্মোচন ও মুক্তি: উপন্যাসের শেষে গোরা জানতে পারে যে, সে আসলে এক আইরিশ দম্পতির সন্তান। এই সত্য জানার পর তার সমস্ত জাতি ও ধর্মের অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে, ভারত কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা জাতির দেশ নয়, ভারত হল এক মহামানবের সাগর।
উপসংহার: এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ ‘গোরা’র মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, prawdziwy nacjonalizm opiera się na humanizmie, a nie na nienawiści czy wykluczeniu. (প্রকৃত জাতীয়তাবাদ মানবতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, ঘৃণা বা বর্জনের উপর নয়)।
১০. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) ব্যর্থতার কারণগুলি কী ছিল?
উত্তর:
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়েছিল।
কারণসমূহ:
১. যোগ্য নেতৃত্বের অভাব: বিদ্রোহের কোনো সর্বভারতীয় বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, লক্ষ্মীবাইয়ের মতো স্থানীয় নেতারা বীর হলেও, তাঁদের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। নামমাত্র সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছিলেন দুর্বল ও বয়স্ক।
২. অসংগঠিত ও পরিকল্পনাহীন: বিদ্রোহটি ছিল মূলত স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ছিল না। এটি ভারতের সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ও পাঞ্জাব শান্ত ছিল।
৩. শিক্ষিত শ্রেণির অসহযোগিতা: বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি, যা বিদ্রোহীদের নৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়।
৪. ব্রিটিশদের উন্নত শক্তি: ব্রিটিশদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র (এনফিল্ড রাইফেল, কামান), সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (টেলিগ্রাফ, রেল) এবং যোগ্য সেনাপতিত্বের (ক্যাম্পবেল, হ্যাভলক) কাছে বিদ্রোহীরা টিকে থাকতে পারেনি।
৫. দেশীয় শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা: হায়দ্রাবাদের নিজাম, সিন্ধিয়া, ভূপালের বেগমের মতো বহু দেশীয় শাসক ব্রিটিশদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল।
১১. উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের বিকাশে ‘আনন্দমঠ’-এর ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) উপন্যাসটি উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল। এটিকে ‘জাতীয়তাবাদের গীতা’ বলা হয়।
ভূমিকা:
১. দেশপ্রেম ও ধর্মের সমন্বয়: বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দেশকে ‘মা’ রূপে কল্পনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, দেশপ্রেম ও ধর্ম আলাদা নয়; দেশের সেবা করাই হল প্রকৃত ধর্মপালন। এই ধারণাটি বহু ভারতীয়কে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।
২. ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীত: এই উপন্যাসের ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি ছিল দেশপ্রেমের এক শক্তিশালী প্রকাশ। পরবর্তীকালে এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্রে পরিণত হয় এবং क्रांतिकारীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।
৩. ‘সন্তান’ দলের আদর্শ: উপন্যাসের ‘সন্তান’ দলের সদস্যরা ছিলেন নিঃস্বার্থ, disciplined এবং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত। এই ‘সন্তান’দের আদর্শ পরবর্তীকালের বহু বিপ্লবী সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল।
সীমাবদ্ধতা: তবে, উপন্যাসের তীব্র হিন্দু ভাবাদর্শ এবং মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব এর আবেদনকে কিছুটা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জন্ম দিয়েছিল বলেও অনেকে মনে করেন।
১২. টীকা লেখো: জমিদার সভা।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘জমিদার সভা’ বা ‘Landholders’ Society’ ছিল ভারতের প্রথম প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠন, যা ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্দেশ্য: এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এর সভাপতি। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে থাকা বাংলার জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করা।
কার্যাবলী:
১. জমিদার সভা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করত। তারা আবেদন-নিবেদন ও স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করত।
২. এটিই প্রথম সংগঠন যা শুধুমাত্র জমিদারদের নয়, রায়তদের স্বার্থ নিয়েও কিছু কথা বলেছিল।
৩. এর কার্যকলাপ শুধুমাত্র বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, লন্ডনেও এর একটি শাখা ছিল।
গুরুত্ব: জমিদার সভা ছিল মূলত একটি শ্রেণি-স্বার্থবাহী সংগঠন। কিন্তু এটিই প্রথম ভারতীয়দের সংঘবদ্ধভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন করতে শিখিয়েছিল। এই কারণেই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।
১৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি কীভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক শক্তিশালী প্রতীকে পরিণত হয়েছিল।
চিত্রের বর্ণনা ও তাৎপর্য:
১. আধ্যাত্মিক রূপ: এই ছবিতে ভারতমাতাকে কোনো উগ্র দেবী রূপে নয়, বরং এক শান্ত, সৌম্য, গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা সন্ন্যাসিনী রূপে দেখানো হয়েছে। তাঁর চারটি হাত, যা তাঁর দেবীরূপের পরিচায়ক।
২. আত্মশক্তির প্রতীক: তাঁর চার হাতে রয়েছে পুস্তক (শিক্ষা), ধানের শিষ (অন্ন), জপের মালা (দীক্ষা) এবং শ্বেতবস্ত্র (বস্ত্র)। এর মাধ্যমে শিল্পী বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক—উভয় প্রয়োজনই মেটাতে সক্ষম। তিনি বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নন। এটি ছিল স্বদেশী যুগের ‘আত্মশক্তি’র আদর্শের শৈল্পিক প্রকাশ।
৩. জাতীয়তাবাদের প্রতীক: এই ছবিটি তৎকালীন ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে immense ভূমিকা পালন করে। ভগিনী নিবেদিতা এই ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন মিছিলে এই ছবিটি ব্যবহার করা হত। এটি সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক ও আত্মনির্ভরশীল ভারতের এক নতুন কল্পনা তৈরি করে।
১৪. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) অর্থনৈতিক কারণগুলি আলোচনা করো।
উত্তর:
মহাবিদ্রোহের পিছনে একাধিক অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল, যা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।
কারণসমূহ:
১. ভূমিরাজস্ব নীতি: কোম্পানির প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারি ও মহালওয়ারি ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের উপর চড়া হারে করের বোঝা চাপে। কর দিতে না পারায় কৃষকরা তাদের জমি হারায়।
২. দেশীয় শিল্পের ধ্বংস: ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে সস্তা মেশিনে তৈরি জিনিসপত্রে ভারতের বাজার ছেয়ে যায়। এর ফলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হয়ে পড়ে।
৩. নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত: লর্ড বেন্টিঙ্ক ও ডালহৌসির আমলে ‘ইনকিলাব কমিশন’ গঠন করে বহু জমিদার ও তালুকদারের নিষ্কর বা লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়, যা অভিজাত শ্রেণিকে ক্ষুব্ধ করে।
৪. সিপাহিদের অসন্তোষ: ভারতীয় সিপাহিরা ব্রিটিশ সিপাহিদের তুলনায় অনেক কম বেতন পেত। এছাড়া, তাদের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া এবং দূরের প্রদেশে যুদ্ধ করতে পাঠানো তাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই সম্মিলিত অর্থনৈতিক শোষণই মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।
১৫. জাতীয়তাবাদের বিকাশে ‘গোরা’ উপন্যাসের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ উপন্যাসটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিষয়ক এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। এটি শুধুমাত্র দেশপ্রেমের কাহিনী নয়, এটি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ নিয়ে এক গভীর আত্ম-অনুসন্ধান।
ভূমিকা:
১. সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সমালোচনা: উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোরা প্রথমে ছিল এক উগ্র, গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী। সে মনে করত, কঠোর হিন্দু আচার-নিষ্ঠার মাধ্যমেই ভারতের মুক্তি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের মাধ্যমে সংকীর্ণ, বিভেদকামী ও বর্জনপন্থী জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন।
২. প্রকৃত ভারতভাবনার সন্ধান: উপন্যাসের শেষে গোরা যখন জানতে পারে যে সে জন্মসূত্রে একজন আইরিশ, তখন তার সমস্ত জাত্যাভিমান চূর্ণ হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে যে, ভারত কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, জাতি বা আচারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। ভারত হল এক মহামানবের মিলনক্ষেত্র।
৩. মানবতাবাদী আদর্শ: রবীন্দ্রনাথ ‘গোরা’র মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত দেশপ্রেম হল দেশের সকল মানুষকে ভালোবাসা, কোনো সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা নয়। তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল বিশ্বমানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।
উপসংহার: ‘গোরা’ উপন্যাস ভারতীয়দের এক উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয়তাবাদের সন্ধান দিয়েছিল, যা আজও প্রাসঙ্গিক।
১৬. ভারত সভা কীভাবে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারত সভা ছিল প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন যা সচেতনভাবে একটি সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জনের চেষ্টা করেছিল।
সর্বভারতীয় রূপ লাভের কারণ:
১. সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ও সদস্যপদ: ভারত সভার নেতৃত্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর মতো বাঙালি নেতারা থাকলেও, এটি দ্রুত বাংলার বাইরে শাখা বিস্তার করে। লাহোর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, পুনা প্রভৃতি শহরে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু অ-বাঙালি নেতা এর সঙ্গে যুক্ত হন।
২. সর্বভারতীয় ইস্যু গ্রহণ: ভারত সভা স্থানীয় সমস্যার পরিবর্তে সর্বভারতীয় ইস্যুগুলিকে তাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু করে। যেমন—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন, অস্ত্র আইন ও সংবাদপত্র আইনের বিরোধিতা ইত্যাদি।
৩. দেশব্যাপী সফর ও প্রচার: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করে এই বিষয়গুলির স্বপক্ষে জনমত গঠন করেন, যা এর আগে কোনো নেতা করেননি।
৪. জাতীয় সম্মেলন: ভারত সভার উদ্যোগে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালে কলকাতায় দুটি সর্বভারতীয় সম্মেলন বা ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স’ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সারা ভারতের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এটিই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত পূর্বসূরি।
১৭. ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে স্বদেশপ্রেমের ধারণা ব্যক্ত করেছেন?
উত্তর:
ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দের লেখা ‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থটি তাঁর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার এক উজ্জ্বল দলিল।
স্বদেশপ্রেমের ধারণা:
১. অতীত গৌরব ও বর্তমান অধঃপতন: বিবেকানন্দ প্রথমে ভারতের গৌরবময় অতীত (বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে) বর্ণনা করেছেন এবং তারপর ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর মধ্যে আত্মগৌরব বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।
২. পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের সমালোচনা: তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, ভারতের মুক্তি পাশ্চাত্যের অনুকরণে নয়, বরং নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির জাগরণের মাধ্যমেই সম্ভব।
৩. সেবা ও ত্যাগের আদর্শ: তাঁর স্বদেশপ্রেমের মূল কথা ছিল দেশের দরিদ্র, অশিক্ষিত ও নিপীড়িত মানুষের সেবা। তিনি বলতেন, “হে ভারত, ভুলিও না… তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।” তিনি দেশমাতৃকার সেবায় আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন।
৪. শূদ্র জাগরণের ডাক: বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ‘শূদ্র’ বা সাধারণ মানুষের জাগরণের ডাক। তিনি বিশ্বাস করতেন, শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের উত্থানের মাধ্যমেই এক নতুন ও শক্তিশালী ভারত গড়ে উঠবে।
১৮. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রতি বিভিন্ন শ্রেণির ভারতীয়দের মনোভাব কেমন ছিল?
উত্তর:
মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রতি ভারতের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মনোভাব ছিল ভিন্ন ভিন্ন।
১. সিপাহি: বিদ্রোহের সূচনা করেছিল সিপাহিরা। ধর্মনাশের আশঙ্কা এবং বেতন ও পদমর্যাদার বৈষম্য তাদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারাই ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান চালিকাশক্তি।
২. সামন্ত শ্রেণি: স্বত্ববিলোপ নীতি এবং লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করার ফলে ক্ষমতাচ্যুত বহু জমিদার, তালুকদার ও দেশীয় রাজা (যেমন—নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাই, কুনওয়ার সিংহ) নিজেদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য এই বিদ্রোহে যোগ দেন।
৩. কৃষক ও কারিগর: কোম্পানির ভূমিরাজস্ব নীতি এবং দেশীয় শিল্প ধ্বংসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বহু কৃষক ও কারিগর এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। তারা তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তির আশায় বিদ্রোহী হয়।
৪. শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি: বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। তারা ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করত এবং বিদ্রোহের হিংসাত্মক প্রকৃতিকে ভয় পেত। তাদের মতে, এটি ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ।
১৯. ‘সভা-সমিতির যুগ’ হিসেবে উনিশ শতকের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল?
উত্তর:
ঐতিহাসিক অনিল শীল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল:
১. সংগঠনের জন্ম: এই সময়ে ভারতে, বিশেষ করে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে, একাধিক রাজনৈতিক সভা-সমিতি গড়ে ওঠে। যেমন—ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, পুনা সার্বজনিক সভা, ভারত সভা, মাদ্রাজ মহাজন সভা ইত্যাদি।
২. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন: এই সভা-সমিতিগুলির আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল মূলত নিয়মতান্ত্রিক। তারা হিংসার পথে না গিয়ে আবেদন-নিবেদন, স্মারকলিপি প্রদান, সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রে লেখার মাধ্যমে সরকারের কাছে নিজেদের দাবি পেশ করত।
৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব: এই সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ছিল মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে। জমিদারদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে।
৪. সর্বভারতীয় চেতনার উন্মেষ: ভারত সভার মতো প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় সমস্যার গণ্ডি পেরিয়ে সিভিল সার্ভিস, অস্ত্র আইনের মতো সর্বভারতীয় ইস্যু নিয়ে আন্দোলন শুরু করে, যা ছিল এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটিই পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।
২০. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি কীভাবে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা করেছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। তিনি তাঁর ছবির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন।
সমালোচনা:
১. ‘বাবু’ সংস্কৃতির সমালোচনা: তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকারী, নব্য-ধনী বাঙালি ‘বাবু’ শ্রেণি। ‘অদ্ভুত লোক’ (Weird folks), ‘বিরূপ বজ্র’ (Play of Opposites) প্রভৃতি অ্যালবামে তিনি এই শ্রেণির অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রা, পোশাক-আশাক এবং আচার-আচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন।
২. সামাজিক ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন: তিনি তৎকালীন সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভণ্ডামি, জাতিভেদ প্রথা এবং অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও তাঁর তুলি ব্যবহার করেছেন। ‘জাতি-অসুরের কারখানা’ নামক ব্যঙ্গচিত্রটি এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।
৩. ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা: তিনি সরাসরি ব্রিটিশদের সমালোচনা না করলেও, তাদের প্রভাবে সৃষ্ট বিকৃত বাঙালি সমাজকে ব্যঙ্গ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনেরই সমালোচনা করেছেন।
উপসংহার: গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রগুলি ছিল ঔপনিবেশিক সমাজের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী শৈল্পিক প্রতিবাদ, যা মানুষকে আত্ম-সমালোচনা করতে এবং জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।
২১. টীকা লেখো: ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘জমিদার সভা’ এবং ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি’—এই দুটি সংগঠনকে একত্রিত করে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল উনিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠন।
নেতৃত্ব: এর সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
উদ্দেশ্য ও দাবি:
১. এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের, বিশেষ করে জমিদার শ্রেণির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার আদায় করা।
২. তাদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে ছিল—আইনসভায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ, সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ এবং লবণ, আফিম ও আবগারি শুল্কের বিলোপ।
গুরুত্ব: ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনই প্রথম সংগঠন যারা ১৮৫৩ সালের সনদ আইন পাসের আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয়দের দাবিদাওয়া জানিয়ে স্মারকলিপি পাঠায়। এটি মূলত জমিদারদের স্বার্থবাহী সংগঠন হলেও, এর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরবর্তী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির পথপ্রদর্শক ছিল।
২২. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: মহাবিদ্রোহের পিছনে একাধিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ থাকলেও, এর প্রত্যক্ষ বা உடனടി কারণ ছিল ‘এনফিল্ড রাইফেল’-এর টোটার প্রচলন।
টোটার ঘটনা:
১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে পুরোনো ব্রাউন বেস রাইফেলের পরিবর্তে নতুন ‘এনফিল্ড রাইফেল’ চালু করা হয়। এই রাইফেলের টোটা (cartridge) একটি মোড়কে ভরা থাকত, যা ব্যবহারের আগে দাঁত দিয়ে কেটে ভরতে হত।
গুজব ও প্রতিক্রিয়া: সিপাহিদের মধ্যে গুজব রটে যায় যে, এই টোটার মোড়কে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো আছে। গরু হিন্দুদের কাছে পবিত্র এবং শূকর মুসলিমদের কাছে নিষিদ্ধ হওয়ায়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সিপাহিই মনে করে যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের ধর্মনাশ করার ষড়যন্ত্র করছে।
প্রথম প্রতিবাদ: এই টোটা ব্যবহারে প্রথম আপত্তি জানান ব্যারাকপুরের সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে। তিনি ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ একজন ব্রিটিশ অফিসারকে আক্রমণ করেন। এর জন্য তাঁর ফাঁসি হয়। এই ঘটনাই দাবানলের মতো সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং মহাবিদ্রোহের সূচনা করে।
২৩. ‘জাতীয়তাবাদের বিকাশে লেখকদের ভূমিকা বেশি, না কি শিল্পীদের?’— তোমার মতামত দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে লেখক ও শিল্পী—উভয়ের ভূমিকাই ছিল অপরিসীম এবং একে অপরের পরিপূরক। কার ভূমিকা বেশি, তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে তাদের প্রভাবের ধরন ভিন্ন ছিল।
লেখকদের ভূমিকা:
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (‘আনন্দমঠ’), স্বামী বিবেকানন্দ (‘বর্তমান ভারত’), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (‘গোরা’)-এর মতো লেখকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের একটি বৌদ্ধিক ও দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। তাঁরা দেশপ্রেম, আত্মশক্তি এবং ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার করে শিক্ষিত সমাজের মননকে প্রভাবিত করেন। তাঁদের লেখা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে এবং বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়।
শিল্পীদের ভূমিকা:
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (‘ভারতমাতা’), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ব্যঙ্গচিত্র)-এর মতো শিল্পীরা জাতীয়তাবাদকে একটি দৃশ্যমান ও আবেগঘন রূপ দিয়েছিলেন। একটি ছবি বা ব্যঙ্গচিত্র যা বার্তা দিতে পারে, তা অনেক সময় হাজার শব্দের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। ‘ভারতমাতা’র মতো চিত্র নিরক্ষর মানুষের কাছেও দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল।
মতামত: আমার মতে, লেখকরা জাতীয়তাবাদের ‘মস্তিষ্ক’ তৈরি করেছিলেন, আর শিল্পীরা তার ‘হৃদয়’-কে স্পর্শ করেছিলেন। শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবিত করতে এবং একটি আদর্শগত ভিত্তি তৈরি করতে লেখকদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করতে এবং জাতীয়তাবাদকে একটি চাক্ষুষ প্রতীকে পরিণত করতে শিল্পীদের ভূমিকা ছিল বেশি। তাই উভয়ের অবদানই সমান গুরুত্বপূর্ণ।
২৪. মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রধান চালিকাশক্তি ছিল সিপাহিরা। তাই বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমূল পরিবর্তন আনে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
পরিবর্তনসমূহ:
১. পিল কমিশনের সুপারিশ: ‘পিল কমিশন’-এর সুপারিশ অনুযায়ী সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা কমিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয়। পূর্বে এই অনুপাত ছিল প্রায় ৬:১, যা কমিয়ে ২:১ (বাংলায়) বা ৩:১ (অন্যত্র) করা হয়।
২. ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি: ‘জাতিগত বিভাজন ও শাসন’ (Divide and Rule) নীতি প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও অঞ্চলের সৈন্যদের মিশিয়ে রেজিমেন্ট গঠন করা হয়, যাতে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে।
৩. ‘মার্শাল’ ও ‘নন-মার্শাল’ জাতির ধারণা: যেসব অঞ্চলের সিপাহিরা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল (যেমন—অযোধ্যা), তাদের ‘নন-মার্শাল’ (অ-যুদ্ধবাজ) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে, যারা বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল (যেমন—গুর্খা, শিখ, পাঠান), তাদের ‘মার্শাল’ (যুদ্ধবাজ) জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে সেনাবাহিনীতে বেশি সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়।
৪. গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ন্ত্রণ: গোলন্দাজ বাহিনীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে শুধুমাত্র ব্রিটিশ সৈন্যদের রাখা হয়।
২৫. ‘জমিদার সভা’ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এর গুরুত্ব কী?
উত্তর:
প্রতিষ্ঠার কারণ:
উনিশ শতকের প্রথমভাগে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিরাজস্ব নীতি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলে জমিদার শ্রেণির স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে থাকা বাংলার জমিদাররা নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখের উদ্যোগে ‘জমিদার সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়।
গুরুত্ব:
১. প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন: জমিদার সভা ছিল ভারতের প্রথম প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠন, যা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করত।
২. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা: এটিই প্রথম আবেদন-নিবেদন, সভা-সমিতি এবং প্রচারের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করে, যা পরবর্তী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।
৩. অ-জমিদারদের অন্তর্ভুক্তি: যদিও এর নাম ছিল ‘জমিদার সভা’, এটি শুধুমাত্র জমিদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছু অ-জমিদার সদস্যও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এটি রায়তদের স্বার্থ নিয়েও কথা বলেছিল।
সীমাবদ্ধতা: এটি মূলত একটি শ্রেণি-স্বার্থবাহী সংগঠন ছিল এবং এর আবেদন ছিল সীমিত। তা সত্ত্বেও, ভারতীয়দের মধ্যে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৮ (১০টি)
১. ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে। কেউ একে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’, কেউ ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’, আবার কেউ ‘সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া’ বলে অভিহিত করেছেন।
বিভিন্ন মত:
১. সিপাহী বিদ্রোহ: চার্লস রেক্স, জন সিলি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো সমকালীন ব্যক্তি এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এই বিদ্রোহ ছিল মূলত সিপাহিদের অসন্তোষের ফল। সাধারণ মানুষ এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়নি এবং এর কোনো জাতীয় চরিত্র ছিল না।
২. ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ: বিনায়ক দামোদর সাভারকর, কার্ল মার্কস, অশোক মেহতা প্রমুখ ঐতিহাসিকরা একে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলেছেন। তাঁদের মতে, এটি শুধুমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; কৃষক, কারিগর, জমিদার সহ বহু অসামরিক মানুষ এতে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, যা এর জাতীয় চরিত্রের পরিচায়ক।
৩. সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া: রজনীপাম দত্তের মতো মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এটি ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত সামন্ত শ্রেণির (জমিদার, দেশীয় রাজা) নিজেদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার একটি প্রচেষ্টা। এটি কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন ছিল না।
৪. জাতীয় বিদ্রোহ: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরেলি এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতো ঐতিহাসিকরা একে ‘জাতীয় বিদ্রোহ’ বলেছেন। তাঁদের মতে, যদিও এটি সারা ভারতে ছড়ায়নি, তবে এর ব্যাপকতা এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অংশগ্রহণ একে একটি জাতীয় চরিত্র দান করেছিল।
উপসংহার: কোনো একটি নির্দিষ্ট তকমা দিয়ে এই বিদ্রোহের চরিত্র বোঝা সম্ভব নয়। এটি সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হলেও, দ্রুত তা গণবিদ্রোহের রূপ নেয় এবং এর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক, কৃষক ও জাতীয়তাবাদী—সব ধরনের উপাদানই মিশ্রিত ছিল। তাই ড. সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতো বলা যায়, “যা ধর্মযুদ্ধ রূপে শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে শেষ হয়।”
২. লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহিত্য ও শিল্পকলার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন লেখকের শক্তিশালী রচনা এবং শিল্পীর আঁকা ছবি ভারতীয়দের মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল।
লেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ:
১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’: এই উপন্যাসটিকে ‘জাতীয়তাবাদের গীতা’ বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দেশমাতাকে দেবী দুর্গার সঙ্গে এক করে দেখেছেন এবং দেশের মুক্তির জন্য ‘সন্তান’দের আত্মত্যাগের আদর্শ তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্রে পরিণত হয়।
২. স্বামী বিবেকানন্দের ‘বর্তমান ভারত’: এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের তীব্র সমালোচনা করে ভারতীয় যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী হতে এবং দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ছিল মানবতাবাদ ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা। তিনি শূদ্র বা সাধারণ মানুষের জাগরণের মাধ্যমে এক নতুন, শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’: এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ, উগ্র ও বর্জনপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি ‘গোরা’ চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ভারতের প্রকৃত পরিচয় কোনো ধর্ম বা জাতির গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তা এক উদার ও বিশ্বমানবতাবাদী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।
রেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ:
১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’: স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আঁকা এই চিত্রটি ছিল জাতীয়তাবাদের এক শক্তিশালী চাক্ষুষ প্রতীক। এতে ভারতমাতাকে এক শান্ত, সৌম্য, গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা সন্ন্যাসিনী রূপে দেখানো হয়েছে, যিনি তাঁর সন্তানদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও দীক্ষা দিচ্ছেন। এটি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে ‘আত্মশক্তি’র আদর্শের শৈল্পিক প্রকাশ।
২. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র: গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বেড়ে ওঠা ইংরেজি অনুকরণপ্রিয় ‘বাবু’ সংস্কৃতি এবং সামাজিক ভণ্ডামির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই ছবিগুলি পরোক্ষভাবে জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।
উপসংহার: এইভাবে, উনিশ শতকের লেখা ও রেখা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক এবং আবেগঘন ভিত্তি তৈরি করেছিল, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে প্রশস্ত করে।
৩. উনিশ শতকে ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে সভা-সমিতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ভারতে, বিশেষ করে বাংলায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। এই শ্রেণিই নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতি গড়ে তোলে। এই সভা-সমিতিগুলিই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ঐতিহাসিক অনিল শীল এই সময়কালকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন।
বিভিন্ন সভা-সমিতির ভূমিকা:
১. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬): এটি ছিল ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। এটি নিষ্কর জমির উপর কর আরোপের মতো সরকারি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করে।
২. জমিদার সভা (১৮৩৮): দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সভা ছিল মূলত জমিদারদের স্বার্থরক্ষার সংগঠন। কিন্তু এটিই প্রথম সংঘবদ্ধভাবে এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে দাবিদাওয়া আদায়ের কৌশল গ্রহণ করে, যা ছিল এক নতুন পদক্ষেপ।
৩. ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১): এটি ছিল জমিদার সভা এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির মিলিত রূপ। এই সংগঠন আইনসভায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দাবি জানায়।
৪. হিন্দু মেলা (১৮৬৭): নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি সরাসরি রাজনৈতিক না হলেও, দেশীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ‘আত্মশক্তি’র আদর্শ প্রচার করে জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করেছিল।
৫. ভারত সভা (১৮৭৬): সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভারত সভা ছিল ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। এটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমানোর বিরুদ্ধে, অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে আন্দোলন সংগঠিত করে। এটিই প্রথম স্থানীয় ইস্যুর গণ্ডি পেরিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে জনমত গঠন করতে সক্ষম হয়।
উপসংহার: এই সভা-সমিতিগুলির কার্যকলাপের মাধ্যমেই ভারতীয়রা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে শেখে এবং তাদের মধ্যে এক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
৪. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোনো একটি বিশেষ কারণে ঘটেনি। এটি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ একশত বছরের শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এর কারণগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।
কারণসমূহ:
১. রাজনৈতিক কারণ: লর্ড ওয়েলেসলির ‘অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি’ এবং লর্ড ডালহৌসির ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’র মাধ্যমে ব্রিটিশরা বহু দেশীয় রাজ্যকে সাম্রাজ্যভুক্ত করে। এর ফলে ঝাঁসি, অযোধ্যা, সাতারা প্রভৃতি রাজ্যের শাসকরা ক্ষুব্ধ হন। এছাড়া, মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে অপমান করা হয়, যা মুসলিমদের ভাবাবেগে আঘাত করে।
২. অর্থনৈতিক কারণ: কোম্পানির চড়া ভূমিরাজস্ব নীতির ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতের বস্ত্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হয়ে পড়ে। নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার ফলে বহু জমিদারও কোম্পানির উপর ক্ষুব্ধ হয়।
৩. সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ: ব্রিটিশরা সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহের মতো সংস্কারমূলক কাজ করলেও, রক্ষণশীল ভারতীয়রা একে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ কার্যকলাপ এবং জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই আতঙ্কিত করে তোলে।
৪. সামরিক কারণ: ভারতীয় সিপাহিরা ব্রিটিশ সিপাহিদের তুলনায় কম বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পেত এবং তাদের পদোন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। এছাড়া, ‘সাধারণ সার্ভিস তালিকাভুক্তি আইন’ দ্বারা তাদের সমুদ্রপারে যেতে বাধ্য করা হয়, যা ছিল হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী।
৫. প্রত্যক্ষ কারণ: এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালে ‘এনফিল্ড রাইফেল’-এর টোটার প্রচলন। এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো আছে—এই গুজব রটলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সিপাহিই মনে করে যে, সরকার তাদের ধর্মনাশ করার ষড়যন্ত্র করছে। এই ঘটনাই মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৫. ভারত সভা কি জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বসূরি ছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: হ্যাঁ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভারত সভাকে (১৮৭৬) সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) যথার্থ পূর্বসূরি বলা হয়। যদিও এর আগেও একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন ছিল, কিন্তু ভারত সভাই প্রথম একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।
যুক্তি:
১. সর্বভারতীয় লক্ষ্য ও কর্মসূচি: ভারত সভার আগেকার সংগঠনগুলি (যেমন—জমিদার সভা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) ছিল মূলত আঞ্চলিক এবং শ্রেণি-স্বার্থবাহী। ভারত সভাই প্রথম ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চল নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নেয় এবং সিভিল সার্ভিস আন্দোলন, অস্ত্র আইনের বিরোধিতা করার মতো সর্বভারতীয় ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করে।
২. সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ও শাখা: ভারত সভার নেতৃত্ব বাঙালি হলেও, এর শাখা বাংলার বাইরে লাহোর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, পুনা প্রভৃতি শহরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বহু অ-বাঙালি নেতা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
৩. জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন: জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে ভারত সভাই প্রথম সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালে কলকাতায় দুটি ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স’ বা জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনগুলিতে সারা ভারতের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এই সম্মেলনের গঠন, কার্যপ্রণালী এবং আদর্শ অনেকটাই পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল।
৪. সুরেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি: ১৮৮৫ সালে যখন বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে, তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ভারত সভার দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করছিলেন। এই কারণেই তিনি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি। পরে ভারত সভা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায়।
উপসংহার: এই সমস্ত কারণ বিচার করে বলা যায় যে, ভারত সভাই তার কর্মসূচি ও সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের পথ তৈরি করে দিয়েছিল। তাই একে জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বসূরি বলা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।
৬. মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যাপকতা ও বীরত্ব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এর ব্যর্থতার পিছনে একাধিক কারণ ছিল এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।
ব্যর্থতার কারণ:
১. নেতৃত্বের অভাব ও সমন্বয়হীনতা: বিদ্রোহের কোনো যোগ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাই, কুনওয়ার সিংহের মতো স্থানীয় নেতারা বীর হলেও তাঁদের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না।
২. পরিকল্পনার অভাব: বিদ্রোহটি ছিল মূলত স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল না।
৩. সর্বভারতীয় প্রসারের অভাব: বিদ্রোহটি মূলত উত্তর ও মধ্য ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা এবং দক্ষিণ ভারত শান্ত ছিল, যা ব্রিটিশদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করে।
৪. শিক্ষিত শ্রেণির অসহযোগিতা: বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি, যা বিদ্রোহীদের নৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়।
৫. ব্রিটিশদের উন্নত শক্তি: ব্রিটিশদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (টেলিগ্রাফ, রেল) এবং যোগ্য সেনাপতিত্বের কাছে বিদ্রোহীরা টিকে থাকতে পারেনি।
ফলাফল:
১. কোম্পানি শাসনের অবসান: বিদ্রোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান। ১৮৫৮ সালের ‘ভারত শাসন আইন’ দ্বারা ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ রাজ বা মহারানির হাতে চলে যায়।
২. মহারানির ঘোষণাপত্র: মহারানি ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারতীয়দের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন।
৩. সেনাবাহিনী পুনর্গঠন: ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা কমিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি প্রয়োগ করা হয়।
৪. সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সূচনা: বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করে, যা ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে।
৭. ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস এবং ‘ভারতমাতা’ চিত্র— এই দুটি কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উসকে দিয়েছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে জাগিয়ে তুলতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ চিত্র— এই দুটি শিল্পকর্ম এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল।
‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের ভূমিকা:
১. দেশপ্রেমকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীতকরণ: বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দেশকে ‘মা’ রূপে কল্পনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, দেশপ্রেম ও ধর্ম আলাদা নয়; দেশমাতৃকার সেবা করাই হল প্রকৃত ধর্মপালন। এই ধারণাটি দেশবাসীর মনে এক নতুন আধ্যাত্মিক ও আবেগঘন জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।
২. ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্র: উপন্যাসের ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি ছিল দেশপ্রেমের এক শক্তিশালী প্রকাশ। এই গানটি পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্রে পরিণত হয় এবং লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।
৩. আত্মত্যাগের আদর্শ: উপন্যাসের ‘সন্তান’ দলের সদস্যরা ছিলেন নিঃস্বার্থ, disciplined এবং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত। এই ‘সন্তান’দের আদর্শ পরবর্তীকালের বহু বিপ্লবী সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল।
‘ভারতমাতা’ চিত্রের ভূমিকা:
১. জাতীয়তাবাদের চাক্ষুষ প্রতীক: স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আঁকা ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি জাতীয়তাবাদকে একটি দৃশ্যমান রূপ দিয়েছিল। এটি ভারতমাতার এক শান্ত, সৌম্য ও আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্তি তৈরি করে, যা ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে ‘আত্মশক্তি’র আদর্শের শৈল্পিক প্রকাশ।
২. আত্মনির্ভরতার বার্তা: ভারতমাতার চার হাতে থাকা পুস্তক, ধানের শিষ, জপের মালা ও শ্বেতবস্ত্র— এই প্রতীকগুলির মাধ্যমে শিল্পী বুঝিয়েছেন যে, ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং তিনি বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নন।
৩. ব্যাপক আবেদন: একটি চিত্র হওয়ায় এটি শিক্ষিত-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের মিছিলে এই ছবিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।
উপসংহার: ‘আনন্দমঠ’ যেখানে জাতীয়তাবাদের বৌদ্ধিক ও আবেগঘন ভিত্তি তৈরি করেছিল, ‘ভারতমাতা’ সেখানে তাকে একটি সর্বজনীন ও চাক্ষুষ রূপ দিয়েছিল। উভয়ই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।
৮. মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রতি শিক্ষিত সমাজের মনোভাব কেমন ছিল? এই বিদ্রোহের ফলাফল আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। এই বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত সমাজের মনোভাব এবং এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।
শিক্ষিত সমাজের মনোভাব:
মহাবিদ্রোহের প্রতি ভারতের শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করে বাংলার শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণি ছিল মূলত উদাসীন এবং ব্রিটিশদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এর কারণগুলি হল:
১. ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আস্থা: শিক্ষিত শ্রেণি মনে করত যে, ব্রিটিশ শাসনই ভারতে আধুনিকতার এনেছে এবং সতীদাহ নিবারণের মতো সংস্কার করেছে। তাই তারা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চায়নি।
২. বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে সংশয়: তারা এই বিদ্রোহকে প্রগতিশীল আন্দোলন হিসেবে দেখেনি। বরং এটিকে সিপাহিদের দ্বারা পরিচালিত একটি সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ বলে মনে করত, যা ভারতকে আবার মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।
৩. শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষে: বিদ্রোহের হিংসাত্মক কার্যকলাপ শিক্ষিত শ্রেণিকে ভীত করে তুলেছিল। তারা শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে ছিল। এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলি বিদ্রোহের বিরোধিতা করে।
ফলাফল:
১. কোম্পানি শাসনের অবসান ও ব্রিটিশ রাজের শাসন প্রতিষ্ঠা: বিদ্রোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান। ১৮৫৮ সালের ‘ভারত শাসন আইন’ দ্বারা ভারতের শাসনভার সরাসরি ব্রিটিশ রাজ বা মহারানির হাতে চলে যায়। গভর্নর-জেনারেল পদটির সঙ্গে ‘ভাইসরয়’ বা রাজপ্রতিনিধি উপাধি যুক্ত হয়।
২. মহারানির ঘোষণাপত্র: মহারানি ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারতীয়দের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, স্বত্ববিলোপ নীতি বাতিল এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন।
৩. সেনাবাহিনী পুনর্গঠন: ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা কমিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি প্রয়োগ করা হয়।
৪. সাম্প্রদায়িক বিভাজন: বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশরা ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতিকে আরও সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করে এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে।
৯. টীকা লেখো: (ক) ভারত সভা (খ) হিন্দু মেলা।
উত্তর:
(ক) ভারত সভা (The Indian Association):
ভূমিকা: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘ভারত সভা’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বসূরি।
উদ্দেশ্য: এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১) সারা ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠন করা, (২) ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করা, (৩) হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা এবং (৪) রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা।
কার্যাবলী: ভারত সভা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমানোর বিরুদ্ধে, অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করে। এটি ইলবার্ট বিলকে সমর্থন জানিয়েও আন্দোলন করে। ভারত সভার উদ্যোগে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালে কলকাতায় দুটি সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
গুরুত্ব: ভারত সভাই প্রথম স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করে, যা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল।
(খ) হিন্দু মেলা:
ভূমিকা: উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ‘হিন্দু মেলা’ বা ‘চৈত্র মেলা’ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণায় এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
উদ্দেশ্য: এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ‘আত্মশক্তি’ বা আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার করা। বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব থেকে যুবসমাজকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং দেশীয় শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শরীরচর্চার উন্নতি সাধন করা ছিল এর প্রধান লক্ষ্য।
কার্যাবলী: প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। এখানে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য, দেশীয় ব্যায়াম (কুস্তি, জিমন্যাস্টিকস) প্রদর্শিত হত এবং দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ ও সংগীত পরিবেশন করা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিশোর বয়সে এই মেলায় কবিতা পাঠ করেন। ‘ন্যাশানাল পেপার’ ছিল এর মুখপত্র।
গুরুত্ব: হিন্দু মেলা সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হলেও, এটিই প্রথম ভারতীয়দের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল।
১০. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি কীভাবে জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহায্য করেছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। তিনি তাঁর ছবির মাধ্যমে সরাসরি জাতীয়তাবাদের প্রচার না করলেও, ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করে পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদের বিকাশে সাহায্য করেছিলেন।
জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ:
১. ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা: গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে সৃষ্ট বিকৃত বাঙালি সমাজ। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকারী, নব্য-ধনী বাঙালি ‘বাবু’ শ্রেণিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর ‘অদ্ভুত লোক’ বা ‘বিরূপ বজ্র’-এর মতো অ্যালবামে এই শ্রেণির অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রা, ইংরেজি মেশানো বাংলা বলা এবং পোশাক-আশাকের অনুকরণকে হাস্যকরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই আত্ম-সমালোচনা দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তোলে।
২. সামাজিক ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন: তিনি তৎকালীন সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভণ্ডামি, জাতিভেদ প্রথা এবং অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও তাঁর তুলি ব্যবহার করেছেন। ‘জাতি-অসুরের কারখানা’ নামক ব্যঙ্গচিত্রটি এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই ছবিগুলি সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলি দূর করে এক শক্তিশালী জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে।
৩. প্রতিবাদের নতুন ভাষা: গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্রগুলি ছিল ঔপনিবেশিক সমাজের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অথচ বুদ্ধিদীপ্ত শৈল্পিক প্রতিবাদ। এটি মানুষকে হাসির ছলে গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করত। এটি ছিল প্রতিবাদের এক নতুন ও আধুনিক ভাষা।
উপসংহার: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সরাসরি ‘ভারতমাতা’র মতো জাতীয়তাবাদের প্রতীক তৈরি করেননি। কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলি ভারতীয়দের আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল এবং ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছিল, যা জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য অপরিহার্য ছিল।
Class 10 History সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ Question Answer MCQ,অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : class 10 সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ প্রশ্ন উত্তর