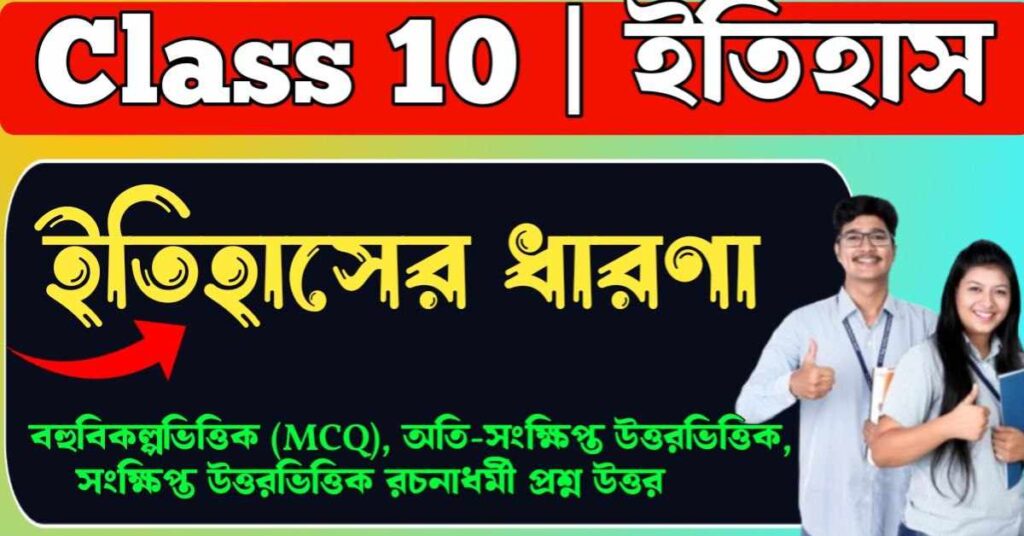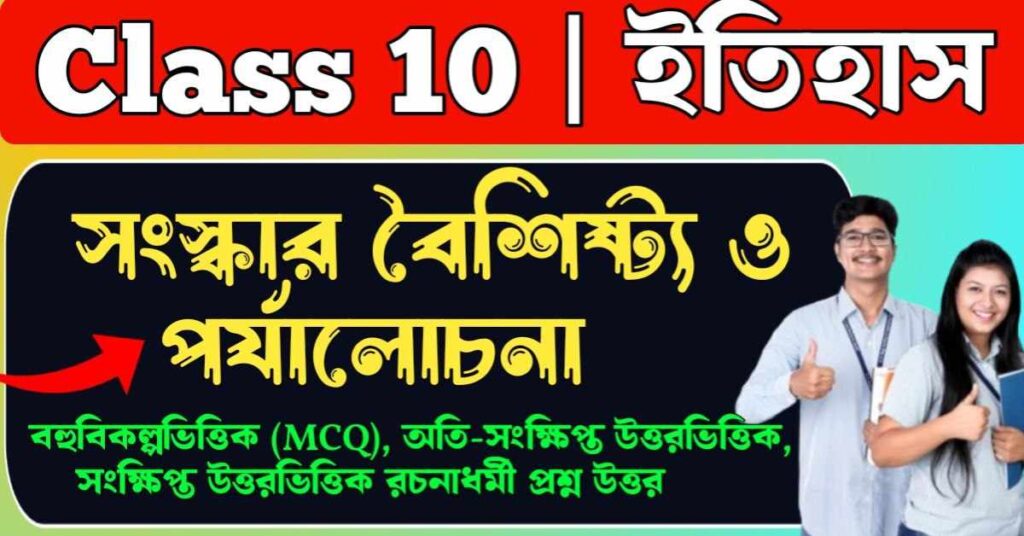বিশ শতকের ভারতে কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. একা বা একতা আন্দোলন (১৯২১-২২) হয়েছিল –
২. সর্বভারতীয় কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল –
৩. সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন –
৪. নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল –
৫. AITUC-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন –
৬. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-৩৩) হয়েছিল –
৭. তেভাগা আন্দোলনের দাবি ছিল –
৮. কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল (Congress Socialist Party) প্রতিষ্ঠিত হয় –
৯. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল –
১০. বারদৌলি সত্যাগ্রহের (১৯২৮) নেতৃত্ব দেন –
১১. ‘লাঙল’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন –
১২. মোপলা বিদ্রোহ (১৯২১) হয়েছিল –
১৩. ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় –
১৪. ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’ যুক্ত ছিল –
১৫. ‘সর্দার’ উপাধি বল্লভভাই প্যাটেলকে দিয়েছিলেন –
১৬. বাবা রামচন্দ্র কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন –
১৭. ‘গণবাণী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন –
১৮. ফরোয়ার্ড ব্লক দলটি গঠন করেন –
১৯. একা আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন –
২০. মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম ছিল –
২১. তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল –
২২. ‘The Socialist’ নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন –
২৩. কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন –
২৪. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার সভাপতি ছিলেন –
২৫. ‘বিপ্লবী’ (Radical) গণতান্ত্রিক দল গঠন করেন –
২৬. ‘নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন –
২৭. ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (তাসখন্দে) প্রতিষ্ঠা করেন –
২৮. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কৃষক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল –
২৯. বিংশ শতকের ভারতে যে আন্দোলনটি অহিংস পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, তা হল –
৩০. কংগ্রেসের যে অধিবেশনে প্রথমবার কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় –
৩১. কোন আইন দ্বারা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়?
৩২. তেভাগা আন্দোলনের একজন নেত্রী ছিলেন –
৩৩. ‘অবধ কিষাণ সভা’ গঠনে কার ভূমিকা ছিল?
৩৪. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন –
৩৫. ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’-এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন –
৩৬. ‘বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
৩৭. অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন –
৩৮. বামপন্থীরা কংগ্রেসের ভেতরে থেকে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় কোন সময়কালে?
৩৯. সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন –
৪০. ‘বিদ্যুৎ বাহিনী’ গড়ে তোলা হয়েছিল কোন আন্দোলনের সময়?
৪১. ‘হাতি তোর, নাঙ্গল যার, জমি তার’ – এই স্লোগানটি কোন আন্দোলনের?
৪২. ‘Why Socialism?’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
৪৩. ‘ট্রাইবিউন’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন –
৪৪. কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল –
৪৫. তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল প্রধানত –
৪৬. ‘জাতীয় সরকার’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে জেলায়, তা হল –
৪৭. ‘পূর্ণ স্বরাজ’ দাবিটি জনপ্রিয় করতে সাহায্য করে –
৪৮. ভারতের ‘শ্রমিক দল’-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন –
৪৯. কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন না –
৫০. ‘Bengal Peasants Life’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
৫১. তেলেঙ্গানা আন্দোলন ছিল মূলত –
৫২. ‘রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ কবে গঠিত হয়?
৫৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন (কানপুরে, ১৯২৫) এর সভাপতি কে ছিলেন?
৫৪. ‘চম্পারণ কৃষি বিল’ পাস হয় –
৫৫. ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’-র পূর্ব নাম কী ছিল?
৫৬. ‘জমির ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা’ কোন আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল?
৫৭. ‘Indian Struggle’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
৫৮. বিহারে কৃষক আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন –
৫৯. ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৬০. ‘ট্রেড ইউনিয়ন আইন’ কবে পাস হয়?
৬১. তেভাগা আন্দোলনের সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
৬২. ‘গেরিলা যুদ্ধকৌশল’ কোন বিদ্রোহে ব্যবহৃত হয়েছিল?
৬৩. কে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না?
৬৪. ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ – এই নীতি প্রচার করে –
৬৫. ‘বর্গাদার বিল’ কোন আন্দোলনের ফলে পেশ করা হয়?
৬৬. মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন (১৯১৮) প্রতিষ্ঠা করেন –
৬৭. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কতজন নেতা অভিযুক্ত হন?
৬৮. ‘ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী’ কাকে বলা হয়?
৬৯. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কী ছিল?
৭০. ‘অখিল ভারতীয় মজদুর সংঘ’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. একা আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল?
উত্তর: ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে।
২. একা আন্দোলনের একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: মাদারী পাসি।
৩. সর্বভারতীয় কিষাণ সভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল।
৪. সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রথম অধিবেশন কোথায় বসে?
উত্তর: লখনউ-তে।
৫. AITUC-এর পুরো নাম কী?
উত্তর: অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।
৬. ভারতে কবে প্রথম মে দিবস পালিত হয়?
উত্তর: ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে।
৭. কার উদ্যোগে ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়?
উত্তর: সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার-এর উদ্যোগে।
৮. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কবে শুরু হয়?
উত্তর: ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে।
৯. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত একজন ব্রিটিশের নাম লেখো।
উত্তর: ফিলিপ স্প্র্যাট।
১০. তেভাগা কথার অর্থ কী?
উত্তর: তিন ভাগ, যার মধ্যে দুই ভাগ পাবে কৃষক।
১১. তেভাগা আন্দোলন কোথায় হয়েছিল?
উত্তর: অবিভক্ত বাংলায়।
১২. কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: জয়প্রকাশ নারায়ণ।
১৩. ফরোয়ার্ড ব্লক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে।
১৪. ‘লাঙল’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম।
১৫. ‘গণবাণী’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: মুজফ্ফর আহমেদ।
১৬. মোপলা বিদ্রোহ কোথায় হয়েছিল?
উত্তর: কেরলের মালাবার উপকূলে।
১৭. বারদৌলি সত্যাগ্রহ কেন হয়েছিল?
উত্তর: সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে।
১৮. ‘সর্দার’ উপাধি কে পান?
উত্তর: বল্লভভাই প্যাটেল।
১৯. বাবা রামচন্দ্র কোন অঞ্চলের কৃষক নেতা ছিলেন?
উত্তর: যুক্তপ্রদেশের (অবধ)।
২০. মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম কী?
উত্তর: নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
২১. ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে।
২২. ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’র পূর্ব নাম কী ছিল?
উত্তর: লেবার স্বরাজ পার্টি।
২৩. তেভাগা আন্দোলনের একজন শহিদের নাম লেখো।
উত্তর: শিবরাম মাঝি।
২৪. তেলেঙ্গানা আন্দোলন কবে হয়েছিল?
উত্তর: ১৯৪৬-৫১ খ্রিস্টাব্দে।
২৫. ‘تام্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’ কোথায় গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: মেদিনীপুর জেলার তমলুকে।
২৬. ‘বিদ্যুৎ বাহিনী’ কে গঠন করেন?
উত্তর: সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে গঠিত তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।
২৭. একজন বামপন্থী কংগ্রেস নেতার নাম লেখো।
উত্তর: জওহরলাল নেহরু।
২৮. ‘বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দল’ (Radical Democratic Party) কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: মানবেন্দ্রনাথ রায় (M. N. Roy)।
২৯. ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ – এই স্লোগানটি কার?
উত্তর: সর্বভারতীয় কিষাণ সভার।
৩০. কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: এস. এ. ডাঙ্গে।
৩১. কোন আইন দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
উত্তর: ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন।
৩২. AITUC-এর বিভাজন কবে হয়?
উত্তর: ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে।
৩৩. ‘অবধ কিষাণ সভা’ কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।
৩৪. মোপলা কাদের বলা হত?
উত্তর: মালাবার উপকূলের দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের মোপলা বলা হত।
৩৫. ‘ইন্টারন্যাশনাল’ সঙ্গীতটি বাংলায় কে অনুবাদ করেন?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম।
৩৬. ‘জনযুদ্ধ’ তত্ত্ব কে দিয়েছিলেন?
উত্তর: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়)।
৩৭. ‘ভাগচাষি’ কাদের বলা হত?
উত্তর: যারা অন্যের জমিতে উৎপন্ন ফসলের ভাগের বিনিময়ে চাষ করত, তাদের ভাগচাষি বা বর্গাদার বলা হত।
৩৮. ‘বেঠ-বেগারী’ প্রথা কী?
উত্তর: বিনাপারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমদান প্রথা।
৩৯. সর্বভারতীয় কিষাণ কংগ্রেসের নাম কবে ‘সর্বভারতীয় কিষাণ সভা’ হয়?
উত্তর: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
৪০. ‘হোমরুল লিগ’-এর দুজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: অ্যানি বেসান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলক।
৪১. ‘Why Socialism?’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: জয়প্রকাশ নারায়ণ।
৪২. ‘레드 ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ (RTUC) কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: এন. এম. যোশী।
৪৩. ‘বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে।
৪৪. তেভাগা আন্দোলনের মূল স্লোগান কী ছিল?
উত্তর: “নিজ খোলানে ধান তোলো”।
৪৫. ইলা মিত্র কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উত্তর: তেভাগা আন্দোলন (বিশেষত নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ)।
৪৬. ‘জাতীয়তাবাদী মুসলিম’ কাদের বলা হত?
উত্তর: যে সমস্ত মুসলিম নেতা মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক নীতির বিরোধিতা করে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।
৪৭. কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়?
উত্তর: ১৯৫৫ সালের আবাডি অধিবেশনে।
৪৮. ভারতের একজন বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতার নাম লেখো।
উত্তর: আচার্য নরেন্দ্র দেব।
৪৯. ‘India in Transition’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: মানবেন্দ্রনাথ রায়।
৫০. ‘ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন’ (ITUF) কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: এন. এম. যোশী।
৫১. কোন দশকটিকে ভারতে ‘বামপন্থী প্রভাবের দশক’ বলা হয়?
উত্তর: ১৯৩০-এর দশককে।
৫২. ‘ভগিনী সেনা’ কোন সরকারের অংশ ছিল?
উত্তর: তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের।
৫৩. ‘কমরেড’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: বন্ধু বা সহযোদ্ধা।
৫৪. কে ‘কংগ্রেস রেডিও’ পরিচালনা করতেন?
উত্তর: ঊষা মেহতা।
৫৫. ‘স্বাধীন ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপাত্র হিসেবে সতীশচন্দ্র সামন্ত।
৫৬. ‘জোতদার’ কাদের বলা হত?
উত্তর: বাংলার ধনী ও প্রভাবশালী ভূস্বামীদের জোতদার বলা হত।
৫৭. ‘নানকানা হত্যাকাণ্ড’ কবে ঘটে?
উত্তর: ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে।
৫৮. ‘আকালি আন্দোলন’ কোথায় হয়েছিল?
উত্তর: পাঞ্জাবে।
৫৯. ‘পূর্ণ স্বরাজ’ এর দাবি কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে গৃহীত হয়?
উত্তর: ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে।
৬০. ভারতে গান্ধীজি পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন কোনটি?
উত্তর: রাওলাট সত্যাগ্রহ (১৯১৯)।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. একা আন্দোলন কী?
উত্তর: ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের (তৎকালীন যুক্তপ্রদেশ) হরদোই, বারাবাঙ্কি, সীতাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকদের ওপর জমিদার ও তালুকদারদের অত্যাচার এবং অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা একা বা একতা আন্দোলন নামে পরিচিত। মাদারী পাসি ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান নেতা।
২. তেভাগা আন্দোলন বলতে কী বোঝো?
উত্তর: ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বর্গাদার বা ভাগচাষিরা জোতদারদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ চাষি পাবে এবং এক ভাগ জোতদার পাবে। এই দাবি থেকেই আন্দোলনটি ‘তেভাগা আন্দোলন’ নামে পরিচিত।
৩. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কী?
উত্তর: ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট প্রভাব এবং শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ৩৩ জন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। এই মামলাই ইতিহাসে ‘মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে পরিচিত।
৪. নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত AITUC-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিচ্ছিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একটি সর্বভারতীয় মঞ্চে একত্রিত করা, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণিকে যুক্ত করা।
৫. কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কেন গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপসকামী নীতির বিরোধিতা করে এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয়।
৬. ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: ভারতে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ‘লেবার স্বরাজ পার্টি’ নামে একটি দল গঠিত হয়। পরে এই দলটিই ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’ নাম নেয়।
৭. বারদৌলি সত্যাগ্রহের গুরুত্ব কী ছিল?
উত্তর: বারদৌলি সত্যাগ্রহের দুটি প্রধান গুরুত্ব হল: (১) এই অহিংস আন্দোলনের চাপে সরকার বর্ধিত রাজস্ব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়, যা ছিল কৃষকদের এক বিরাট জয়। (২) এই আন্দোলনের সফল নেতৃত্বের জন্য বল্লভভাই প্যাটেল ‘সর্দার’ উপাধিতে ভূষিত হন এবং জাতীয় নেতা হিসেবে তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।
৮. ‘লাঙ্গল’ ও ‘গণবাণী’ পত্রিকা দুটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: ‘লাঙ্গল’ (সম্পাদক: কাজী নজরুল ইসলাম) ও ‘গণবাণী’ (সম্পাদক: মুজফ্ফর আহমেদ) ছিল বাংলার ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির দুটি প্রধান মুখপত্র। এই পত্রিকাগুলি বাংলায় বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার এবং কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়ে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
৯. সর্বভারতীয় কিষাণ সভা কী কী দাবি উত্থাপন করেছিল?
উত্তর: সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রধান দাবিগুলি ছিল: (১) জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, (২) কৃষকদের সমস্ত ঋণ মকুব করা, (৩) সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং (৪) ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাসজমি বণ্টন করা।
১০. ‘জনযুদ্ধ’ তত্ত্বটি কী?
উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪১) জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ-বিরোধী অবস্থান পরিবর্তন করে। তারা এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ‘জনযুদ্ধ’ বলে ঘোষণা করে এবং ব্রিটিশদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই নীতিই ‘জনযুদ্ধ তত্ত্ব’ নামে পরিচিত।
১১. বাবা রামচন্দ্র কে ছিলেন?
উত্তর: বাবা রামচন্দ্র ছিলেন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) একজন গুরুত্বপূর্ণ কৃষক নেতা। তিনি জমিদার ও তালুকদারদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন এবং ‘অবধ কিষাণ সভা’ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
১২. মোপলা বিদ্রোহের দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: মোপলা বিদ্রোহের দুটি প্রধান কারণ হল: (১) হিন্দু জমিদারদের দ্বারা মুসলিম মোপলা কৃষকদের ওপর شدید শোষণ ও অত্যাচার। (২) খিলাফত আন্দোলনের প্রভাবে মোপলাদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী এবং জমিদার-বিরোধী চেতনা বৃদ্ধি পাওয়া।
১৩. ‘পূর্ণ স্বরাজ’-এর দাবিতে বামপন্থীদের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বামপন্থী নেতারা ব্রিটিশদের দেওয়া ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’-এর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাদের চাপেই ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয়।
১৪. মানবেন্দ্রনাথ রায় (M. N. Roy) স্মরণীয় কেন?
উত্তর: মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট নেতা। তিনি ১৯২০ সালে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
১৫. ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’ কী ছিল?
উত্তর: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় (১৯৪২) মেদিনীপুরের তমলুকে ব্রিটিশ শাসন অচল করে দিয়ে সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’ নামে পরিচিত। এই সরকার প্রায় দু’বছর ধরে টিকে ছিল।
১৬. ‘বেঠ-বেগারী’ প্রথা বলতে কী বোঝো?
উত্তর: ‘বেঠ-বেগারী’ ছিল একটি শোষণমূলক প্রথা, যেখানে কৃষকদের জমিদার বা সরকারের জন্য বিনাপারিশ্রমিকে বা নামমাত্র পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম দিতে হত। এটি ছিল কৃষক শোষণের একটি অন্যতম মাধ্যম।
১৭. স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী কে ছিলেন?
উত্তর: স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ছিলেন একজন সন্ন্যাসী এবং ভারতের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি বিহারে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন এবং ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।
১৮. ‘তিন আইন’ কী?
উত্তর: ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতে শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য তিনটি দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে। এগুলি হল: (১) ট্রেড ডিসপিউটস অ্যাক্ট বা শিল্পবিরোধ আইন, (২) পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট বা জননিরাপত্তা আইন এবং (৩) প্রেস অ্যাক্ট বা মুদ্রণ আইন। এই তিনটি আইন একত্রে ‘তিন আইন’ নামে পরিচিত।
১৯. ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ – এই নীতির তাৎপর্য কী?
উত্তর: এই নীতির তাৎপর্য হল, যারা সরাসরি জমিতে শ্রম দিয়ে ফসল ফলায়, জমির মালিকানা তাদেরই হওয়া উচিত। এই নীতি জমিদারি প্রথার অবসান এবং প্রকৃত কৃষকের হাতে জমির মালিকানা দেওয়ার দাবিকে তুলে ধরেছিল, যা কৃষক আন্দোলনকে এক নতুন দিশা দেখায়।
২০. ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার দুটি কারণ হল: (১) কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পর সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের আপসকামী নীতির বিরুদ্ধে একটি আপসহীন সংগ্রামী মঞ্চ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। (২) বামপন্থী শক্তিগুলিকে একত্রিত করে স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও তীব্র করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।
২১. ‘ট্রেড ইউনিয়ন’ কাকে বলে?
উত্তর: শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়, মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময় কমানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য যে সংগঠন গড়ে তোলে, তাকে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ বলা হয়।
২২. ‘কৃষক প্রজা পার্টি’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: বাংলার কৃষক, বিশেষ করে মুসলিম কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এ. কে. ফজলুল হক ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরে ‘কৃষক প্রজা পার্টি’ নামে পরিচিত হয়।
২৩. কংগ্রেস কেন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করেনি?
উত্তর: কংগ্রেস ছিল একটি সর্বস্তরের মানুষের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রেণি-সংগ্রামের দাবিগুলিকে পুরোপুরি সমর্থন করলে জমিদার ও শিল্পপতিদের মতো ধনী শ্রেণি কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যেত, যা জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারত। এই কারণে কংগ্রেস শ্রেণি-সংগ্রামের বদলে শ্রেণি-সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করে।
২৪. ‘ডান্ডি অভিযান’-এ শ্রমিকদের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানকে কেন্দ্র করে বোম্বাই, শোলাপুর, কলকাতা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট ও বিক্ষোভে অংশ নেয়। বিশেষত, শোলাপুরের শ্রমিক ধর্মঘট ব্রিটিশ প্রশাসনকে প্রায় অচল করে দিয়েছিল।
২৫. তেলেঙ্গানা আন্দোলনের দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: তেলেঙ্গানা আন্দোলনের দুটি প্রধান কারণ হল: (১) হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে থাকা জমিদার ও देशमुखদের দ্বারা কৃষকদের ওপর شدید শোষণ ও ‘বেঠ-বেগারী’ প্রথা। (২) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণি-সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জমি দখলের ডাক।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. সর্বভারতীয় কিষাণ সভার উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ আলোচনা করো।
ভূমিকা: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লখনউতে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
উদ্দেশ্য:
১. ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক সংগঠনগুলিকে একটি সর্বভারতীয় মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করা।
২. জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা।
৩. কৃষকদের সমস্ত ঋণ মকুব করা এবং নামমাত্র সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।
৪. ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ নীতি প্রতিষ্ঠা করা।
কার্যকলাপ: কিষাণ সভা কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে দেশব্যাপী প্রচার চালায়, বিভিন্ন স্থানে কৃষক সম্মেলন আয়োজন করে এবং ইস্তেহার প্রকাশ করে। তারা জাতীয় কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কৃষক-স্বার্থবাহী প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করার চেষ্টা করে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে কিষাণ সভার নেতৃত্বে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে।
২. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব লেখো।
প্রেক্ষাপট: ১৯২০-এর দশকের শেষ দিকে ভারতে কমিউনিস্ট ভাবধারা দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন এবং বিভিন্ন শিল্প ধর্মঘটে কমিউনিস্টদের সক্রিয় ভূমিকা ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তিত করে তোলে। এই ক্রমবর্ধমান বামপন্থী প্রভাবকে দমন করার জন্যই সরকার এক চরম দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
গুরুত্ব:
১. এই মামলার মাধ্যমে সরকার কমিউনিস্ট নেতাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য কারারুদ্ধ করে আন্দোলনকে সাময়িকভাবে দুর্বল করতে সক্ষম হয়।
২. মামলার শুনানির সময় অভিযুক্তরা আদালতকে তাদের মতাদর্শ প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেন। এর ফলে সারা দেশে, এমনকি বিদেশেও, কমিউনিস্ট মতাদর্শ সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
৩. রোমাঁ রোলাঁ, আইনস্টাইনের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বরা এই মামলার প্রতিবাদ করলে এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত হয়।
৪. এই মামলা জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে।
৩. টীকা লেখো: ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি।
ভূমিকা: বিশ শতকের ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের প্রসারে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি (WPP) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
প্রতিষ্ঠা: ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দিন আহমেদ প্রমুখের উদ্যোগে ‘লেবার স্বরাজ পার্টি’ নামে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ‘ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’ রাখা হয়।
উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি: এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা এবং একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তাদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি।
গুরুত্ব: এই দলটি ‘লাঙ্গল’ ও ‘গণবাণী’ পত্রিকার মাধ্যমে বামপন্থী ভাবধারা প্রচার করে এবং বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় এর বহু নেতা অভিযুক্ত হলে দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টিতে মিশে যায়।
৪. বিশ শতকের ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: বিশ শতকের ভারতে শ্রমিক আন্দোলনকে একটি নতুন দিশা দেখিয়েছিল বামপন্থী বা কমিউনিস্টরা। তাদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়।
ভূমিকা:
১. ট্রেড ইউনিয়ন গঠন: এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমেদ, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে শ্রমিকদের সংগঠিত করেন।
২. শ্রেণি-সংগ্রামের ধারণা: বামপন্থীরা শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি-সচেতনতা ও শ্রেণি-সংগ্রামের ধারণা প্রচার করে। তারা বোঝায় যে, মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থ এক নয়।
৩. রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ: বামপন্থীদের প্রভাবে শ্রমিকরা সাইমন কমিশন বয়কট, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বিভিন্ন ধর্মঘট ও বিক্ষোভে অংশ নেয়।
৪. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ: বামপন্থীরা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে।
উপসংহার: যদিও ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন (যেমন মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা) এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে বামপন্থীরা অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হয়, তবুও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে একটি বিপ্লবী চরিত্র দানে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
৫. ভারত ছাড়ো আন্দোলনে (১৯৪২) কৃষক ও শ্রমিকদের ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ, যেখানে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
কৃষকদের ভূমিকা: এই আন্দোলনে কৃষকরা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকরা সরকারি সম্পত্তি (যেমন – থানা, রেললাইন, ডাকঘর) আক্রমণ করে এবং খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বাংলার মেদিনীপুরে সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’ এবং উত্তরপ্রদেশের বালিয়াতে চিত্তু পান্ডের নেতৃত্বে ‘জাতীয় সরকার’ গঠিত হয়, যেখানে কৃষকদের ভূমিকা ছিল প্রধান।
শ্রমিকদের ভূমিকা: গান্ধীজির ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ ডাকে সাড়া দিয়ে বোম্বাই, আমেদাবাদ, জামশেদপুর, কানপুর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে। আমেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা প্রায় তিন মাস ধরে ধর্মঘট চালিয়ে যায়, যা ব্রিটিশ অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।
৬. টীকা লেখো: কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল।
প্রতিষ্ঠা: কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার তরুণ নেতাদের উদ্যোগে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে ‘কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল’ (Congress Socialist Party – CSP) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ।
উদ্দেশ্য:
১. কংগ্রেসের ভেতরে থেকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করা এবং কংগ্রেসকে একটি বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত করা।
২. ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীন ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
৩. কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের স্বার্থে আন্দোলন পরিচালনা করা।
গুরুত্ব: এই দলটি কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণে বামপন্থী চাপ সৃষ্টি করে, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর দলটি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক ‘সমাজতন্ত্রী দল’ গঠন করে।
৭. তেভাগা আন্দোলনের কারণ ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।
কারণ:
১. বাংলার ভাগচাষিদের (বর্গাদার) উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক জোতদারদের দিয়ে দিতে হত, যা ছিল এক চরম শোষণ।
২. ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ মন্বন্তরের পর কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে।
৩. ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশে উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষিকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু সরকার তা কার্যকর করেনি।
৪. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার নেতৃত্বে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।
গুরুত্ব:
১. এই আন্দোলন ছিল বাংলার সবচেয়ে ব্যাপক ও সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ, যা জোতদার ও সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেয়।
২. আন্দোলনের চাপে সরকার ‘বর্গাদার বিল’ পেশ করতে বাধ্য হয়।
৩. এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম কৃষকদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করে।
৪. স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং ভূমি সংস্কারের পথ প্রশস্ত করে এই আন্দোলন।
৮. একা আন্দোলনের পরিচয় দাও।
ভূমিকা: অসহযোগ আন্দোলনের আবহে ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) যে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ‘একা’ বা ‘একতা’ আন্দোলন নামে পরিচিত।
কারণ: নির্দিষ্ট খাজনার ওপর অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ কর আদায়, বেগার শ্রম এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা ক্ষুব্ধ ছিল।
নেতৃত্ব ও বিস্তার: কংগ্রেস ও খিলাফত নেতারা প্রথমে এই আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও পরে মাদারী পাসি ও সহরেব-এর মতো স্থানীয় নেতারা এর নেতৃত্ব দেন। হরদোই, বারাবাঙ্কি, সীতাপুর প্রভৃতি জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।
বৈশিষ্ট্য: কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ থাকার শপথ গ্রহণ করত। তাদের প্রধান দাবি ছিল, তারা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট খাজনা দেবে, অতিরিক্ত কর দেবে না। আন্দোলনটি পরবর্তীকালে হিংসাত্মক রূপ নিলে কংগ্রেস এর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং সরকার কঠোর হস্তে এটি দমন করে।
৯. ভারতের বামপন্থী আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (M. N. Roy) অবদান কী ছিল?
ভূমিকা: মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ এবং আন্তর্জাতিক স্তরের কমিউনিস্ট নেতা।
অবদান:
১. পার্টি প্রতিষ্ঠা: তিনি ১৯২০ সালে রাশিয়ার তাসখন্দে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ভারতের বাইরে গঠিত প্রথম কমিউনিস্ট সংগঠন।
২. মতাদর্শ প্রচার: তিনি ‘ভ্যানগার্ড’, ‘ম্যাসেজ’ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে এবং ‘India in Transition’-এর মতো গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতে মার্কসবাদী ভাবধারা প্রচার করেন।
৩. সাংগঠনিক ভূমিকা: তিনি লেনিনের পরামর্শে ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।
৪. পরবর্তী পর্ব: পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সরে এসে তিনি ‘র্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি’ বা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দল গঠন করেন এবং ‘নব্য মানবতাবাদ’ (New Humanism) নামে এক নতুন রাজনৈতিক দর্শন প্রচার করেন।
১০. জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থীদের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ ছিল?
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এক জটিল ও পরিবর্তনশীল সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।
সম্পর্ক:
১. সহযোগিতা: ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন, কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা একসঙ্গে কাজ করেন।
২. সংঘাত: কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব (যেমন – গান্ধীজি, প্যাটেল) বামপন্থীদের শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্বকে সমর্থন করেননি। তারা শ্রেণি-সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টদের ‘জনযুদ্ধ’ নীতি কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে তীব্র তিক্ততা সৃষ্টি করে।
উপসংহার: কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আর বামপন্থীদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণেই তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের সম্পর্ক বজায় ছিল।
১১. বিশ শতকের ভারতে কৃষক আন্দোলনের কারণগুলি কী ছিল?
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনগুলির পিছনে কিছু সাধারণ কারণ বিদ্যমান ছিল।
কারণসমূহ:
১. অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা: ব্রিটিশ সরকারের চিরস্থায়ী, রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের ওপর অত্যধিক করের বোঝা চাপে। এর পাশাপাশি জমিদার ও মহাজনদের শোষণ তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।
২. বেগার শ্রম ও অন্যান্য শোষণ: কৃষকদের প্রায়ই জমিদারদের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে (বেঠ-বেগারী) কাজ করতে বাধ্য করা হত। নজরানা, সেলামি ইত্যাদি বিভিন্ন বেআইনি করও আদায় করা হত।
৩. মহাজনী শোষণ: কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হত এবং প্রায়শই ঋণ শোধ করতে না পেরে তাদের জমি হারাত।
৪. রাজনৈতিক চেতনার প্রসার: জাতীয় কংগ্রেস, কিষাণ সভা এবং বামপন্থী দলগুলির কার্যকলাপের ফলে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে।
১২. টীকা লেখো: বারদৌলি সত্যাগ্রহ (১৯২৮)।
ভূমিকা: ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলি তালুকে যে অহিংস কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা বারদৌলি সত্যাগ্রহ নামে পরিচিত।
কারণ: বোম্বাই সরকার বারদৌলি তালুকে হঠাৎ করে ৩০% (পরে কমিয়ে ২২%) রাজস্ব বৃদ্ধি করে। এই অন্যায্য কর বৃদ্ধির প্রতিবাদেই কৃষকরা আন্দোলনের পথে নামে।
নেতৃত্ব ও কর্মসূচি: মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে বল্লভভাই প্যাটেল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা কর বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। সত্যাগ্রহীরা অহিংস পথে সরকারি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রতিরোধ করে এবং সামাজিক বয়কটের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করে। বারদৌলির নারীরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।
ফলাফল: কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে সরকার একটি তদন্ত কমিটি (ম্যাক্সওয়েল-ব্রুমফিল্ড কমিটি) গঠন করে এবং বর্ধিত কর প্রত্যাহার করে নেয়। এই সাফল্যের জন্য বারদৌলির নারীরা বল্লভভাই প্যাটেলকে ‘সর্দার’ উপাধি দেন।
১৩. কৃষক আন্দোলনে স্বামী বিদ্যানন্দের ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: স্বামী বিদ্যানন্দ ছিলেন বিহারের একজন গুরুত্বপূর্ণ কৃষক নেতা, যিনি دربhanga-র মহারাজার শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন।
ভূমিকা:
১. তিনি دربhanga মহারাজার এস্টেটে বেগার শ্রম, অতিরিক্ত কর আদায় এবং কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।
২. তিনি কৃষকদের নিয়ে সভা-সমিতি করেন এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন।
৩. তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
৪. তিনি বিহারের কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় স্তরের নেতাদের (যেমন – গান্ধীজি) নজরে আনেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করেন। তাঁর আন্দোলনই পরবর্তীকালে বিহারে কিষাণ সভা গঠনের পথ প্রশস্ত করে।
১৪. ‘레ড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ কেন গঠিত হয়েছিল?
ভূমিকা: ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নাগপুর অধিবেশনে AITUC-এর মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের সংঘাত তীব্র হয়, যার ফলে AITUC ভেঙে যায়।
গঠনের কারণ:
১. জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে নাগপুর অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত হুইটলি কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এন. এম. যোশীর মতো নরমপন্থী নেতারা AITUC ত্যাগ করেন।
২. কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং তাদের আপসহীন সংগ্রামী নীতি নরমপন্থী নেতাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।
৩. এই পরিস্থিতিতে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রণদিভে ও দেশপান্ডের নেতৃত্বে চরমপন্থী বা কমিউনিস্ট সদস্যরা মূল AITUC থেকে বেরিয়ে এসে ‘রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ (RTUC) গঠন করেন। এর ফলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
১৫. ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি লেখো।
সাদৃশ্য:
১. উভয় আন্দোলনই ছিল মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের সৃষ্ট দেশীয় শোষক শ্রেণির (জমিদার, মহাজন, শিল্পপতি) বিরুদ্ধে।
২. উভয় ক্ষেত্রেই বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীরা সংগঠন ও নেতৃত্ব দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
৩. উভয় আন্দোলনই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছিল এবং কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।
বৈসাদৃশ্য:
১. কৃষক আন্দোলনের মূল দাবি ছিল জমি সংক্রান্ত (খাজনা হ্রাস, জমিদারি উচ্ছেদ), আর শ্রমিক আন্দোলনের দাবি ছিল মজুরি, কাজের পরিবেশ ও সময় সংক্রান্ত।
২. কৃষক আন্দোলন ছিল মূলত গ্রামীণ, আর শ্রমিক আন্দোলন ছিল শহর ও শিল্পকেন্দ্রিক।
৩. কৃষক আন্দোলনগুলি প্রায়শই স্থানীয় ও বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির ছিল, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন সর্বভারতীয় স্তরে (AITUC) অনেক বেশি সংগঠিত ছিল।
১৬. মোপলা বিদ্রোহকে কি সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ বলা যায়? যুক্তিসহ লেখো।
ভূমিকা: ১৯২১ সালে কেরলের মালাবার উপকূলে সংঘটিত মোপলা বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।
সাম্প্রদায়িক বলার কারণ: এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা ছিলেন মূলত দরিদ্র মুসলিম (মোপলা) এবং শোষক জমিদাররা ছিলেন মূলত ধনী হিন্দু (জেনমি)। আন্দোলনের এক পর্যায়ে মোপলারা বহু হিন্দু জমিদারকে আক্রমণ করে, হত্যা করে এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করে। এই ঘটনাগুলির জন্য কিছু ঐতিহাসিক একে সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন।
অসাম্প্রদায়িক বলার কারণ: অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল শ্রেণি-সংঘাত, অর্থাৎ কৃষক ও জমিদারের মধ্যেকার অর্থনৈতিক শোষণ। বিদ্রোহীরা প্রথমে ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারতন্ত্র উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই শুরু করেছিল। খিলাফত আন্দোলনের প্রভাবও এর ওপর ছিল। তাই একে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক তকমা দেওয়া অনুচিত। এটি ছিল একটি কৃষক বিদ্রোহ যা পরিস্থিতিগত কারণে সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল।
১৭. ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’-এর কার্যাবলি আলোচনা করো।
ভূমিকা: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরের তমলুকে সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’ গঠিত হয়। এই সমান্তরাল সরকার প্রায় দু’বছর (১৯৪৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত) সক্রিয় ছিল।
কার্যাবলি:
১. প্রশাসন: এই সরকার নিজস্ব বিচার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অর্থ বিভাগ, যুদ্ধ বিভাগ ইত্যাদি গঠন করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে।
২. আইন-শৃঙ্খলা: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিজস্ব থানা ও বিচারালয় স্থাপন করা হয়।
৩. সশস্ত্র বাহিনী: ‘বিদ্যুৎ বাহিনী’ নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী এবং ‘ভগিনী সেনা’ নামে একটি নারী বাহিনী গঠন করা হয়।
৪. জনকল্যাণমূলক কাজ: সরকার ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে এবং স্কুল-কলেজের জন্য আর্থিক অনুদান দেয়।
১৮. ফরোয়ার্ড ব্লক কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এর কর্মসূচি কী ছিল?
প্রতিষ্ঠার কারণ: ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী সদস্যদের অসহযোগিতার কারণে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই আপসহীন বামপন্থী সংগ্রাম চালানোর উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের ৩রা মে ‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ নামে একটি নতুন দল গঠন করেন।
কর্মসূচি:
১. কংগ্রেসের আপসকামী নীতির বিরোধিতা করা।
২. দেশের সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা।
৩. অবিলম্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দেওয়া।
৪. স্বাধীন ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
১৯. বিশ শতকের ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
ভূমিকা: বিশ শতকে, বিশেষ করে গান্ধীজির নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর, ভারতের নারীরা ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে অংশ নেয়।
বৈশিষ্ট্য:
১. ব্যাপক অংশগ্রহণ: অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে পিকেটিং, মিছিল, সভা-সমিতিতে অংশ নেয়।
২. অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রাম: একদিকে যেমন সরোজিনী নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো নারীরা অহিংস সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন, তেমনই অন্যদিকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাসের মতো নারীরা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেও যোগ দেন।
৩. নেতৃত্ব প্রদান: নারীরা শুধুমাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণই করেনি, অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বও দিয়েছে। যেমন, আইন অমান্য আন্দোলনে সরোজিনী নাইডু বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঊষা মেহতা ও অরুণা আসফ আলি।
৪. সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ: রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীদের সামাজিক অবরোধ থেকেও মুক্তি দেয় এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।
২০. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর বামপন্থী চিন্তাধারার পরিচয় দাও।
ভূমিকা: সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান বামপন্থী নেতা। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।
বামপন্থী চিন্তাধারা:
১. পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি: তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’-এর ধারণার তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং প্রথম থেকেই ‘পূর্ণ স্বরাজ’ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিদার ছিলেন।
২. সমাজতান্ত্রিক আদর্শ: তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক মডেল দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং স্বাধীন ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র ও পরিকল্পনা কমিশন গঠনের স্বপ্ন দেখতেন।
৩. কৃষক-শ্রমিকদের গুরুত্ব: তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করার ওপর জোর দিতেন।
৪. আপসহীন সংগ্রাম: তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনো প্রকার আপসের বিরোধী ছিলেন এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এই চিন্তারই প্রতিফলন।
২১. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে কৃষক শ্রেণির ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন মূলত শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই আন্দোলনে কৃষক শ্রেণির অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত।
অংশগ্রহণের কারণ:
১. অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রচেষ্টা: বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের মতো কিছু নেতা কৃষকদের আন্দোলনে যুক্ত করার চেষ্টা করেন।
২. রাখিবন্ধন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখিবন্ধন উৎসব কিছু হিন্দু-মুসলিম কৃষকের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়াতে সাহায্য করে।
অংশগ্রহণ না করার কারণ:
১. কংগ্রেসের উদাসীনতা: কংগ্রেস নেতারা কৃষকদের খাজনা বন্ধ বা জমি সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া নিয়ে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেননি।
২. মুসলিম নেতাদের বিরোধিতা: ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সহ বহু মুসলিম নেতা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করায় পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলিম কৃষক এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিল।
২২. বিশ শতকের ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের অবদান কী ছিল?
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী বা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীরা এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিকেও যুক্ত করে।
অবদান:
১. পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি: বামপন্থীরাই প্রথম কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাইরে থেকে ‘পূর্ণ স্বরাজ’-এর দাবিকে জোরালো করে তোলে।
২. কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠিত করা: তারা কিষাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিকদের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে এবং জাতীয় আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
৩. সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন: বামপন্থীরা তাদের লেখনী ও প্রচারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণমূলক চরিত্রকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে।
৪. আপসহীন সংগ্রাম: তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে যেকোনো ধরনের আপসের বিরোধিতা করে আপসহীন সংগ্রামের পক্ষে সওয়াল করে, যা জাতীয় আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে।
২৩. টীকা লেখো: কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪)।
প্রেক্ষাপট: ১৯২০-এর দশকের শুরুতে ভারতে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এম. এন. রায়, এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমেদ প্রমুখ নেতারা কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচার করছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এই ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিল।
ঘটনা: এই প্রেক্ষাপটে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমেদ, শওকত উসমানি, নলিনী গুপ্তা প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতার বিরুদ্ধে ভারতে ব্রিটিশ সম্রাটের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে। এই মামলাই ‘কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে পরিচিত।
ফলাফল: এই মামলায় অভিযুক্তদের চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই মামলার ফলে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সাময়িকভাবে ধাক্কা খেলেও, এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯২৫ সালে কানপুরেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৪. ‘নৌবিদ্রোহে’ (১৯৪৬) শ্রমিকদের ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাইয়ের ‘তলোয়ার’ জাহাজের নাবিকরা বর্ণবিদ্বেষ ও খারাপ খাবারের প্রতিবাদে যে বিদ্রোহ শুরু করে, তা নৌবিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে ভারতের শ্রমিক শ্রেণি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।
শ্রমিকদের ভূমিকা:
১. নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাইয়ের কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতন্ত্রী দল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়।
২. এই ডাকে সাড়া দিয়ে বোম্বাইয়ের প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নেয়, যা ব্রিটিশ প্রশাসনকে অচল করে দেয়।
৩. শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে ব্যারিকেড তৈরি করে এবং ব্রিটিশ পুলিশ ও সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।
৪. বোম্বাই ছাড়াও করাচি, কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের শ্রমিকরাও নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে ধর্মঘট ও মিছিল করে। শ্রমিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নৌবিদ্রোহকে একটি গণ-অভ্যুত্থানের রূপ দেয়।
২৫. আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) কৃষক সমাজের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: ১৯৩০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হওয়া আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষক সমাজ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে, যা এই আন্দোলনকে এক নতুন শক্তি প্রদান করে।
ভূমিকা:
১. কর বয়কট: গুজরাটের বারদৌলি ও খেড়া, যুক্তপ্রদেশের রায়বেরিলি, বাংলার মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকরা সরকারি খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এটি ‘নো-ট্যাক্স’ বা ‘কর-বন্ধ’ আন্দোলন নামে পরিচিত।
২. চৌকিদারি কর বন্ধ: বাংলা ও বিহারে কৃষকরা চৌকিদারি কর দিতে অস্বীকার করে, যা ছিল ব্রিটিশ গ্রামীণ প্রশাসনের অন্যতম ভিত্তি।
৩. বন আইন অমান্য: মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে কৃষকরা ব্রিটিশ সরকারের অরণ্য আইন অমান্য করে জঙ্গলে প্রবেশ করে কাঠ সংগ্রহ ও পশুচারণ করে।
৪. সংগঠিত অংশগ্রহণ: এই সময়ে কৃষক আন্দোলন আগের চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছিল। কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্রিটিশ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৮ (১০টি)
১. বিশ শতকের ভারতে কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা করো।
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কৃষক আন্দোলন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ের আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল না, বরং তা ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল।
বৈশিষ্ট্য:
১. গান্ধীবাদী প্রভাব: বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কৃষক আন্দোলনে গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যাগ্রহের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চম্পারণ, খেড়া ও বারদৌলি সত্যাগ্রহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই আন্দোলনগুলিতে অহিংস পদ্ধতিতে কর বয়কট ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।
২. বামপন্থী প্রভাব: ১৯৩০-এর দশক থেকে কৃষক আন্দোলনে বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সর্বভারতীয় কিষাণ সভা গঠন এবং তেভাগা ও তেলেঙ্গানার মতো সংগ্রামী আন্দোলনগুলি শ্রেণি-সংগ্রামের আদর্শে পরিচালিত হয়েছিল।
৩. জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক: কৃষক আন্দোলনগুলির সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল জটিল। কংগ্রেস নীতিগতভাবে কৃষকদের সমর্থন করলেও জমিদার ও ধনী শ্রেণির স্বার্থে অনেক সময় আপসকামী নীতি গ্রহণ করত। তবে একা, বারদৌলি প্রভৃতি আন্দোলনে কংগ্রেস নেতারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
৪. ধর্মীয় প্রভাব: কিছু কৃষক আন্দোলন, যেমন – মোপলা বিদ্রোহ বা আকালি আন্দোলন, ধর্মীয় পরিচিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মোপলা বিদ্রোহে ইসলাম এবং আকালি আন্দোলনে শিখ ধর্মগুরুদের প্রভাব ছিল স্পষ্ট।
৫. আঞ্চলিক বৈচিত্র্য: কৃষক আন্দোলনগুলি সারা ভারতে একই রকম ছিল না। যুক্তপ্রদেশে একা আন্দোলন, বিহারে স্বামী বিদ্যানন্দের আন্দোলন, অন্ধ্রে এন. জি. রঙ্গের আন্দোলন এবং বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের দাবি ও চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন ছিল।
পর্যালোচনা: বিশ শতকের কৃষক আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ শাসন ও দেশীয় জমিদারতন্ত্রের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনগুলি কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সামিল করে। যদিও এই আন্দোলনগুলি সবসময় সফল হয়নি এবং অনেক সময় কঠোরভাবে দমিত হয়েছে, তবুও এগুলি স্বাধীন ভারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কারের পথকে প্রশস্ত করেছিল। এই আন্দোলনগুলি প্রমাণ করে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধুমাত্র মধ্যবিত্তের আন্দোলন ছিল না, এর ভিত্তি ছিল সাধারণ কৃষক সমাজ।
২. বিশ শতকের ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ এবং এই আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলির ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: বিশ শতকের শুরুতে ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হয় এবং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বিকাশ:
১. প্রাথমিক পর্যায় (১৯০০-১৯২০): এই পর্বে শ্রমিক আন্দোলন ছিল মূলত স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত এবং স্থানীয়। বি. পি. ওয়াদিয়ার ‘মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন’ (১৯১৮) ছিল ভারতের প্রথম সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন।
২. সংগঠিত রূপ (১৯২০-১৯৩০): ১৯২০ সালে ‘নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ (AITUC) প্রতিষ্ঠা শ্রমিক আন্দোলনকে একটি সর্বভারতীয় রূপ দেয়। এই সময় শ্রমিকরা অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।
৩. বামপন্থী প্রভাবের বিস্তার (১৯৩০-১৯৪৭): এই পর্বে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব দৃঢ় হয়। আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়। তবে এই সময় AITUC-তে বিভাজনও দেখা যায়।
জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা: কংগ্রেস প্রথমদিকে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে উদাসীন থাকলেও, ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। লালা লাজপত রায়, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো নেতারা AITUC-এর সভাপতি হন। তবে কংগ্রেস শ্রেণি-সংগ্রামের বিরোধী ছিল এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সমন্বয়ের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তাই তারা শ্রমিকদের বিপ্লবী কর্মসূচিকে সমর্থন করত না।
বামপন্থীদের ভূমিকা: বামপন্থীরাই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে প্রকৃত অর্থে একটি বিপ্লবী চরিত্র দান করে। তারা শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি-সচেতনতা বৃদ্ধি করে, তাদের সংগঠিত করে এবং তাদের অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিকে যুক্ত করে। তাদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা একাধিক সফল ধর্মঘট পালন করে এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দেয়। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা বামপন্থীদের দমন করার জন্যই করা হয়েছিল, যা তাদের গুরুত্ব প্রমাণ করে।
উপসংহার: বিশ শতকের শ্রমিক আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, যাকে শক্তি জুগিয়েছিল কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা এবং বামপন্থীদের বিপ্লবী চেতনা।
৩. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থী আন্দোলনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা: বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় ভারতে বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রসার ঘটে। এই ভাবধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করে।
ভূমিকা:
১. স্বাধীনতার লক্ষ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি: বামপন্থীরাই প্রথম ‘পূর্ণ স্বরাজ’ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে জনপ্রিয় করে তোলে। তারা মনে করত, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি কৃষক ও শ্রমিকের অর্থনৈতিক মুক্তিও প্রয়োজন। এই ধারণা জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যকে আরও व्यापक করে তোলে।
২. কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ: বামপন্থীরা ‘সর্বভারতীয় কিষাণ সভা’ এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে দেশের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত করে। তারা এই শোষিত শ্রেণিগুলিকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূল স্রোতে নিয়ে আসে, যা আন্দোলনকে এক গণচরিত্র দান করে।
৩. কংগ্রেসের ওপর প্রভাব: জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো কংগ্রেসের তরুণ নেতাদের ওপর বামপন্থী চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ছিল। তাদের চাপে কংগ্রেস বিভিন্ন কৃষক-শ্রমিক-স্বার্থবাহী প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা এই প্রভাবেরই ফল।
৪. সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন: বামপন্থীরা তাদের লেখনী ও প্রচারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণমূলক চরিত্রকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে। তারা বোঝায় যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ।
৫. আপসহীন সংগ্রামের নীতি: বামপন্থীরা ব্রিটিশদের সঙ্গে যেকোনো ধরনের আপস বা সমঝোতার তীব্র বিরোধী ছিল। তারা নিরবচ্ছিন্ন ও আপসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী ছিল।
সীমাবদ্ধতা: তবে বামপন্থী আন্দোলনের কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। ‘জনযুদ্ধ’ তত্ত্বের কারণে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।また, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সংঘাত অনেক সময় জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করেছে।
উপসংহার: কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটি গণমুখী ও বিপ্লবী চরিত্র দানে বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তারা স্বাধীনতার লড়াইকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত করেছিল।
৪. টীকা লেখো: তেভাগা আন্দোলন।
ভূমিকা: ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে ব্যাপক ও সংগ্রামী কৃষক আন্দোলন ছিল তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল মূলত জোতদারদের বিরুদ্ধে বর্গাদার বা ভাগচাষিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।
কারণ:
১. শোষণের তীব্রতা: বাংলার ভাগচাষিদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক জোর করে জোতদাররা নিয়ে যেত। এর পাশাপাশি আবওয়াব বা বিভিন্ন বেআইনি করও আদায় করা হত।
২. ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ: ১৯৪০ সালে সরকারি ফ্লাউড কমিশন সুপারিশ করে যে, ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষি পাবে। কিন্তু সরকার এই সুপারিশ কার্যকর না করায় কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়।
৩. মন্বন্তরের প্রভাব: ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ মন্বন্তর (পঞ্চাশের মন্বন্তর) কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়, যা তাদের বিদ্রোহী করে তোলে।
৪. কিষাণ সভার ভূমিকা: বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা কৃষকদের সংগঠিত করে এবং ‘তেভাগা চাই’, ‘নিজ খোলানে ধান তোলো’ প্রভৃতি স্লোগানের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে।
আন্দোলনের বিস্তার ও প্রকৃতি: এই আন্দোলন মূলত উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, যশোর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকরা জোর করে খেতের সমস্ত ধান নিজেদের খামারে তুলতে শুরু করলে জোতদার ও পুলিশের সঙ্গে তাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। শিবরাম মাঝি, দেবী সিংহ, ইলা মিত্র প্রমুখ এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেন।
গুরুত্ব: তেভাগা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এটি বাংলার কৃষক সমাজে এক নতুন জাগরণ নিয়ে আসে, হিন্দু-মুসলিম কৃষক ঐক্যকে দৃঢ় করে এবং স্বাধীন ভারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কারের প্রেক্ষাপট রচনা করে।
৫. আইন অমান্য আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা কীরূপ ছিল? এই আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?
ভূমিকা: ১৯৩০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হওয়া আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতের শ্রমিক শ্রেণি এক গুরুত্বপূর্ণ ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল।
শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা:
১. ব্যাপক ধর্মঘট: গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, শোলাপুর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে অংশ নেয়। গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার (GIP) রেলওয়ের শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
২. শোলাপুরের অভ্যুত্থান: মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে শহরের প্রশাসন ব্যবস্থা দখল করে নেয় এবং প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সেখানে ব্রিটিশ শাসন অচল ছিল। তারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং একটি সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে।
৩. হিংসাত্মক প্রতিরোধ: অনেক জায়গায়, যেমন – কলকাতা ও চট্টগ্রামে, শ্রমিকরা অহিংসার পথ ছেড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সরকারি সম্পত্তি আক্রমণ করে।
কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি: এই আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জটিল ও সমালোচনামূলক।
১. কমিউনিস্টরা মনে করত, গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব বুর্জোয়া বা ধনী শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের আন্দোলন ছিল আপসকামী এবং তারা শ্রমিকদের স্বার্থকে পুরোপুরি গুরুত্ব দেবে না।
২. তারা কংগ্রেসের লবণ সত্যাগ্রহের মতো কর্মসূচির সমালোচনা করে এবং এর পরিবর্তে শ্রমিকদের নিজস্ব দাবিতে পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট ও বিপ্লবের ডাক দেয়।
৩. এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কমিউনিস্টরা আইন অমান্য আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনের একটি বড় অংশ জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল।
৬. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী ছিল? এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ ও সর্বাত্মক পর্যায়। এই আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।
ঐতিহাসিক তাৎপর্য:
১. গণবিদ্রোহের চরিত্র: এটি ছিল একটি নেতা-বিহীন স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষক, ছাত্র ও যুবকরা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়।
২. ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়বড়ে করা: এই আন্দোলনের তীব্রতা ব্রিটিশ সরকারকে বুঝিয়ে দেয় যে, ভারতে তাদের শাসন আর দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তারা উপলব্ধি করে যে, বলপ্রয়োগ করে ভারতীয়দের আর দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়।
৩. সমান্তরাল সরকার গঠন: বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের মতো বিভিন্ন স্থানে ‘জাতীয় সরকার’ বা সমান্তরাল সরকার গঠিত হয়, যা ব্রিটিশ প্রশাসনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে।
৪. স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করা: এই আন্দোলন ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে এবং ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করার প্রেক্ষাপট রচনা করে।
কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা: ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রপক্ষে যোগ দিলে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ‘জনযুদ্ধ’ বলে ঘোষণা করে। এই নীতির কারণে তারা ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করে। তারা এই আন্দোলনকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ বলে অভিহিত করে এবং এর থেকে দূরে থাকে। কমিউনিস্টদের এই ভূমিকার জন্য তারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয় এবং জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
৭. বিশ শতকের ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী বা ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে কৃষক সমাজ এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনওই গণ-আন্দোলনের রূপ পেত না।
বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা:
১. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-১১): এই আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য, কারণ এটি ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং কৃষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মসূচি এতে ছিল না।
২. চম্পারণ, খেড়া ও বারদৌলি সত্যাগ্রহ: গান্ধীজির নেতৃত্বে এই তিনটি আঞ্চলিক কৃষক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। কৃষকরা অহিংস পদ্ধতিতে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায্য কর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সাফল্য লাভ করে।
৩. অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২): এই সময়ে যুক্তপ্রদেশে ‘একা আন্দোলন’ এবং মালাবারে ‘মোপলা বিদ্রোহ’-এর মতো কৃষক বিদ্রোহগুলি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং জমিদার ও ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।
৪. আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪): এই আন্দোলনে কৃষকরা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। তারা ‘কর-বন্ধ’ আন্দোলন শুরু করে, চৌকিদারি কর দিতে অস্বীকার করে এবং বন আইন অমান্য করে।
৫. ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২): এই আন্দোলনে কৃষকরা ছিল প্রধান শক্তি। তারা যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে, সরকারি দপ্তর আক্রমণ করে এবং বিভিন্ন স্থানে সমান্তরাল ‘জাতীয় সরকার’ গঠন করে ব্রিটিশ শাসনকে অচল করে দেয়।
৬. তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭): স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই দুটি সংগ্রামী কৃষক আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের পাশাপাশি দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেও এক চরম আঘাত হানে।
উপসংহার: বিশ শতকের প্রতিটি পর্যায়ে কৃষকরা নিজেদের দাবি-দাওয়ার পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। তাদের ত্যাগ ও সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা অর্জনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।
৮. অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) কৃষক ও শ্রমিকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা: ১৯২০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন ছিল ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে একে এক নতুন মাত্রা দেয়।
কৃষকদের ভূমিকা:
১. যুক্তপ্রদেশে বাবা রামচন্দ্রের নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদার ও তালুকদারদের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেসের অসহযোগ নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।
২. যুক্তপ্রদেশের হরদোই, বারাবাঙ্কি প্রভৃতি অঞ্চলে ‘একা আন্দোলন’ গড়ে ওঠে, যেখানে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে অতিরিক্ত কর না দেওয়ার শপথ নেয়।
৩. বিহারে স্বামী বিদ্যানন্দের নেতৃত্বে কৃষকরা دربhanga-র জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে।
৪. কেরলের মালাবার উপকূলে মুসলিম মোপলা কৃষকরা হিন্দু জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যা ‘মোপলা বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত।
শ্রমিকদের ভূমিকা:
১. অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশজুড়ে প্রায় ৪০০টি ধর্মঘট হয়। বাংলার চা-বাগান, রেল ও স্টিমার কোম্পানির শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
২. আসামের চা-বাগানের শ্রমিকরা শোষণের বিরুদ্ধে বাগান ছেড়ে ‘মুলুকে চলো’ বা দেশে ফেরার আন্দোলন শুরু করে।
৩. ১৯২০ সালে AITUC প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলন আরও সংগঠিত রূপ পায় এবং অসহযোগ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে।
উপসংহার: যদিও চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কৃষক-শ্রমিকরা হতাশ হয়, তবুও এই আন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, ভারতের সাধারণ মানুষও স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে প্রস্তুত।
৯. বিশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজের অবদান আলোচনা করো। এই প্রসঙ্গে ‘দীপালি সংঘ’ ও ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’র ভূমিকা উল্লেখ করো।
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমাজও এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল। তারা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে এসে অহিংস ও সশস্ত্র উভয় পথেই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল।
নারী সমাজের অবদান:
১. স্বদেশি যুগ: এই সময়ে নারীরা মূলত বিদেশি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার এবং অরন্ধন পালনের মতো কর্মসূচিতে অংশ নিত। সরলাদেবী চৌধুরানী ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রতিষ্ঠা করেন।
২. গান্ধীবাদী আন্দোলন: অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, মাতঙ্গিনী হাজরা, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ নারীরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তারা পিকেটিং, মিছিল, লবণ তৈরি এবং গোপন বেতার কেন্দ্র পরিচালনায় অংশ নেয়।
৩. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন: বাংলার নারীরা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেও পিছিয়ে ছিল না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দেন, কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যুক্ত ছিলেন এবং বীণা দাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন।
‘দীপালি সংঘ’ ও ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’র ভূমিকা:
দীপালি সংঘ: ১৯২৩ সালে লীলা নাগ (রায়) ঢাকায় ‘দীপালি সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটানো এবং তাদের বিপ্লবী কাজের জন্য প্রস্তুত করা। এটি ছিল মূলত একটি বিপ্লবী সংগঠন।
নারী সত্যাগ্রহ সমিতি: আইন অমান্য আন্দোলনের সময় (১৯৩০) কলকাতায় বাসন্তী দেবীর (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী) নেতৃত্বে ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যরা কলকাতায় পিকেটিং, মিছিল এবং লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
উপসংহার: নারী সমাজের এই বহুমুখী অংশগ্রহণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ করে তুলেছিল।
১০. ভারতের জাতীয় আন্দোলনে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর বামপন্থী ভাবধারার প্রকৃতি ও তাদের মধ্যেকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো।
ভূমিকা: জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দুই প্রধান তরুণ নেতা, যারা বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে একটি শক্তিশালী বামপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।
বামপন্থী ভাবধারার প্রকৃতি:
১. জওহরলাল নেহরু: নেহরু ছিলেন একজন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তার সমাজতন্ত্র ছিল গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন।
২. সুভাষচন্দ্র বসু: সুভাষচন্দ্র বসুর সমাজতন্ত্র ছিল অনেক বেশি র্যাডিক্যাল বা চরমপন্থী। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি ফ্যাসিবাদী ইতালির শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি আপসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অধীনে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন।
সাদৃশ্য:
১. দুজনেই ‘পূর্ণ স্বরাজ’ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস’-এর ধারণার বিরোধী ছিলেন।
২. দুজনেই কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করার ওপর গুরুত্ব দিতেন।
৩. দুজনেই স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে ছিলেন।
বৈসাদৃশ্য:
১. নেহরু গান্ধীজির নেতৃত্ব ও অহিংস নীতির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির নীতির সমালোচক ছিলেন এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন।
২. নেহরু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে কাজ করায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাতের পর কংগ্রেস ত্যাগ করে ‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ গঠন করেন।
৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেহরু ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরোধিতা করেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র ‘শত্রুর শত্রু আমার মিত্র’ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন।
উপসংহার: ভাবাদর্শগত মিল থাকা সত্ত্বেও, কর্মপন্থা ও গান্ধীজির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে পার্থক্যের কারণে এই দুই নেতার পথ পরবর্তীকালে ভিন্ন হয়ে যায়।
Class 10 History বিশ শতকের ভারতে কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা Question Answer MCQ,অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : class 10 বিশ শতকের ভারতে কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন প্রশ্ন উত্তর