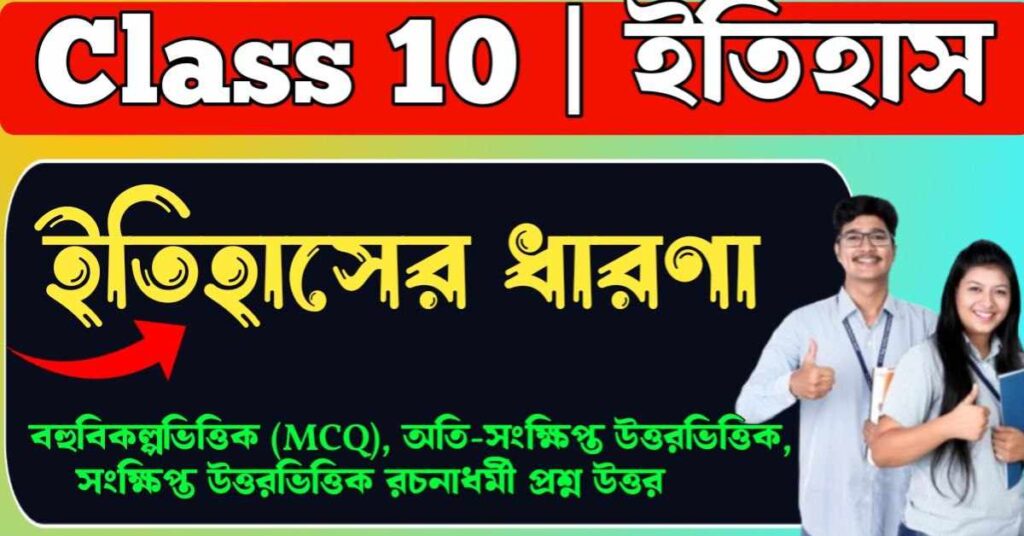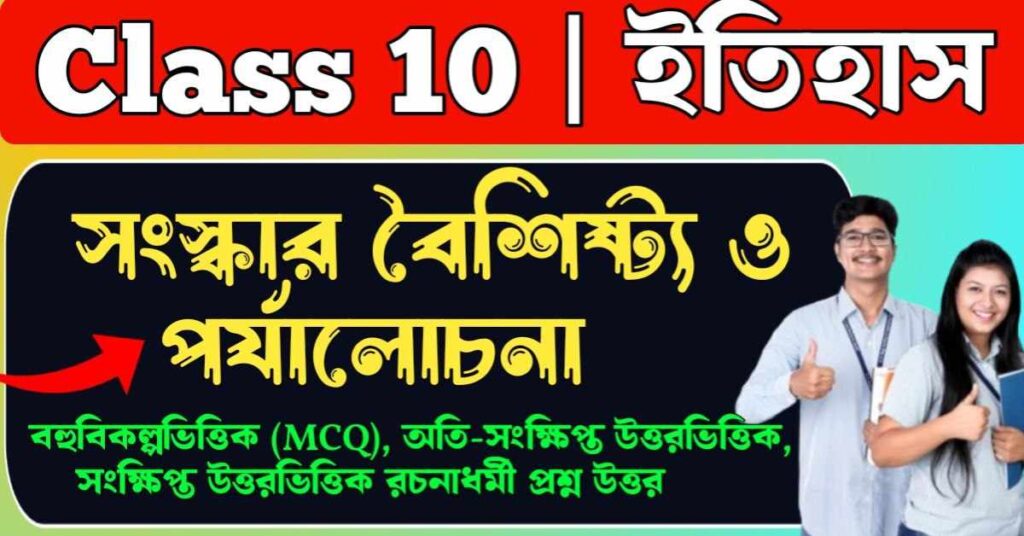বিশ শতকের ভারতে নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন –
২. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন –
৩. অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন –
৪. দলিতদের ‘হরিজন’ আখ্যা দিয়েছিলেন –
৫. পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল –
৬. বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা করেন –
৭. ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন নেত্রী ছিলেন –
৮. অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় –
৯. সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের নারী সদস্য ছিলেন –
১০. ‘নমঃশূদ্র’ আন্দোলন শুরু হয়েছিল –
১১. ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন আন্দোলনের সময়?
১২. ভাইকম সত্যাগ্রহ হয়েছিল –
১৩. রশিদ আলি দিবস পালিত হয় –
১৪. ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ দলের সদস্য ছিলেন –
১৫. পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল গান্ধীজি ও –
১৬. ‘গান্ধী বুড়ি’ নামে পরিচিত ছিলেন –
১৭. মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন –
১৮. ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ ছিল একটি –
১৯. ‘কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট’ স্টিভেন্সকে হত্যা করেন –
২০. যে আইনের দ্বারা দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, তা হল –
২১. ‘ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী’ বলা হয় –
২২. ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন –
২৩. কার্লাইল সার্কুলার জারি করা হয়েছিল –
২৪. ‘Annihilation of Caste’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
২৫. ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রতিষ্ঠা করেন –
২৬. ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন –
২৭. ‘মাস্টারদা’ নামে পরিচিত ছিলেন –
২৮. ‘অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস লিগ’ প্রতিষ্ঠা করেন –
২৯. যে ছাত্রীটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নরকে গুলি করেন, তিনি হলেন –
৩০. ‘লাইফ ডিভাইন’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
৩১. রশিদ আলি ছিলেন –
৩২. ‘ফরওয়ার্ড’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন –
৩৩. ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন –
৩৪. ভারতীয় সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন –
৩৫. ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৩৬. ‘অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্টস ফেডারেশন’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৩৭. যে বিপ্লবী নারী ‘পটাশিয়াম সায়ানাইড’ খেয়ে আত্মহত্যা করেন, তিনি হলেন –
৩৮. ‘অনুশীলন সমিতি’র নারী সদস্য ছিলেন –
৩৯. যে আন্দোলনে নারীরা প্রথম ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে, তা হল –
৪০. ‘ভগিনী সেনা’ গঠিত হয়েছিল কোন আন্দোলনের সময়?
৪১. ‘হরিজন সেবক সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৪২. ‘ছাত্রী সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৪৩. ‘রাইটার্স বিল্ডিং’ অভিযান হয় –
৪৪. স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন –
৪৫. ভারতের ‘নাইটিঙ্গেল’ বলা হয় –
৪৬. ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ গঠিত হয় –
৪৭. যে বিখ্যাত নারী লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজির সঙ্গে নেতৃত্ব দেন –
৪৮. ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৪৯. ‘সত্যশোধক সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৫০. ‘সিমলা দৌত্য’ (১৯০৬) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন –
৫১. সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যে ছাত্রনেতা প্রাণ হারান –
৫২. ‘মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৫৩. ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী চক্র’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
৫৪. ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৫৫. ‘যুগান্তর’ দলের নারী সদস্য কে ছিলেন?
৫৬. ‘সারা ভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী লিগ’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
৫৭. ‘শ্রীসংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৫৮. ‘বীরাষ্টমী ব্রত’ চালু করেন –
৫৯. ‘অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন’ (ABSA) কবে গঠিত হয়?
৬০. ‘ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট’ (১৮৭৬) এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল –
৬১. ‘জয়শ্রী’ পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন –
৬২. নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক গুরু কে ছিলেন?
৬৩. ‘কংগ্রেস রেডিও’র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন –
৬৪. ‘নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ’ কবে হয়েছিল?
৬৫. ‘সবিতা’ ছদ্মনামে কে পরিচিত ছিলেন?
৬৬. ‘স্বদেশ বান্ধব সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন –
৬৭. কোন গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ আম্বেদকর দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানান?
৬৮. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তমলুকে ‘ভগিনী সেনা’র নেতৃত্ব দেন –
৬৯. ‘আত্মশক্তি’ প্রবন্ধটি কার লেখা?
৭০. ‘অস্পৃশ্যতা’ দূরীকরণের জন্য গান্ধীজি যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, তার নাম –
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. দীপালি সংঘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: লীলা নাগ (রায়)।
২. দীপালি সংঘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।
৩. একজন সশস্ত্র বিপ্লবী নারীর নাম লেখো।
উত্তর: প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
৪. অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।
৫. পুনা চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর।
৬. পুনা চুক্তি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে।
৭. ‘গান্ধী বুড়ি’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: মাতঙ্গিনী হাজরাকে।
৮. অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
৯. ‘মাস্টারদা’ নামে কে পরিচিত ছিলেন?
উত্তর: সূর্য সেন।
১০. নমঃশূদ্র আন্দোলনের একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: গুরুচাঁদ ঠাকুর।
১১. নারী সত্যাগ্রহ সমিতির একজন নেত্রীর নাম লেখো।
উত্তর: বাসন্তী দেবী।
১২. ভাইকম সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে দলিতদের হাঁটার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
১৩. রশিদ আলি কে ছিলেন?
উত্তর: আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন ক্যাপ্টেন।
১৪. ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ দলের তিনজন বিখ্যাত শহিদের নাম লেখো।
উত্তর: বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত।
১৫. দলিতদের ‘হরিজন’ নামের অর্থ কী?
উত্তর: ঈশ্বরের সন্তান।
১৬. শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কেন বিখ্যাত?
উত্তর: কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করার জন্য।
১৭. মতুয়া মহাসঙ্ঘ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর।
১৮. ‘কার্লাইল সার্কুলার’ কী ছিল?
উত্তর: বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের জারি করা একটি দমনমূলক নির্দেশ।
১৯. ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’ কে ঘোষণা করেন?
উত্তর: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড।
২০. সরলাদেবী চৌধুরানী কোন ব্রত চালু করেন?
উত্তর: বীরাষ্টমী ব্রত।
২১. ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২২. ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’র সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
উত্তর: সূর্য সেন।
২৩. কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ‘রশিদ আলি দিবস’ পালিত হয়?
উত্তর: আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলির ৭ বছর কারাদণ্ডকে কেন্দ্র করে।
২৪. ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তারের নাম কী?
উত্তর: কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (বসু)।
২৫. ‘জয়শ্রী’ পত্রিকার সম্পাদিকা কে ছিলেন?
উত্তর: লীলা নাগ (রায়)।
২৬. একজন দলিত নেতার নাম লেখো।
উত্তর: ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।
২৭. পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব কে দেন?
উত্তর: প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
২৮. ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।
২৯. ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ কী উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়?
উত্তর: স্বদেশি জিনিসপত্র বিক্রির জন্য।
৩০. অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনের প্রথম অধিবেশন কোথায় বসে?
উত্তর: লখনউ-তে।
৩১. ‘অনুশীলন সমিতি’র একজন নেতার নাম লেখো।
উত্তর: পুলিনবিহারী দাস।
৩২. ‘স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন’ কার রচনা?
উত্তর: সূর্য সেনের।
৩৩. ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর একজন নারী বিপ্লবীর নাম লেখো।
উত্তর: ননীবালা দেবী।
৩৪. ‘অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস কংগ্রেস’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।
৩৫. ‘ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে।
৩৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা এম. এ. কে ছিলেন?
উত্তর: চন্দ্রমুখী বসু।
৩৭. রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান কবে হয়?
উত্তর: ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর।
৩৮. গুরুচাঁদ ঠাকুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করো।
উত্তর: তিনি নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
৩৯. ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তমলুকের নেতৃত্ব কে দেন?
উত্তর: সতীশচন্দ্র সামন্ত।
৪০. ‘অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন’ (ABSA) এর প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: প্রমোদ ঘোষাল।
৪১. ‘হরিজন’ পত্রিকা কে প্রকাশ করেন?
উত্তর: মহাত্মা গান্ধী।
৪২. ‘ছাত্রী সংঘ’ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: কলকাতায়।
৪৩. ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।
৪৪. ‘নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা’য় কার ফাঁসি হয়?
উত্তর: অনন্ত কানহেরের।
৪৫. চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কবে হয়েছিল?
উত্তর: ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল।
৪৬. ‘সঞ্জীবনী সভা’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: রাজনারায়ণ বসু।
৪৭. ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’-এর নারী বাহিনীর নাম কী ছিল?
উত্তর: ঝাঁসির রানি ব্রিগেড।
৪৮. ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক কারা?
উত্তর: কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু।
৪৯. ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ এর প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: রাসবিহারী ঘোষ।
৫০. ‘শ্রীসংঘ’ কোন শহরের বিপ্লবী সংগঠন ছিল?
উত্তর: ঢাকার।
৫১. আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কলকাতার মেয়র কে ছিলেন?
উত্তর: যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৫২. ‘মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: লতিকা ঘোষ।
৫৩. ‘অস্পৃশ্যতা’ আইনত নিষিদ্ধ হয় কোন সালে?
উত্তর: ১৯৫৫ সালে।
৫৪. ‘বয়কট’ প্রস্তাব প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকায়।
৫৫. ‘বেথুন স্কুল’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন।
৫৬. ‘কংগ্রেস রেডিও’ কোন আন্দোলনের সময় সক্রিয় ছিল?
উত্তর: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়।
৫৭. ‘ননীবালা দেবী’ কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উত্তর: যুগান্তর দল।
৫৮. ‘মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন’ কবে পাস হয়?
উত্তর: ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।
৫৯. ‘যতীন দাস’ কতদিন অনশন করে প্রাণত্যাগ করেন?
উত্তর: ৬৩ দিন।
৬০. ‘ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট’ কবে পাস হয়?
উত্তর: ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. দীপালি সংঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে লীলা নাগের নেতৃত্বে ঢাকায় দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটানো এবং ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য নারীদের প্রস্তুত করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।
২. অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি কী?
উত্তর: বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার কার্লাইল সার্কুলার জারি করে ছাত্রদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এর প্রতিবাদে ১৯০৫ সালে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নেতৃত্বে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি দমননীতির কারণে বিতাড়িত ছাত্রদের বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৩. পুনা চুক্তির (১৯৩২) দুটি শর্ত লেখো।
উত্তর: পুনা চুক্তির দুটি প্রধান শর্ত হল: (১) দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি প্রত্যাহার করা হবে। (২) এর পরিবর্তে, प्रादेशिक আইনসভাগুলিতে দলিতদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৭১টি থেকে বাড়িয়ে ১৪৮টি করা হবে।
৪. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণীয় কেন?
উত্তর: প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের একজন অন্যতম সদস্য। তিনি ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দেন। আক্রমণ শেষে ধরা পড়ার আগে তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ বিপ্লবীদের কাছে এক অনুপ্রেরণা ছিল।
৫. ‘অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন’ কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৩৬ সালে লখনউতে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে একটি সর্বভারতীয় মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করা এবং ছাত্র সমাজকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা।
৬. মাতঙ্গিনী হাজরা কে ছিলেন?
উত্তর: মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন মেদিনীপুরের একজন গান্ধীবাদী নেত্রী, যিনি ‘গান্ধী বুড়ি’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তমলুকে একটি মিছিল নিয়ে থানা দখল করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তাঁর আত্মত্যাগ আজও স্মরণীয়।
৭. দলিত কাদের বলা হয়?
উত্তর: ভারতের বর্ণহিন্দু সমাজব্যবস্থায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের যে সমস্ত মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষিত ও নিপীড়িত, তাদের দলিত বলা হয়। ব্রিটিশ আমলে তাদের ‘তফসিলি জাতি’ বা ‘Scheduled Caste’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৮. নারী সত্যাগ্রহ সমিতি কেন গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: আইন অমান্য আন্দোলনের সময় (১৯৩০) নারীদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যরা বিদেশি মদের দোকান ও বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং এবং লবণ আইন অমান্য করার মতো কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।
৯. বিনয়-বাদল-দীনেশ স্মরণীয় কেন?
উত্তর: বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ছিলেন ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ দলের তিন বিপ্লবী। তারা ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ (বর্তমান মহাকরণ) প্রবেশ করে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ‘রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান’ বা ‘অলিন্দ যুদ্ধ’ নামে পরিচিত।
১০. গুরুচাঁদ ঠাকুর কে ছিলেন?
উত্তর: গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র এবং বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছিলেন।
১১. রশিদ আলি দিবস কেন পালিত হয়েছিল?
উত্তর: আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলিকে ব্রিটিশ সরকার ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিলে তার প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ছাত্ররা এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এই দিনটিই ‘রশিদ আলি দিবস’ নামে পরিচিত।
১২. কল্পনা দত্তের বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিচয় দাও।
উত্তর: কল্পনা দত্ত ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেনের ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’র একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন এবং সূর্য সেনের সঙ্গে আত্মগোপন করে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান। পরে ধরা পড়ে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।
১৩. ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’ নীতি কী?
উত্তর: ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষিত একটি নীতি, যার দ্বারা ভারতের মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টানদের পাশাপাশি অনুন্নত হিন্দু বা দলিত সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।
১৪. সরলাদেবী চৌধুরানী স্মরণীয় কেন?
উত্তর: সরলাদেবী চৌধুরানী ছিলেন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নারী নেত্রী। তিনি যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগানোর জন্য ‘বীরাষ্টমী ব্রত’ ও ‘প্রতাপাদিত্য উৎসব’ চালু করেন এবং স্বদেশি জিনিসপত্রের প্রচারের জন্য ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রতিষ্ঠা করেন।
১৫. ‘ডন সোসাইটি’ কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ‘ডন সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে জাতীয় শিক্ষা প্রদান করা এবং তাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।
১৬. বীণা দাসের বিপ্লবী কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর: বীণা দাস ছিলেন বাংলার একজন সশস্ত্র বিপ্লবী নারী। তিনি ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। যদিও গভর্নর বেঁচে যান, বীণা দাসের এই অসম সাহসিকতা সমগ্র ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।
১৭. ‘ভাইকম সত্যাগ্রহ’ কী ছিল?
উত্তর: কেরালার ভাইকম নামক স্থানের একটি মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে দলিতদের হাঁটার অধিকার ছিল না। এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে নারায়ণ গুরু, টি. কে. মাধবন প্রমুখের নেতৃত্বে যে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ‘ভাইকম সত্যাগ্রহ’ নামে পরিচিত।
১৮. ‘হরিজন’ বলতে গান্ধীজি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: গান্ধীজি ভারতের অস্পৃশ্য বা দলিত সম্প্রদায়কে সম্মান জানাতে ‘হরিজন’ নামে অভিহিত করেন। ‘হরিজন’ শব্দের অর্থ ‘হরির (ঈশ্বরের) সন্তান’। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দলিতরা ঈশ্বরের সন্তান এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের অস্পৃশ্য মনে করা পাপ।
১৯. ‘শ্রীসংঘ’ ও ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ কারা প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: ঢাকায় ‘শ্রীসংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন অনিল রায় এবং কলকাতায় ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ (B.V.) প্রতিষ্ঠা করেন হেমচন্দ্র ঘোষ। দুটিই ছিল বাংলার গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন।
২০. ‘নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন’ কী?
উত্তর: হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলায় নমঃশূদ্রদের মধ্যে যে সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা ‘নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন’ বা মতুয়া আন্দোলন নামে পরিচিত। এর মূল কথা ছিল ভক্তি ও মানবপ্রেমের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।
২১. ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ (Direct Action Day) কী?
উত্তর: পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি আদায়ের জন্য মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ পালনের ডাক দেয়। এই দিন কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, যা ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ নামে পরিচিত।
২২. ‘ভগিনী সেনা’ কী ছিল?
উত্তর: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের তমলুকে গঠিত ‘তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার’-এর নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ‘ভগিনী সেনা’ বলা হত। মাতঙ্গিনী হাজরা এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এরা ত্রাণকাজ, সংবাদ আদান-প্রদান এবং আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নিত।
২৩. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কে ছিলেন?
উত্তর: যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন একজন বিশিষ্ট দলিত (নমঃশূদ্র) নেতা। তিনি প্রথমে ডঃ আম্বেদকরের অনুগামী ছিলেন, কিন্তু পরে মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট গঠন করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমমন্ত্রী হন।
২৪. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের দুটি ভূমিকা লেখো।
উত্তর: বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের দুটি ভূমিকা হল: (১) তারা বিদেশি দ্রব্য, বিশেষ করে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট করে। (২) তারা পিকেটিং, মিছিল এবং স্বদেশি দ্রব্যের প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
২৫. অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনে ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য দলিতদের শিক্ষিত ও সংগঠিত হওয়ার ডাক দেন। তিনি ১৯২৭ সালে ‘মহাদ সত্যাগ্রহ’ এবং ১৯৩০ সালে ‘কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহ’-এর মতো আন্দোলনের মাধ্যমে দলিতদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেন।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষ করে বাংলায়, নারীরা শুধুমাত্র অহিংস আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তারা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল।
চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য:
১. সক্রিয় অংশগ্রহণ: নারীরা বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া, খবর আদান-প্রদান করা বা অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার মতো সহায়ক ভূমিকার পাশাপাশি সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ক্লাব আক্রমণ বা বীণা দাসের গভর্নরকে গুলি করার ঘটনা এর প্রমাণ।
২. সাংগঠনিক অন্তর্ভুক্তি: নারীরা ‘দীপালি সংঘ’, ‘ছাত্রী সংঘ’-এর মতো নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি ‘যুগান্তর’, ‘অনুশীলন সমিতি’, ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’-এর মতো প্রধান বিপ্লবী দলেও যোগদান করে।
৩. সামাজিক প্রথার অচলায়তন ভাঙা: তাদের এই কর্মকাণ্ড ছিল প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে এক বিরাট বিদ্রোহ। পর্দা প্রথা ও রক্ষণশীলতাকে অগ্রাহ্য করে তাদের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
৪. আত্মত্যাগ: প্রীতিলতার আত্মাহুতি, কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাবাস প্রমাণ করে যে, দেশের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারে তারা পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না।
২. টীকা লেখো: দলিত অধিকার বিষয়ে গান্ধী-আম্বেদকর বিতর্ক।
ভূমিকা: ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হয়েছিল। এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ‘পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী’র প্রশ্ন।
আম্বেদকরের যুক্তি: ডঃ আম্বেদকর মনে করতেন, দলিতরা হিন্দু সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও শোষিত। তাই তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রয়োজন, যেখানে শুধু দলিতরাই দলিত প্রার্থীকে ভোট দেবে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এই দাবি উত্থাপন করেন।
গান্ধীর যুক্তি: গান্ধীজি আম্বেদকরের দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করতেন, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দলিতদের হিন্দু সমাজ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং হিন্দু সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করবে। তিনি এর পরিবর্তে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর অধীনে দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব দেন।
ফলাফল: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’ নীতিতে দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ঘোষণা করলে, গান্ধীজি তার প্রতিবাদে পুনার যারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। অবশেষে আম্বেদকর নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং উভয়ের মধ্যে ‘পুনা চুক্তি’ (১৯৩২) স্বাক্ষরিত হয়, যা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পরিবর্তে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে।
৩. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনকে একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত করার পিছনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।
ভূমিকা:
১. বয়কট ও পিকেটিং: ছাত্ররা ছিল বয়কট আন্দোলনের প্রধান শক্তি। তারা বিদেশি স্কুল-কলেজ, আদালত বয়কট করে এবং বিদেশি লবণ, চিনি ও কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করে।
২. স্বদেশি দ্রব্যের প্রচার: ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্বদেশি দ্রব্য বিক্রি করত এবং মানুষকে স্বদেশি জিনিসপত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করত।
৩. সংগঠন প্রতিষ্ঠা: সরকারি দমননীতির (যেমন – কার্লাইল সার্কুলার) প্রতিবাদে ছাত্ররা ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’র মতো সংগঠন গড়ে তোলে এবং বিতাড়িত ছাত্রদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।
৪. বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান: স্বদেশি আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বহু ছাত্র সশস্ত্র বিপ্লবী পথ বেছে নেয় এবং ‘অনুশীলন সমিতি’ ও ‘যুগান্তর’ দলের মতো সংগঠনে যোগ দেয়।
উপসংহার: ছাত্রদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক অংশগ্রহণ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল এবং ব্রিটিশ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।
৪. টীকা লেখো: নমঃশূদ্র আন্দোলন।
ভূমিকা: উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা নমঃশূদ্র আন্দোলন নামে পরিচিত।
নেতৃত্ব: এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। তারা ‘মতুয়া মহাসঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠা করে নমঃশূদ্রদের সংগঠিত করেন।
আন্দোলনের প্রকৃতি:
১. সামাজিক: এই আন্দোলন ছিল মূলত বর্ণহিন্দুদের সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে। নমঃশূদ্ররা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেয়।
২. ধর্মীয়: হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রচারিত ‘মতুয়া’ ধর্ম ছিল এক সহজ সরল ভক্তিধর্ম, যা জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল।
৩. রাজনৈতিক: গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা সরকারি চাকরি ও আইনসভায় নিজেদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। তারা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিল, কারণ তারা মনে করত নতুন প্রদেশে তাদের উন্নতি হবে।
উপসংহার: নমঃশূদ্র আন্দোলন ছিল বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সফল প্রচেষ্টা।
৫. ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ (B.V.) দলের বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিচয় দাও।
ভূমিকা: ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ বা B.V. ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন। ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের জন্য এটি একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসেবে গঠিত হলেও, পরে হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এটি একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়।
বিপ্লবী কার্যকলাপ:
১. অপারেশন ফ্রিডম: এই দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুঃসাহসিক অ্যাকশনের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। তাদের এই কার্যকলাপ ‘অপারেশন ফ্রিডম’ নামে পরিচিত ছিল।
২. লোম্যান হত্যা: ১৯৩০ সালে এই দলের সদস্য বিনয় বসু ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করেন।
৩. রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান: এই দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান। তারা কারা বিভাগের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেন।
অন্যান্য কার্যকলাপ: এছাড়া এই দলের সদস্যরা জেলাশাসক পেডি, ডগলাস ও বার্জ হত্যা এবং গভর্নর অ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টাতেও যুক্ত ছিল।
৬. আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ছিল প্রথম আন্দোলন, যেখানে ভারতের নারীরা বিপুল সংখ্যায় ঘরের বাইরে এসে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল।
ভূমিকা:
১. লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ: নারীরা গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানে অংশ নেয়। গান্ধীজির গ্রেপ্তারের পর সরোজিনী নাইডু ধারাসানা লবণ গোলা অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
২. পিকেটিং ও বয়কট: নারীরা বিদেশি মদের দোকান ও কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করে, যা ছিল আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি।
৩. সংগঠন গড়ে তোলা: এই সময়ে কলকাতায় বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে ‘নারী সত্যাগ্রহ সমিতি’ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণায় লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে ‘মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ’ গড়ে ওঠে, যা নারীদের সংগঠিত করতে সাহায্য করে।
৪. কারাবরণ: হাজার হাজার নারী আইন অমান্য করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কারাবরণকারী প্রথম ভারতীয় নারীদের অন্যতম। তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আন্দোলনকে এক নতুন শক্তি জোগায়।
৭. টীকা লেখো: মাস্টারদা সূর্য সেন ও ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (IRA)।
ভূমিকা: মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের এক কিংবদন্তি নেতা। তিনি চট্টগ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তাই ‘মাস্টারদা’ নামে পরিচিত ছিলেন।
ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (IRA): সূর্য সেন আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রামে ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’ বা IRA নামে একটি বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলেন। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্তের মতো নারীরাও এই দলে ছিলেন।
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন: IRA-এর সবচেয়ে বড় কীর্তি হল ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। এই দিন বিপ্লবীরা একযোগে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার ও সহায়ক বাহিনীর অস্ত্রাগার দখল করে নেয় এবং টেলিফোন ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। তারা চট্টগ্রামে স্বাধীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করে।
ফলাফল: যদিও এই সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী, জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে অসম লড়াইয়ে বহু বিপ্লবী প্রাণ হারান। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন ধরা পড়েন এবং ১৯৩৪ সালে তাঁর ফাঁসি হয়।
৮. পুনা চুক্তির (১৯৩২) প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
প্রেক্ষাপট:
১. দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ আম্বেদকর দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানালে গান্ধীজি তার বিরোধিতা করেন।
২. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’ নীতি ঘোষণা করে আম্বেদকরের দাবি মেনে নেন।
৩. গান্ধীজি এই নীতির প্রতিবাদে পুনার যারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর জীবন বিপন্ন হলে এক চাপের পরিস্থিতি তৈরি হয়।
গুরুত্ব:
১. এই চুক্তির ফলে গান্ধীজির জীবন রক্ষা পায় এবং হিন্দু সমাজের বিভাজন রোধ করা সম্ভব হয়।
২. দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর পরিবর্তে আইনসভায় তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৭১ থেকে বাড়িয়ে ১৪৮টি করা হয়। এতে দলিতদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।
৩. এই চুক্তি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আন্দোলনকে গতি দেয়। গান্ধীজি ‘হরিজন সেবক সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অস্পৃশ্যতা-বিরোধী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।
৪. এই চুক্তি ডঃ আম্বেদকরকে দলিতদের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।
৯. ভারত ছাড়ো আন্দোলনে (১৯৪২) ছাত্রসমাজের অবদান লেখো।
ভূমিকা: ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল মূলত একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেয়।
অবদান:
১. আন্দোলনের সূচনা: বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্কে কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর ছাত্ররাই প্রথম সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং আন্দোলনের সূচনা করে।
২. প্রচার ও সংগঠন: ছাত্ররা গোপন ইস্তেহার ছাপিয়ে, লিফলেট বিলি করে এবং ‘কংগ্রেস রেডিও’র মতো গোপন বেতার কেন্দ্র চালিয়ে আন্দোলনের খবর ও নির্দেশ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়।
৩. ধর্মঘট ও বিক্ষোভ: ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বয়কট করে এবং দেশজুড়ে হরতাল, পিকেটিং ও বিক্ষোভ সংগঠিত করে।
৪. ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ: অনেক ছাত্র হিংসাত্মক পথ বেছে নেয়। তারা রেললাইন উপড়ে ফেলে, টেলিফোন-টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয় এবং থানা ও সরকারি দপ্তরে আগুন লাগিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা করে। ছাত্ররাই ছিল এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি।
১০. বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলনে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলনকে একটি সংগঠিত ও রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিলেন। তাঁকে নমঃশূদ্র জাগরণের প্রাণপুরুষ বলা হয়।
ভূমিকা:
১. শিক্ষাবিস্তার: তিনি ‘Education is the backbone of a nation’ – এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করতেন।
২. সামাজিক সংস্কার: তিনি নমঃশূদ্রদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা করেন।
৩. রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা: তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সরকারি চাকরি ও আইনসভায় নমঃশূদ্রদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানান এবং বহু ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন।
৪. সংগঠন: তিনি ‘মতুয়া মহাসঙ্ঘ’-কে একটি শক্তিশালী সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেন। তাঁর নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়।
১১. অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা কীরূপ ছিল?
ভূমিকা: ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন ছিল প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন, যেখানে নারীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে।
ভূমিকা:
১. বয়কট ও পিকেটিং: নারীরা বিদেশি বস্ত্র ও মদের দোকানের সামনে পিকেটিং-এ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। কলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী, বোন ঊর্মিলা দেবী এবং ভাগ্নি সুনীতি দেবী এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন।
২. স্বদেশি দ্রব্যের প্রচার: নারীরা চরকায় সুতো কেটে খদ্দরের পোশাক তৈরি ও ব্যবহারে উৎসাহিত হয়। তারা তিলক স্বরাজ তহবিলে নিজেদের গয়না ও অর্থ দান করে।
৩. সংগঠন: এই সময়ে নারীরা নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করে, যা তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে।
৪. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নারীরাই এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। যদিও এই অংশগ্রহণ মূলত শহরকেন্দ্রিক ছিল, তবুও এটি ছিল নারী জাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।
১২. টীকা লেখো: অনুশীলন সমিতি।
ভূমিকা: অনুশীলন সমিতি ছিল বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার সর্বপ্রধান সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন।
প্রতিষ্ঠা: ১৯০২ সালে কলকাতায় প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সতীশচন্দ্র বসু ও ব্যারিস্টার পি. মিত্র ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এর মূল মন্ত্র ছিল ‘অনুশীলন দ্বারা তত্ত্বলাভ’।
শাখা: এর দুটি প্রধান শাখা ছিল – ঢাকা অনুশীলন সমিতি (নেতা: পুলিনবিহারী দাস) এবং কলকাতা অনুশীলন সমিতি (নেতা: যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ ঘোষ)। ঢাকা শাখাই ছিল বেশি সক্রিয়।
কর্মসূচি: এর কর্মসূচি ছিল দ্বিবিধ – (১) বাহ্যিক কর্মসূচি: লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরচর্চা ও যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগানো। (২) অভ্যন্তরীণ বা গুপ্ত কর্মসূচি: বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ এবং অত্যাচারী ব্রিটিশ ಅಧಿಕಾರಿদের হত্যা করে ত্রাস সৃষ্টি করা।
উপসংহার: অনুশীলন সমিতি বাংলার যুবসমাজকে বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত রচনা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
১৩. আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং তার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করো।
ভূমিকা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের ধৃত সৈন্যদের বিরুদ্ধে দিল্লির লালকেল্লায় এক প্রকাশ্য সামরিক আদালতে বিচার শুরু করে।
বিচার: প্রথম পর্যায়ে তিনজন বিশিষ্ট সেনাপতি – প্রেম কুমার সেহগল (হিন্দু), গুরুবক্স সিং ধিলন (শিখ) এবং শাহনওয়াজ খান (মুসলিম)-এর বিচার শুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হয়।
প্রতিক্রিয়া: এই বিচারের বিরুদ্ধে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে।
১. রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া: কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল বিচারের বিরোধিতা করে। ভুলাভাই দেশাই, জওহরলাল নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রুর মতো নেতারা অভিযুক্তদের সমর্থনে আইনজীবি হিসেবে দাঁড়ান।
২. গণ-আন্দোলন: দেশজুড়ে ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ’ ধ্বনি ওঠে। ছাত্র, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ বিচারের বিরুদ্ধে সভা, মিছিল, ধর্মঘট পালন করে। কলকাতায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।
ফলাফল: গণ-আন্দোলনের চাপে সামরিক আদালত অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দিলেও, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সেই দণ্ড মকুব করতে বাধ্য হন। এটি ছিল ভারতীয় জনগণের এক বিরাট নৈতিক জয়।
১৪. টীকা লেখো: যতীন দাস।
ভূমিকা: যতীন দাস ছিলেন বাংলার একজন অমর বিপ্লবী এবং শহিদ।
বিপ্লবী জীবন: তিনি প্রথমে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং পরে ভগত সিং-এর ‘হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন’-এর সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি বোমা তৈরিতে পারদর্শী ছিলেন।
অনশন ও আত্মত্যাগ: ১৯২৯ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে রাজনৈতিক বন্দিদের মর্যাদা এবং উন্নততর সুযোগ-সুবিধার দাবিতে তিনি ও ভগত সিং-এর মতো অন্যান্য বিপ্লবীরা অনশন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার দাবি না মানায় তিনি অনশন চালিয়ে যান এবং একটানা ৬৩ দিন অনশনের পর ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
গুরুত্ব: তাঁর এই আত্মত্যাগ সারা ভারতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হলে এক বিরাট শোকমিছিল বের হয়। যতীন দাসের আত্মত্যাগ ভারতের যুবসমাজকে বিপ্লবী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।
১৫. টীকা লেখো: যুগান্তর দল।
ভূমিকা: যুগান্তর ছিল বাংলার একটি প্রথম সারির সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন। এটি কলকাতা অনুশীলন সমিতির অভ্যন্তরীণ একটি গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব: ১৯০৬ সালে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই), অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রমুখের উদ্যোগে এই দলটি গড়ে ওঠে। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন এর প্রধান অনুপ্রেরণা। ‘যুগান্তর’ নামে তাদের একটি মুখপত্রও ছিল।
কার্যকলাপ: এই দলের প্রধান কার্যকলাপ ছিল বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহ এবং গুপ্তহত্যা। তাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা (মুজফ্ফরপুর ষড়যন্ত্র মামলা)। এছাড়া তারা ডাকাতির মাধ্যমে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করত।
আলিপুর বোমা মামলা: ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সহ এই দলের বহু নেতা গ্রেপ্তার হলে দলটি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে এটি পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
১৬. জাতীয়তাবাদের বিকাশে ছাত্র আন্দোলনের অবদান কী ছিল?
ভূমিকা: ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্ররা ছিল আন্দোলনের অগ্রদূত এবং নতুন ভাবধারার বাহক।
অবদান:
১. চেতনার প্রসার: ছাত্ররা সভা-সমিতি, পত্রিকা প্রকাশ এবং বিতর্কের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিত।
২. আন্দোলনের চালিকাশক্তি: বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছাত্ররাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। তারা ধর্মঘট, পিকেটিং ও মিছিল সংগঠিত করত।
৩. নতুন নেতৃত্বের জন্ম: ছাত্র আন্দোলন থেকেই জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতাদের আবির্ভাব ঘটে।
৪. আত্মত্যাগ: যতীন দাস, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ ছাত্ররা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে চরম আত্মত্যাগের নিদর্শন স্থাপন করেন, যা সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করে।
১৭. ডঃ বি. আর. আম্বেদকর কেন দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি করেছিলেন?
ভূমিকা: ডঃ আম্বেদকর ছিলেন দলিত সমাজের অবিসংবাদী নেতা। তিনি মনে করতেন, দলিতদের মুক্তি শুধুমাত্র সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য।
দাবির কারণ:
১. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: তিনি মনে করতেন, দলিতরা হিন্দু সমাজের অংশ নয়, বরং এক শোষিত ও পৃথক জনগোষ্ঠী। বর্ণহিন্দুদের দ্বারা তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যাচারিত হয়েছে।
২. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: আম্বেদকরের মতে, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীতে বর্ণহিন্দুদের ভোটে দলিত প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে, সেই প্রতিনিধিরা বর্ণহিন্দুদের প্রতি অনুগত থাকবে, দলিতদের স্বার্থ দেখবে না।
৩. আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা: পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে দলিতরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে। এর ফলে তাদের রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারবে।
৪. প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব: তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীই আইনসভায় দলিতদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারে।
১৮. স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী হিসাবে মাতঙ্গিনী হাজরার অবদান আলোচনা করো।
ভূমিকা: মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তি শহিদ। ৭৩ বছর বয়সে তাঁর আত্মত্যাগ তাঁকে অমর করে রেখেছে।
অবদান:
১. গান্ধীবাদী আন্দোলন: তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সময় লবণ আইন অমান্য করে এবং চৌকিদারি কর বন্ধ আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন।
২. ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্ব: ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের তমলুকের প্রধান নেত্রী। তিনি ‘ভগিনী সেনা’ নামে নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে সাহায্য করেন।
৩. আত্মত্যাগ: ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি তমলুক থানা দখলের জন্য একটি বিশাল মিছিলের পুরোভাগে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে যান। ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার পরও তিনি ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যান এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুবরণ আজও ভারতের মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়।
১৯. ‘নৌবিদ্রোহ’ (১৯৪৬) এর কারণ ও তাৎপর্য লেখো।
কারণ:
১. ব্রিটিশ ও ভারতীয় নৌ-সেনাদের মধ্যে বেতন, পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে গুরুতর বৈষম্য।
২. ভারতীয় নাবিকদের প্রতি ব্রিটিশ অফিসারদের বর্ণবিদ্বেষী আচরণ ও অসম্মান।
৩. আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের বিচার এবং দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাবিকদের প্রভাবিত করে।
৪. নিম্নমানের খাবার সরবরাহ ছিল এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ।
তাৎপর্য:
১. এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ – সেনাবাহিনীও আর অনুগত নেই।
২. এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেয় যে, তাদের ভারত ছেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।
৩. এই বিদ্রোহ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করে।
৪. এই বিদ্রোহ ব্রিটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।
২০. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের অবদান আলোচনা করো।
ভূমিকা: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রসমাজের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। তারা ছিল আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী এবং নতুন ভাবধারার ধারক।
অবদান:
১. স্বদেশি আন্দোলন: ছাত্ররা বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দ্রব্য বয়কট করে এবং পিকেটিং-এ নেতৃত্ব দেয়। ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’ গঠন করে তারা সরকারি দমননীতির মোকাবিলা করে।
২. অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন: এই দুটি আন্দোলনে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে অংশ নেয় এবং জাতীয়তাবাদী প্রচার চালায়।
৩. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন: বহু ছাত্র ‘অনুশীলন সমিতি’, ‘যুগান্তর’, ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ প্রভৃতি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল। বিনয়-বাদল-দীনেশ, যতীন দাস প্রমুখ ছিলেন ছাত্র।
৪. ভারত ছাড়ো আন্দোলন: এই আন্দোলনে ছাত্ররা ছিল প্রধান চালিকাশক্তি। তারা ধর্মঘট, বিক্ষোভ, প্রচার এবং গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ছাত্ররাই ছিল এই নেতা-বিহীন আন্দোলনের প্রকৃত নেতা।
২১. টীকা লেখো: কার্লাইল সার্কুলার।
ভূমিকা: ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তিত করে তোলে। ছাত্রদের আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য সরকার এক দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে।
সার্কুলার: তৎকালীন বাংলার চিফ সেক্রেটারি আর. ডব্লিউ. কার্লাইলের নামানুসারে ১৯০৫ সালের ১০ই অক্টোবর একটি নির্দেশিকা বা সার্কুলার জারি করা হয়।
নির্দেশাবলী: এই সার্কুলারে বলা হয়, (১) কোনো ছাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে বা পিকেটিং-এ অংশ নিলে তাকে স্কুল-কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হবে। (২) যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেবে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে।
প্রতিক্রিয়া: এই দমনমূলক সার্কুলারের প্রতিবাদে ছাত্ররা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নেতৃত্বে ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’ গঠিত হয় এবং সারা বাংলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
২২. বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনে ‘দীপালি সংঘ’-এর অবদান কী ছিল?
ভূমিকা: ‘দীপালি সংঘ’ ছিল বাংলার নারী বিপ্লবীদের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ১৯২৩ সালে ঢাকায় বিপ্লবী লীলা নাগের (রায়) নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
অবদান:
১. নারী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন: এই সংঘের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা এবং তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে দীপালি স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।
২. বিপ্লবী তৈরি: এর গোপন উদ্দেশ্য ছিল নারীদের সশস্ত্র বিপ্লবী কাজের জন্য প্রস্তুত করা। এখানে সদস্যরা লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ নিত।
৩. বিপ্লবীদের আশ্রয়দান: দীপালি সংঘের সদস্যরা পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করতেন।
৪. নেতৃত্ব সৃষ্টি: এই সংঘের মাধ্যমেই বহু নারী বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করে। বীণা দাসের মতো বিপ্লবীরাও এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এটি ছিল নারী বিপ্লবীদের আঁতুড়ঘর।
২৩. টীকা লেখো: অলিন্দ যুদ্ধ।
ভূমিকা: ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ (B.V.) দলের তিন বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের দ্বারা সংঘটিত রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান ‘অলিন্দ যুদ্ধ’ নামে ইতিহাসে পরিচিত।
ঘটনা: এই তিন বিপ্লবী ইউরোপীয় পোশাকে ছদ্মবেশে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এর (বর্তমান মহাকরণ) দোতলায় ওঠেন এবং কারা বিভাগের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে তাঁর নিজের অফিসে গুলি করে হত্যা করেন।
যুদ্ধ: সিম্পসনকে হত্যার পর তারা ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিতে দিতে রাইটার্সের অলিন্দে (বারান্দা) ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হন।
পরিণতি: ধরা পড়ার আগে বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন, বিনয় বসু নিজের রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে হাসপাতালে মারা যান এবং দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হওয়ার পর বিচারে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করেন। এই দুঃসাহসিক অভিযান ব্রিটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
২৪. দলিত আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
ভূমিকা: ভারতের বর্ণহিন্দু সমাজব্যবস্থায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষিত ও নিপীড়িত তথাকথিত অস্পৃশ্য বা দলিত সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাকেই দলিত আন্দোলন বলা হয়।
বৈশিষ্ট্য:
১. আত্মমর্যাদার লড়াই: এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক অসাম্য ও অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটিয়ে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।
২. রাজনৈতিক অধিকারের দাবি: ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিতরা আইনসভা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের মতো রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানায়।
৩. ধর্মীয় সংস্কার: ভাইকম সত্যাগ্রহ বা কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহের মতো আন্দোলনের মাধ্যমে তারা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দাবি করে।
৪. বিকল্প ধর্ম গ্রহণ: হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ডঃ আম্বেদকর বহু অনুগামীসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এটি ছিল দলিত আন্দোলনের এক চরম পদক্ষেপ।
২৫. আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা: ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রসমাজ এক অগ্রণী ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল।
ভূমিকা:
১. বয়কট ও পিকেটিং: ছাত্ররা সরকারি স্কুল-কলেজ বয়কট করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বিদেশি পণ্যের দোকানের সামনে পিকেটিং সংগঠিত করে।
২. আইন অমান্য: ছাত্ররা লবণ আইন অমান্য করে, নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পত্রিকা বিলি করে এবং সভা-মিছিলে অংশ নিয়ে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে।
৩. সংগঠন: এই সময়ে ‘অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন’ (ABSA)-এর মতো ছাত্র সংগঠনগুলি আন্দোলনকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৪. সশস্ত্র আন্দোলন: আইন অমান্য আন্দোলনের আবহে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়, তার বেশিরভাগ সদস্যই ছিল ছাত্র ও যুবক। কলকাতায় বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানও এই সময়ের ঘটনা। ছাত্রদের এই বহুমুখী কার্যকলাপ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৮ (১০টি)
১. বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের অংশগ্রহণের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। তারা শুধুমাত্র পুরুষের সহযোগী হিসেবে নয়, সক্রিয় যোদ্ধা ও নেত্রী হিসেবে জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। তাদের অংশগ্রহণের চরিত্র ছিল বহুমুখী, যা অহিংস সত্যাগ্রহ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
অহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণ:
১. স্বদেশি আন্দোলন: এই আন্দোলনে নারীরা প্রথম ঘরের বাইরে এসে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়। তারা বিদেশি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার এবং রাখিবন্ধন উৎসবে যোগ দেয়। সরলাদেবী চৌধুরানী ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রতিষ্ঠা করে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেন।
২. গান্ধীবাদী আন্দোলন: অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো – এই তিনটি আন্দোলনেই নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। বাসন্তী দেবী, সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, মাতঙ্গিনী হাজরা, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ নারীরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তারা সভা-সমিতি, পিকেটিং, লবণ তৈরি, কর-বন্ধ আন্দোলন এবং গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মত্যাগ এই পর্বের এক চরম নিদর্শন।
সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ:
বাংলার নারীরা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেও এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে।
১. সংগঠন: লীলা নাগের ‘দীপালি সংঘ’ বা কল্যাণী দাসের ‘ছাত্রী সংঘ’ নারী বিপ্লবীদের আঁতুড়ঘর হিসেবে কাজ করত। এখানে তারা শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষিত হত।
২. প্রত্যক্ষ সংগ্রাম: প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দেন, কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে সূর্য সেনের সহযোগী ছিলেন এবং বীণা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার গভর্নরকে গুলি করেন। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেন।
বৈশিষ্ট্য:
১. বিশ শতকের নারী আন্দোলন শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির নারীরাও এতে অংশ নিয়েছিল।
২. নারীরা শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী ছিল না, তারা নেত্রী হিসেবেও উঠে এসেছিল।
৩. তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সামাজিক কুসংস্কার ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধেও এক শক্তিশালী আঘাত হেনেছিল।
উপসংহার: নারী সমাজের এই বহুমুখী ও নিঃস্বার্থ অবদান ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অসম্পূর্ণ থাকত। তাদের ত্যাগ ও সংগ্রাম শুধুমাত্র দেশের মুক্তিকেই ত্বরান্বিত করেনি, নারীমুক্তির পথকেও প্রশস্ত করেছিল।
২. বিশ শতকে ভারতে দলিত আন্দোলন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলিতদের আন্দোলন ছিল আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ছিলেন এই আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা, যিনি দলিতদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন।
দলিত আন্দোলনের কারণ ও প্রকৃতি:
ভারতের বর্ণহিন্দু সমাজব্যবস্থায় দলিতরা ছিল অস্পৃশ্য এবং যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের মন্দিরে প্রবেশ, জলাশয় ব্যবহার বা শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না। এই অমানবিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধেই দলিত আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল ত্রিবিধ – সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়।
ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকা:
১. সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা: আম্বেদকর মনে করতেন, শিক্ষার মাধ্যমেই দলিতদের উন্নতি সম্ভব। তিনি ‘বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা’ প্রতিষ্ঠা করে দলিতদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হন। তিনি ১৯২৭ সালে ‘মহাদ সত্যাগ্রহ’-এর মাধ্যমে দলিতদের সাধারণ জলাশয় ব্যবহারের অধিকার এবং ১৯৩০ সালে ‘কালারাম মন্দির সত্যাগ্রহ’-এর মাধ্যমে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেন।
২. রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা: আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া দলিতদের মুক্তি সম্ভব নয়। তিনি দলিতদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য:
(ক) দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানান।
(খ) গান্ধীজির সঙ্গে বিতর্কের পর ‘পুনা চুক্তি’ (১৯৩২) স্বাক্ষর করেন, যার মাধ্যমে আইনসভায় দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।
(গ) তিনি ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি’ এবং পরে ‘অল ইন্ডিয়া শিডিউলড কাস্টস ফেডারেশন’ নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন।
৩. সাংবিধানিক ভূমিকা: তিনি স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই সংবিধানে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং দলিতদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়।
৪. ধর্মীয় প্রতিবাদ: হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি জীবনের শেষ দিকে হাজার হাজার অনুগামীসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, যা ছিল বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত প্রতিবাদ।
উপসংহার: ডঃ আম্বেদকর শুধুমাত্র একজন দলিত নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন যুগস্রষ্টা, যিনি ভারতের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন।
৩. বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের যে ধারা গড়ে ওঠে, তার মূল ভিত্তি ছিল ছাত্র ও যুবসমাজ। স্বদেশি আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন বহু ছাত্রকে অহিংসার পথ ছেড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়।
বিপ্লবী সংগঠন ও ছাত্রসমাজ:
বাংলার প্রধান বিপ্লবী সংগঠন, যেমন – ‘অনুশীলন সমিতি’, ‘যুগান্তর দল’, ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ (B.V.), ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’ (IRA) প্রভৃতির সদস্য ও কর্মীর অধিকাংশই ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র। এই সংগঠনগুলি ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তুলত।
উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপ:
১. গুপ্তহত্যা: ছাত্র বিপ্লবীরা বহু অত্যাচারী ব্রিটিশ官僚 ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের হত্যা করে ব্রিটিশ প্রশাসনে ত্রাস সৃষ্টি করে। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা (প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু), সিম্পসন হত্যা (বিনয়-বাদল-দীনেশ), স্টিভেন্স হত্যা (শান্তি-সুনীতি) প্রভৃতি ঘটনায় ছাত্ররাই ছিল protagonista।
২. অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা তৈরি: বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ নিত। যতীন দাস, উল্লাসকর দত্তের মতো ছাত্ররা বোমা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।
৩. সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা: মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ছিল একটি সংগঠিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা, যার প্রায় সকল সদস্যই ছিল ছাত্র ও যুবক।
৪. আত্মত্যাগ: বহু ছাত্র বিপ্লবী দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছে। ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি, যতীন দাসের ৬৩ দিনের অনশনে মৃত্যু, বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ যুদ্ধ – এই সমস্ত ঘটনাই ছাত্রসমাজের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের চরম নিদর্শন।
উপসংহার: বাংলার ছাত্রসমাজ নিজেদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নিগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়েই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গৌরবান্বিত হয়েছে।
৪. টীকা লেখো: চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
ভূমিকা: ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’ (IRA)-র সদস্যরা চট্টগ্রামে যে দুঃসাহসিক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়, তা ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’ নামে খ্যাত। এটি ছিল ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা।
পরিকল্পনা: সূর্য সেনের পরিকল্পনা ছিল, একই সময়ে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার ও সহায়ক বাহিনীর অস্ত্রাগার দখল করা, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ধ্বংস করে চট্টগ্রামকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করা।
ঘটনাপ্রবাহ: পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, রাত দশটায় গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা পুলিশ অস্ত্রাগার ও সহায়ক বাহিনীর অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। তারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সূর্য সেনকে সামরিক অভিবাদন জানায় এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু ভুলবশত তারা কার্তুজের ভান্ডার খুঁজে না পাওয়ায় সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র অকেজো হয়ে পড়ে।
জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ: এই ঘটনার পর ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রামের কাছে জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদের এক অসম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ১২ জন বিপ্লবী শহিদ হন এবং বহু ব্রিটিশ সৈন্য হতাহত হয়।
গুরুত্ব: চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।
১. এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভারতীয় বিপ্লবীরা শুধুমাত্র গুপ্তহত্যা নয়, একটি সংগঠিত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোরও ক্ষমতা রাখে।
২. এই ঘটনা সমগ্র বাংলার যুবসমাজকে, বিশেষ করে নারীদের, বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে।
৩. এটি ব্রিটিশ সরকারের দম্ভে এক जोरदार আঘাত হানে এবং তাদের শক্তির অজেয় ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দেয়।
৫. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে নারী ও ছাত্র সমাজের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন। এই আন্দোলনকে গণমুখী করে তোলার পিছনে নারী ও ছাত্র সমাজের অবদান ছিল অপরিসীম।
নারী সমাজের ভূমিকা:
এই আন্দোলনেই প্রথম ভারতীয় নারীরা সীমিত আকারে হলেও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়।
১. বয়কট ও স্বদেশি গ্রহণ: নারীরা বাড়িতে বিদেশি জিনিসপত্র, বিশেষ করে কাঁচের চুড়ি, বিলাতি লবণ-চিনি ইত্যাদি বর্জন করে। তারা চরকায় সুতো কেটে স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহারে উৎসাহ জোগায়।
২. সংগঠন ও উৎসব: সরলাদেবী চৌধুরানী ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘বীরাষ্টমী ব্রত’ চালু করে নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।
৩. রাখিবন্ধন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নারীরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখি পরিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেয়।
৪. অরন্ধন পালন: বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন (১৬ই অক্টোবর) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে নারীরা বাড়িতে অরন্ধন পালন করে প্রতিবাদ জানায়।
ছাত্র সমাজের ভূমিকা:
ছাত্ররা ছিল এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি।
১. বয়কট ও পিকেটিং: ছাত্ররা সরকারি স্কুল-কলেজ বয়কট করে এবং বিদেশি দ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেটিং করে বয়কট আন্দোলনকে সফল করে তোলে।
২. জাতীয় শিক্ষার প্রসার: ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’ গঠন করে এবং জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নেয়।
৩. প্রচার ও সংগঠন: ছাত্ররা সভা-সমিতি, মিছিল এবং ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনির মাধ্যমে সারা বাংলায় স্বদেশি ভাবধারা ছড়িয়ে দেয়। ‘ডন সোসাইটি’, ‘অনুশীলন সমিতি’র মতো সংগঠনগুলির মাধ্যমে তারা সংগঠিত হয়।
উপসংহার: নারী ও ছাত্র সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নতুন শক্তি ও মাত্রা প্রদান করেছিল, যা ব্রিটিশ সরকারকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য করে।
৬. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা লেখো। এই প্রসঙ্গে বীণা দাস ও কল্পনা দত্তের অবদান আলোচনা করো।
ভূমিকা: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, বিশেষত বাংলায়, নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তারা গুপ্ত সমিতির সদস্য হওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নিজেদের সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। লীলা নাগের ‘দীপালি সংঘ’ বা কল্যাণী দাসের ‘ছাত্রী সংঘ’ ছিল নারী বিপ্লবীদের প্রস্তুতির ক্ষেত্র। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরীর মতো বহু নারী বিপ্লবী এই আন্দোলনে অমর হয়ে আছেন।
বীণা দাসের অবদান:
বীণা দাস ছিলেন বাংলার একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী। তিনি ‘ছাত্রী সংঘ’ ও ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় মঞ্চে উঠে বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো। যদিও তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হয় এবং তিনি ধরা পড়েন, কিন্তু তাঁর এই কাজ ব্রিটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দেয় এবং প্রমাণ করে যে, নারীরাও চরম সাহসিকতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে পারে। এই ঘটনায় তাঁর ৯ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।
কল্পনা দত্তের অবদান:
কল্পনা দত্ত ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেনের ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’র অন্যতম প্রধান সদস্যা। তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপ ছিল বহুমুখী:
১. তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।
২. অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর তিনি মাস্টারদার সঙ্গে আত্মগোপন করেন এবং পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান।
৩. ১৯৩৩ সালে গৈরালা গ্রামে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি সূর্য সেনের সঙ্গে ধরা পড়েন।
৪. বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কল্পনা দত্তের ধৈর্য, সাহস ও বিপ্লবী নিষ্ঠা তাঁকে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে।
উপসংহার: বীণা দাস ও কল্পনা দত্তের মতো নারীদের আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য ও গৌরবোজ্জ্বল।
৭. দলিত অধিকার প্রতিষ্ঠায় জ্যোতিবা ফুলে এবং নারায়ণ গুরুর ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: ডঃ আম্বেদকরের আগে থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলে এবং কেরালার নারায়ণ গুরুর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।
জ্যোতিবা ফুলের ভূমিকা:
জ্যোতিবা ফুলে ছিলেন উনিশ শতকে মহারাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক এবং দলিত আন্দোলনের পথিকৃৎ।
১. অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ বিরোধিতা: তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।
২. দলিত ও নারী শিক্ষা: তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া দলিতদের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি ১৮৪৮ সালে পুনায় ভারতের প্রথম নিম্নবর্গের বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শিক্ষা বিস্তারের কাজ চালিয়ে যান।
৩. সত্যশোধক সমাজ: ১৮৭৩ সালে তিনি ‘সত্যশোধক সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পুরোহিতদের ছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করা এবং নিম্নবর্গের মানুষকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করা।
৪. রচনা: তিনি ‘গুলামগিরি’, ‘ব্রাহ্মণদের চাতুরী’ প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্র তুলে ধরেন।
নারায়ণ গুরুর ভূমিকা:
নারায়ণ গুরু ছিলেন দক্ষিণ ভারতের, বিশেষ করে কেরালার, একজন মহান সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারক। তিনি মূলত এজহাভা নামক এক অনুন্নত সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য কাজ করেন।
১. মন্দির প্রতিষ্ঠা: সেই সময়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নারায়ণ গুরু এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নিজেই ১৮৮৮ সালে আরুভিপ্পুরমে একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের গায়ে লেখেন – ‘জাতিভেদ ও ধর্মীয় বিদ্বেষহীন এক আদর্শ স্থান, যেখানে সকলে ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে বাস করবে’।
২. একেশ্বরবাদ প্রচার: তিনি ‘এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঈশ্বর’ (One Caste, One Religion, One God for man) – এই বাণী প্রচার করে জাতিভেদের অসারতা প্রমাণ করেন।
৩. ভাইকম সত্যাগ্রহে অনুপ্রেরণা: তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই পরবর্তীকালে কেরালায় বিখ্যাত ‘ভাইকম সত্যাগ্রহ’ শুরু হয়েছিল।
উপসংহার: জ্যোতিবা ফুলে এবং নারায়ণ গুরু তাদের কাজের মাধ্যমে দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে আত্মমর্যাদা ও চেতনার সঞ্চার করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে আম্বেদকরের আন্দোলনকে পথ দেখিয়েছিল।
৮. টীকা লেখো: রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান (অলিন্দ যুদ্ধ)।
ভূমিকা: ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ (B.V.) দলের তিন তরুণ বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের দ্বারা সংঘটিত দুঃসাহসিক রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে ‘অলিন্দ যুদ্ধ’ নামে খ্যাত।
প্রেক্ষাপট: ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ দলের নীতি ছিল দুঃসাহসিক অ্যাকশনের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হেনে তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। এই নীতির অঙ্গ হিসেবেই তারা কলকাতার ব্রিটিশ ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র – রাইটার্স বিল্ডিং (বর্তমান মহাকরণ) আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কারা বিভাগের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন. এস. সিম্পসন, যিনি জেলে বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন।
ঘটনাপ্রবাহ: ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর, দুপুরবেলা, বিনয়, বাদল ও দীনেশ ইউরোপীয় পোশাকে ছদ্মবেশে রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রবেশ করেন। তারা সরাসরি সিম্পসনের ঘরে ঢুকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। আকস্মিক এই আক্রমণে রাইটার্স বিল্ডিং-এ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
অলিন্দ যুদ্ধ ও আত্মত্যাগ: সিম্পসনকে হত্যার পর তারা পালানোর চেষ্টা না করে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিতে দিতে রাইটার্সের দীর্ঘ অলিন্দে (বারান্দা) অবস্থান নেন এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধই ‘অলিন্দ যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ না করে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। বাদল গুপ্ত ঘটনাস্থলেই পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন, বিনয় বসু নিজের রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে মারা যান। একমাত্র দীনেশ গুপ্ত বেঁচে যান এবং বিচারের পর ১৯৩১ সালে তাঁর ফাঁসি হয়।
গুরুত্ব: এই অভিযান ব্রিটিশ শাসকদের দম্ভে এক जोरदार আঘাত হানে। এটি প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুও বিপ্লবীদের আক্রমণের ঊর্ধ্বে নয়। এই তিন তরুণের আত্মত্যাগ বাংলার যুবসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। আজ কলকাতার ‘বি-বা-দী বাগ’ (বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) তাদের স্মৃতি বহন করছে।
৯. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো।
ভূমিকা: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রসমাজের অবদান ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল ও গৌরবময়। তারা ছিল আন্দোলনের অগ্রণী বাহিনী, নতুন ভাবধারার ধারক এবং অসীম সাহসের প্রতীক। বিশ শতকের প্রায় প্রতিটি বড় আন্দোলনেই ছাত্ররা সক্রিয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রদের অবদান:
১. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-১১): এই আন্দোলনেই প্রথম ছাত্ররা সংগঠিতভাবে রাজনীতিতে অংশ নেয়। তারা বিদেশি স্কুল-কলেজ ও দ্রব্য বয়কট, পিকেটিং এবং স্বদেশি দ্রব্যের প্রচারে নেতৃত্ব দেয়। ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক ‘কার্লাইল সার্কুলার’-এর বিরুদ্ধে তারা ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’ গঠন করে প্রতিবাদের এক নতুন নজির সৃষ্টি করে।
২. অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২০-৩৪): গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার ছাত্র সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা খদ্দর প্রচার, তিলক স্বরাজ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারাবরণ করে।
৩. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন: স্বদেশি আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বাংলার বহু ছাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। ‘অনুশীলন সমিতি’, ‘যুগান্তর’, ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স’ প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সিংহভাগ সদস্যই ছিল ছাত্র। বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রফুল্ল চাকী, দীনেশ মজুমদার, যতীন দাসের মতো অসংখ্য ছাত্র বিপ্লবী দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।
৪. ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২): এই নেতা-বিহীন আন্দোলনে ছাত্ররাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। কংগ্রেসের নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর ছাত্ররা ধর্মঘট, বিক্ষোভ, প্রচার এবং গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনকে প্রায় অচল করে দেয়।
৫. শেষ পর্বের আন্দোলন (১৯৪৫-৪৬): আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের মুক্তির দাবিতে এবং রশিদ আলির কারাদণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্ররা কলকাতায় যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে, তা ব্রিটিশ শাসনের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়।
উপসংহার: ছাত্রসমাজ তাদের মেধা, শ্রম, সাহস এবং জীবন দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ছাড়া মুক্তি সংগ্রাম গণ-আন্দোলনের রূপ পেত না।
১০. বিশ শতকের ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (দলিত) ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: বিশ শতকে ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি আরও একটি ধারা সক্রিয় ছিল, তা হল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দলিতদের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তাদের আন্দোলন ছিল দ্বিমুখী – একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যদিকে داخلی বর্ণহিন্দু সমাজের শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে।
আন্দোলনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য:
দলিত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সাম্য, রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। তারা মনে করত, শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেই তাদের মুক্তি আসবে না, তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই কারণে তাদের আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল জটিল।
বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা:
১. প্রাথমিক পর্ব (বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন): হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলায় নমঃশূদ্ররা সংগঠিত হয়। তারা শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। রাজনৈতিকভাবে তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করত এবং অনেক সময় কংগ্রেসের বিরোধিতা করত।
২. গান্ধীবাদী পর্ব ও অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন: গান্ধীজি প্রথম জাতীয় স্তরে অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটিকে কংগ্রেসের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দলিতদের ‘হরিজন’ আখ্যা দেন এবং ‘হরিজন সেবক সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নেতৃত্বে ভাইকম সত্যাগ্রহের মতো আন্দোলন দলিতদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
৩. আম্বেদকরের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন: ডঃ বি. আর. আম্বেদকর দলিত আন্দোলনকে এক নতুন রাজনৈতিক ও সংগ্রামী মাত্রা দেন। তিনি শুধুমাত্র সামাজিক সংস্কার নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ওপর জোর দেন।
(ক) তিনি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি তুলে দলিতদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয়ের চেষ্টা করেন।
(খ) ‘পুনা চুক্তি’র মাধ্যমে তিনি আইনসভায় দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করেন।
(গ) তিনি রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দলিতদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।
উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে অবস্থান:
দলিত নেতারা প্রায়শই কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনকে ‘বর্ণহিন্দুদের আন্দোলন’ বলে মনে করতেন। তারা আশঙ্কা করতেন, ব্রিটিশদের বিতাড়নের পর বর্ণহিন্দুদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দলিতদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। তাই তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে দর কষাকষি করে নিজেদের অধিকার আগে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে অনেক সময় তারা উপনিবেশ-বিরোধী মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছেন।
উপসংহার: প্রান্তিক বা দলিত জনগোষ্ঠীর আন্দোলন ছিল এক জটিল ও বহুমুখী সংগ্রাম। তারা একদিকে যেমন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করত, তেমনই নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিকেও সমান গুরুত্ব দিত। তাদের এই দ্বিমুখী সংগ্রাম ভারতের সমাজ ও রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।
Class 10 History বিশ শতকের ভারতে নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা Question Answer MCQ,অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : class 10 বিশ শতকের ভারতে নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন প্রশ্ন উত্তর