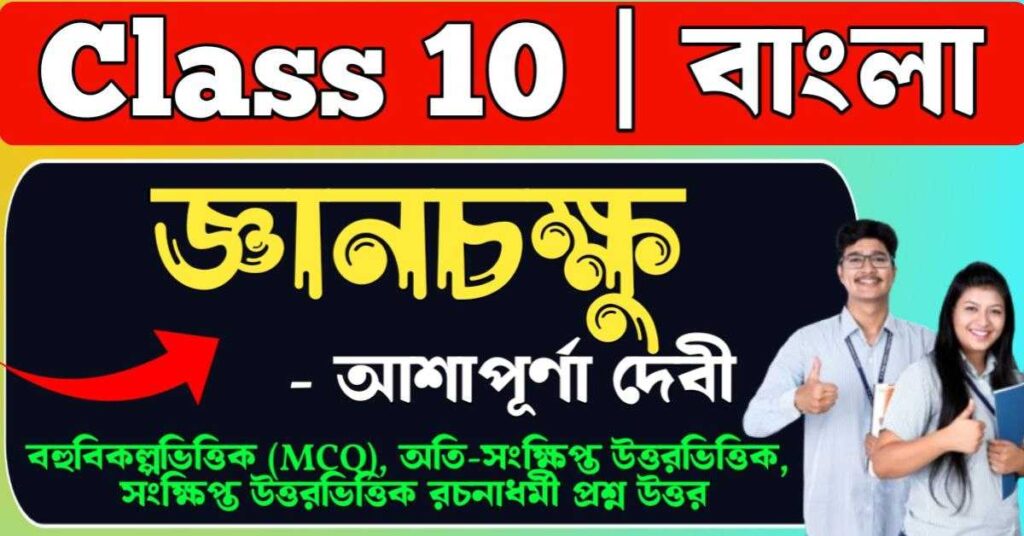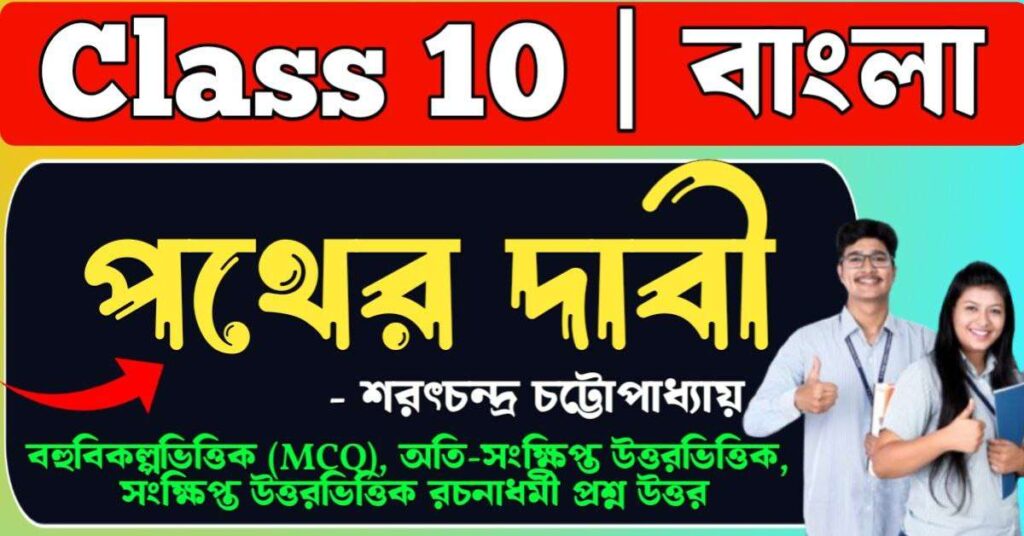বহুরূপী গল্পের প্রশ্ন উত্তর
বহুরূপী (সুবোধ ঘোষ)
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৫০টি)
১. ‘বহুরূপী’ গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম কী?
২. হরিদা কী সেজে চকের বাসস্ট্যান্ডে গিয়েছিলেন?
৩. জগদীশবাবু বিরাগীকে কত টাকা দিতে চেয়েছিলেন?
৪. “সেটাই তো হরিদার জীবনের পেশা।” – হরিদার পেশা কী ছিল?
৫. হরিদার আড্ডায় কতজন বন্ধু ছিল?
৬. “তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।” – কথাটি কে বলেছে?
৭. হরিদা পুলিশ সেজে কোথায় দাঁড়িয়েছিলেন?
৮. বাইজির ছদ্মবেশে হরিদার রোজগার কত হয়েছিল?
৯. জগদীশবাবু কেমন স্বভাবের মানুষ ছিলেন?
১০. হরিদার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বকশিশ কী ছিল?
১১. “আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়?” – এই প্রশ্ন কে কাকে করেছিল?
১২. হরিদার ছোট্ট ঘরটি শহরের কোন জায়গায় অবস্থিত?
১৩. বাসের ড্রাইভারের নাম কী ছিল?
১৪. “অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।” – হরিদার কোন ভুল?
১৫. হিমালয়ের গুহায় বাস করা সন্ন্যাসী কতদিন জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন?
১৬. হরিদা সপ্তাহে কতদিন বহুরূপী সেজে বাইরে যান?
১৭. বিরাগী সেজে হরিদার ঝোলায় কী ছিল?
১৮. হরিদার কোন সাজ দেখে জগদীশবাবু মোহিত হয়েছিলেন?
১৯. “সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস।” – দুর্লভ জিনিসটি কী?
২০. হরিদার উনোনের হাঁড়িতে কীসের ভাতের গন্ধ পাওয়া যেত?
২১. “পরমাত্মা যার কাছে একটা নোংরা কৌতুক” – কার কাছে?
২২. হরিদা কী কাজ করতে রাজি ছিলেন না?
২৩. “ছি ছি, আপনি অমন কথা বলবেন না।” – বক্তা কে?
২৪. “খুব হয়েছে হরিদা, এইবার সরে পড়ো।” – কথাগুলো কারা বলেছিল?
২৫. সন্ন্যাসী সারাবছর কী খেতেন?
২৬. হরিদা কোন সাজে কোনো বকশিশ নেননি?
২৭. হরিদার আড্ডার ঘরটি কেমন ছিল?
২৮. হরিদা কী দেখে চমকে উঠেছিলেন?
২৯. বিরাগীর মতে, পরমাত্মা কার কাছে কৌতুক?
৩০. ‘বহুরূপী’ গল্পটি কোন গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
৩১. “কি অদ্ভুত কথা বলেন হরিদা!” – বক্তা কে?
৩২. চকের বাসস্ট্যান্ডে পাগল সেজে হরিদা কী করছিলেন?
৩৩. হরিদার বন্ধুরা তার ঘরে কী নিয়ে আড্ডা দিত?
৩৪. “নইলে আমি শান্তি পাব না” – বক্তা কে?
৩৫. হরিদার রোজগারের ধরন কেমন ছিল?
৩৬. বিরাগীর গায়ে কী ছিল?
৩৭. জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা সন্ন্যাসীর বয়স কত ছিল?
৩৮. ‘রিপু’ শব্দের অর্থ কী?
৩৯. “যাবার আগে আমি দুটো একটা জবর খেলা দেখিয়ে যাব।” – ‘জবর খেলা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৪০. হরিদা কোন সাজে এক টাকা বকশিশ পেয়েছিলেন?
৪১. “রাগ নামে কোনো রিপু আমার নেই” – বক্তা কে?
৪২. লিচুবাগানে হরিদা কতজন স্কুলছাত্রকে ধরেছিলেন?
৪৩. বিরাগী জগদীশবাবুকে কী দান করে গিয়েছিলেন?
৪৪. হরিদার কোন গল্পটা শুনে লেখকের বন্ধুরা হাসতে থাকে?
৪৫. হরিদা কার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিলেন?
৪৬. বিরাগী সেজে হরিদা যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেটি কার?
৪৭. হরিদা দারিদ্র্য সত্ত্বেও কোন জিনিসটি হারাননি?
৪৮. জগদীশবাবু বিরাগীর কাছে কী প্রার্থনা করেছিলেন?
৪৯. “এ তো বেশ মজার ব্যাপার” – কোন ব্যাপারটিকে মজার বলা হয়েছে?
৫০. হরিদার মনের ভেতর কীসের আগুন জ্বলছিল?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৪০টি)
১. ‘বহুরূপী’ গল্পটি কার লেখা?
উত্তর: ‘বহুরূপী’ গল্পটি সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের লেখা।
২. হরিদা কী কাজ করতে ভালোবাসতেন না?
উত্তর: হরিদা কোনো ধরাবাঁধা বা একঘেয়ে কাজ করতে ভালোবাসতেন না।
৩. জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা সন্ন্যাসী কোথা থেকে এসেছিলেন?
উত্তর: জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা সন্ন্যাসী হিমালয়ের গুহা থেকে এসেছিলেন।
৪. হরিদার দারিদ্র্যের চিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে?
উত্তর: হরিদার উনোনের হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে, ভাত ফোটে না—এই বর্ণনার মাধ্যমে তার দারিদ্র্য ফুটে উঠেছে।
৫. “সেটা আমার বহুরূপী জীবনের সবচেয়ে বড়ো বকশিশ।” – সবচেয়ে বড়ো বকশিশ কোনটি?
উত্তর: জগদীশবাবুর কাছ থেকে পাওয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ছিল হরিদার কাছে সবচেয়ে বড়ো বকশিশ।
৬. বিরাগী সেজে হরিদা জগদীশবাবুকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
উত্তর: বিরাগী সেজে হরিদা জগদীশবাবুকে ধন, জন, যৌবনকে বঞ্চনা বলে মনে করে ঈশ্বরের খোঁজ করতে বলেছিলেন।
৭. হরিদার বন্ধুরা কোথায় আড্ডা দিত?
উত্তর: হরিদার বন্ধুরা তার ছোট্ট ঘরে চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে আড্ডা দিত।
৮. হরিদা পুলিশ সেজে কত টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন?
উত্তর: হরিদা পুলিশ সেজে স্কুল মাস্টারের কাছ থেকে আট আনা ঘুষ নিয়েছিলেন।
৯. পাগল সেজে হরিদা কী করছিলেন?
উত্তর: পাগল সেজে হরিদা চকের বাসস্ট্যান্ডে আসা বাসগুলির দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছিলেন।
১০. বাসের ড্রাইভার কাশিনাথ হরিদার উপর কেন রেগে গিয়েছিল?
উত্তর: হরিদা পাগল সেজে বাসের দিকে ইট ছোঁড়ায় ড্রাইভার কাশিনাথ রেগে গিয়েছিল।
১১. “কি অদ্ভুত কথা বলেন হরিদা!” – কোন কথাকে অদ্ভুত বলা হয়েছে?
উত্তর: বিরাগী সেজে টাকা প্রত্যাখ্যান করাকে হরিদার বন্ধুরা অদ্ভুত কথা বলেছে।
১২. জগদীশবাবু বিরাগীর কাছে কী প্রার্থনা করেছিলেন?
উত্তর: জগদীশবাবু বিরাগীর কাছে তার বাড়িতে কয়েকদিন থাকার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।
১৩. সন্ন্যাসীর পায়ে কীসের খড়ম ছিল?
উত্তর: সন্ন্যাসীর পায়ে সোনার বোল লাগানো কাঠের খড়ম ছিল।
১৪. হরিদা কেন বিরাগী সেজেছিলেন?
উত্তর: হরিদা একটি জবর খেলা দেখানোর জন্য এবং জগদীশবাবুর কাছ থেকে মোটা টাকা রোজগারের আশায় বিরাগী সেজেছিলেন।
১৫. “আমি বিরাগী, রাগ নামে কোনো রিপু আমার নেই।” – কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: কথাটির অর্থ হলো, বক্তা একজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তাই ক্রোধ বা রাগ তার মধ্যে নেই।
১৬. হরিদার আড্ডার সঙ্গী কারা ছিল?
উত্তর: হরিদার আড্ডার সঙ্গী ছিল কথক, অনাদি ও ভবতোষ।
১৭. দয়ালবাবুর লিচুবাগান কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: দয়ালবাবুর লিচুবাগান শহরের মধ্যেই অবস্থিত।
১৮. হরিদা বিরাগী সেজে কী কী জিনিস সঙ্গে নিয়েছিলেন?
উত্তর: হরিদা বিরাগী সেজে একটি ঝোলা, ঝোলার মধ্যে একটি গীতা এবং একটি চিমটে সঙ্গে নিয়েছিলেন।
১৯. “তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।” – কিসে ঢং নষ্ট হয়ে যায়?
উত্তর: বিরাগীর ছদ্মবেশে টাকা-পয়সা স্পর্শ করলে বা গ্রহণ করলে তার অভিনয়ের ‘ঢং’ বা মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়।
২০. হরিদার কোন সাজ দেখে লেখকের বন্ধুরা ভয় পেয়েছিল?
উত্তর: হরিদার কাপালিক সাজ দেখে লেখকের বন্ধুরা ভয় পেয়েছিল।
২১. হরিদা সপ্তাহে ক’দিন বহুরূপী সাজতেন?
উত্তর: হরিদা সপ্তাহে বড়জোর একদিন বহুরূপী সাজতেন।
২২. হরিদার ছোট্ট ঘরটি কোথায় ছিল?
উত্তর: হরিদার ছোট্ট ঘরটি শহরের সবচেয়ে সরু একটি গলির ভিতরে ছিল।
২৩. “এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন হরিদা।” – একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করো।
উত্তর: একটি চমৎকার ঘটনা হলো হরিদার পাগল সেজে চকের বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের দিকে ইট ছোঁড়া।
২৪. ভবতোষ হরিদার কোন কাজকে ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন’ বলেছেন?
উত্তর: ভবতোষ হরিদার বিরাগী সেজে একশো এক টাকা ফিরিয়ে দেওয়াকে ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন’ কাজ বলেছেন।
২৫. জগদীশবাবু কেমন মানুষ?
উত্তর: জগদীশবাবু একাধারে কৃপণ কিন্তু অন্যদিকে অত্যন্ত ধার্মিক ও অতিথি সেবাপরায়ণ মানুষ।
২৬. হরিদা কীসের প্রতি উদাসীন ছিলেন?
উত্তর: হরিদা জাগতিক মোহ ও অর্থলোভের প্রতি উদাসীন ছিলেন।
২৭. বিরাগী জগদীশবাবুকে কার চেয়ে বড়ো বলেছেন?
উত্তর: বিরাগী জগদীশবাবুকে ভগবানের চেয়েও বড়ো বলতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি বিরাগীকে প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন।
২৮. হরিদার জীবনে কীসের অভাব ছিল?
উত্তর: হরিদার জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা বা অর্থের অভাব ছিল।
২৯. হরিদা কীসের জোরে দারিদ্র্যকে জয় করেছিলেন?
উত্তর: হরিদা তার শিল্পীসত্তা ও আত্মমর্যাদার জোরে দারিদ্র্যকে জয় করেছিলেন।
৩০. ‘বহুরূপী’ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ‘বহুরূপী’ শব্দের অর্থ হলো যিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন।
৩১. “ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা।” – কোনগুলোকে বঞ্চনা বলা হয়েছে?
উত্তর: ধন, জন এবং যৌবনকে বিরাগী ‘সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা’ বলেছেন।
৩২. বাইজির সাজে হরিদা কোথায় গিয়েছিলেন?
উত্তর: বাইজির সাজে হরিদা শহরের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু এলাকা দিয়ে নাচ ও গান গেয়ে গিয়েছিলেন।
৩৩. “খাঁটি মানুষ তো নই” – কে, কেন এ কথা বলেছেন?
উত্তর: হরিদা এ কথা বলেছেন কারণ তিনি খাঁটি সন্ন্যাসী নন, একজন বহুরূপী মাত্র।
৩৪. জগদীশবাবুর বাড়িতে কী উপলক্ষে সন্ন্যাসী এসেছিলেন?
উত্তর: জগদীশবাবুর বাড়িতে কোনো বিশেষ উপলক্ষে সন্ন্যাসী আসেননি, তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন।
৩৫. বিরাগীর চেহারার বর্ণনা দাও।
উত্তর: বিরাগীর মাথায় সাদা চুল, পরনে সাদা উত্তরীয় এবং তার ধবধবে সাদা শরীর থেকে যেন এক পবিত্র স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছিল।
৩৬. হরিদার রোজগারকে ‘অদৃষ্টের চালে চলত’ বলার কারণ কী?
উত্তর: কারণ হরিদার কোনো নির্দিষ্ট আয় ছিল না, যেদিন যেমন সাজতেন, ভাগ্যে যা জুটত তাতেই তার চলত।
৩৭. “গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা।” – কোন গল্প শুনে?
উত্তর: জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা এক উঁচু দরের সন্ন্যাসীর গল্প শুনে হরিদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।
৩৮. বিরাগী কী স্পর্শ করেন না?
উত্তর: বিরাগী সোনা বা টাকা-পয়সা জাতীয় কোনো বস্তু স্পর্শ করেন না।
৩৯. “একটা বিরাট কাণ্ড।” – কোন কাণ্ডকে বিরাট বলা হয়েছে?
উত্তর: জগদীশবাবুর বাড়িতে এক উঁচু দরের সন্ন্যাসীর আগমন এবং তার প্রতি জগদীশবাবুর ভক্তিকে বিরাট কাণ্ড বলা হয়েছে।
৪০. গল্পের শেষে হরিদা কী খাচ্ছিলেন?
উত্তর: গল্পের শেষে হরিদা তার উনোনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি ভাত রান্না করে খাচ্ছিলেন।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ৩ (২৫টি)
১. “অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।” – বক্তা কে? হরিদার কোন ভুলকে ক্ষমা না করার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: উক্তিটির বক্তা হলেন হরিদার বন্ধু অনাদি। হরিদা বিরাগীর ছদ্মবেশে জগদীশবাবুর কাছ থেকে একশো এক টাকার প্রণামী গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে দেওয়ার এই ঘটনাকেই অনাদি ‘ভুল’ বলে মনে করেছেন এবং তার মতে, অদৃষ্ট এই ভুলের জন্য হরিকে ক্ষমা করবে না।
২. “তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।” – কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য কী?
উত্তর: বিরাগী সেজে একশো এক টাকা প্রত্যাখ্যান করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হরিদা তার বন্ধুদের কাছে এই উক্তিটি করেছেন। উক্তিটির তাৎপর্য হলো, হরিদার কাছে তার শিল্প বা অভিনয়টাই আসল। তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করেন, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। বিরাগী হিসেবে টাকা স্পর্শ করলে তার চরিত্রের মহত্ত্ব ও নির্লোভ ভাবটি নষ্ট হয়ে যেত, যা একজন শিল্পীর কাছে তার শিল্পের অপমান।
৩. “আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়?” – কে, কাকে, কেন এই প্রশ্ন করেছিল?
উত্তর: বিরাগীর ছদ্মবেশে হরিদা এই প্রশ্নটি জগদীশবাবুকে করেছিলেন। জগদীশবাবু যখন বিরাগীকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তার বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, তখন বিরাগী এই প্রশ্নটি করেন। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, ভগবান মানুষকে যা দেন, মানুষ তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু জগদীশবাবু টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রলুব্ধ করতে চাইছেন, যা ভগবানের চেয়েও বড়ো হওয়ার স্পর্ধার সমান।
৪. হরিদার দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি কোন বিষয়ে আপসহীন ছিলেন?
উত্তর: হরিদা অত্যন্ত দরিদ্র জীবনযাপন করলেও দুটি বিষয়ে তিনি আপসহীন ছিলেন। প্রথমত, তিনি কোনো ধরাবাঁধা একঘেয়ে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে চাইতেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি তার শিল্পীসত্তা ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে কখনও আপস করতেন না। বিরাগী সেজে টাকা প্রত্যাখ্যান করা তার আত্মমর্যাদারই পরিচয় দেয়।
৫. “সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস।” – কোন জিনিসকে কেন দুর্লভ বলা হয়েছে?
উত্তর: জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা উঁচু দরের সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলোকে ‘ভয়ানক দুর্লভ জিনিস’ বলা হয়েছে। একে দুর্লভ বলার কারণ হলো, সেই সন্ন্যাসী কাউকে তার পা ছুঁতে দিতেন না। জগদীশবাবু অনেক কৌশল করে তার পায়ের ধুলো সংগ্রহ করেছিলেন। এমন একজন মহাত্মার আশীর্বাদ বা স্পর্শ পাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে সত্যিই দুর্লভ।
৬. চকের বাসস্ট্যান্ডে হরিদার কার্যকলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
উত্তর: হরিদা একবার উন্মাদ পাগলের ছদ্মবেশে চকের বাসস্ট্যান্ডে গিয়েছিলেন। তার চেহারা, মুখভঙ্গি এবং পোশাক ছিল একেবারে নিখুঁত পাগলের মতো। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে একটি থালা হাতে নিয়ে পথচারীদের দিকে এবং বাসগুলির দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছিলেন। তার এই ভয়ংকর রূপ দেখে বাসের ড্রাইভার কাশিনাথ ও যাত্রীরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং তাকে সরে যেতে বলেছিল।
৭. হরিদার পুলিশ সাজার ঘটনাটি লেখো।
উত্তর: হরিদা একবার পুলিশ সেজে দয়ালবাবুর লিচুবাগানের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এতটাই নিখুঁত সেজেছিলেন যে, বাগানের মালিকের স্কুলের মাস্টারমশাইও তাকে চিনতে পারেননি। তিনি চারজন স্কুলছাত্রকে লিচু চুরির অপরাধে ধরেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে ঘুষ হিসেবে আট আনা আদায় করেছিলেন। এই ঘটনায় তার অভিনয়ের দক্ষতা প্রকাশ পায়।
৮. জগদীশবাবুর চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর: জগদীশবাবু একজন ধনী এবং আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি সাধুসন্তদের সেবা করতে ভালোবাসেন, কিন্তু তার মধ্যে কৃপণতাও রয়েছে। তিনি একদিকে যেমন সন্ন্যাসীর জন্য সোনার খড়ম তৈরি করান, তেমনই বিরাগীকে টাকা দিয়ে বশ করতে চান। তার ভক্তির মধ্যে এক ধরনের অহংকার ও জাগতিক হিসাব-নিকাশ কাজ করে, যা খাঁটি ভক্তির পরিপন্থী।
৯. “নইলে আমি শান্তি পাব না।” – বক্তার अशाন্তির কারণ কী? তিনি কীভাবে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন?
উত্তর: উক্তিটির বক্তা জগদীশবাবু। তার অশান্তির কারণ হলো, বিরাগী তার কোনো সেবা বা দান গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। একজন সাধুকে সেবা করতে না পারার অতৃপ্তিই তার অশান্তির কারণ। তিনি বিরাগীকে একশো এক টাকা প্রণামী দিয়ে এবং তার পায়ের ধুলো নিয়ে তার সেবা করার ইচ্ছা পূরণ করে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন।
১০. হরিদার আড্ডার বর্ণনা দাও।
উত্তর: হরিদার আড্ডা বসত শহরের একটি সরু গলির ভিতরে তার ছোট্ট ঘরটিতে। সেখানে কথক এবং তার তিন বন্ধু—অনাদি ও ভবতোষ—প্রতি সন্ধ্যায় আসতেন। তারা চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে হরিদার জীবনের নানা গল্প, তার বহুরূপী সাজার অভিজ্ঞতা এবং শহরের নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই আড্ডাই ছিল তাদের বিনোদনের প্রধান উৎস।
১১. “কি চমৎকার সাজ সেজেছেন হরিদা!” – হরিদার কোন সাজের কথা বলা হয়েছে? সেই সাজের বর্ণনা দাও।
উত্তর: এখানে হরিদার বিরাগী সাজের কথা বলা হয়েছে। তার মাথায় ছিল ধবধবে সাদা চুল, পরনে একটি সাদা উত্তরীয়, এবং তার ফরসা শরীর থেকে যেন পবিত্র জ্যোতি বের হচ্ছিল। তার হাতে ছিল একটি ঝোলা, যার মধ্যে একটি গীতা ছিল এবং অন্য হাতে একটি চিমটে। তার শান্ত ও সৌম্য চেহারা দেখে তাকে সত্যিকারের সংসারত্যাগী বিরাগী বলেই মনে হচ্ছিল।
১২. “কিন্তু কাজটা কি ঠিক হবে?” – কোন কাজের কথা বলা হয়েছে? বক্তার মনে এই সংশয়ের কারণ কী?
উত্তর: এখানে বিরাগী সেজে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে টাকা রোজগার করার কাজের কথা বলা হয়েছে। বক্তা, অর্থাৎ হরিদার বন্ধুদের মনে এই সংশয় দেখা দিয়েছিল কারণ জগদীশবাবু অত্যন্ত ধার্মিক এবং চতুর মানুষ। তারা ভেবেছিল, হরিদার অভিনয় যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে জগদীশবাবু হয়তো রেগে গিয়ে পুলিশে দিতে পারেন। তাই এই কাজটির ঝুঁকি নিয়ে তাদের মনে সংশয় ছিল।
১৩. “গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা।” – কোন গল্প শুনে হরিদা গম্ভীর হয়েছিলেন? তার এই গাম্ভীর্যের কারণ কী?
উত্তর: জগদীশবাবুর বাড়িতে হিমালয় থেকে আসা এক উঁচু দরের সন্ন্যাসীর গল্প শুনে হরিদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তার গাম্ভীর্যের কারণ হলো, তিনি এই ঘটনাটির মধ্যে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, তিনিও এমন একটি ‘জবর খেলা’ দেখাবেন, যা দিয়ে তিনি তার শৈল্পিক দক্ষতা প্রমাণ করতে পারবেন এবং মোটা অঙ্কের টাকাও রোজগার করতে পারবেন।
১৪. বিরাগী ও জগদীশবাবুর কথোপকথন সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর: বিরাগী ও জগদীশবাবুর কথোপকথনে দুটি ভিন্ন আদর্শের সংঘাত ফুটে উঠেছে। জগদীশবাবু বিরাগীকে জাগতিক বস্তু (টাকা, আশ্রয়) দিয়ে সেবা করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, বিরাগী তাকে শিখিয়েছেন যে, সত্যিকারের শান্তি জাগতিক বস্তুতে নেই, তা আছে ঈশ্বরের পায়ে। বিরাগী জগদীশবাবুর ধনগর্বকে আঘাত করে বুঝিয়ে দেন যে, ঈশ্বরের চেয়ে বড়ো কেউ নয়।
১৫. “খাঁটি মানুষ তো নই, এই বহুরূপীর জীবনের থেকে বেশি কী আশা করতে পারি?” – বক্তার এই উক্তির তাৎপর্য কী?
উত্তর: উক্তিটি হরিদার। এর তাৎপর্য হলো, হরিদা তার নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। তিনি জানেন যে, তিনি সত্যিকারের সন্ন্যাসী নন, একজন অভিনেতা মাত্র। তাই একজন খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সম্মান বা স্থান তিনি আশা করতে পারেন না। এই উক্তির মাধ্যমে তার সততা ও শিল্পী হিসেবে নিজের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রকাশ পায়।
১৬. হরিদার রোজগারের বিবরণ দাও।
উত্তর: হরিদার রোজগার ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত। তিনি সপ্তাহে বড়জোর একদিন বহুরূপী সাজতেন। পাগল সেজে তিনি কিছু পয়সা ও একটি টাকা পেয়েছিলেন। বাইজির সাজে তার আট টাকা দশ আনা রোজগার হয়েছিল। পুলিশ সেজে তিনি আট আনা ঘুষ পেয়েছিলেন। এই সামান্য আয় দিয়েই তার দিন চলত, অনেক সময় তার উনোনে হাঁড়িও চড়ত না।
১৭. “এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন হরিদা।” – হরিদা কীভাবে চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করতেন?
উত্তর: হরিদা তার বহুরূপী সাজার মাধ্যমে শহরের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনতেন। কখনও পাগল সেজে, কখনও পুলিশ, কখনও বাউল বা কাপালিক সেজে তিনি সাধারণ মানুষকে চমকে দিতেন। তার নিখুঁত অভিনয় ও সাজপোশাক এতটাই বাস্তবসম্মত হতো যে, लोग তাকে চিনতে পারত না। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলোই শহরের জীবনে চমৎকারিত্ব যোগ করত।
১৮. “ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা।” – কোন জিনিসগুলিকে এবং কেন বঞ্চনা বলা হয়েছে?
উত্তর: বিরাগী রূপী হরিদা ধন, জন এবং যৌবনকে ‘সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা’ বলেছেন। এগুলিকে বঞ্চনা বলার কারণ হলো, এই জাগতিক জিনিসগুলি মানুষকে মোহে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ঈশ্বরকে খোঁজা থেকে বিরত রাখে। এগুলি আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর হলেও আসলে মানুষকে প্রতারিত করে, তাই এগুলি বঞ্চনা।
১৯. “আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাব।” – ‘জবর খেলা’টি কী ছিল? তার পরিণতি কী হয়েছিল?
উত্তর: ‘জবর খেলা’টি ছিল হরিদার বিরাগী সেজে জগদীশবাবুর বাড়িতে যাওয়া। তিনি এতটাই নিখুঁতভাবে অভিনয় করেছিলেন যে, জগদীশবাবু তাকে সত্যিকারের সাধু ভেবে বসেন এবং তাকে একশো এক টাকা প্রণামী দিতে চান। কিন্তু হরিদা সেই টাকা প্রত্যাখ্যান করে তার চরিত্রের প্রতি সৎ থাকেন। এর ফলে তিনি আর্থিক লাভ না করলেও, শিল্পী হিসেবে চরম আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।
২০. “এক এক সময় সত্যি দুটো দুটো করেข้าว ফুটিয়ে খান।” – এই উক্তির মাধ্যমে হরিদার চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
উত্তর: এই উক্তির মাধ্যমে হরিদার চরম দারিদ্র্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ‘দুটো দুটো করেข้าว’ বলতে ভাতের অভাবকে বোঝানো হয়েছে। তার আয় এতটাই কম ছিল যে, প্রতিদিন দু’বেলা পেট ভরে ভাত খাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হতো না। এই দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি তার শিল্প এবং আত্মসম্মানের সঙ্গে কোনো আপস করেননি, যা তার চরিত্রকে মহৎ করে তুলেছে।
২১. “পরমাত্মা যার কাছে একটা নোংরা কৌতুক।” – এই উক্তির আলোকে জগদীশবাবুর চরিত্র বিচার করো।
উত্তর: বিরাগীর এই উক্তিটি জগদীশবাবুর চরিত্রের ভণ্ডামি ও জাগতিক আসক্তিকে তুলে ধরে। জগদীশবাবু নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করলেও, তার ভক্তি প্রদর্শনের মধ্যে অহংকার ও স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তিনি টাকা দিয়ে সাধুর সেবা কিনতে চান। তার কাছে ঈশ্বর বা পরমাত্মা ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং অর্থ ও প্রতিপত্তি দেখানোর একটি মাধ্যম, যা এক ধরনের ‘নোংরা কৌতুক’-এর সমান।
২২. বিরাগীর সাজ ও আসল সন্ন্যাসীর সাজের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল?
উত্তর: বিরাগী রূপী হরিদার সাজে ছিল আড়ম্বরহীনতা ও পবিত্রতা। তার পরনে ছিল সাধারণ সাদা উত্তরীয়, যা তার নির্লোভ সত্তার প্রতীক। অন্যদিকে, জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা আসল সন্ন্যাসীর পায়ে ছিল সোনার বোল লাগানো খড়ম। এই খড়ম তার মহিমার প্রতীক হলেও, এটি জাগতিক ঐশ্বর্যের চিহ্নও বহন করে, যা বিরাগীর সাজে অনুপস্থিত ছিল।
২৩. “হরিদার জীবন এইরকম বহুরূপের খেলা দেখিয়েই একরকম চলে যাচ্ছে।” – ‘বহুরূপের খেলা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কীভাবে তার জীবন চলে?
উত্তর: ‘বহুরূপের খেলা’ বলতে হরিদার বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে মানুষকে চমকে দেওয়া এবং তার থেকে সামান্য কিছু রোজগার করাকে বোঝানো হয়েছে। এই খেলা তার কাছে শুধু পেশা নয়, এক ধরনের শিল্প। এই অনিশ্চিত আয় দিয়েই তার অভাব-অনটনের জীবন কোনোমতে চলে যায়। তবে আর্থিক কষ্টের চেয়েও শিল্পের আনন্দই তার কাছে বড়।
২৪. “একটা চাকরির দরকার।” – হরিদা কেন চাকরি করেননি?
উত্তর: হরিদার বন্ধুরা মনে করত তার একটা চাকরি করা উচিত। কিন্তু হরিদা চাকরি করেননি কারণ তার শিল্পীমন কোনো ধরাবাঁধা, একঘেয়ে কাজ পছন্দ করত না। তার মতে, ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়ম করে অফিসে যাওয়া-আসা তার স্বাধীন সত্তার পরিপন্থী। তিনি বহুরূপী সেজে যে শৈল্পিক আনন্দ ও স্বাধীনতা পেতেন, তা চাকরির মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।
২৫. ‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদার শিল্পীসত্তার পরিচয় দাও।
উত্তর: হরিদা একজন জাতশিল্পী। তার কাছে বহুরূপী সাজাটা শুধু রোজগারের উপায় নয়, এটি একটি শিল্প সাধনা। তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করেন, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যান। বিরাগী সেজে টাকা প্রত্যাখ্যান করা তার শিল্পীসত্তারই চরম প্রকাশ। তিনি অর্থের চেয়ে শিল্পের সম্মানকে বড় করে দেখেন এবং এই সততাই তাকে একজন প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।
ঘ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৫ (১০টি)
১. ‘বহুরূপী’ গল্পের নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে, তা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পের নামকরণ তার বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ‘বহুরূপী’ শব্দের অর্থ যিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। গল্পের প্রধান চরিত্র হরিদা এই কাজটিকেই তার পেশা ও শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
চরিত্রকেন্দ্রিকতা: গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হরিদার বিভিন্ন রূপ ধারণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি কখনও উন্মাদ পাগল, কখনও পুলিশ, কখনও বাইজি, আবার কখনও বাউল বা কাপালিক সেজে শহরের মানুষকে চমকে দেন। তার জীবন এই বহুরূপের খেলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তাই চরিত্রকেন্দ্রিক দিক থেকে নামকরণটি যথার্থ।
ভাবব্যঞ্জনা: ‘বহুরূপী’ শব্দটি এখানে শুধুমাত্র ছদ্মবেশ ধারণকে বোঝায় না, এটি একটি গভীরতর অর্থ বহন করে। হরিদা বিরাগী সেজে প্রমাণ করেন যে, তিনি শুধু বাইরের রূপ পরিবর্তন করেন না, চরিত্রের অন্তরাত্মাকেও ধারণ করেন। তিনি দেখান যে, একজন সত্যিকারের শিল্পী অর্থের লোভে তার শিল্পের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না।
উপসংহার: হরিদার জীবন ও শিল্পসাধনা ‘বহুরূপী’ শব্দের আক্ষরিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী—উভয় অর্থকেই সার্থক করে তুলেছে। গল্পের মূল সুর, বিষয়বস্তু এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র—সবকিছুই এই নামকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাই ‘বহুরূপী’ নামকরণটি সবদিক থেকেই সার্থক।
২. ‘বহুরূপী’ গল্প অবলম্বনে হরিদা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদা একজন ব্যতিক্রমী শিল্পী, যার জীবনযাপন ও আদর্শ আমাদের মুগ্ধ করে।
১. শিল্পীসত্তা: হরিদা একজন জাতশিল্পী। বহুরূপী সাজা তার কাছে কেবল জীবিকা নয়, শিল্পসাধনা। তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করেন, তার গভীরে প্রবেশ করেন। তার পাগল, পুলিশ বা বিরাগীর সাজ এতটাই নিখুঁত হয় যে, কেউ তাকে চিনতে পারে না।
২. নির্লোভ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন: হরিদা অত্যন্ত দরিদ্র হলেও লোভী নন। তার আত্মসম্মানবোধ প্রবল। বিরাগী সেজে জগদীশবাবুর দেওয়া একশো এক টাকা তিনি অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ টাকা নিলে তার চরিত্রের ‘ঢং’ বা শিল্পের মহত্ত্ব নষ্ট হয়ে যেত।
৩. স্বাধীনচেতা: হরিদা কোনো ধরাবাঁধা বা একঘেয়ে জীবনের শৃঙ্খল মানতে রাজি নন। তাই তিনি কোনো চাকরি করেননি। তার কাছে শিল্পের স্বাধীনতা ও আনন্দই মুখ্য।
৪. রসবোধ: দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যেও হরিদার রসবোধ অটুট। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠেন এবং জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করেন।
উপসংহার: হরিদা চরিত্রটি আসলে এক আদর্শ শিল্পীর প্রতিচ্ছবি, যিনি অর্থের চেয়ে শিল্পকে, জাগতিকতার চেয়ে আত্মসম্মানকে বড় করে দেখেন এবং এই আদর্শের জন্যই তিনি পাঠকের মনে স্থায়ী জায়গা করে নেন।
৩. “সেটাই তো হরিদার জীবনের পেশা। হরিদার জীবনের পেশার পরিচয় দাও। এই পেশার প্রতি তার মনোভাব কেমন ছিল?”
উত্তর:
পেশার পরিচয়: হরিদার জীবনের পেশা ছিল বহুরূপী সেজে মানুষের মনোরঞ্জন করে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করা। তিনি কোনো ধরাবাঁধা চাকরি বা ব্যবসা করতেন না। সপ্তাহে হয়তো একদিন তিনি কোনো বিশেষ চরিত্রে সেজে রাস্তায় বের হতেন। তার সাজার ঝুলিতে ছিল পাগল, পুলিশ, বাইজি, বাউল, কাপালিক, ফিরিঙ্গি সাহেব ইত্যাদি নানা চরিত্র। তার সাজ ও অভিনয় এতটাই নিখুঁত হতো যে, দর্শকরা চমকে যেত এবং খুশি হয়ে তাকে কিছু বকশিশ দিত। এই অনিশ্চিত আয় দিয়েই তার জীবন চলত।
পেশার প্রতি মনোভাব: হরিদার কাছে এই পেশা কেবল অর্থ উপার্জনের উপায় ছিল না, এটি ছিল তার শিল্প সাধনা। তিনি এই কাজটিকে ভালোবাসতেন এবং এর প্রতি তার গভীর নিষ্ঠা ও সততা ছিল।
১. শৈল্পিক আনন্দ: তিনি এই কাজের মধ্যে শৈল্পিক আনন্দ খুঁজে পেতেন। একঘেয়ে জীবনের পরিবর্তে নতুন নতুন চরিত্র ধারণ করা তাকে আনন্দ দিত।
২. চরিত্রের প্রতি সততা: তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করতেন, তার প্রতি সম্পূর্ণ সৎ থাকতেন। বিরাগী সেজে টাকা প্রত্যাখ্যান করার ঘটনা এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি মনে করতেন, টাকা নিলে তার চরিত্রের মহত্ত্ব ও শিল্পের সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে।
৩. আত্মসম্মান: এই পেশা তাকে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান দিয়েছে, যা কোনো সাধারণ চাকরিতে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি এই পেশা নিয়ে গর্বিত ছিলেন।
৪. “তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।” – বক্তা কে? কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
বক্তা ও প্রসঙ্গ: উক্তিটির বক্তা ‘বহুরূপী’ গল্পের প্রধান চরিত্র হরিদা। জগদীশবাবুর দেওয়া একশো এক টাকার প্রণামী কেন তিনি গ্রহণ করেননি, বন্ধুদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কথাটি বলেছিলেন। বিরাগী সেজে টাকা গ্রহণ করলে তার অভিনয়ের ‘ঢং’ বা মেজাজ নষ্ট হয়ে যেত বলে তিনি জানান।
তাৎপর্য বিশ্লেষণ: এই উক্তিটির মধ্যে হরিদার শিল্পীসত্তার মূল পরিচয় লুকিয়ে আছে।
১. শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা: ‘ঢং’ বলতে এখানে শুধুমাত্র অভিনয় বা ভান বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে চরিত্রের মেজাজ বা তার অন্তর্নিহিত সত্তাকে। হরিদা যখন বিরাগী সেজেছিলেন, তখন তিনি শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপ ধারণ করেননি, তিনি বিরাগীর নির্লোভ, নিরাসক্ত সত্তাকেও নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। টাকা গ্রহণ করলে সেই চরিত্রের প্রতি তিনি অসৎ হতেন।
২. অর্থের ঊর্ধ্বে শিল্প: এই উক্তির মাধ্যমে হরিদা প্রমাণ করেছেন যে, একজন সত্যিকারের শিল্পীর কাছে অর্থের চেয়ে শিল্পের মূল্য অনেক বেশি। একশো এক টাকার লোভ তার শৈল্পিক সততাকে টলাতে পারেনি।
৩. আত্মসম্মানবোধ: হরিদা জানতেন, তিনি একজন বহুরূপী, খাঁটি সাধু নন। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে তার যে সম্মান, তা তিনি বিসর্জন দিতে চাননি। টাকা নিলে তিনি জগদীশবাবুর কাছে একজন সাধারণ ভিখারি বা ভণ্ড হিসেবে প্রতিপন্ন হতেন, যা তার শিল্পী হিসেবে আত্মসম্মানে আঘাত করত।
সুতরাং, এই একটি মাত্র উক্তি হরিদার চরিত্রকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।
৫. “হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে।” – হরিদার জীবনের নাটকীয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদার জীবন সাধারণ মানুষের একঘেয়ে জীবনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার জীবন নানা ঘটনা ও চরিত্রে ভরপুর, যা তাকে এক নাটকীয় বৈচিত্র্য দান করেছে।
বৈচিত্র্যের পরিচয়:
১. বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ: হরিদার জীবন যেন একটি নাটকের মঞ্চ, যেখানে তিনি নিজেই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। তিনি কখনও উন্মাদ পাগল, যার কাণ্ড দেখে সবাই ভয় পায়; কখনও কঠোর পুলিশ, যিনি ঘুষ নিতেও ছাড়েন না; আবার কখনও বা নারীবেশী বাইজি, যার ঘুঙুরের শব্দে লোক জমে যায়। এই চরিত্রগুলি তার জীবনে প্রতিনিয়ত বৈচিত্র্য নিয়ে আসে।
২. দারিদ্র্য ও শিল্পের সহাবস্থান: তার জীবনে একদিকে রয়েছে চরম দারিদ্র্য, যেখানে অনেক সময় হাঁড়িতে ভাত চড়ে না। অন্যদিকে রয়েছে শিল্পের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও নিষ্ঠা। এই দুই বিপরীতধর্মী দিকের সহাবস্থান তার জীবনকে নাটকীয় করে তুলেছে।
৩. অপ্রত্যাশিত ঘটনা: হরিদার কার্যকলাপ সবসময়ই অপ্রত্যাশিত। কখন তিনি কী সাজবেন, তা কেউ জানে না। তার সবচেয়ে বড় নাটকীয় মুহূর্তটি হলো বিরাগী সেজে জগদীশবাবুর বাড়িতে যাওয়া এবং মোটা অঙ্কের টাকা অবলীলায় ফিরিয়ে দেওয়া। এই ঘটনা তার জীবনের সাধারণত্বকে ছাপিয়ে এক অসাধারণ নাটকীয়তা তৈরি করে।
উপসংহার: এইভাবেই, হরিদার জীবন ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে, নানা রূপ, রস এবং ঘটনার সমন্বয়ে এক নাটকীয় বৈচিত্র্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।
৬. জগদীশবাবুর বাড়িতে হরিদার বিরাগী সেজে যাওয়ার ঘটনাটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। এই ঘটনা থেকে হরিদার চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে ওঠে?
উত্তর:
ঘটনার বর্ণনা: জগদীশবাবুর বাড়িতে এক উঁচু দরের সন্ন্যাসীর গল্প শুনে হরিদা একটি ‘জবর খেলা’ দেখানোর পরিকল্পনা করেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ধবধবে সাদা চুল, সাদা উত্তরীয় এবং হাতে একটি চিমটে ও ঝোলা নিয়ে বিরাগী সেজে জগদীশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হন। তার শান্ত, সৌম্য ও পবিত্র রূপ দেখে জগদীশবাবু মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাকে সত্যিকারের সাধু ভেবে বসেন। জগদীশবাবু তাকে সেবা করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং একশো এক টাকার একটি থলি তার পায়ের কাছে রাখেন। কিন্তু বিরাগী রূপী হরিদা টাকা স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি বিরাগী, টাকা-পয়সা তার কাছে অর্থহীন। তিনি জগদীশবাবুর ধনগর্বকে আঘাত করে ঈশ্বর-সাধনার উপদেশ দেন এবং কেবল পায়ের ধুলো দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন।
চরিত্রের উন্মোচিত দিক: এই ঘটনা থেকে হরিদার চরিত্রের দুটি প্রধান দিক ফুটে ওঠে—
১. নিখুঁত অভিনয় দক্ষতা: হরিদা এতটাই নিখুঁতভাবে বিরাগীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যে, জগদীশবাবুর মতো চতুর মানুষও তাকে চিনতে পারেননি। এটি তার অসাধারণ শিল্পী প্রতিভার পরিচায়ক।
২. নির্লোভ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সত্তা: চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও একশো এক টাকার মতো বড় অঙ্কের লোভ তিনি সংবরণ করেন। তার কাছে শিল্পের সম্মান ও চরিত্রের প্রতি সততা ছিল অর্থের চেয়ে অনেক বড়। এই ঘটনা তার প্রবল আত্মসম্মানবোধ এবং নির্লোভ মানসিকতার চরম নিদর্শন।
৭. “সেটা আমার বহুরূপী জীবনের সবচেয়ে বড়ো বকশিশ।” – বক্তা কে? কোনটি তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বকশিশ এবং কেন?
উত্তর:
বক্তা: উক্তিটির বক্তা ‘বহুরূপী’ গল্পের প্রধান চরিত্র হরিদা।
সবচেয়ে বড়ো বকশিশ: বিরাগী সেজে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে তার কাছ থেকে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা তিনি আদায় করতে পেরেছিলেন, সেই অদৃশ্য প্রাপ্তিকেই হরিদা তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বকশিশ বলে মনে করেছেন। একশো এক টাকার থলিটি ছিল জাগতিক বকশিশ, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।
কারণ: এই প্রাপ্তিকে সবচেয়ে বড়ো বকশিশ বলার কারণ হলো—
১. শিল্পের সার্থকতা: একজন শিল্পীর কাছে তার শিল্পের সর্বোচ্চ পুরস্কার হলো দর্শকের স্বীকৃতি। হরিদা তার নিখুঁত অভিনয়ের দ্বারা জগদীশবাবুর মনে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পেরেছিলেন, তা তার শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।
২. আত্মতৃপ্তি: টাকা গ্রহণ করলে তিনি হয়তো সাময়িকভাবে আর্থিক কষ্ট দূর করতে পারতেন, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তার আত্মতৃপ্তি হতো না। টাকা প্রত্যাখ্যান করে এবং ভক্তি অর্জন করে তিনি যে মানসিক ও শৈল্পিক আনন্দ পেয়েছেন, তার মূল্য জাগতিক যেকোনো পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি।
৩. আদর্শের জয়: এই ঘটনাটি ছিল হরিদার নির্লোভ আদর্শের জয়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শিল্পকে বিক্রি করা যায় না। এই আদর্শগত জয়ই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।
৮. “আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়?” – উক্তিটির আলোকে বিরাগী ও জগদীশবাবুর মানসিকতার পার্থক্য তুলে ধরো।
উত্তর:
ভূমিকা: বিরাগী রূপী হরিদার এই একটি মাত্র প্রশ্ন জগদীশবাবুর ভণ্ড ধার্মিকতা এবং নিজের নির্লোভ আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট প্রাচীর তুলে ধরেছে।
জগদীশবাবুর মানসিকতা: জগদীশবাবু একজন ধনী ব্যক্তি এবং তার ধার্মিকতাও ধনগর্বের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি মনে করেন, অর্থ দিয়ে সবকিছু কেনা যায়, এমনকি সাধুসন্তদের সেবা ও আশীর্বাদও। তিনি যখন বিরাগীকে টাকা দিয়ে তার বাড়িতে রাখতে চান, তখন তিনি আসলে নিজের অর্থ ও প্রতিপত্তি দিয়েই তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। তার কাছে ঈশ্বর সাধনার চেয়েও জাগতিক প্রাপ্তি ও লোকদেখানো ভক্তিই বড়।
বিরাগীর মানসিকতা: অন্যদিকে, বিরাগী (হরিদা) আধ্যাত্মিকতা ও নির্লোভ আদর্শের প্রতীক। তার কাছে ঈশ্বরই পরম সত্য এবং জাগতিক ধনসম্পত্তি হলো ‘বঞ্চনা’। তিনি জগদীশবাবুর অর্থের প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করে বুঝিয়ে দেন যে, সত্যিকারের সাধনা কোনো জাগতিক বস্তুর বিনিময়ে হয় না। তার প্রশ্নটি সরাসরি জগদীশবাবুর অহংকারে আঘাত হানে এবং তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, কোনো মানুষই ভগবানের চেয়ে বড় হতে পারে না এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টাও এক ধরনের স্পর্ধা।
পার্থক্য: মূল পার্থক্য হলো, জগদীশবাবুর মানসিকতা ভোগবাদী ও জাগতিক, আর বিরাগীর মানসিকতা ত্যাগবাদী ও আধ্যাত্মিক।
৯. “গল্পটা শুনতে বেশ ভালো লাগছিল।” – কোন গল্পের কথা বলা হয়েছে? গল্পটা শুনে বক্তা ও তার বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?
উত্তর:
গল্পের পরিচয়: এখানে হরিদার মুখে তার বিরাগী সেজে জগদীশবাবুর বাড়িতে যাওয়ার অভিজ্ঞতার গল্পের কথা বলা হয়েছে। হরিদা বর্ণনা করছিলেন কীভাবে তিনি বিরাগী সেজেছিলেন, কীভাবে জগদীশবাবু তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কীভাবে তিনি টাকা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিশেষে কীভাবে তিনি জগদীশবাবুকে জ্ঞানের কথা শুনিয়ে চলে এসেছিলেন।
বক্তা ও বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া:
গল্পটি শুনতে কথক ও তার বন্ধুদের বেশ ভালো লাগছিল। তারা হরিদার অভিনয়ের দক্ষতায় মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। কিন্তু গল্পের শেষে যখন তারা জানতে পারল যে, হরিদা একশো এক টাকার মতো মোটা অঙ্কের বকশিশ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন তাদের মুগ্ধতা হতাশায় পরিণত হলো।
১. হতাশা ও বিস্ময়: তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, হরিদার মতো একজন দরিদ্র মানুষ এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারে। তারা এই কাজটিকে ‘কাণ্ডজ্ঞানহীন’ বলে মনে করে।
২. ভর্ৎসনা: বন্ধু অনাদি তো বলেই ফেলে যে, “অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।” তারা হরিদার আদর্শকে বুঝতে না পেরে তাকে বাস্তববাদী না হওয়ার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করে।
৩. ভিন্ন দৃষ্টিকোণ: এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হরিদার আদর্শবাদী, শৈল্পিক মানসিকতা এবং তার বন্ধুদের সাধারণ, বাস্তববাদী মানসিকতার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
১০. ‘বহুরূপী’ গল্পে একদিকে হরিদার দারিদ্র্য এবং অন্যদিকে তার শিল্পীসত্তার যে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় দেখানো হয়েছে, তা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: সুবোধ ঘোষের ‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদার চরিত্রটি দারিদ্র্য ও শিল্পীসত্তার এক অসামান্য দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।
দ্বন্দ্ব: হরিদার জীবনের মূল দ্বন্দ্বটি হলো তার পেটের ক্ষুধা এবং আত্মার ক্ষুধার মধ্যে।
১. পেটের ক্ষুধা: হরিদা অত্যন্ত দরিদ্র। তার উনোনে অনেক সময় ভাত চড়ে না। এই দারিদ্র্য তাকে অর্থ উপার্জনের জন্য বহুরূপী সাজতে বাধ্য করে। জগদীশবাবুর বাড়িতে যাওয়ার আগেও তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মোটা অঙ্কের টাকা রোজগার করা। এটি তার বাস্তব জীবনের তাড়না।
২. আত্মার ক্ষুধা: অন্যদিকে, তার মধ্যে বাস করে এক শিল্পী, যার ক্ষুধা হলো শিল্পের প্রতি সততা ও সম্মান রক্ষা করা। এই আত্মার ক্ষুধার কারণেই তিনি কোনো একঘেয়ে চাকরি করতে পারেন না। এই ক্ষুধার কারণেই তিনি বিরাগী সেজে টাকা স্পর্শ করতে পারেন না, কারণ তাতে তার শিল্পের অপমান হয়।
সমন্বয়: হরিদার মহত্ত্ব এখানেই যে, তিনি এই দুই বিপরীতমুখী চাহিদার মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন।
যখন পেটের ক্ষুধা বড় হয়ে ওঠে, তখন তিনি পাগল বা পুলিশ সেজে সামান্য রোজগার করেন। কিন্তু যখন আত্মার প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়, যেমন বিরাগীর চরিত্রে, তখন তিনি পেটের ক্ষুধাকে অনায়াসে জয় করেন। তিনি টাকা প্রত্যাখ্যান করে তার শিল্পীসত্তাকে বিজয়ী করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, দারিদ্র্য তার শরীরকে স্পর্শ করতে পারলেও, তার আত্মাকে কলুষিত করতে পারেনি।
উপসংহার: এভাবেই, দারিদ্র্যের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পীসত্তার আপসহীন আদর্শের মেলবন্ধন ঘটিয়ে হরিদা চরিত্রটি এক অনন্য সাধারণ উচ্চতায় পৌঁছেছে।
Class 10 bengali বহুরূপী question answer
বহুরূপী (সুবোধ ঘোষ) গল্পের প্রশ্ন উত্তর, MCQ, অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : Class 10 bengali বহুরূপী প্রশ্ন উত্তর