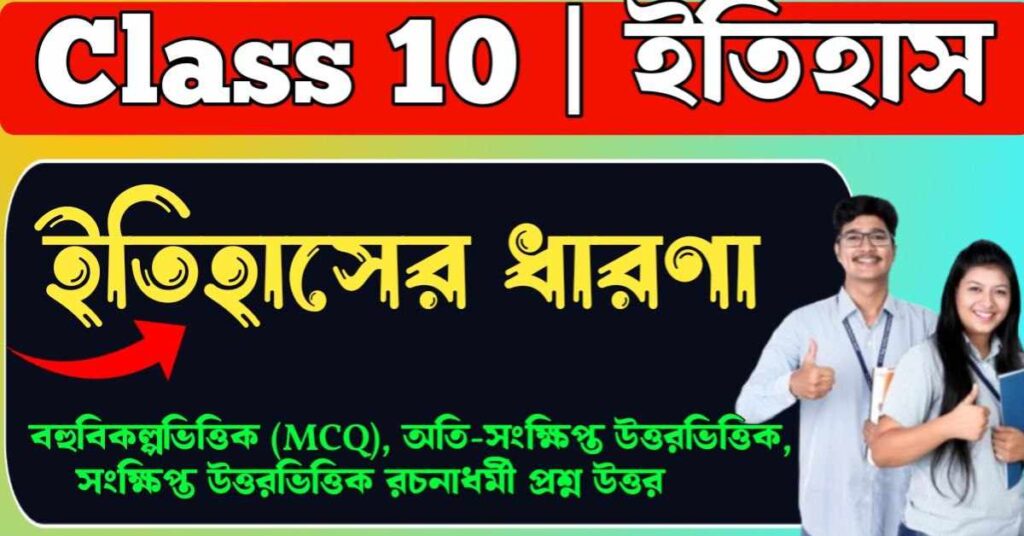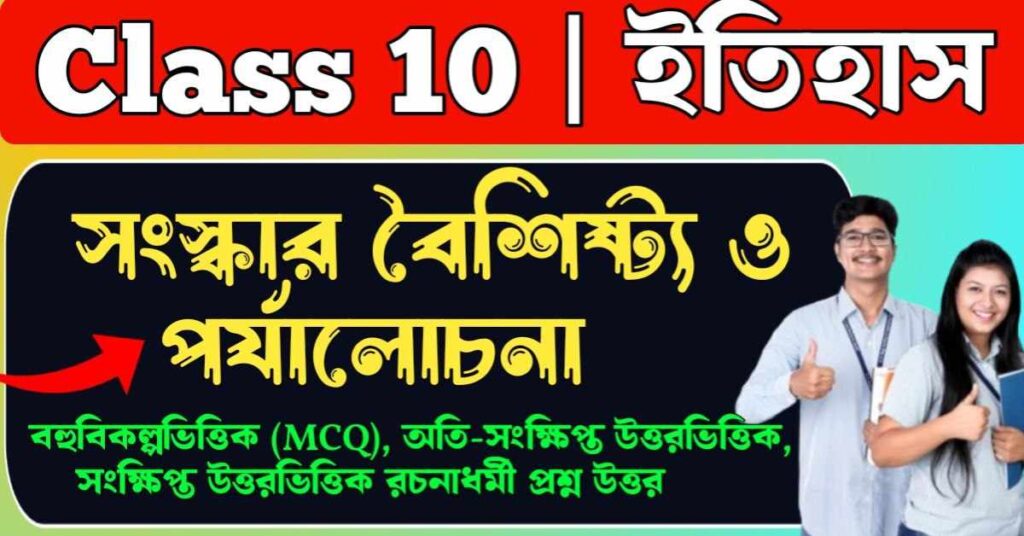বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. ‘বেঙ্গল গেজেট’ প্রকাশ করেন—
২. ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ (National Council of Education) গঠিত হয়—
৩. বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন—
৪. ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ (B.T.I.) প্রতিষ্ঠিত হয়—
৫. I.A.C.S. (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স) প্রতিষ্ঠা করেন—
৬. ভারতে হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং পদ্ধতির প্রবর্তন করেন—
৭. ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৮. শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়—
৯. ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল’-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—
১০. ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ নামে পরিচিত ছিলেন—
১১. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন—
১২. ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়—
১৩. ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে—
১৪. প্রথম সচিত্র বাংলা বই হল—
১৫. ‘গোলদিঘির গোলামখানা’ বলা হত—
১৬. ‘বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ’-এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন—
১৭. শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
১৮. ভারতের প্রথম বাঙালি মুদ্রণশিল্পী ও অক্ষর খোদাইকারী ছিলেন—
১৯. ‘ডন সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন—
২০. ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থটি হল একটি—
২১. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়—
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেন—
২৩. ‘City Book Society’ প্রতিষ্ঠা করেন—
২৪. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় কোন পত্রিকার প্রভাব ছিল?
২৫. ‘A Grammar of the Bengal Language’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
২৬. ‘ক্রেসকোগ্রাফ’ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন—
২৭. প্রথম বাঙালি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন—
২৮. শান্তিনিকেতনে ‘কলাভবন’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
২৯. যে বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি হলেন—
৩০. ‘যন্তর মন্তর’ কী?
৩১. ‘U. Ray & Sons’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৩২. ‘বেঙ্গল গেজেট’ প্রকাশিত হয়—
৩৩. ‘সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৩৪. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন—
৩৫. ‘শিশুশিক্ষা’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
৩৬. বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়—
৩৭. ‘A History of Hindu Chemistry’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
৩৮. ‘সন্দেশ’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন—
৩৯. ‘শ্রীনিকেতন’ ছিল—
৪০. কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৪১. ‘Anti-Circular Society’র সম্পাদক ছিলেন—
৪২. ‘লাইনোটাইপ’ তৈরি করেন—
৪৩. ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স’ প্রকাশ করেন—
৪৪. ‘তোতা কাহিনী’র লেখক হলেন—
৪৫. ছাপাখানার মুদ্রণের জন্য সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর তৈরি করেন—
৪৬. ‘জাতীয় শিক্ষা’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন—
৪৭. ‘ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেন—
৪৮. বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য ছিলেন—
৪৯. ‘বেঙ্গল গেজেট’ কী ধরনের পত্রিকা ছিল?
৫০. ‘বিদ্যাসাগর সাট’ বলা হয়—
৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত—
৫২. ‘ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৫৩. ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থটি রচনা করেন—
৫৪. ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৫৫. ‘যাঁদের অনুপ্রেরণায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়, তারা হলেন’—
৫৬. ‘রমন এফেক্ট’-এর আবিষ্কারক ছিলেন—
৫৭. ‘দিকদর্শন’ পত্রিকার প্রকাশক ছিল—
৫৮. ‘বিশ্বভারতী’ নামের ‘বিশ্ব’ কথাটির অর্থ হল—
৫৯. ‘বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ’-এর প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল—
৬০. ‘গুটেনবার্গ’ যে দেশের মানুষ ছিলেন—
৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান—
৬২. ঔপনিবেশিক শিক্ষা ছিল—
৬৩. পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন একজন—
৬৪. ‘শিক্ষা হেরফের’ প্রবন্ধটি কার লেখা?
৬৫. ‘ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস’-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন—
৬৬. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—
৬৭. ‘বেঙ্গল গেজেট’ পত্রিকাটি ছিল—
৬৮. ‘যত্র জীব তত্র শিব’— এই উক্তিটি কার?
৬৯. ‘শ্রীরামপুর কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়—
৭০. ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. ‘বেঙ্গল গেজেট’ কে প্রকাশ করেন?
উত্তর: জেমস অগাস্টাস হিকি।
২. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ।
৩. বিশ্বভারতী কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪. বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (BTI) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে।
৫. IACS-এর পুরো নাম কী?
উত্তর: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স।
৬. হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং কে প্রবর্তন করেন?
উত্তর: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
৭. বসু বিজ্ঞান মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।
৮. শান্তিনিকেতন আশ্রম কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯. বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
১০. ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ নামে কারা পরিচিত?
উত্তর: উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড।
১১. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: রাসবিহারী ঘোষ।
১২. ‘বর্ণপরিচয়’ কবে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে।
১৩. ভারতে প্রথম কোথায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: গোয়ায়।
১৪. প্রথম সচিত্র বাংলা বইয়ের নাম কী?
উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ‘অন্নদামঙ্গল’।
১৫. ‘গোলদিঘির গোলামখানা’ কাকে বলা হত?
উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে।
১৬. বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?
উত্তর: অরবিন্দ ঘোষ।
১৭. শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে।
১৮. প্রথম বাঙালি অক্ষর খোদাইকারী কে ছিলেন?
উত্তর: পঞ্চানন কর্মকার।
১৯. ডন সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২০. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেন?
উত্তর: জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে।
২২. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হত?
উত্তর: ‘সাধনা’ পত্রিকায়।
২৩. ‘A Grammar of the Bengal Language’ কে রচনা করেন?
উত্তর: ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।
২৪. ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রের কাজ কী?
উত্তর: উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপ করা।
২৫. প্রথম বাঙালি প্রকাশক কে ছিলেন?
উত্তর: গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য।
২৬. শান্তিনিকেতনে ‘কলাভবন’ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।
২৭. IACS-এ গবেষণা করে কে নোবেল পুরস্কার পান?
উত্তর: চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন (সি. ভি. রমন)।
২৮. ‘U. Ray & Sons’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
২৯. ‘সার্ভে অব ইন্ডিয়া’ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: ভারতের ভৌগোলিক সমীক্ষা ও মানচিত্র তৈরির জন্য।
৩০. ‘শিশুশিক্ষা’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
৩১. বিশ্বভারতী কবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়?
উত্তর: ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে।
৩২. ‘A History of Hindu Chemistry’ কার লেখা?
উত্তর: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের।
৩৩. ‘সন্দেশ’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
৩৪. শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: গ্রামের মানুষের सर्वांगीण উন্নতির জন্য কৃষিকাজ, সমবায় ও হস্তশিল্পের শিক্ষা দেওয়া।
৩৫. কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তর: স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
৩৬. ‘Anti-Circular Society’ কেন গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিতাড়িত ছাত্রদের বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য।
৩৭. ‘লাইনোটাইপ’ কী?
উত্তর: বাংলা হরফের একটি উন্নত ও দ্রুত মুদ্রণ পদ্ধতি, যা সুরেশচন্দ্র মজুমদার তৈরি করেন।
৩৮. ‘তোতাকাহিনী’ গল্পের মূল বক্তব্য কী?
উত্তর: ঔপনিবেশিক শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা ও যান্ত্রিকতাকে ব্যঙ্গ করা।
৩৯. বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক কাকে বলা হয়?
উত্তর: চার্লস উইলকিন্সকে।
৪০. ‘জাতীয় শিক্ষা’ কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?
উত্তর: প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
৪১. বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪২. ‘বেঙ্গল গেজেট’ কী ভাষায় প্রকাশিত হত?
উত্তর: ইংরেজি ভাষায়।
৪৩. ‘বিদ্যাসাগর সাট’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগকে একত্রে ‘বিদ্যাসাগর সাট’ বলা হয়।
৪৪. রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কী?
উত্তর: প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো।
৪৫. ‘অব্যক্ত’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: জগদীশচন্দ্র বসু।
৪৬. কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে।
৪৭. ‘রমন এফেক্ট’ কী?
উত্তর: আলোর বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার, যার জন্য সিভি রমন নোবেল পুরস্কার পান।
৪৮. ‘দিকদর্শন’ পত্রিকার প্রকাশক কারা?
উত্তর: শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন।
৪৯. ‘বিশ্বভারতী’ নামের অর্থ কী?
উত্তর: যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি নীড়ে পরিণত হয় (‘যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্’)।
৫০. ছাপা বইয়ের একটি সুবিধা লেখো।
উত্তর: ছাপা বইয়ের ফলে কম খরচে ও সহজে বহু মানুষের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।
৫১. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি সীমাবদ্ধতা লেখো।
উত্তর: এটি মূলত কারিগরি শিক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছিল, সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারেনি।
৫২. ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স’ কে প্রকাশ করত?
উত্তর: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স (IACS)।
৫৩. রবীন্দ্রনাথ কেন শান্তিনিকেতনে উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার কথা বলেন?
উত্তর: কারণ তিনি মনে করতেন, প্রকৃতির সান্নিধ্যেই শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ পরিপূর্ণভাবে সম্ভব।
৫৪. ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ত্রুটি লেখো।
উত্তর: এটি ছিল পুঁথি-সর্বস্ব ও মুখস্থ-নির্ভর এবং এর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো যোগ ছিল না।
৫৫. ‘যন্তর মন্তর’ কে নির্মাণ করেন?
উত্তর: জয়পুরের মহারাজা সোয়াই জয় সিংহ।
৫৬. ‘সমাচার দর্পণ’ কী ধরনের পত্রিকা ছিল?
উত্তর: এটি ছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
৫৭. ‘সারা ভারত কিষান সভা’ কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। (এই প্রশ্নটি পরবর্তী অধ্যায়ের)।
৫৮. কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের দুজন প্রধান দাতার নাম লেখো।
উত্তর: তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ।
৫৯. ‘বেঙ্গল গেজেট’ কেন বন্ধ হয়ে যায়?
উত্তর: গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশের জন্য।
৬০. ‘গুটেনবার্গ’ কেন বিখ্যাত?
উত্তর: ইউরোপে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসেবে।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের সম্পর্ক কী?
উত্তর: ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে কম সময়ে ও কম খরচে প্রচুর বই ছাপানো সম্ভব হয়। এর ফলে বই সহজলভ্য হয় এবং সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে যায়, যা শিক্ষাবিস্তারে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।
২. ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ নামে কারা পরিচিত? তারা কেন বিখ্যাত?
উত্তর: উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড—এই তিনজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি একত্রে ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ নামে পরিচিত। তাঁরা বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য বিখ্যাত।
৩. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উত্তর: স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫) ব্রিটিশ সরকার কার্লাইল সার্কুলার জারি করে ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করে। এর প্রতিবাদে বহু ছাত্র সরকারি স্কুল ত্যাগ করলে তাদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং জাতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন নয়, বরং প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—এই চারটি দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো।
৫. IACS বা ‘বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: ড. মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স’ (IACS) প্রতিষ্ঠা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই ভারতীয়দের উদ্যোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার সুযোগ তৈরি করা।
৬. ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস’ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কী?
উত্তর: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস’ ছিল ভারতের প্রথম ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা। এর গুরুত্ব হল, এটি স্বদেশী যুগে ভারতীয়দের আত্মনির্ভরশীল হতে এবং বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
৭. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মুদ্রণশিল্পে কেন বিখ্যাত?
উত্তর: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মুদ্রণশিল্পে বিখ্যাত কারণ তিনি ভারতে প্রথম ‘হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং’ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এর ফলে বইয়ে সাদা-কালো ছবি ছাপার মান অনেক উন্নত হয়। তিনি ‘U. Ray & Sons’ নামে একটি উন্নত মানের ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।
৮. ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার দুটি ত্রুটি লেখো।
উত্তর: (১) এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল পুঁথি-সর্বস্ব ও মুখস্থ-নির্ভর, এর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো যোগ ছিল না। (২) এর মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য কেরানি তৈরি করা, শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো নয়।
৯. ‘ডন সোসাইটি’ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, নৈতিকতা এবং দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে ‘ডন সোসাইটি’ (১৯০২) প্রতিষ্ঠা করেন।
১০. বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন ভারতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা) মৌলিক গবেষণার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ (১৯১৭) প্রতিষ্ঠা করেন।
১১. শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
উত্তর: (১) চার দেওয়ালের বাইরে প্রকৃতির কোলে উন্মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান করা হত। (২) পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত।
১২. ‘শ্রীনিকেতন’ কী? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: ‘শ্রীনিকেতন’ হল বিশ্বভারতীর একটি শাখা, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষের सर्वांगीण উন্নতির জন্য কৃষিকাজ, সমবায়, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন হস্তশিল্পের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা।
১৩. পঞ্চানন কর্মকারের অবদান কী?
উত্তর: পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন একজন দক্ষ বাঙালি অক্ষর খোদাইকারী। তিনি চার্লস উইলকিন্সের সহযোগী হিসেবে বাংলা মুদ্রণের জন্য প্রথম সচল ও সুন্দর বাংলা হরফ বা টাইপ তৈরি করেন, যা বাংলা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
১৪. ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ (BTI) কেন গড়ে উঠেছিল?
উত্তর: জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সদস্যরা যখন মূলত কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছিলেন, তখন তারকনাথ পালিতের মতো ব্যক্তিত্বরা কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ গড়ে তোলেন।
১৫. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ব্যর্থতার দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: (১) সরকারি চাকরির সুযোগ না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। (২) স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্যোগের প্রতি মানুষের উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তা কমে যায়।
১৬. গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য কেন স্মরণীয়?
উত্তর: গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি নিজস্ব উদ্যোগে ছাপাখানা (‘বেঙ্গল গেজেটি প্রেস’) প্রতিষ্ঠা করেন এবং বই প্রকাশ ও বিক্রি শুরু করেন। তিনি ‘বেঙ্গল গেজেট’ নামে একটি বাংলা সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন।
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিশ্বভারতী’ ভাবনার মূল কথা কী ছিল?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথের ‘বিশ্বভারতী’ ভাবনার মূল কথা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানো। তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ‘যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি নীড়ে পরিণত হবে’ (‘যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্’)।
১৮. কার্লাইল সার্কুলার কী?
উত্তর: স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি কার্লাইল একটি নির্দেশনামা বা সার্কুলার জারি করেন। এতে বলা হয়, যে সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেবে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে।
১৯. ‘গোলদিঘির গোলামখানা’— এই কথাটি কে, কেন বলেছিলেন?
উত্তর: জাতীয়তাবাদী নেতারা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘গোলদিঘির গোলামখানা’ বলে ব্যঙ্গ করতেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র ব্রিটিশদের অনুগত কেরানি বা ‘গোলাম’ তৈরি করে, স্বাধীন চিন্তার মানুষ তৈরি করে না।
২০. ‘রমন এফেক্ট’ কী? এর গুরুত্ব কী?
উত্তর: ‘রমন এফেক্ট’ হল আলোর বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন IACS-এ গবেষণা করার সময় এটি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব হল, এর জন্য তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান, যা ছিল এশিয়ার প্রথম বিজ্ঞানে নোবেল জয়।
২১. ছাপাখানার বিকাশে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র একজন লেখকই ছিলেন না, তিনি মুদ্রণ শিল্পেরও একজন সফল উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ‘সংস্কৃত প্রেস’ নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের বইগুলি সুন্দর ও নির্ভুলভাবে ছাপিয়ে সুলভে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।
২২. ‘শিক্ষা সমন্বয়’ বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: ‘শিক্ষা সমন্বয়’ বলতে রবীন্দ্রনাথ পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রকলা এবং প্রকৃতি পাঠের মেলবন্ধনকে বুঝিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, এই সমন্বয়ের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।
২৩. ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’র কাজ কী ছিল?
উত্তর: শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নেতৃত্বে গঠিত ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’র প্রধান কাজ ছিল কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য যে সমস্ত ছাত্রদের স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হত, তাদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
২৪. বাংলার মুদ্রণশিল্পে বটতলা প্রকাশনার গুরুত্ব কী?
উত্তর: উনিশ শতকে কলকাতার বটতলা অঞ্চল থেকে প্রচুর সস্তা দামের বই প্রকাশিত হত। এই বইগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলত ধর্মীয়, পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনী। এই প্রকাশনাগুলি উচ্চমানের না হলেও, এগুলি ছাপা বইকে বাংলার সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।
২৫. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দুটি বিভাগ কী কী ছিল?
উত্তর: জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দুটি প্রধান বিভাগ ছিল: (১) সাধারণ বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ (Arts and Science) এবং (২) কারিগরি বিভাগ (Technical)।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে বাংলায় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে ছাপাখানা ও ছাপা বইয়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ছাপাখানার আবিষ্কার শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাত থেকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।
সম্পর্ক:
১. বইয়ের সহজলভ্যতা: ছাপাখানার আগে বই ছিল মূলত হাতে লেখা পুঁথি, যা ছিল দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল। ছাপাখানার ফলে কম সময়ে ও কম খরচে প্রচুর বই ছাপানো সম্ভব হয়, ফলে বইয়ের দাম কমে এবং তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসে।
২. পাঠ্যপুস্তকের জোগান: স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি এবং বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রেস প্রচুর পাঠ্যপুস্তক ছেপে এই অভাব দূর করে।
৩. নারীশিক্ষা ও গণশিক্ষার প্রসার: ছাপা বইয়ের সহজলভ্যতার ফলেই নারীশিক্ষা ও গণশিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’-এর মতো বই ঘরে ঘরে বাংলা শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়।
উপসংহার: সুতরাং, বলা যায় যে ছাপা বই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল এবং বাংলার নবজাগরণের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল।
২. বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন একাধারে শিশুসাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী এবং মুদ্রণ প্রযুক্তিতে একজন যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর হাত ধরেই বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের আধুনিকীকরণ ঘটে।
ভূমিকা:
১. হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং: তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ভারতে প্রথম ‘হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং’ পদ্ধতির প্রবর্তন। এর মাধ্যমে বইয়ে সাদা-কালো ছবির বিভিন্ন শেড বা টোন ছাপানো সম্ভব হয়, যা ছবিকে অনেক বেশি জীবন্ত করে তোলে। তিনি এই বিষয়ে বিদেশে গবেষণা করেন এবং দেশে ফিরে এই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করেন।
২. ‘U. Ray & Sons’ প্রতিষ্ঠা: ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স’ নামে একটি উন্নত মানের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি শুধুমাত্র একটি ছাপাখানা ছিল না, এটি ছিল মুদ্রণ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার একটি কেন্দ্র।
৩. রঙিন ছবির মুদ্রণ: তিনি ডায়াফ্রাম সিস্টেম, স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করে রঙিন ছবি ছাপার কৌশলও আবিষ্কার করেন।
৪. উন্নত প্রকাশনা: তাঁর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকা এবং তাঁর নিজের লেখা বইগুলি (যেমন—’ছোটদের রামায়ণ’, ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’) ছিল মুদ্রণ সৌকর্যের उत्कृष्ट উদাহরণ। তিনিই প্রথম মুদ্রণকে একটি শিল্প পর্যায়ে উন্নীত করেন।
৩. বিজ্ঞান চর্চার বিকাশে ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’-এর অবদান কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ (Bose Institute) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার এক অগ্রণী প্রতিষ্ঠান।
অবদান:
১. মৌলিক গবেষণার কেন্দ্র: এই প্রতিষ্ঠানটি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, মাইক্রোবায়োলজি এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার এক আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রে পরিণত হয়।
২. উদ্ভিদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা: জগদীশচন্দ্র বসু এই প্রতিষ্ঠানেই তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে এবং তারা উত্তেজনায় সাড়া দেয়। তাঁর আবিষ্কৃত ‘ক্রেসকোগ্রাফ’ যন্ত্র এই গবেষণায় সাহায্য করেছিল।
৩. আন্তর্জাতিক খ্যাতি: বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বহু বিদেশি বিজ্ঞানী এখানে গবেষণা করতে আসেন। এটি ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।
৪. জাতীয়তাবাদের উন্মেষ: পরাধীন ভারতে সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে এমন একটি বিশ্বমানের গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল।
৪. কারিগরি শিক্ষার বিকাশে ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ (BTI)-এর ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দুটি ধারার মধ্যে একটি ছিল কারিগরি শিক্ষার ধারা। এই ধারার প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ (BTI)।
ভূমিকা:
১. প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট: জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধিকাংশ নেতা যখন কলা ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছিলেন, তখন তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার, রাসবিহারী ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বরা উপলব্ধি করেন যে, দেশের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা ১৯০৬ সালে BTI প্রতিষ্ঠা করেন।
২. পাঠ্যক্রম: এখানে মূলত ফলিত রসায়ন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয় পড়ানো হত।
৩. জাতীয় শিল্প গঠনে সাহায্য: BTI থেকে পাশ করা ছাত্ররা পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেশের শিল্পায়নে সাহায্য করে।
৪. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর: পরবর্তীকালে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট একত্রিত হয়ে ‘কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি’ (CET) নামে পরিচিত হয়, যা আজ ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে খ্যাত।
৫. টীকা লেখো: জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।
উত্তর:
ভূমিকা: স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক শিক্ষানীতির (যেমন—কার্লাইল সার্কুলার) প্রতিবাদে এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে এক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ (National Council of Education) গঠিত হয়।
উদ্দেশ্য:
১. সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে জাতীয় আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দান করা।
২. ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো।
৩. শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজলভ্য করে তোলা।
নেতৃত্ব: এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত প্রমুখ। রাসবিহারী ঘোষ ছিলেন এর প্রথম সভাপতি।
কার্যাবলী: জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে ‘বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল’ এবং ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ (BTI) প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সরকারি চাকরির অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক সংকটের কারণে এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।
৬. ছাপাখানার বিকাশে ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’র অবদান কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের শুরুতে বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের মিলিত প্রচেষ্টা ছিল অবিস্মরণীয়। তাঁরা একত্রে ‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ নামে পরিচিত।
অবদান:
১. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা: তাঁরা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন, যা ‘শ্রীরামপুর মিশন প্রেস’ নামে পরিচিত। এটি তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাপাখানা ছিল।
২. বাংলা মুদ্রণের উন্নতি: এই প্রেস থেকে উন্নত মানের বাংলা হরফ বা টাইপ তৈরি করা হয়। পঞ্চানন কর্মকারের মতো দক্ষ কারিগর এখানে কাজ করতেন।
৩. বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ: এই প্রেস থেকে বাংলা সহ প্রায় ৪০টি ভাষায় বাইবেল এবং অন্যান্য গ্রন্থ (যেমন—রামায়ণ, মহাভারত) অনুবাদ করে ছাপানো হয়।
৪. সংবাদপত্র প্রকাশ: তাঁরা বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা ‘দিকদর্শন’ (১৮১৮) এবং প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘সমাচার দর্পণ’ (১৮১৮) প্রকাশ করেন, যা বাংলা সাংবাদিকতার ভিত্তি স্থাপন করে।
৭. বিজ্ঞান গবেষণার প্রসারে IACS-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ড. মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স’ (IACS, ১৮৭৬) ছিল ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম ও প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান।
ভূমিকা:
১. মৌলিক গবেষণার সুযোগ: IACS প্রতিষ্ঠার আগে ভারতে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার কোনো সুযোগ ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বমানের গবেষণার পরিকাঠামো তৈরি করে।
২. জাতীয়তাবাদী উদ্যোগ: এটি ছিল সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে এবং ভারতীয়দের অর্থে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান, যা পরাধীন ভারতে জাতীয় আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে।
৩. বিশ্বমানের বিজ্ঞানী তৈরি: এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেই সি. ভি. রমন তাঁর বিখ্যাত ‘রমন এফেক্ট’ আবিষ্কার করেন এবং ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। এছাড়া, কে. এস. কৃষ্ণান, মেঘনাদ সাহার মতো বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী এখানে গবেষণা করেছেন।
উপসংহার: IACS শুধুমাত্র একটি গবেষণাগার ছিল না, এটি ছিল একটি আন্দোলন যা ভারতে বিজ্ঞান চেতনা ও আধুনিক গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচক ছিলেন। তিনি মনে করতেন, এই শিক্ষা ব্যবস্থা যান্ত্রিক, পুঁথি-সর্বস্ব এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এর বিকল্প হিসেবেই তিনি শান্তিনিকেতনে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।
ভাবনা:
১. প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলে ছিল প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ। তিনি বিশ্বাস করতেন, চার দেওয়ালের বাইরে প্রকৃতির কোলে উন্মুক্ত পরিবেশেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব।
২. আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা: তিনি পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রকলা, ঋতু-উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদানের উপর জোর দেন।
৩. স্বাধীনতার পরিবেশ: তিনি মনে করতেন, কঠোর শাসন বা শৃঙ্খলার পরিবর্তে স্বাধীনতার পরিবেশেই শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।
৪. সমন্বয়: তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করা এবং শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—এই চারটি দিকের সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো।
৯. টীকা লেখো: ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
উত্তর:
ভূমিকা: ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, তাকেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ১৮৩৫ সালের মেকলের প্রতিবেদন।
বৈশিষ্ট্য ও সমালোচনা:
১. উদ্দেশ্য: এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য স্বল্প বেতনের ইংরেজি-জানা কেরানি বা কর্মচারী তৈরি করা, ভারতীয়দের প্রকৃত জ্ঞানদান নয়।
২. মাধ্যম: শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। এর ফলে শিক্ষা মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।
৩. পুঁথি-সর্বস্ব ও মুখস্থ-নির্ভর: এই শিক্ষা ছিল পুঁথি-কেন্দ্রিক ও মুখস্থ-নির্ভর। এর সঙ্গে বাস্তব জীবন বা দেশের প্রয়োজনের কোনো যোগ ছিল না।
৪. নেতিবাচক প্রভাব: এই শিক্ষা ভারতীয়দের মনে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে হীনম্মন্যতা তৈরি করে এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের জন্ম দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ‘তোতাকাহিনী’র সঙ্গে তুলনা করেছেন।
১০. বাংলার নবজাগরণে বটতলা প্রকাশনার ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে কলকাতার বটতলা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এক ধরনের জনপ্রিয় ও বাণিজ্যিক প্রকাশনা শিল্প গড়ে উঠেছিল, যা ‘বটতলা প্রকাশনা’ নামে পরিচিত।
ভূমিকা:
১. গণশিক্ষার প্রসার: বটতলার বইগুলির দাম ছিল খুব কম এবং বিষয়বস্তু ছিল সহজ-সরল। এর ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে অল্পশিক্ষিত ও গ্রামীণ পাঠকদের কাছে ছাপা বই পৌঁছে যায়, যা গণশিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে।
২. বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য: এখানে মূলত ধর্মীয়, পৌরাণিক কাহিনী, পঞ্জিকা, লোককথা এবং কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যঙ্গ ও কিস্সা-কাহিনী ছাপা হত। এগুলি সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের চাহিদা মেটাত।
৩. মুদ্রণ শিল্পের বিস্তার: বটতলা প্রকাশনার বিপুল চাহিদার ফলে কলকাতায় বহু ছোট ছোট ছাপাখানা গড়ে ওঠে এবং মুদ্রণ শিল্পের বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটে।
সীমাবদ্ধতা: যদিও এই বইগুলির সাহিত্যমূল্য বা মুদ্রণমান খুব উন্নত ছিল না এবং অনেক সময় অশ্লীল বিষয়ও থাকত, তবুও বাংলার পাঠক সমাজ তৈরিতে এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।
১১. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে তোলার প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ১৯০৬ সালে ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ প্রতিষ্ঠা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ফল। এর পিছনে একাধিক প্রেক্ষাপট কাজ করেছিল।
প্রেক্ষাপট:
১. ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রতি অসন্তোষ: উনিশ শতক থেকেই শিক্ষিত ভারতীয়রা ঔপনিবেশিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা (যেমন—কেরানি তৈরি, জাতীয় সংস্কৃতির অবহেলা) নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা একটি বিকল্প, জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।
২. ডন সোসাইটির প্রভাব: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ‘ডন সোসাইটি’ ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় আদর্শ ও চরিত্র গঠনের কাজ শুরু করে, যা জাতীয় শিক্ষা ভাবনার প্রসারে সাহায্য করে।
৩. সরকারি দমননীতি (প্রত্যক্ষ কারণ): ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বহু ছাত্র এতে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য ‘কার্লাইল সার্কুলার’ জারি করে ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করে।
৪. অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি: এর প্রতিবাদে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নেতৃত্বে ‘অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি’ গঠিত হয়। বহু ছাত্র সরকারি স্কুল ত্যাগ করলে তাদের জন্য একটি বিকল্প জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ গঠিত হয়।
১২. টীকা লেখো: বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস।
উত্তর:
ভূমিকা: ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস’ (BCPW) হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা। এটি ছিল স্বদেশী উদ্যোগের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য: প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৭০০ টাকা মূলধন নিয়ে তাঁর নিজের বাড়িতে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:
১. ঔষধ শিল্পে বিদেশি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে তৈরি ঔষধ সুলভে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
২. বাঙালি যুবকদের মধ্যে ব্যবসা ও উদ্যোগের মানসিকতা তৈরি করা, যাতে তারা শুধুমাত্র চাকরির উপর নির্ভরশীল না থাকে।
গুরুত্ব:
স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। এটি প্রমাণ করে যে, ভারতীয়রাও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সফল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম। ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস’ ছিল আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার এক মূর্ত প্রতীক, যা বহু ভারতীয়কে নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছিল।
১৩. বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বিপুল অর্থ সাহায্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ‘ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স’ বা ‘কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়।
ভূমিকা:
১. স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন ও গবেষণা: বিজ্ঞান কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত) স্নাতকোত্তর স্তরের পঠনপাঠন এবং মৌলিক গবেষণার সুযোগ তৈরি করা।
২. বিশ্বমানের বিজ্ঞানী তৈরি: আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সারা ভারত থেকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকদের এখানে নিয়ে আসেন। সিভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মতো বিশ্বমানের বিজ্ঞানীরা এখানে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেছেন।
৩. যুগান্তকারী আবিষ্কার: এখানেই মেঘনাদ সাহা তাঁর বিখ্যাত ‘তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব’ (Thermal Ionization Theory) এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ‘বोस-आइंस्टाइन পরিসংখ্যান’ (Bose-Einstein statistics) সংক্রান্ত গবেষণা করেন, যা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি লাভ করে।
উপসংহার: কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং দেশকে বিজ্ঞানের মানচিত্রে এক সম্মানজনক স্থান দেয়।
১৪. টীকা লেখো: শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
বৈশিষ্ট্য:
১. প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ: এই বিদ্যালয়ের মূল আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতের তপোবনের মতো গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্কের ভিত্তিতে শিক্ষাদান।
২. প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষা: এখানে চার দেওয়ালের পরিবর্তে গাছের তলায়, উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ক্লাস নেওয়া হত।
৩. সমন্বয়মূলক শিক্ষা: এখানে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি আশ্রমিক জীবনযাপন, খেলাধুলা, বাগান করা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের উপর জোর দেওয়া হত।
৪. আত্মনির্ভরশীলতা: ছাত্রদের নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হত, যা তাদের আত্মনির্ভরশীল ও শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলত।
এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই পরবর্তীকালে বিকশিত হয়ে বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়।
১৫. বাংলার ছাপাখানার বিকাশে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের শুরুতে যখন মুদ্রণ শিল্প মূলত বিদেশি মিশনারিদের হাতে ছিল, তখন গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি এই ক্ষেত্রে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন।
ভূমিকা:
১. প্রথম বাঙালি প্রকাশক ও বিক্রেতা: তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি বই প্রকাশ ও বিক্রিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে কাজ করার পর কলকাতায় এসে বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন।
২. ‘বেঙ্গল গেজেটি প্রেস’ প্রতিষ্ঠা: ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর সহযোগী হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মিলে ‘বেঙ্গল গেজেটি প্রেস’ নামে নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
৩. বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ: তাঁর ছাপাখানা থেকে তিনি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ (প্রথম সচিত্র বাংলা বই), ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
৪. সংবাদপত্র প্রকাশ: তিনি ‘বেঙ্গল গেজেট’ নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন।
উপসংহার: গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, বাঙালিরাও মুদ্রণ শিল্পের মতো আধুনিক প্রযুক্তিতে সফল হতে পারে। তিনি ছিলেন বাঙালি প্রকাশনা শিল্পের পথিকৃৎ।
১৬. ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলেছিলেন?
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম কঠোর সমালোচক। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, যেমন—’শিক্ষার হেরফের’, এবং ‘তোতাকাহিনী’র মতো রূপক গল্পে এই শিক্ষার ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছেন।
সমালোচনা:
১. যান্ত্রিক ও প্রাণহীন: রবীন্দ্রনাথের মতে, এই শিক্ষা ছিল খাঁচায় বন্দি পাখির মতো, যা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা গেলানো হত। এটি ছিল যান্ত্রিক, প্রাণহীন এবং মুখস্থ-নির্ভর।
২. জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন: এই শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন, সমাজ বা প্রকৃতির কোনো যোগ ছিল না। এটি ছিল ‘কলের তৈরি’ শিক্ষা।
৩. মাতৃভাষার অবহেলা: ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে ছাত্ররা তাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং তাদের চিন্তার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হত।
৪. আনন্দের অভাব: তিনি মনে করতেন, এই শিক্ষাব্যবস্থায় আনন্দের কোনো স্থান ছিল না। এটি ছিল ছাত্রদের কাছে এক বিরাট বোঝা। এই কারণেই তিনি শান্তিনিকেতনে এক বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।
১৭. মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র একজন শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না, তিনি বাংলার মুদ্রণ শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।
অবদান:
১. ‘সংস্কৃত প্রেস’ প্রতিষ্ঠা: তিনি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে মিলে ‘সংস্কৃত প্রেস’ নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাপাখানা।
২. উন্নত মানের মুদ্রণ: বিদ্যাসাগর নির্ভুল, সুন্দর এবং ঝকঝকে ছাপার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর প্রেস থেকে প্রকাশিত বইগুলি মুদ্রণ সৌকর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।
৩. বাংলা হরফের সংস্কার: তিনি বাংলা বর্ণমালাকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজান এবং ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থের মাধ্যমে তার একটি নির্দিষ্ট রূপ দেন, যা মুদ্রণের কাজকে অনেক সহজ করে তোলে।
৪. বইয়ের ব্যবসা: তিনি ‘সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি’ নামে একটি বইয়ের দোকান খোলেন এবং বই প্রকাশ ও বিক্রিকে একটি সফল ব্যবসায় পরিণত করেন। এর ফলে লেখকরাও আর্থিকভাবে লাভবান হতে শুরু করেন।
১৮. ‘ডন সোসাইটি’ কীভাবে জাতীয় শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করেছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ‘ডন সোসাইটি’ (১৯০২) ছিল স্বদেশী যুগের প্রাক্কালে জাতীয় শিক্ষা ভাবনার প্রসারের এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।
ভূমিকা:
১. বিকল্প শিক্ষার রূপরেখা: ডন সোসাইটি ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে এক নতুন ধরনের শিক্ষার কথা বলে। এর মুখপত্র ‘ডন’ পত্রিকায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষার রূপরেখা प्रस्तुत করেন।
২. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ: এই সোসাইটির লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং দেশাত্মবোধক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।
৩. শিল্প ও বিজ্ঞানের গুরুত্ব: এটি ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের উপরও জোর দিত।
৪. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনে অনুপ্রেরণা: স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়, তখন ডন সোসাইটির ছাত্র ও সদস্যরা এবং তার আদর্শ এক গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। বলা যায়, ডন সোসাইটিই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পথপ্রদর্শক ছিল।
১৯. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
উত্তর:
স্বদেশী যুগে গড়ে ওঠা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়েছিল।
ব্যর্থতার কারণ:
১. সরকারি চাকরির মোহ: জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ডিগ্রি সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল না। তাই সরকারি চাকরির আকর্ষণে অধিকাংশ ছাত্র ও অভিভাবক সরকারি স্কুল-কলেজের প্রতিই আস্থাশীল ছিলেন।
২. আর্থিক সংকট: জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত জনগণের দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সাহায্যও কমে আসে, যা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কঠিন করে তোলে।
৩. অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ: জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নেতাদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর ফলে পরিষদ বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।
৪. কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব: আন্দোলনটি সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরি শিক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছিল, ফলে এর আবেদন সর্বজনীন হতে পারেনি।
২০. টীকা লেখো: চার্লস উইলকিন্স।
উত্তর:
ভূমিকা: চার্লস উইলকিন্স ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী এবং বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জনক।
অবদান:
১. বাংলা হরফ তৈরি: গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রণের জন্য সচল বা বিচল ধাতব হরফ বা টাইপ তৈরি করেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন পঞ্চানন কর্মকার।
২. প্রথম বাংলা বই মুদ্রণ: ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলিতে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখান থেকে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের লেখা ‘A Grammar of the Bengal Language’ নামক গ্রন্থটি ছাপান। এটিই ছিল বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বই।
গুরুত্ব: উইলকিন্সের এই উদ্যোগই বাংলায় মুদ্রণ যুগের সূচনা করে। তাঁর তৈরি করা হরফের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বাংলা মুদ্রণ শিল্প বিকশিত হয়েছিল। এই কারণে তাঁকে ‘বাংলা মুদ্রণ শিল্পের গুটেনবার্গ’ বলা হয়।
২১. টীকা লেখো: বিশ্বভারতী।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার মূর্ত প্রতীক হল ‘বিশ্বভারতী’। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বিকশিত করে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠা করেন।
আদর্শ ও লক্ষ্য:
বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ হল ‘যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্’—অর্থাৎ, যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি নীড়ে বা বাসায় পরিণত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল:
১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান ও মেলবন্ধন ঘটানো।
২. পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়ে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে এক समग्र শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
৩. কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য এবং মানববিদ্যা চর্চার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র তৈরি করা।
পরিণতি: রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। এটি আজও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে বহন করে চলেছে।
২২. ‘মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয়’ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শনের মূল কথাই ছিল মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার মধ্যে এক গভীর সমন্বয় সাধন করা।
সমন্বয়ের ধারণা:
১. প্রকৃতির ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতি হল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশেই শিশুর মন ও আত্মা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে চার দেওয়ালের বাইরে, গাছের তলায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।
২. মানুষের সঙ্গে সংযোগ: তিনি মনে করতেন, শিক্ষা যদি মানুষকে তার চারপাশের সমাজ ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তবে তা অর্থহীন। তাই তিনি শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের মানুষের সঙ্গে ছাত্রদের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন।
৩. শিক্ষার লক্ষ্য: তাঁর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল এই প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনশীলতা, সংবেদনশীলতা ও বিশ্বমানবতাবোধ জাগিয়ে তোলা। পুঁথিগত জ্ঞান নয়, বরং এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করাই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।
২৩. ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্পর্কে লেখো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ধর্মপ্রচার বা জ্ঞানবিস্তারের পাশাপাশি ছাপাখানা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল।
উদ্যোগ:
১. ইউরোপীয় উদ্যোগ: জেমস অগাস্টাস হিকি ‘বেঙ্গল গেজেট’ প্রকাশ করে বাণিজ্যিক সাংবাদিকতার সূচনা করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসও বই বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত।
২. বাঙালি উদ্যোগ: গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি বই প্রকাশ ও বিক্রিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ‘সংস্কৃত প্রেস’ ও ‘ডিপোজিটরি’র মাধ্যমে বইয়ের ব্যবসাকে এক নতুন মাত্রা দেন।
৩. বটতলা প্রকাশনা: উনিশ শতকে কলকাতার বটতলা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এক ধরনের জনপ্রিয় ও বাণিজ্যিক প্রকাশনা শিল্প গড়ে ওঠে। এখানকার প্রকাশকরা কম দামে প্রচুর বই ছেপে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিত এবং লাভ করত।
এইভাবে, উনিশ শতকে ছাপাখানা শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল না, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছিল।
২৪. বিজ্ঞান চর্চায় ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান কী ছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: ড. মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং বিজ্ঞান প্রসারের একনিষ্ঠ কর্মী।
অবদান:
১. বিজ্ঞান সভার স্বপ্ন: তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরাধীন ভারতে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুকরণ করলে চলবে না, দেশীয় উদ্যোগে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্বপ্ন থেকেই তিনি একটি জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।
২. IACS প্রতিষ্ঠা: তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং কিছু মানুষের দানে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স’ (IACS) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল ভারতের প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার।
৩. বিজ্ঞান চেতনা প্রসার: তিনি নিয়মিত বক্তৃতার মাধ্যমে এবং তাঁর সম্পাদিত ‘ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন’ পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের চেষ্টা করেন।
উপসংহার: মহেন্দ্রলাল সরকার নিজে কোনো বড় বিজ্ঞানী না হলেও, তিনি ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার যে পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেই পথেই হেঁটে সি. ভি. রমনের মতো বিজ্ঞানীরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
২৫. ‘তোতাকাহিনী’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ কোন শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং কেন?
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘লিপিকা’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘তোতাকাহিনী’ নামক রূপক গল্পে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন।
ব্যঙ্গের কারণ:
১. গল্পে একটি স্বাধীন, গান-জানা তোতাপাখিকে শিক্ষাদানের নামে সোনার খাঁচায় বন্দি করে পুঁথিগত বিদ্যা গেলানো হচ্ছিল। এখানে ‘তোতাপাখি’ হল ছাত্র এবং ‘খাঁচা’ হল স্কুল। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে এক যান্ত্রিক ও প্রাণহীন ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে।
২. শিক্ষকরা তোতার মুখে পুঁথির পাতা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু তোতা কিছুই শিখছিল না, শেষে মরেই গেল। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের উপর শুধুমাত্র তথ্যের বোঝা চাপায়, তাদের ভেতরের মানুষটিকে মেরে ফেলে।
৩. এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন বা আনন্দের কোনো যোগ নেই। এটি শুধুমাত্র কেরানি তৈরির এক কারখানা। এই অন্তঃসারশূন্যতাকেই রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করেছেন।
ঙ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৮ (১০টি)
১. মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমালোচক। তিনি মনে করতেন, ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা যান্ত্রিক, প্রাণহীন এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই শিক্ষার বিকল্প হিসেবে তিনি এক নতুন শিক্ষাদর্শের কথা বলেন, যার মূল ভিত্তি ছিল মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার মধ্যে গভীর সমন্বয় সাধন। তাঁর এই শিক্ষাচিন্তার মূর্ত রূপ হল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী।
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা:
১. প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রকৃতি। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতি হল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। চার দেওয়ালের বন্ধ ক্লাসরুমের পরিবর্তে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে, গাছের তলায়, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাদানই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এলে শিশুর মন ও আত্মা উদার হয়, তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সংবেদনশীলতা বাড়ে।
২. আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা: প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর শাসন ও শাস্তির তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষা হওয়া উচিত আনন্দের উৎস, বোঝা নয়। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রকলা, ঋতু-উৎসব (যেমন—বসন্তোৎসব, পৌষমেলা) ইত্যাদির মাধ্যমে এক আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।
৩. স্বাধীনতার পরিবেশ: রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, স্বাধীনতার পরিবেশেই শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। তিনি ছাত্রদের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব আগ্রহ অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতেন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ভয়ের নয়, বরং স্নেহ ও শ্রদ্ধার।
৪. মানুষের সঙ্গে সংযোগ ও সেবা: শিক্ষা যদি মানুষকে তার চারপাশের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তবে তা অর্থহীন। এই ভাবনা থেকেই তিনি বিশ্বভারতীর একটি শাখা হিসেবে ‘শ্রীনিকেতন’ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষের জীবনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করানো এবং কৃষি, সমবায় ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তুলে গ্রামোন্নয়নে সাহায্য করা।
৫. আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সমন্বয়: তাঁর শিক্ষাচিন্তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বিশ্বমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা। তিনি বিশ্বভারতীকে এমন একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, ‘যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি নীড়ে পরিণত হবে’ (‘যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্’)। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।
উপসংহার: রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাচিন্তা ছিল গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে এক সামগ্রিক জীবনদর্শন, যা আজও বিশ্বজুড়ে প্রাসঙ্গিক।
২. উনিশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশে যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে বাংলায় সমাজ সংস্কার ও সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক নতুন জাগরণ দেখা যায়। ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি বহু দেশীয় উদ্যোগেও এই শিক্ষার প্রসার ঘটে।
বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ:
১. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫): লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ ছিল ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। এখানে মধুসূদন গুপ্তের প্রথম শবব্যবচ্ছেদ ভারতে আধুনিক শরীরবিদ্যা চর্চার পথ খুলে দেয়।
২. কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ (১৯১৪): স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের অর্থ সাহায্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সিভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বিশ্বমানের বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা করে ভারতকে বিজ্ঞানের মানচিত্রে এক সম্মানজনক স্থান দেন।
৩. ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স (IACS, ১৮৭৬): ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ছিল ভারতে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম জাতীয় কেন্দ্র। এখানেই সিভি রমন তাঁর ‘রমন এফেক্ট’ আবিষ্কার করেন।
৪. বসু বিজ্ঞান মন্দির (১৯১৭): আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে।
কারিগরি শিক্ষার বিকাশ:
১. শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১৮৫৬): এটি ছিল ভারতের প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির অন্যতম, যা দেশের পরিকাঠামো নির্মাণে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করত।
২. বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (BTI, ১৯০৬): স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।
৩. বেঙ্গল কেমিক্যালস (১৮৯২): আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি ছিল স্বদেশী উদ্যোগে গড়ে ওঠা এক সফল রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্প, যা কারিগরি শিক্ষাকে বাস্তব প্রয়োগে উৎসাহিত করেছিল।
উপসংহার: এই সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের ফলেই উনিশ শতকে বাংলায় এক শক্তিশালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা দেশের আধুনিকীকরণে অপরিহার্য ছিল।
৩. বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এবং গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের অবদান আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকের শুরুতে বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে বিদেশি মিশনারি এবং দেশীয় উদ্যোক্তা—উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস এবং গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন অগ্রগণ্য।
শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের অবদান:
‘শ্রীরামপুর ত্রয়ী’ (উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে যে ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন, তা বাংলার মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে এক মাইলফলক।
১. উন্নত ছাপাখানা: এটি ছিল তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাপাখানা, যেখানে উন্নত মানের মুদ্রণ সম্ভব ছিল।
২. বাংলা হরফের উন্নতি: এই প্রেসের উদ্যোগেই পঞ্চানন কর্মকারের মতো কারিগররা বাংলা হরফ বা টাইপকে আরও সুন্দর ও সুগঠিত রূপ দেন।
৩. বিপুল গ্রন্থ প্রকাশ: এই প্রেস থেকে বাংলা সহ প্রায় ৪০টি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে ছাপানো হয়। এছাড়া, রামায়ণ, মহাভারত, ইতিহাস ও ভূগোলের মতো বিভিন্ন বিষয়ের বই ছেপে শিক্ষাবিস্তারে enormous ভূমিকা পালন করে।
৪. সংবাদপত্র প্রকাশ: তাঁরা বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা ‘দিকদর্শন’ (১৮১৮) এবং প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘সমাচার দর্পণ’ (১৮১৮) প্রকাশ করেন, যা বাংলা সাংবাদিকতার সূচনা করে।
গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের অবদান:
গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি মুদ্রণ শিল্পকে একটি সফল ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত করেন।
১. প্রথম বাঙালি প্রকাশক ও বিক্রেতা: তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি বই প্রকাশ ও বিক্রিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
২. নিজস্ব প্রেস প্রতিষ্ঠা: তিনি শ্রীরামপুর মিশনে কাজ করার পর কলকাতায় এসে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ‘বেঙ্গল গেজেটি প্রেস’ নামে নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
৩. উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা: তাঁর প্রেস থেকে তিনি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ (প্রথম সচিত্র বাংলা বই), ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ প্রভৃতি জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
৪. সংবাদপত্র প্রকাশ: তিনি ‘বেঙ্গল গেজেট’ নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন, যা ছিল কোনো বাঙালির দ্বারা প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।
উপসংহার: শ্রীরামপুর মিশন যেখানে মুদ্রণ শিল্পের প্রযুক্তিগত ভিত্তি স্থাপন করেছিল, গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য সেখানে তাকে একটি দেশীয় ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত করার পথ দেখিয়েছিলেন। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলায় মুদ্রণ শিল্প বিকশিত হয়েছিল।
৪. ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
উত্তর:
ভূমিকা: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ (১৯০৬)।
প্রেক্ষাপট:
স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদান বন্ধ করার জন্য ‘কার্লাইল সার্কুলার’-এর মতো দমনমূলক নির্দেশ জারি করে। এর প্রতিবাদে বহু ছাত্র সরকারি স্কুল-কলেজ ত্যাগ করলে তাদের জন্য একটি বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগে ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ গঠিত হয়।
উদ্দেশ্য ও আদর্শ:
১. সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে জাতীয় আদর্শে শিক্ষাদান করা।
২. শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজলভ্য করা।
৩. সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি—এই তিন ধারার সমন্বয়ে এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।
৪. ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো।
কার্যাবলী ও প্রতিষ্ঠান:
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে সারা বাংলায় বেশ কিছু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ‘বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল’ এবং ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ (BTI)। ‘বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ’-এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।
ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা:
এত মহৎ উদ্যোগ সত্ত্বেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। এর কারণগুলি হল:
১. জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ডিগ্রির কোনো সরকারি স্বীকৃতি ছিল না, ফলে সরকারি চাকরির আকর্ষণে ছাত্ররা এদিকে কম আকৃষ্ট হত।
২. স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যও কমে আসে।
৩. সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।
গুরুত্ব: ব্যর্থতা সত্ত্বেও, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগ ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার জন্ম দিয়েছিল। এটি প্রমাণ করেছিল যে, ভারতীয়রা নিজেরাই একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। এর কারিগরি শিক্ষার উদ্যোগই পরবর্তীকালে বিখ্যাত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম দেয়।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা ও শান্তিনিকেতন ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক কঠোর সমালোচক। তাঁর মতে, এই শিক্ষা ছিল ‘তোতাকাহিনী’র মতো, যা ছাত্রদের সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে এক যান্ত্রিক ও প্রাণহীন ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। এর বিকল্প হিসেবেই তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন ভাবনার মাধ্যমে এক নতুন শিক্ষাদর্শ प्रस्तुत করেন।
শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্র:
১. প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলে ছিল প্রকৃতি। তিনি বিশ্বাস করতেন, চার দেওয়ালের বন্ধ ক্লাসরুমের পরিবর্তে প্রকৃতির কোলে উন্মুক্ত পরিবেশেই শিশুর স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। তাই শান্তিনিকেতনে গাছের তলায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
২. আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা: তিনি মনে করতেন, শিক্ষা হওয়া উচিত আনন্দের উৎস, বোঝা নয়। তাই তিনি পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি নাচ, গান, অভিনয়, চিত্রকলা, ঋতু-উৎসব (যেমন—বসন্তোৎসব) ইত্যাদির মাধ্যমে এক আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদানের উপর জোর দেন।
৩. স্বাধীনতার পরিবেশ: তাঁর মতে, কঠোর শাসন বা শৃঙ্খলার পরিবর্তে স্বাধীনতার পরিবেশেই শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও আত্মবিকাশ ঘটে। তিনি গুরু-শিষ্যের মধ্যে এক স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।
শান্তিনিকেতন ভাবনা ও তার রূপায়ণ:
১. ব্রহ্মচর্যাশ্রম (১৯০১): তিনি তাঁর পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদলে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন।
২. বিশ্বভারতী (১৯২১): এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই পরবর্তীকালে বিকশিত হয়ে ‘বিশ্বভারতী’তে পরিণত হয়। এর মূল আদর্শ ছিল ‘যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্’—অর্থাৎ, যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি নীড়ে পরিণত হয়। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়।
৩. শ্রীনিকেতন (১৯২২): শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সংযোগ ঘটানোর জন্য তিনি গ্রামের মানুষের सर्वांगीण উন্নতির লক্ষ্যে ‘শ্রীনিকেতন’ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে কৃষি, সমবায় ও হস্তশিল্পের শিক্ষা দেওয়া হত।
উপসংহার: রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাচিন্তা ছিল গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে এক সামগ্রিক জীবনদর্শন, যা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন নয়, এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরির উপর জোর দিয়েছিল।
৬. ছাপাখানার বিস্তার কীভাবে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এনেছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে বাংলায় ছাপাখানার বিস্তার শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছিল না, এটি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব এনেছিল।
সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন:
১. শিক্ষাবিস্তার: ছাপাখানার ফলে বই, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক, সহজলভ্য ও সস্তা হয়। এর ফলে শিক্ষা আর মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ বা রামসুন্দর বসাকের ‘बाल्यशिक्षा’ ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়। নারীশিক্ষার প্রসারেও ছাপা বইয়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।
২. বাংলা গদ্যের বিকাশ: ছাপাখানার প্রয়োজনেই বাংলা গদ্যের একটি নির্দিষ্ট ও মান্য রূপ তৈরি হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা এবং পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্য সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে।
৩. জনমত গঠন ও জাতীয়তাবাদের প্রসার: ‘সমাচার দর্পণ’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’-এর মতো সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি ছাপাখানার মাধ্যমেই প্রকাশিত হত। এগুলি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গঠন করত এবং ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদের প্রসারে সাহায্য করত।
৪. ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন: রামমোহন রায় ছাপাখানার মাধ্যমেই তাঁর একেশ্বরবাদী মতবাদ এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালান। অন্যদিকে, রক্ষণশীল হিন্দুরাও ‘সমাচার চন্দ্রিকা’র মতো পত্রিকা ছেপে তার বিরোধিতা করে। অর্থাৎ, ছাপাখানা वाद-প্রতিবাদের এক নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে।
৫. নতুন পাঠক শ্রেণির উদ্ভব: বটতলার মতো প্রকাশনাগুলি সস্তা দামের বই ছেপে এক বিশাল নতুন পাঠক শ্রেণি তৈরি করে, যারা ছিল মূলত অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ।
উপসংহার: এইভাবে, ছাপাখানা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল এবং সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।
৭. বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার বিকাশে ড. মহেন্দ্রলাল সরকার এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ ও বিশ শতকে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার বিকাশে এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা জাগরণে ড. মহেন্দ্রলাল সরকার ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান ছিল পথিকৃতের।
ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান:
মহেন্দ্রলাল সরকার নিজে বিজ্ঞানী না হলেও, তিনি ছিলেন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার একনিষ্ঠ সংগঠক।
১. বিজ্ঞান সভার স্বপ্ন: তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরাধীন ভারতে জাতীয় গর্ব ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হলে দেশীয় উদ্যোগে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।
২. IACS প্রতিষ্ঠা: তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং কিছু মানুষের দানে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স’ (IACS) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল ভারতের প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার।
৩. গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত: এই প্রতিষ্ঠানটিই পরবর্তীকালে সি. ভি. রমন, কে. এস. কৃষ্ণান, মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীদের গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। এখানেই সিভি রমন তাঁর নোবেলজয়ী গবেষণাটি করেছিলেন।
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান:
জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী।
১. যুগান্তকারী গবেষণা: তিনি পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা—উভয় ক্ষেত্রেই যুগান্তকারী গবেষণা করেন। তিনি প্রথম প্রমাণ করেন যে, বেতার তরঙ্গ কোনো তার ছাড়াই বহুদূরে যেতে পারে, যা ছিল মার্কনির আগেকার আবিষ্কার।
২. উদ্ভিদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা: তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ‘ক্রেসকোগ্রাফ’ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে এবং তারা বাহ্যিক উত্তেজনায় সাড়া দেয়। এই আবিষ্কার বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।
৩. বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা: তিনি তাঁর সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে ১৯১৭ সালে ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার এক অগ্রণী প্রতিষ্ঠান।
উপসংহার: মহেন্দ্রলাল সরকার যেখানে বিজ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, জগদীশচন্দ্র বসু সেখানে নিজের গবেষণা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টা বাংলায় বিজ্ঞান নবজাগরণের পথ প্রশস্ত করে।
৮. উনিশ শতকে বাংলায় ছাপাখানার বিস্তার কীভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এনেছিল?
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে বাংলায় ছাপাখানার বিস্তার শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছিল না, এটি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব এনেছিল। এই ‘মুদ্রণ বিপ্লব’ বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল।
সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন:
১. শিক্ষাবিস্তার: ছাপাখানার ফলে বই, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক, সহজলভ্য ও সস্তা হয়। এর ফলে শিক্ষা আর মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ বা রামসুন্দর বসাকের ‘बाल्यशिक्षा’ ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়। নারীশিক্ষার প্রসারেও ছাপা বইয়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।
২. বাংলা গদ্যের বিকাশ: ছাপাখানার প্রয়োজনেই বাংলা গদ্যের একটি নির্দিষ্ট ও মান্য রূপ তৈরি হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা এবং পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্য সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে।
৩. জনমত গঠন ও জাতীয়তাবাদের প্রসার: ‘সমাচার দর্পণ’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’-এর মতো সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি ছাপাখানার মাধ্যমেই প্রকাশিত হত। এগুলি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গঠন করত এবং ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদের প্রসারে সাহায্য করত।
৪. ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন: রামমোহন রায় ছাপাখানার মাধ্যমেই তাঁর একেশ্বরবাদী মতবাদ এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালান। অন্যদিকে, রক্ষণশীল হিন্দুরাও ‘সমাচার চন্দ্রিকা’র মতো পত্রিকা ছেপে তার বিরোধিতা করে। অর্থাৎ, ছাপাখানা वाद-প্রতিবাদের এক নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে, যা সমাজকে আলোড়িত করে।
৫. নতুন পাঠক শ্রেণির উদ্ভব: বটতলার মতো প্রকাশনাগুলি সস্তা দামের বই ছেপে এক বিশাল নতুন পাঠক শ্রেণি তৈরি করে, যারা ছিল মূলত অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ। এর ফলে জ্ঞানের পরিধি সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।
উপসংহার: এইভাবে, ছাপাখানা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল এবং সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।
৯. বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ব্রিটিশ ভারতে সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটলেও, কারিগরি শিক্ষার প্রতি ঔপনিবেশিক সরকারের তেমন আগ্রহ ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল কেরানি তৈরি করা, ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তিবিদ তৈরি করা নয়। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় উদ্যোগে বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশের প্রচেষ্টা শুরু হয়।
বিকাশের পর্যায়:
১. সরকারি উদ্যোগ: ব্রিটিশ সরকার নিজেদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ’ (যা পরে ‘বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ’ নামে পরিচিত হয়)। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল Public Works Department (PWD)-এর জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করা।
২. স্বদেশী যুগের উদ্যোগ: বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল স্বদেশী আন্দোলন। এই সময় জাতীয় আত্মনির্ভরতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।
৩. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ: ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষদ’ কারিগরি শিক্ষাকে তাদের পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে।
৪. বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (BTI): জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নেতাদের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার, রাসবিহারী ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বরা ১৯০৬ সালে ‘বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট’ (BTI) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল কারিগরি শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় উদ্যোগ। এখানে ফলিত রসায়ন, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো বিষয় পড়ানো হত।
৫. শিল্পের সঙ্গে যোগ: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস’-এর মতো সংস্থাগুলি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং হাতে-কলমে শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে।
পরিণতি: পরবর্তীকালে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট একত্রিত হয়ে ‘কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি’ (CET) নামে পরিচিত হয়, যা আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে খ্যাত।
উপসংহার: সীমিত সামর্থ্য ও সরকারি অসহযোগিতা সত্ত্বেও, উনিশ ও বিশ শতকে বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশের এই দেশীয় উদ্যোগগুলি ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল।
১০. উনিশ শতকে বাংলায় ‘বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ’-এর গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো।
উত্তর:
ভূমিকা: উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসন ও সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু ‘বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ’ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, IACS এবং দেশীয় ছাপাখানাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উদ্যোগগুলির যেমন গুরুত্ব ছিল, তেমনই কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল।
গুরুত্ব:
১. জাতীয়তাবাদের উন্মেষ: এই উদ্যোগগুলি পরাধীন ভারতে জাতীয় গৌরব ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছিল। এগুলি প্রমাণ করে যে, ভারতীয়রাও ব্রিটিশদের সাহায্য ছাড়াই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম।
২. আত্মনির্ভরতার আদর্শ প্রচার: ‘আত্মশক্তি’র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই উদ্যোগগুলি দেশের অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক আত্মনির্ভরতার পথ দেখিয়েছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালস বা জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ছিল এর মূর্ত প্রতীক।
৩. ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সমালোচনা: এই বিকল্প উদ্যোগগুলি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এবং তার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
৪. ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন: এই উদ্যোগগুলিই পরবর্তীকালে ভারতের আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা ও শিল্প বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা বসু বিজ্ঞান মন্দির আজও তার সাক্ষী।
সীমাবদ্ধতা:
১. শহর-কেন্দ্রিকতা ও精英দের অংশগ্রহণ: এই উদ্যোগগুলি ছিল মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মূলত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষেরা। বাংলার বিশাল গ্রামীণ জনতা বা সাধারণ মানুষ এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়নি।
২. আর্থিক সংকট: এই প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত জনগণের দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। সরকারি সাহায্যের অভাবে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সহায়তার অভাবে এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দুর্বল হয়ে পড়ে।
৩. সরকারি চাকরির মোহ: জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ডিগ্রির কোনো সরকারি স্বীকৃতি না থাকায়, সরকারি চাকরির আকর্ষণে অধিকাংশ ছাত্রই সরকারি স্কুল-কলেজের দিকে ঝুঁকেছিল।
৪. সমন্বয়ের অভাব: অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দেখা দেয়, যেমন—জাতীয় শিক্ষা পরিষদে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বিতর্ক।
উপসংহার: এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের এই বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগগুলি ছিল ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। এগুলি হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে ব্রিটিশদের কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে পারেনি, কিন্তু এগুলিই ভারতের ভবিষ্যৎ আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পথকে প্রশস্ত করেছিল।
Class 10 History বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা Question Answer MCQ,অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : class 10 বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা প্রশ্ন উত্তর