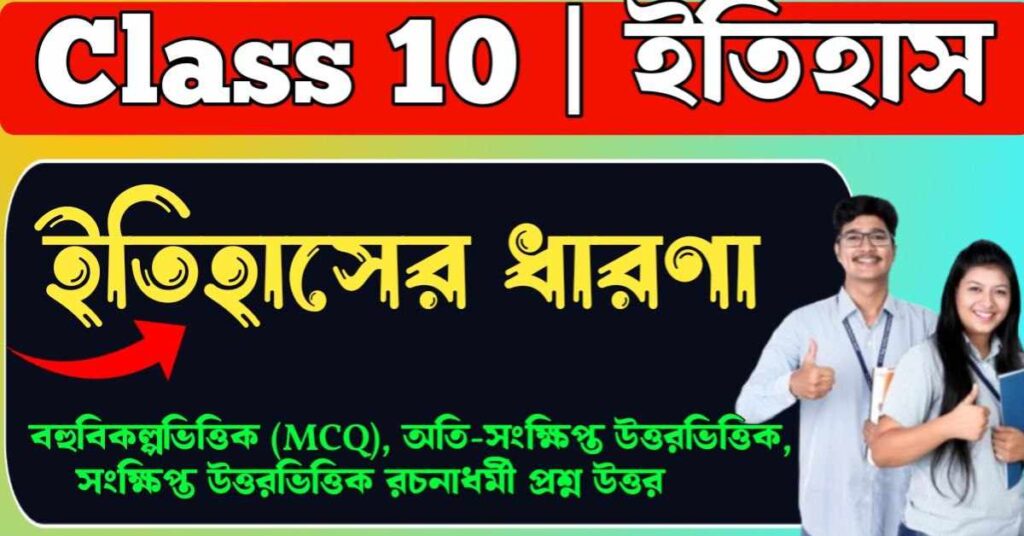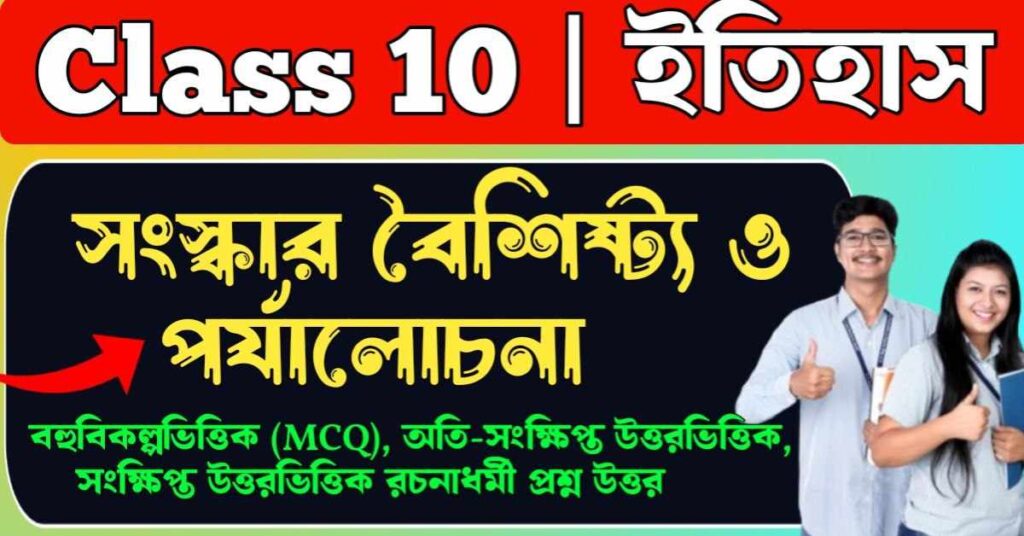উত্তর ঔপনিবেশিক ভারত বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব Class 10
ক) বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী (MCQ) – মান ১ (৭০টি)
১. স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ছিলেন –
২. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন –
৩. রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৩) এর সভাপতি ছিলেন –
৪. ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসেবে প্রথম গঠিত হয় –
৫. হায়দ্রাবাদ রাজ্যটি ভারতভুক্ত হয় –
৬. ‘অপারেশন পোলো’র মাধ্যমে যে দেশীয় রাজ্যটি ভারতভুক্ত হয়, তা হল –
৭. জুনাগড় রাজ্যটি ভারতভুক্ত হয় –
৮. ভারতের ‘লৌহমানব’ বলা হয় –
৯. ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় –
১০. নেহরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় –
১১. ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয় –
১২. ‘উদ্বাস্তু’ নামক গ্রন্থটি রচনা করেন –
১৩. স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন –
১৪. রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস হয় –
১৫. গোয়া ভারতভুক্ত হয় –
১৬. ভাষার ভিত্তিতে গুজরাট রাজ্যটি গঠিত হয় –
১৭. ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ গ্রন্থটি রচনা করেন –
১৮. ভারতের সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন –
১৯. কাশ্মীর ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন –
২০. স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর-জেনারেল ছিলেন –
২১. জে.ভি.পি. কমিটির সদস্য ছিলেন না –
২২. ‘The Marginal Men’ গ্রন্থটি রচনা করেন –
২৩. ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় –
২৪. ভারতের ‘বিসমার্ক’ কাকে বলা হয়?
২৫. হায়দ্রাবাদের নিজামের আধা-সামরিক বাহিনীর নাম ছিল –
২৬. দণ্ডকারণ্য প্রকল্পটি গড়ে উঠেছিল –
২৭. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন –
২৮. পট্টি শ্রীরামুলু যে রাজ্যের জন্য অনশন করে প্রাণ দেন, তা হল –
২৯. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল –
৩০. দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সচিব ছিলেন –
৩১. দেশভাগের ফলে উদ্ভূত একটি সমস্যা হল –
৩২. ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয় –
৩৩. ‘Train to Pakistan’ গ্রন্থটি লেখেন –
৩৪. ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা হল –
৩৫. ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের’ যে উপন্যাসে দেশভাগের কথা আছে, তা হল –
৩৬. গোয়া কাদের উপনিবেশ ছিল?
৩৭. গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন –
৩৮. ভারতের বিদেশ নীতির মূল ভিত্তি ছিল –
৩৯. ‘Discovery of India’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
৪০. ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা (National Archives of India) অবস্থিত –
৪১. ভারতের প্রথম IIT স্থাপিত হয় –
৪২. ‘মেমোরি লেন’ নামক আত্মজীবনীটি কার?
৪৩. ‘এক নতুন তীর্থ’ (A New Pilgrimage) বলে জওহরলাল নেহরু অভিহিত করেন –
৪৪. ভারত-চীন যুদ্ধ হয় –
৪৫. UCRC-এর পুরো নাম হল –
৪৬. ‘What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables’ গ্রন্থটি রচনা করেন –
৪৭. ‘ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন’ হল –
৪৮. ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন –
৪৯. ‘পঞ্চশীল’ নীতি স্বাক্ষরিত হয় ভারত ও –
৫০. ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ গৃহীত হয় মুসলিম লিগের যে অধিবেশনে, তা হল –
৫১. সিকিম ভারতভুক্ত হয় –
৫২. ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসটি কার লেখা?
৫৩. হায়দ্রাবাদের শাসককে বলা হত –
৫৪. ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?
৫৫. ‘A Nation in Making’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
৫৬. ভাষার ভিত্তিতে গঠিত ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য হল –
৫৭. দেশভাগের সময় কাশ্মীরের মহারাজা ছিলেন –
৫৮. গণপরিষদের প্রথম অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন –
৫৯. ‘পেরিয়ার’ নামে কে পরিচিত ছিলেন?
৬০. ‘এক জাতি, এক রাষ্ট্র’ স্লোগানটি জনপ্রিয় করে –
৬১. ‘ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
৬২. যে দেশীয় রাজ্যটি গণভোটের মাধ্যমে ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে রায় দেয় –
৬৩. স্বাধীন ভারতের শেষ গভর্নর-জেনারেল ছিলেন –
৬৪. ‘স্বাধীনতার স্বাদ’ গ্রন্থটি রচনা করেন –
৬৫. ‘ধর কমিশন’ কী বিষয়ে গঠিত হয়েছিল?
৬৬. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন –
৬৭. ‘মেঘে ঢাকা তারা’ চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন –
৬৮. ভারতীয় অর্থনীতিতে ‘মিশ্র অর্থনীতি’র (Mixed Economy) ধারণা দেন –
৬৯. যে দেশীয় রাজ্যটি প্রথমে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নেয় –
৭০. ‘নেটিভ স্টেটস্ অফ ইন্ডিয়া’ গ্রন্থটির রচয়িতা –
খ) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী (SAQ) – মান ১ (৬০টি)
১. স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: জওহরলাল নেহরু।
২. ভারতের ‘লৌহমানব’ কাকে বলা হয়?
উত্তর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে।
৩. রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে।
৪. রাজ্য পুনর্গঠন আইন কবে পাস হয়?
উত্তর: ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে।
৫. ভাষার ভিত্তিতে গঠিত ভারতের প্রথম রাজ্য কোনটি?
উত্তর: অন্ধ্রপ্রদেশ।
৬. ‘অপারেশন পোলো’ কী?
উত্তর: হায়দ্রাবাদকে ভারতভুক্ত করার জন্য পরিচালিত সামরিক অভিযান।
৭. নেহরু-লিয়াকত চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে।
৮. ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত হয়?
উত্তর: ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর।
৯. ভারতের সংবিধান কবে কার্যকর হয়?
উত্তর: ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি।
১০. দেশীয় রাজ্য দপ্তরের প্রধান কে ছিলেন?
উত্তর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।
১১. দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সচিব কে ছিলেন?
উত্তর: ভি. পি. মেনন।
১২. ‘উদ্বাস্তু’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩. স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তর: ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।
১৪. গোয়া কবে ভারতভুক্ত হয়?
উত্তর: ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে।
১৫. ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ কার লেখা?
উত্তর: দক্ষিণারঞ্জন বসুর।
১৬. ভারতের সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।
১৭. কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় সেখানকার রাজা কে ছিলেন?
উত্তর: মহারাজা হরি সিং।
১৮. স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর-জেনারেল কে ছিলেন?
উত্তর: চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।
১৯. JVP কমিটির পুরো নাম কী?
উত্তর: জওহরলাল-বল্লভভাই-পট্টভি সীতারামাইয়া কমিটি।
২০. ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কবে হয়?
উত্তর: ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে।
২১. রাজাকার বাহিনী কোন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত?
উত্তর: হায়দ্রাবাদ।
২২. দণ্ডকারণ্য প্রকল্প কীসের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল?
উত্তর: পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য।
২৩. ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
উত্তর: জওহরলাল নেহরু।
২৪. পট্টি শ্রীরামুলু কে ছিলেন?
উত্তর: একজন গান্ধীবাদী নেতা, যিনি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের দাবিতে অনশন করে প্রাণত্যাগ করেন।
২৫. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় বসেছিল?
উত্তর: দিল্লিতে।
২৬. ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।
২৭. ‘ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন’ কী?
উত্তর: দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির জন্য স্বাক্ষর করার দলিল।
২৮. ভারত-চীন যুদ্ধ কবে হয়?
উত্তর: ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে।
২৯. ‘পঞ্চশীল’ নীতি কোন দুটি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর: ভারত ও চীনের মধ্যে।
৩০. ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ কে উত্থাপন করেন?
উত্তর: এ. কে. ফজলুল হক।
৩১. ভারতের প্রথম IIT কোথায় স্থাপিত হয়?
উত্তর: খড়গপুরে।
৩২. ভারতের প্রথম পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্র কোনটি?
উত্তর: ট্রম্বেতে অবস্থিত ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC)।
৩৩. ‘মেঘে ঢাকা তারা’ চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
উত্তর: ঋত্বিক ঘটক।
৩৪. স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।
৩৫. ‘धर কমিশন’ কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে।
৩৬. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
উত্তর: মহম্মদ আলি জিন্না।
৩৭. হায়দ্রাবাদের शासकকে কী বলা হত?
উত্তর: নিজাম।
৩৮. ‘জোট নিরপেক্ষ নীতি’র প্রধান রূপকার কে?
উত্তর: জওহরলাল নেহরু।
৩৯. গণপরিষদের খসড়া কমিটি কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট।
৪০. ‘The Story of the Integration of the Indian States’ গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর: ভি. পি. মেনন।
৪১. ভারতের ‘জাতীয় দিবস’ (প্রজাতন্ত্র দিবস) কবে পালিত হয়?
উত্তর: ২৬শে জানুয়ারি।
৪২. ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর কবে ভারতভুক্ত হয়?
উত্তর: ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে (আইনত ১৯৫১)।
৪৩. ভারতের ‘জাতীয় কংগ্রেস’-এর প্রথম সভাপতি (স্বাধীনতার পর) কে ছিলেন?
উত্তর: পট্টভি সীতারামাইয়া।
৪৪. জুনাগড়ের নবাব কে ছিলেন?
উত্তর: তৃতীয় মহব্বত খান।
৪৫. ভারতের সংবিধানে ভারতকে কী ধরনের রাষ্ট্র বলা হয়েছে?
উত্তর: একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।
৪৬. ‘তোবা টেক সিং’ ছোটগল্পটি কার লেখা?
উত্তর: সাদত হাসান মান্টো।
৪৭. কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দল কোনটি ছিল?
উত্তর: ন্যাশনাল কনফারেন্স।
৪৮. রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দুজন সদস্যের নাম লেখো।
উত্তর: কে. এম. পানিক্কর ও হৃদয়নাথ কুঞ্জরু।
৪৯. ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
উত্তর: সুকুমার সেন।
৫০. কোন আইন দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন।
৫১. ‘পেরিয়ার’ নামে কে পরিচিত ছিলেন?
উত্তর: ই. ভি. রামস্বামী নাইকার।
৫২. কোন দেশীয় রাজ্যটি ভারতভুক্তিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি করেছিল?
উত্তর: হায়দ্রাবাদ।
৫৩. ‘UGC’ এর পুরো নাম কী?
উত্তর: University Grants Commission (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন)।
৫৪. ‘উদ্বাস্তু শিবির’-এর একটি ক্যাম্পের নাম লেখো।
উত্তর: শিয়ালদহ ক্যাম্প বা মানা ক্যাম্প।
৫৫. ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়?
উত্তর: ভারী শিল্পের ওপর।
৫৬. ‘আজাদ কাশ্মীর’ কী?
উত্তর: পাকিস্তানের অধিকৃত কাশ্মীর অংশ।
৫৭. স্বাধীন ভারতের প্রথম রেলমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: জন মাথাই।
৫৮. ‘মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন’ কবে পাস হয়?
উত্তর: ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।
৫৯. ‘লাইন অফ কন্ট্রোল’ (LOC) কোন দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত?
উত্তর: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে (কাশ্মীর সীমান্তে)।
৬০. ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: सुचेता কৃপালনী (উত্তরপ্রদেশ)।
গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী – মান ২ (২৫টি)
১. ‘ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন’ বা অন্তর্ভুক্তি দলিল কী?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। যে দলিলে স্বাক্ষর করে কোনো দেশীয় রাজ্য ভারত ইউনিয়নে যোগদান করত, তাকেই ‘ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন’ বা ভারতভুক্তির দলিল বলা হয়।
২. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা কী ছিল?
উত্তর: স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেন। তিনি তাঁর সচিব ভি. পি. মেননের সহায়তায় একদিকে যেমন আলাপ-আলোচনা ও বোঝানোর মাধ্যমে (গাজর নীতি), তেমনই প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে (লাঠি নীতি) অধিকাংশ রাজ্যকে ভারতভুক্ত করেন।
৩. রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৩) কেন গঠিত হয়েছিল?
উত্তর: স্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি তীব্র হয়ে ওঠে। পট্টি শ্রীরামুলুর মৃত্যুর পর অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হলে, সারা দেশে এই দাবি আরও জোরালো হয়। এই প্রেক্ষাপটে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করার জন্য ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার ফজল আলির নেতৃত্বে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করে।
৪. নেহরু-লিয়াকত চুক্তি (১৯৫০) কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
উত্তর: দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু হলে ভারতে এক ব্যাপক উদ্বাস্তু স্রোত আসে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং উভয় দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
৫. জে.ভি.পি. কমিটি কী?
উত্তর: ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি খতিয়ে দেখার জন্য ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সদস্যরা ছিলেন জওহরলাল নেহরু (J), বল্লভভাই প্যাটেল (V) এবং পট্টভি সীতারামাইয়া (P)। তাদের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে এটি ‘জে.ভি.পি. কমিটি’ নামে পরিচিত। এই কমিটি ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবির বিরোধিতা করে।
৬. কাশ্মীর সমস্যাটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল?
উত্তর: দেশভাগের সময় কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিং স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নেন, যদিও রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন মুসলিম। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান সমর্থিত হানাদার বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করলে, রাজা হরি সিং ভারতের কাছে সামরিক সাহায্য চান এবং ‘ভারতভুক্তির দলিলে’ স্বাক্ষর করেন। এর ফলেই কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়।
৭. ‘অপারেশন পোলো’ কী ছিল?
উত্তর: হায়দ্রাবাদের নিজাম ভারতভুক্তিতে অসম্মত হয়ে স্বাধীন থাকার চেষ্টা করেন এবং তাঁর রাজাকার বাহিনী রাজ্যের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে, ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার হায়দ্রাবাদে যে সামরিক অভিযান চালায়, তা ‘অপারেশন পোলো’ নামে পরিচিত। এই অভিযানের ফলেই হায়দ্রাবাদ ভারতভুক্ত হয়।
৮. পট্টি শ্রীরামুলু কে ছিলেন?
উত্তর: পট্টি শ্রীরামুলু ছিলেন একজন গান্ধীবাদী নেতা। তিনি মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে পৃথক ‘অন্ধ্রপ্রদেশ’ রাজ্য গঠনের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। একটানা ৫৮ দিন অনশনের পর ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়, যার ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়।
৯. উদ্বাস্তু সমস্যা বলতে কী বোঝো?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে নবগঠিত পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে নিরাপত্তার খোঁজে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। এই আশ্রয়হীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষদেরই ‘উদ্বাস্তু’ বলা হয়। তাদের আশ্রয়, খাদ্য ও পুনর্বাসনের সমস্যাই ‘উদ্বাস্তু সমস্যা’ নামে পরিচিত।
১০. দণ্ডকারণ্য প্রকল্প কী?
উত্তর: দণ্ডকারণ্য প্রকল্প ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকারের একটি বৃহৎ পরিকল্পনা। ছত্তিশগড় (তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ), ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত জঙ্গলময় অঞ্চল নিয়ে গঠিত দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের জন্য কৃষি ও অন্যান্য কাজের ব্যবস্থা করা হয়।
১১. ভারতের সংবিধানে কাশ্মীরকে কী বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল?
উত্তর: ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান ও আইনসভার ক্ষমতা ছিল। (উল্লেখ্য: ২০১৯ সালে এই ধারাটি বিলুপ্ত করা হয়)।
১২. দেশভাগ সম্পর্কিত দুটি চলচ্চিত্রের নাম লেখো।
উত্তর: দেশভাগ সম্পর্কিত দুটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ এবং এম. এস. সথ্যুর ‘গরম হাওয়া’। এই চলচ্চিত্রগুলিতে দেশভাগের যন্ত্রণা ও উদ্বাস্তু জীবনের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।
১৩. স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব কী ছিল?
উত্তর: ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের প্রথম ও সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এই নির্বাচনের দুটি গুরুত্ব হল: (১) এটি বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছিল, যা ভারতে সফলভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করে। (২) এই নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের সরকার নির্বাচন করে।
১৪. ভি. পি. মেনন স্মরণীয় কেন?
উত্তর: ভি. পি. মেনন ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা এবং দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সচিব। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের ডান হাত হিসেবে কাজ করেন এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কূটনীতি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিষয়ে তাঁর লেখা ‘The Story of the Integration of the Indian States’ একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
১৫. ‘জোট নিরপেক্ষ নীতি’ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুটি প্রধান শক্তি-শিবিরে (আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কোনো সামরিক শিবিরে যোগ না দিয়ে উভয় শিবিরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে স্বাধীনভাবে বিদেশনীতি পরিচালনার যে নীতি গ্রহণ করেন, তাই ‘জোট নিরপেক্ষ নীতি’ নামে পরিচিত।
১৬. ‘মিಶ್ರ অর্থনীতি’ কী?
উত্তর: স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেন, তাতে সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থার সহাবস্থান ছিল। এই নীতিতে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভারী শিল্প ছিল, তেমনই অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও স্বাগত জানানো হয়েছিল। এই দুই ব্যবস্থার সমন্বয়ই ‘মিশ্র অর্থনীতি’ নামে পরিচিত।
১৭. ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ বলতে কী বোঝো?
উত্তর: ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানানো হয়। ফজলুল হক উত্থাপিত এই প্রস্তাবটিই ইতিহাসে ‘লাহোর প্রস্তাব’ বা ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবই পরবর্তীকালে ভারত বিভাগের ভিত্তি রচনা করে।
১৮. জুনাগড় কীভাবে ভারতভুক্ত হয়েছিল?
উত্তর: জুনাগড়ের মুসলিম নবাব পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে, রাজ্যের হিন্দু প্রজারা তার বিরোধিতা করে। ভারত সরকার এই পরিস্থিতিতে সেখানে গণভোটের আয়োজন করে। গণভোটে রাজ্যের প্রায় ৯৯% মানুষ ভারতের পক্ষে রায় দিলে, জুনাগড় ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৯. ‘পঞ্চশীল নীতি’ কী?
উত্তর: ১৯৫৪ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তিতে পাঁচটি নীতি গৃহীত হয়, যা ‘পঞ্চশীল নীতি’ নামে পরিচিত। এই নীতিগুলি হল: (১) পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা, (২) অনাক্রমণ, (৩) অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সাম্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা, এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।
২০. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা কী ছিল?
উত্তর: ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করতে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনাটিই ‘মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা’ নামে পরিচিত।
২১. দেশভাগের ফলে ভারত কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?
উত্তর: দেশভাগের ফলে ভারত দুটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল: (১) উদ্বাস্তু সমস্যা: লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে, যাদের পুনর্বাসন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। (২) অর্থনৈতিক সমস্যা: ভারতের পাট ও তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি সংকটে পড়ে।
২২. গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: গণপরিষদ গঠনের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল: (১) স্বাধীন ভারতের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনা করা। (২) নতুন সংবিধান রচিত ও কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন আইনসভা বা সংসদ হিসেবে কাজ করা।
২৩. ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কী?
উত্তর: দক্ষিণারঞ্জন বসুর লেখা ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ গ্রন্থটি দেশভাগ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথামূলক রচনা। এই গ্রন্থে লেখক পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের করুণ কাহিনি, তাদের ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা এবং নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেছেন।
২৪. ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের দুটি সুপারিশ লেখো।
উত্তর: ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের দুটি সুপারিশ হল: (১) ভাষার ভিত্তিতে ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা। (২) রাজ্যগুলির মধ্যেকার পূর্বতন ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ প্রভৃতি শ্রেণিবিভাগ বাতিল করে দেওয়া।
২৫. দেশীয় রাজ্য বলতে কী বোঝানো হত?
উত্তর: ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রায় ৫৬২টি ছোট-বড় রাজ্য ছিল, যেগুলি সরাসরি ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হত না, বরং স্থানীয় রাজা বা নবাবদের দ্বারা শাসিত হত। এই রাজ্যগুলি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বায়ত্তশাসিত হলেও, ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করত। এই রাজ্যগুলিকেই ‘দেশীয় রাজ্য’ বলা হত।
ঘ) সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী – মান ৪ (২৫টি)
১. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রায় ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যকে ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত করে অখণ্ড ভারত গঠনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এই কারণেই তাঁকে ভারতের ‘লৌহমানব’ বা ‘বিসমার্ক’ বলা হয়।
ভূমিকা:
১. দেশীয় রাজ্য দপ্তর গঠন: প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পৃথক ‘দেশীয় রাজ্য দপ্তর’ গঠন করেন এবং এর সচিব হিসেবে ভি. পি. মেননকে নিয়োগ করেন।
২. সংযুক্তি দলিল (Instrument of Accession): তিনি একটি সংযুক্তি দলিল তৈরি করেন, যেখানে বলা হয় দেশীয় রাজ্যগুলি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের হাতে তুলে দেবে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।
৩. গাজর ও লাঠি নীতি (Carrot and Stick Policy): প্যাটেল একদিকে যেমন আলাপ-আলোচনা, বোঝানো এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি (গাজর) দিয়ে রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্ত করার চেষ্টা করেন, তেমনই অন্যদিকে প্রয়োজনে সামরিক হস্তক্ষেপের (লাঠি) ভয়ও দেখান।
৪. বিশেষ ভূমিকা: জুনাগড়ে গণভোট, হায়দ্রাবাদে ‘অপারেশন পোলো’র মাধ্যমে সামরিক অভিযান এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে তাঁর দৃঢ় ও কূটনৈতিক ভূমিকা ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সুনিশ্চিত করেছিল। তাঁর এই দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলেই একটি খণ্ডিত ভারতের পরিবর্তে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্ম হয়।
২. টীকা লেখো: হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তি।
ভূমিকা: দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ ছিল আয়তনে ও সম্পদে সর্ববৃহৎ। এর শাসক নিজাম ওসমান আলি খান ভারত বা পাকিস্তান কোনোটিতেই যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নিলে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়।
নিজামের ভূমিকা: নিজাম ভারতের সঙ্গে একটি ‘স্থিতাবস্থা’ বা ‘Standstill’ চুক্তি স্বাক্ষর করলেও, গোপনে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে শুরু করেন।
রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার: নিজামের মদতে কাসিম রিজভির নেতৃত্বে ‘রাজাকার’ নামে এক উগ্র সাম্প্রদায়িক আধা-সামরিক বাহিনী রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার, লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।
অপারেশন পোলো: রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠলে এবং ভারতের নিরাপত্তার আশঙ্কা দেখা দিলে, ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ‘অপারেশন পোলো’ নামে সামরিক অভিযান শুরু করে। মাত্র চারদিনের অভিযানে ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দ্রাবাদ দখল করে নেয় এবং নিজাম আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।
ফলাফল: অবশেষে হায়দ্রাবাদ রাজ্যটি ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা পায়।
৩. টীকা লেখো: কাশ্মীরের ভারতভুক্তি।
ভূমিকা: দেশভাগের সময় কাশ্মীরকে নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তা আজও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক জটিল বিষয় হয়ে আছে।
প্রেক্ষাপট: দেশভাগের সময় কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরা বংশের রাজা মহারাজা হরি সিং তাঁর মুসলিম-সংখ্যাগুরু রাজ্যকে নিয়ে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের পক্ষ থেকে জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জিন্না, উভয়েই কাশ্মীরকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।
পাকিস্তানি আক্রমণ: হরি সিং-এর সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর পাকিস্তান-সমর্থিত পাঠান উপজাতি হানাদার বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে এবং শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।
ভারতভুক্তি: এই পরিস্থিতিতে মহারাজা হরি সিং ভারতের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারত সরকার জানায় যে, ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর না করলে সেনা পাঠানো সম্ভব নয়। অবশেষে, ২৬শে অক্টোবর হরি সিং ‘ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন’ বা ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন।
ফলাফল: দলিল স্বাক্ষরের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশ করে এবং হানাদারদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু ততদিনে কাশ্মীরের একটি বড় অংশ পাকিস্তানের দখলে চলে যায়, যা ‘আজাদ কাশ্মীর’ নামে পরিচিত। এই সমস্যাটি রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপিত হলে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়, যা আজও ভারত-পাকিস্তান বিরোধের মূল কারণ।
৪. স্বাধীন ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যার পরিচয় দাও।
ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ভিটেমাটি, সহায়-সম্বল হারিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হয়।
সমস্যার প্রকৃতি:
১. পশ্চিমী উদ্বাস্তু: পশ্চিম পাকিস্তান (পাঞ্জাব ও সিন্ধু) থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ ভারতে চলে আসে। এই আগমন ছিল মূলত এককালীন এবং ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্য দিয়ে।
২. পূর্বী উদ্বাস্তু: পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে হিন্দুদের আগমন ছিল দীর্ঘমেয়াদি এবং মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে। এই ধারা ১৯৬৪ এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে।
৩. পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ: এই বিপুল সংখ্যক আশ্রয়হীন মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও কাজের ব্যবস্থা করা নবগঠিত ভারত সরকারের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল।
৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব: উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে কলকাতা, দিল্লির মতো শহরগুলির ওপর 엄청난 চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলে সামাজিক সংঘাত, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এই সমস্যা স্বাধীন ভারতের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল।
৫. উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে ভারত সরকারের উদ্যোগ আলোচনা করো।
ভূমিকা: দেশভাগের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা করা ছিল স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ। সরকার এই সমস্যা সমাধানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
উদ্যোগসমূহ:
১. ত্রাণ ও আশ্রয়: সরকার প্রথমে স্কুল-কলেজ, ধর্মশালা এবং সরকারি দপ্তরে অস্থায়ী শিবির খুলে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে।
২. পুনর্বাসন দপ্তর: উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য একটি পৃথক ‘ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রক’ গঠন করা হয়।
৩. অর্থনৈতিক সহায়তা: উদ্বাস্তুদের ব্যবসা শুরু করার জন্য ঋণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে কৃষকদের জমি বণ্টন করা হয়।
৪. নতুন উপনিবেশ স্থাপন: দিল্লি, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের জন্য একাধিক নতুন কলোনি বা উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়। যেমন – দিল্লির লাজপত নগর বা পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে।
৫. দণ্ডকারণ্য প্রকল্প: পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ‘দণ্ডকারণ্য প্রকল্প’ গ্রহণ করা হয়।
এই সমস্ত উদ্যোগ সত্ত্বেও, উদ্বাস্তু সমস্যা, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমস্যা, একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে থেকে যায়।
৬. ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
প্রেক্ষাপট:
স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের পক্ষে ছিল। স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক সুবিধা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত থেকে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি ওঠে।
আন্দোলন ও কমিশন: সরকার প্রথমে ‘ধর কমিশন’ এবং পরে ‘জে.ভি.পি. কমিটি’ নিয়োগ করে, কিন্তু দুটি কমিটিই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের বিরোধিতা করে। এরপর মাদ্রাজ প্রদেশে তেলেগু ভাষাভাষীদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবিতে গান্ধীবাদী নেতা পট্টি শ্রীরামুলু ৫৮ দিন অনশন করে প্রাণত্যাগ করেন। এর ফলে সারা দেশে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। চাপের মুখে সরকার ১৯৫৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করে এবং ফজল আলির নেতৃত্বে ‘রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন’ নিয়োগ করে।
গুরুত্ব:
১. এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ‘রাজ্য পুনর্গঠন আইন’ পাস হয় এবং ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠিত হয়।
২. ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী হয় এবং আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।
৩. এটি ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে রোধ করে এবং জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করে।
৭. টীকা লেখো: রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (SRC)।
ভূমিকা: ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি খতিয়ে দেখার জন্য ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার যে কমিশন গঠন করে, তা ‘রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন’ নামে পরিচিত।
গঠন: সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ফজল আলি ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। এর অপর দুই সদস্য ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কে. এম. পানিক্কর এবং সমাজসেবী হৃদয়নাথ কুঞ্জরু।
সুপারিশ: কমিশন ১৯৫৫ সালে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। এর প্রধান সুপারিশগুলি ছিল:
১. মূলত ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করা যেতে পারে, তবে দেশের একতা ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
২. ‘এক ভাষা, এক রাজ্য’ – এই নীতিকে পুরোপুরি গ্রহণ না করে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলিও বিবেচনা করতে হবে।
৩. রাজ্যগুলির পূর্বতন শ্রেণিবিভাগ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’) বাতিল করে শুধুমাত্র ‘রাজ্য’ ও ‘কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল’ – এই দুটি বিভাগ চালু করা।
৪. বোম্বাইকে দ্বিভাষিক রাজ্য হিসেবে রাখা এবং পাঞ্জাবকে বিভক্ত না করা।
ফলাফল: এই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে কিছু পরিবর্তনসহ ১৯৫৬ সালে ‘রাজ্য পুনর্গঠন আইন’ পাস হয় এবং ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
৮. নেহরু-লিয়াকত চুক্তি বা দিল্লি চুক্তির (১৯৫০) প্রেক্ষাপট ও শর্তগুলি লেখো।
প্রেক্ষাপট: দেশভাগের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, সম্পত্তি দখল এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করার মতো ঘটনা ঘটছিল। ১৯৫০ সালের শুরুতে এই অত্যাচার ভয়াবহ রূপ নিলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, চলে আসতে শুরু করে। এর ফলে ভারতেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং একটি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়।
শর্তাবলী: এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর প্রধান শর্তগুলি হল:
১. উভয় দেশ তাদের নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা এবং নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার দেবে।
২. উভয় দেশে ‘সংখ্যালঘু কমিশন’ গঠন করা হবে।
৩. যারা দেশত্যাগ করেছে, তারা ফিরে এসে নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করার বা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার পাবে।
৪. জোর করে ধর্মান্তরিত করাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।
৯. স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
ভূমিকা: স্বাধীন ভারতের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল গণপরিষদের ওপর।
গণপরিষদ: ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী গণপরিষদ গঠিত হয়। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন এর স্থায়ী সভাপতি।
খসড়া কমিটি: সংবিধানের একটি খসড়া বা রূপরেখা তৈরির জন্য ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে একটি ‘খসড়া কমিটি’ (Drafting Committee) গঠন করা হয়। এই কমিটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধান থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে ভারতের জন্য একটি খসড়া প্রস্তুত করে।
গ্রহণ ও কার্যকর: খসড়া সংবিধানটি নিয়ে গণপরিষদে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর কিছু সংশোধনসহ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এটি গৃহীত হয়। অবশেষে, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি এই নতুন সংবিধান কার্যকর হয় এবং ভারত একটি ‘সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
১০. স্বাধীনোত্তর ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলন কীভাবে হয়েছিল?
ভূমিকা: স্বাধীন ভারতে রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভাষা একটি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। কংগ্রেস স্বাধীনতার আগে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও, স্বাধীনতার পর জাতীয় সংহতির যুক্তিতে তারা এই দাবি থেকে সরে আসে।
আন্দোলনের পর্যায়:
১. প্রাথমিক বিরোধিতা: সরকার নিযুক্ত ‘ধর কমিশন’ (১৯৪৮) এবং কংগ্রেসের ‘জে.ভি.পি. কমিটি’ (১৯৪৯) উভয়ই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের বিরোধিতা করে।
২. পট্টি শ্রীরামুলুর আত্মত্যাগ: এই পরিস্থিতিতে, মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে পৃথক তেলেগুভাষী রাজ্য ‘অন্ধ্রপ্রদেশ’-এর দাবিতে গান্ধীবাদী নেতা পট্টি শ্রীরামুলু আমরণ অনশন শুরু করেন। ৫৮ দিন অনশনের পর তাঁর মৃত্যু হলে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তীব্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।
৩. অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন ও কমিশন নিয়োগ: আন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৫৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করতে বাধ্য হয়। এরপর সারা দেশে এই দাবি জোরালো হলে, সরকার ফজল আলির নেতৃত্বে ‘রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন’ নিয়োগ করে।
৪. আইন পাস: এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ‘রাজ্য পুনর্গঠন আইন’ পাস হয় এবং ভাষার ভিত্তিতে ভারতে ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠিত হয়।
১১. আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথাকে কীভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়?
ভূমিকা: আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। এগুলি থেকে সমসাময়িক কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এক জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়।
ব্যবহার:
১. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানা: জওহরলাল নেহরুর ‘অ্যান অটোবায়োগ্রাফি’ বা মৌলানা আজাদের ‘ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম’ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, নেতাদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ঘটনার পেছনের কারণ জানা যায়।
২. সামাজিক চিত্র: দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা বোঝার জন্য দক্ষিণারঞ্জন বসুর ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ বা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ‘দ্য মার্জিনাল মেন’-এর মতো স্মৃতিকথা অপরিহার্য। এগুলি থেকে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ, তাদের সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা জানা যায়।
৩. ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি: আত্মজীবনী লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে, যা অনেক সময় সরকারি নথিতে পাওয়া যায় না। এটি ইতিহাসকে এক মানবিক মাত্রা দেয়।
সীমাবদ্ধতা: তবে এই উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হয়, কারণ লেখক অনেক সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে ঘটনাকে বিকৃত বা অতিরঞ্জিত করতে পারেন। তাই অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিলিয়ে এগুলিকে ব্যবহার করা উচিত।
১২. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির দলিল বা ‘Instrument of Accession’-এর মূল বিষয়বস্তু কী ছিল?
ভূমিকা: ‘ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন’ ছিল একটি আইনগত দলিল, যার মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত বা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিত। সর্দার প্যাটেল ও ভি. পি. মেনন এই দলিলের খসড়া তৈরি করেছিলেন।
মূল বিষয়বস্তু:
১. দেশীয় রাজ্যগুলি শুধুমাত্র তিনটি প্রধান বিষয় – প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে তুলে দেবে।
২. এই তিনটি বিষয় ছাড়া রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শাসকের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকবে। ভারত সরকার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করবে না।
৩. দেশীয় শাসকরা তাদের উপাধি, মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা (যেমন – প্রিভি পার্স বা রাজন্য ভাতা) আগের মতোই ভোগ করবেন।
৪. এই দলিলে স্বাক্ষরের অর্থ এই নয় যে, রাজ্যটিকে ভারতের সংবিধান মেনে নিতেই হবে। সংবিধান গ্রহণের বিষয়টি তারা পরে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
এই নমনীয় শর্তাবলীর কারণেই অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য সহজেই ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেছিল।
১৩. স্বাধীন ভারতের প্রথম তিন দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছিলেন আধুনিকমনস্ক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ছাড়া ভারতের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা দূর করা সম্ভব নয়।
ভূমিকা:
১. গবেষণাগার স্থাপন: তাঁর উদ্যোগে সারা দেশে একাধিক জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories) স্থাপিত হয়, যেমন – ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি ইত্যাদি।
২. পারমাণবিক কর্মসূচি: তিনি হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার নেতৃত্বে ভারতের পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচির সূচনা করেন এবং ‘ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার’ (BARC) প্রতিষ্ঠা করেন।
৩. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান: তাঁর সময়েই ভারতের প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) খড়গপুরে (১৯৫১) স্থাপিত হয়। এর পর আরও একাধিক IIT প্রতিষ্ঠা করা হয়।
৪. মহাকাশ গবেষণা: ১৯৬২ সালে তাঁর উদ্যোগেই ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ’ (INCOSPAR) গঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে ‘ISRO’-তে রূপান্তরিত হয়। নেহরুর এই দূরদর্শী পদক্ষেপগুলিই ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছিল।
১৪. জুনাগড়ের ভারতভুক্তি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।
ভূমিকা: জুনাগড় ছিল গুজরাটের একটি ছোট দেশীয় রাজ্য। এর ভারতভুক্তি ছিল সর্দার প্যাটেলের কূটনীতির এক বড় সাফল্য।
সমস্যার সূত্রপাত: জুনাগড়ের শাসক ছিলেন মুসলিম নবাব তৃতীয় মহব্বত খান, কিন্তু রাজ্যের প্রায় ৮০% প্রজা ছিল হিন্দু। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট নবাব ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।
ভারতের প্রতিক্রিয়া: ভারত এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি। ভারত জুনাগড়ের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে এবং সেখানকার প্রজাদের নিয়ে ‘আর্জি হুকুমত’ বা অস্থায়ী সরকার গঠনে সমর্থন জানায়।
গণভোট ও অন্তর্ভুক্তি: প্রজাবিদ্রোহ এবং ভারতীয় চাপের মুখে নবাব পাকিস্তানে পালিয়ে যান। এরপর ভারত সরকার সেখানে একটি গণভোটের আয়োজন করে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এই গণভোটে রাজ্যের প্রায় ৯৯% মানুষ ভারতের পক্ষে রায় দেয়। এই গণভোটের রায়ের ভিত্তিতেই জুনাগড় আইনসম্মতভাবে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৫. ভারতের সংবিধানে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ভূমিকা আলোচনা করো।
ভূমিকা: ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরকে ‘ভারতীয় সংবিধানের জনক’ বলা হয়। সংবিধান রচনায় তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক এবং অবিস্মরণীয়।
ভূমিকা:
১. খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান: তিনি গণপরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি – ‘খসড়া কমিটি’র চেয়ারম্যান ছিলেন। সংবিধানের মূল কাঠামো তৈরি এবং তার প্রতিটি ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রচনা করার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।
২. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: তিনি সংবিধানে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (১৭ নং ধারা) এবং দলিত ও আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।
৩. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্থাপন: তিনি সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, আইনের শাসন এবং মৌলিক অধিকারের মতো আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে স্থান দেন।
৪. সমন্বয় সাধন: গণপরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে, তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, যুক্তি এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংবিধান রচনায় সাহায্য করেন।
১৬. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তিকরণে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?
ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার বা স্বাধীন থাকার স্বাধীনতা দেয়। এই পরিস্থিতিতে, নবগঠিত ভারত সরকার একটি ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড ভারত গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।
দৃষ্টিভঙ্গি:
১. আলাপ-আলোচনা ও বোঝানো: সরকারের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাপ-আলোচনা ও বোঝানোর মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে ভারতভুক্ত করা। সর্দার প্যাটেল ও ভি. পি. মেনন দেশীয় শাসকদের বোঝান যে, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাদের পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয় এবং ভারত ইউনিয়নে যোগ দিলেই তাদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা বজায় থাকবে।
২. নমনীয় শর্ত: রাজ্যগুলিকে আকৃষ্ট করার জন্য ‘ইন্সট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন’-এ নমনীয় শর্ত রাখা হয়। শাসকরা অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা (প্রিভি পার্স) ভোগ করার অধিকার পায়।
৩. প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি: যে সমস্ত রাজ্য ভারতভুক্তিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, তাদের ওপর অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়।
৪. সামরিক হস্তক্ষেপ: যখন আলাপ-আলোচনা ও চাপ সৃষ্টি ব্যর্থ হয় (যেমন – হায়দ্রাবাদ), তখন দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সরকার সামরিক হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধা করেনি।
১৭. দেশভাগ নিয়ে রচিত সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের গুরুত্ব কী?
ভূমিকা: দেশভাগ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না, এটি ছিল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসা এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের যন্ত্রণা, রক্তপাত ও মর্মবেদনা সরকারি নথিতে পাওয়া যায় না। এখানেই দেশভাগ নিয়ে রচিত সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের গুরুত্ব।
গুরুত্ব:
১. মানবিক দলিল: খুশবন্ত সিং-এর ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’, সাদত হাসান মান্টোর ‘তোবা টেক সিং’, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’-এর মতো সাহিত্য এবং ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ বা এম. এস. সথ্যুর ‘গরম হাওয়া’-র মতো চলচ্চিত্র দেশভাগের মানবিক দিকটিকে তুলে ধরে।
২. সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ: এগুলি আমাদের দেখায় যে, দেশভাগের ফলে সাধারণ মানুষ কীভাবে তাদের ভিটেমাটি, সংস্কৃতি ও পরিচয় হারিয়েছিল।
৩. ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণ: এই শিল্পকর্মগুলি ইতিহাসের সেই শূন্যস্থান পূরণ করে, যা তথ্যের আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। এগুলি ইতিহাসকে আরও জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী করে তোলে।
৪. সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা: এই সাহিত্য ও চলচ্চিত্রগুলি দেশভাগের ভয়াবহতা দেখিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বার্তা দেয়।
১৮. স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬) লক্ষ্য কী ছিল?
ভূমিকা: সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে ১৯৫০ সালে ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা।
লক্ষ্যসমূহ:
১. কৃষি উন্নয়ন: এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য সংকট দূর করা। এই উদ্দেশ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভাকরা-নাঙ্গাল, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC), হীরাকুদ-এর মতো বৃহৎ বাঁধ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
২. উদ্বাস্তু পুনর্বাসন: দেশভাগের ফলে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ছিল এই পরিকল্পনার একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
৩. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা।
৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি: দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।
১৯. ভারতের সংবিধানকে ‘যুক্তরাষ্ট্রীয়’ (Federal) বলা হয় কেন? এর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
ভূমিকা: ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে একটি ‘রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন’ (Union of States) বলা হলেও, এর কাঠামো মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে বোঝায় যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন থাকে।
যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য:
১. ক্ষমতার বণ্টন: সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে তিনটি তালিকার মাধ্যমে ভাগ করে দিয়েছে – কেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
২. লিখিত ও দুঃষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবর্তন করতে হলে संसद-এর বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অর্ধেক রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়, যা এর দুঃষ্পরিবর্তনীয় চরিত্র প্রমাণ করে।
৩. নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা: ভারতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা রয়েছে (সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট), যা সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করে।
৪. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা (লোকসভা ও রাজ্যসভা) রয়েছে, যেখানে রাজ্যসভা রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।
২০. ভারতের স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭) এর প্রধান দুটি ধারা কী ছিল?
ভূমিকা: ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হওয়া ‘ভারতীয় স্বাধীনতা আইন’ (Indian Independence Act, 1947)-এর মাধ্যমেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে।
প্রধান ধারা:
১. দুটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি: এই আইনে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক ও স্বাধীন ডোমিনিয়ন বা রাষ্ট্র গঠন করা হবে। বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দুটিকে ভাগ করা হবে।
২. ক্ষমতা হস্তান্তর: উভয় ডোমিনিয়নের জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠন করা হবে, যারা নিজেদের দেশের জন্য সংবিধান রচনা করবে। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত এই গণপরিষদগুলিই আইনসভা হিসেবে কাজ করবে এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।
৩. দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা: দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর থেকে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটবে। তারা ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে, অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে। এই ধারাটিই পরবর্তীকালে দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সমস্যার জন্ম দেয়।
২১. উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা কী ছিল?
ভূমিকা: দেশভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যার সবচেয়ে বেশি চাপ পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ওপর। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ভূমিকা:
১. প্রাথমিক ত্রাণ: সরকার প্রথমে শিয়ালদহ স্টেশন ও অন্যান্য জায়গায় অস্থায়ী শিবির খুলে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও বিনামূল্যে খাদ্য (ডোল) বিতরণের ব্যবস্থা করে।
২. কলোনি স্থাপন: কলকাতা ও তার আশেপাশে বহু জবরদখল কলোনি গড়ে উঠলে, সরকার পরবর্তীকালে সেগুলিকে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া সরকার নিজেও পরিকল্পিতভাবে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তোলে, যেমন – বাঘা যতীন, বিজয়গড়, নাকতলা ইত্যাদি।
৩. শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন: উদ্বাস্তুদের সন্তানদের জন্য নতুন স্কুল-কলেজ স্থাপন করা হয় এবং তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
৪. কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে এবং দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মতো পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করে।
২২. ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি কীভাবে নেওয়া হয়েছিল?
ভূমিকা: ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল সদ্য স্বাধীন, বিশাল ও নিরক্ষর একটি দেশের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। নির্বাচন কমিশন সুকুমার সেনের নেতৃত্বে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে।
প্রস্তুতি:
১. ভোটার তালিকা প্রস্তুত: প্রায় ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম নথিভুক্ত করে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়, যা ছিল এক দুরূহ কাজ।
২. নির্বাচনী ক্ষেত্র নির্ধারণ: সারা দেশে লোকসভা ও বিধানসভার জন্য প্রায় ৪,৫০০টি আসন এবং নির্বাচনী ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়।
৩. প্রতীক ব্যবস্থা চালু: দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর হওয়ায়, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য পৃথক প্রতীক (যেমন – কংগ্রেসের জোড়া বলদ, কমিউনিস্ট পার্টির কাস্তে-ধানের শীষ) ব্যবস্থা চালু করা হয়।
৪. ভোটগ্রহণ ও গণনা: প্রায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মীকে ভোটগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছাপিয়ে সারা দেশে পাঠানো হয়। এই ব্যাপক প্রস্তুতিই নির্বাচনকে সফল করে তুলেছিল।
২৩. টীকা লেখো: নেহরুর জোট নিরপেক্ষ নীতি।
ভূমিকা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুটি বিরোধী শক্তি-শিবিরে (পুঁজিবাদী আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন) বিভক্ত হয়ে পড়লে এক ‘ঠান্ডা লড়াই’-এর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এক স্বতন্ত্র বিদেশনীতি গ্রহণ করেন, যা ‘জোট নিরপেক্ষ নীতি’ নামে পরিচিত।
মূল কথা: এই নীতির মূল কথা হল, ভারত কোনো সামরিক শিবিরে যোগ দেবে না, তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নও থাকবে না। ভারত প্রতিটি আন্তর্জাতিক বিষয়কে তার গুণাগুণ বিচার করে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত জানাবে এবং উভয় শিবিরের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে।
উদ্দেশ্য: এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) ভারতের সদ্য অর্জিত সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা, (২) ঠান্ডা লড়াইয়ের উত্তেজনা থেকে দূরে থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া, এবং (৩) বিশ্বে শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।
ফলাফল: নেহরুর নেতৃত্বে ভারত, যুগোস্লাভিয়ার টিটো এবং মিশরের নাসেরের সঙ্গে মিলে ‘জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন’ (NAM) গড়ে তোলেন, যা সদ্য স্বাধীন হওয়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।
২৪. ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।
সপক্ষে যুক্তি:
১. ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হলে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজ এবং শিক্ষা মাতৃভাষায় পরিচালনা করা সহজ হয়, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক।
২. এটি আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশকে উৎসাহিত করে।
৩. একই ভাষাভাষী মানুষ একটি রাজ্যের অধীনে এলে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি পায়।
বিপক্ষে যুক্তি:
১. জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতারা আশঙ্কা করেছিলেন যে, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য ভাগ করলে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদ বৃদ্ধি পাবে এবং তা ভারতের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক হবে।
২. এর ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমানা নিয়ে বিবাদ দেখা দিতে পারে।
৩. বহুভাষিক শহরগুলিকে (যেমন – বোম্বাই) কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে।
২৫. ভারত সরকার কীভাবে গোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল?
ভূমিকা: ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও গোয়া, দমন ও দিউ পোর্তুগালের উপনিবেশ হিসেবে থেকে যায়। ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলি হস্তান্তরের দাবি জানালেও, পোর্তুগালের স্বৈরশাসক সালজার তা প্রত্যাখ্যান করেন।
আন্দোলন: গোয়ার অভ্যন্তরে রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে آزادی আন্দোলন শুরু হয়। ভারত সরকার গোয়ার ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে।
সামরিক অভিযান: শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান না হওয়ায় এবং গোয়ায় ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী ‘অপারেশন বিজয়’ নামে এক সামরিক অভিযান শুরু করে।
অন্তর্ভুক্তি: মাত্র ৩৬ ঘণ্টার অভিযানে ভারতীয় সেনা গোয়া, দমন ও দিউ দখল করে নেয় এবং পোর্তুগিজ গভর্নর আত্মসমর্পণ করেন। এইভাবে গোয়া ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।
Class 10 History উত্তর- ঔপনিবেশিক ভারত : বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব Question Answer MCQ,অতি-সংক্ষিপ্ত, ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উত্তর : class 10 উত্তর- ঔপনিবেশিক ভারত : বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব প্রশ্ন উত্তর